এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের চতুর্থ পাঠের প্রথম অধ্যায়, ‘খেয়া’ -এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে কবির পরিচিতি, কবিতার উৎস, কবিতার পাঠপ্রসঙ্গ, কবিতার সারসংক্ষেপ, কবিতার নামকরণ এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এই আর্টিকেলটি আপনাদের ‘খেয়া’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবে এবং কবিতাটি ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া, নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে কবি ও কবিতার সারসংক্ষেপ সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে, তাই এই তথ্যগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
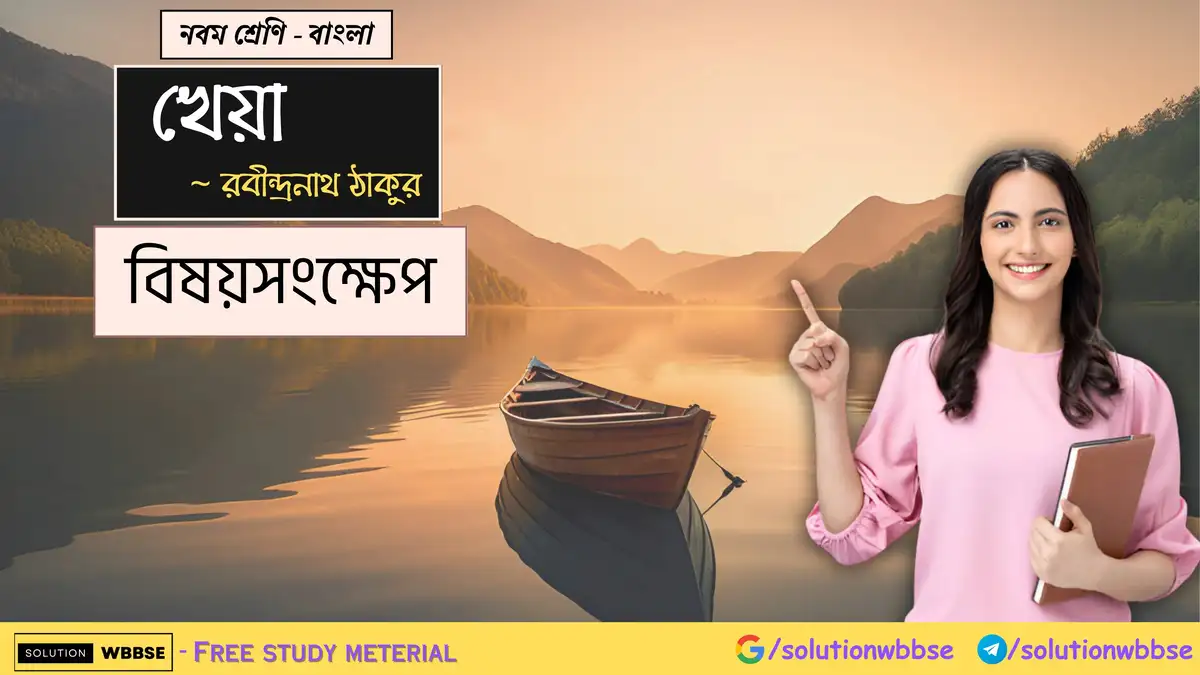
‘খেয়া’ কবিতার কবি পরিচিতি
লালসা, হিংসা, হানাহানির তীব্রতায় জর্জরিত বিশ্বকে যিনি মানবপ্রেমের আদর্শ, কর্ম প্রেরণার মধ্য দিয়ে মানবধর্মের দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থ অর্থে ভারতাত্মার মুক্তিদাতা, তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারা বিস্ময় সৃষ্টি করে। কবিতা, গান, ছোটোগল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার মধ্য দিয়ে তিনি দেশ ও জাতির জীবনে সর্বাত্মকভাবে মুক্তির পথিকৃৎ।
জন্ম
1861 খ্রিস্টাব্দের 7 মে (1268 বঙ্গাব্দের 25 বৈশাখ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান রবীন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন তৎকালীন সম্মানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা
পাঁচ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ক্যালকাটা ট্রেনিং আকাডেমি’-র শিশুশ্রেণিতে ভরতি হন। অন্য মতে তিনি শিশু বয়সে প্রথম ভরতি হন ‘ওরিয়েন্টাল সেমিনারি’-তে। এরপর ‘নর্ম্যাল স্কুল’, ‘বেঙ্গল আকাডেমি’, ‘সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে’ তিনি পড়েছিলেন। প্রথাগত শিক্ষায় কোনোভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি কবি। একারণে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর শিক্ষাপর্ব আরম্ভ করিয়েছিলেন। সতেরো বছর বয়সে ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়তে গেলেও তিনি পড়াশোনা অসম্পূর্ণ রেখেই ফিরে আসেন। ছোটোবেলা থেকেই সাহিত্যচর্চার প্রতি আকর্ষণ ছিল তাঁর। প্রথাগত শিক্ষার শংসাপত্র ছাড়াই তিনি বিশ্বখ্যাতির শীর্ষে অবতরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রতি অগাধ ভালোবাসাই এই পরিণামের মূল কারণ। শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চাই নয় পাশাপাশি সংগীতচর্চা, চিত্রাঙ্কন চর্চাও করতেন তিনি।
জ্যেষ্ঠ দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৌঠান কাদম্বরী দেবীর স্নেহসান্নিধ্যে তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। সতেরো বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গেলেও, তা সম্পূর্ণ হয়নি।
রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘হিন্দুমেলার উপহার’। এখানে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভারতসংগীত’ কবিতার প্রভাব রয়েছে। মাত্র ছয়-সাত বছর বয়সে তিনি প্রথম ছড়া লিখেছিলেন। এরপর আট বছর বয়সে লেখেন ‘অভিলাষ’ কবিতাটি, যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক জীবন
1883 খ্রিস্টাব্দের 9 ডিসেম্বর (1290 বঙ্গাব্দের 24 অগ্রহায়ণ) যশোহরের ফুলতলি গ্রামের বেণীমাধব রায়চৌধুরীর দশম বর্ষীয়া কন্যা ভবতারিণী (মৃণালিনী) দেবীর সঙ্গে কবির বিবাহ হয়। ঠাকুর পরিবারের জামাতা সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের ওপর জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব এলে প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়। রবীন্দ্রনাথের তিন কন্যা – মাধুরীলতা, রেণুকা, মীরা এবং দুই পুত্র-রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধের জাগরণ
পারিবারিক পরিবেশে তাঁর মধ্যে দেশাত্মবোধের জন্ম হয়। তাঁর প্রেরণা জাতীয় আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন। রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন এবং ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ গানটি আজও স্মরণীয়। ইংরেজদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি মুখর ছিলেন আবার গান্ধিজির চরকা কাটার বিষয়টিকেও সর্বাংশে মান্য করতে পারেননি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করেন। হিজলি জেলে বন্দিদের হত্যার প্রতিবাদে তিনি ‘প্রশ্ন’ কবিতাটি লেখেন। দুটি বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে ভীষণভাবে পীড়া দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর দিনগুলোর কথা ভেবে অসুস্থ শরীরে যেমন নিত্য সংবাদ নিতেন তেমন কবিতা লিখে তীব্র প্রতিবাদেও তিনি মুখর হয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা
শিক্ষাবিদ মানুষটি 1901 খ্রিস্টাব্দে বীরভূম জেলার বোলপুরে ভারতীয় সংস্কৃতির ব্রহ্মাচর্যাশ্রম আদর্শে ‘শান্তিনিকেতন’ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এর দ্বারা তিনি শিক্ষার উপর জড়ত্ব, প্রাণহীনতা, শাস্তিদান প্রভৃতির প্রতিবাদ করেছিলেন। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে তিনি ‘শিক্ষা’ (1908 খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এই শান্তিনিকেতন পর্বে 1913 খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ ‘Song offerings’ -এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যসম্ভার
সাহিত্যের সমস্ত শাখায় ছিল রবীন্দ্রনাথের অবাধ বিচরণ। দশ হাজার কবিতা, প্রায় আড়াই হাজার গান, বারোটি উপন্যাস, ছত্রিশটি নাটক-নাটিকা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রবন্ধ ও অসংখ্য ছবি তাঁর সৃষ্টিশীলতার পরিচয় বহন করে কালোত্তীর্ণ হয়ে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে উপনীত করেছে। এমন বিচিত্র প্রতিভার মানুষ বিশ্বে আর জন্মাননি, যিনি বিশ্বমানবের কল্যাণে ও সাহিত্যসৃষ্টির মহনীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। কবির165টি ছোটোগল্প বিশ্বের গল্পসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর বিশিষ্ট কাব্যগুলি হল – ‘কড়ি ও কোমল’, ‘মানসী’, ‘চিত্রা’, ‘চৈতালি’, ‘কল্পনা’, ‘কথা ও কাহিনী’, ‘নৈবেদ্য’, ‘খেয়া’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘বলাকা’, ‘পূরবী’, ‘পুনশ্চ’, ‘সেঁজুতি’, ‘রোগশয্যায়’, ‘আরোগ্য’, ‘জন্মদিনে’ ইত্যাদি। উপন্যাসকর্ম হল – ‘করুণা’, ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’, ‘রাজর্ষি’, ‘চোখের বালি’, ‘নৌকাডুবি’, ‘গোরা’, ‘ঘরে-বাইরে’, ‘যোগাযোগ’, ‘শেষের কবিতা’ ইত্যাদি। বিশিষ্ট নাট্যকর্ম হল – ‘বিসর্জন’, ‘রাজা’, ‘ডাকঘর’, ‘অচলায়তন’, ‘মুক্তধারা’, ‘রক্তকরবী’, ‘কালের যাত্রা’ ইত্যাদি। প্রবন্ধসাহিত্য – ‘সাহিত্য’, ‘স্বদেশ’, ‘ধর্ম’, ‘কালান্তর’, ‘শিক্ষা’ ইত্যাদি। ভ্রমণবৃত্তান্ত- ‘রাশিয়ার চিঠি’ (1931 খ্রিস্টাব্দ), ‘জাপান যাত্রী’, ‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’ ইত্যাদি। এ ছাড়া ‘ছিন্নপত্র’ ও অন্যান্য পত্রাবলির পাশে আত্মকথনধর্মী রচনা ‘জীবনস্মৃতি’ (1912 খ্রিস্টাব্দে) ও ‘ছেলেবেলা’ (1940 খ্রিস্টাব্দে) তাঁর সাহিত্যকর্মের অপরিমেয় সম্পদ।
বিদেশ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচার করেছিলেন শান্তির ললিত বাণী। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে তিনি সুন্দরের উপাসনার পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর কাছে দেশপ্রেম অর্থে মানবতা তথা মানবপ্রেম। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবপ্রেমের মধ্য দিয়েই মানুষ যথার্থ দেশপ্রেমে পৌঁছোয়। অস্ট্রেলিয়া বাদ দিয়ে তিনি 34বার বিদেশভ্রমণ করেছেন এবং বিশ্বমানবকে শুনিয়েছেন ভারতমাতার যথার্থ মর্মবাণী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
1941 খ্রিস্টাব্দের 7 আগস্ট (1348 বঙ্গাব্দের 22 শ্রাবণ) বেলা 12টা 10 মিনিটে 81 বছর বয়সে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেহত্যাগ করেন।
‘খেয়া’ কবিতার উৎস
রবীন্দ্রকাব্য ধারার দ্বিতীয় পর্বে ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 1896 খ্রিস্টাব্দে। আমাদের পাঠ্য ‘খেয়া’ কবিতাটি ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। ‘চৈতালি’-র অন্তর্গত ‘খেয়া’ কবিতাটির রচনাকাল 18 চৈত্র 1302 বঙ্গাব্দ।
‘খেয়া’ কবিতার পাঠপ্রসঙ্গ
নিসর্গসৌন্দর্য ও মানবপ্রেমের সুগভীর প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলিতে। ইউরোপীয় ভাবধারার অভিঘাত ও স্বাদেশিকতার অভ্যুত্থানের মাঝে রবীন্দ্র-ভাবনা দোলায়িত হয়েছে। কবির সনেট রচনার তাগিদ সম্ভবত সেখান থেকেই। ‘চৈতালি’ কাব্যের বেশিরভাগ কবিতাই এই সনেটধর্মী। পাঠ্য ‘খেয়া’ কবিতাটিও একটি পূর্ণাঙ্গ সনেট। শৈলীর দিক থেকে কবি আলোচ্য কবিতায় চতুর্দশপদী কবিতার কাঠামোকে গ্রহণ করে এক শাশ্বত জীবনভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ছোটো পরিসরে।
কবি তখন জমিদারির কাজে নদীবক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর। কবির বোট যেমন – জল ছুঁয়ে থেকেছে অবিরাম, কবির মন তেমনি সারাক্ষণ মগ্ন হয়ে থেকেছে নদীমাতৃক বাংলার নিসর্গ সৌন্দর্য আর নদীতীরবর্তী মানুষের সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবন দর্শনে। কবি প্রকৃতিলগ্ন জীবনকে দেখে মহাজীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। দৈনন্দিন জীবনের পঙ্গুতা, দৈন্যতায় পীড়িত হয়েও ঋষি কবি সুবিশাল প্রেক্ষাপটে জীবনকে অবলোকন করেছেন আলোচ্য কবিতায়। নিভৃতে জীবননদীর তীরে বসে কবির সে আত্মোপলব্ধি এক প্রসারিত শান্তির অনুভূতিতে ভরিয়ে দিয়েছে তাঁর জীবনতরিকে।
‘খেয়া’ কবিতার বিষয়সংক্ষেপ
সকাল থেকে সন্ধে নিরন্তর নদীস্রোতে খেয়া নৌকা পারাপার করে। নিবিড় সম্পর্কে অন্বিত নদীতীরবর্তী দুটি গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এই খেয়া। দুই গ্রামের মানুষ কেউ ঘরে আসে আবার কেউ ঘর থেকে যায়। অন্যদিকে নিত্য-নতুন সমস্যায় পৃথিবীতে দ্বন্দু ‘লেগেই থাকে। সোনার মুকুটের লোভে কত রক্তপ্রবাহ ফেনিয়ে উঠে প্রতিমুহূর্তে। আর এইসব সর্বনাশা সংঘাত নিত্য নতুন ইতিহাস রচনা করে। সভ্যতার নতুন নতুন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কখনও ওঠে সুধা, কখনও বা হলাহল। সর্বনাশা এই সভ্যতা থেকে বহুদূরবর্তী নদীতীরের দুটি গ্রাম, তারা কেউ কারোর নাম না জানলেও পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। খেয়া নৌকা অবিরাম নদীস্রোতে চলাচল করে মানবজীবন প্রবাহকে বহমান রাখে।
মানবসভ্যতার অনিবার্য প্রবাহকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের প্রসারিত আঙিনা থেকে অবলোকন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখেছেন তা বিবর্তনের পথে পথে নানান বাঁকে প্রবাহিত হয়েছে, এসেছে বিচিত্র উত্থান পতন। ক্ষমতার দম্ভে কখনও সে কম্পিত হয়েছে, কখনও আবার হিংসায় উন্মত্ত হয়েছে। সংক্ষুব্ধ প্রবাহপথে সে চলেছে নির্বিকার, থেকেছে উদাসীন। সবার অলক্ষ্যে যে জীবনধারা বয়ে চলেছে, তা যেন ক্লান্তিহীন; সে ধারা উত্তেজিত-উন্মাদ উদাসীন। দুই পারের নদীতটকে জীবনরসে আর্দ্র করে মানবসভ্যতা বয়ে চলেছে অনন্তের উদ্দেশে। নবীনের আগমন ঘটেছে, প্রবীণ চলে গেছে দূরে – কিন্তু তার চলন অবরুদ্ধ হয়নি; ধীর-নিশ্চিত-গতিশীল অথচ নিরুচ্চারিত থেকে মানবসভ্যতার মহৎ প্রবাহ বয়ে চলেছে। খেয়াতরি-দুই তীর-যাত্রীদল-দুই গ্রাম-নদী স্রোতের শাশ্বত উপস্থিতি সেই মানবজীবন প্রবাহের চিরন্তনতাকেই প্রকাশ করেছে ‘খেয়া’ কবিতায়।
‘খেয়া’ কবিতার নামকরণ
ভূমিকা –
সাহিত্যের আঙ্গিনায় শিরোনাম পাঠক আর লেখকের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে। নামকরণের মাধ্যমে পাঠক মূল বিষয়ের একটা আভাস পেয়ে যায় আবার লেখক তাঁর সৃষ্টিকে পাঠকমহলে প্রথম পরিচয়ও করান এই শিরোনামের সহায়তায়—ফলত নামকরণের গুরুত্ব ও অনিবার্যতা আজ প্রশ্নাতীত। মূল বিষয়ের নির্যাস এখানে আভাসিত হয়, সাহিত্যিক সচেতনভাবে সযত্নে এই শিরোনাম প্রয়োগ করেন। ‘খেয়া’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার বিষয়ের গভীর ব্যঞ্জনাকে আরও গভীরতা দান করলেন নামকরণের মাধ্যমে।
নামকরণের সার্থকতা –
মানবজীবন প্রবাহের অনিবার্য ও চিরন্তন গতিময়তাকে কুর্নিশ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কবিতার শিরোনাম রেখেছেন ‘খেয়া’। দেশি এই প্রচলিত শব্দের অনুষঙ্গে এসেছে নদীস্রোত, ঘাট, পারাপার, যাত্রী, তাদের নিত্যকর্ম। শত ব্যস্ততা, প্রতিকূলতার মধ্যে এপার-ওপারকে মিলিয়ে দেয় এই খেয়া। নদীতটের নির্জনতায় বসে উদাসী কবি দেখেছেন মানুষের হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ-রক্তরঞ্জিত ইতিহাসের বহু অধ্যায়। কিন্তু তা জীবনের সহজ অনাড়ম্বর চলনকে রোধ করতে পারেনি কখনও। ঋষিসম উদাসীনতা থেকে নদী বয়ে চলেছে, নবীন আর প্রবীণের ভিড়ে ভরিয়ে দিয়েছে তরিকে।
উপসংহার –
জীবনরসে সিক্ত কবি অনন্ত প্রসারিত দৃষ্টিতে জীবনকেই সর্বদা বিজয়ী হতে দেখেছেন। বক্ষে ভাসমান জীবননদীর খেয়াতরি সদা ভরে থেকেছে নবীন আর প্রবীণ যাত্রীদলের ভিড়ে। তার গতি অপ্রতিরোধ্য, তার গন্তব্য অসীমের দিকে। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘খেয়া’ কবিতায় শিরোনামটি গভীর ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ এবং সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।
এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের চতুর্থ পাঠের প্রথম অধ্যায়, ‘খেয়া’ -এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে কবির পরিচিতি, কবিতার উৎস, কবিতার পাঠপ্রসঙ্গ, কবিতার সারসংক্ষেপ, কবিতার নামকরণ এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আর্টিকেলটি আপনাদের ‘খেয়া’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছে এবং কবিতাটি ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া, নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে কবি পরিচিতি, কবিতার নামকরণ ও কবিতার সারসংক্ষেপ সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে, তাই এই তথ্যগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।






মন্তব্য করুন