এই আর্টিকেলে আমরা WBBSE বোর্ডের 2026 সালের মাধ্যমিক বাংলা বিষয়ের সাজেশন নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে দেওয়া অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
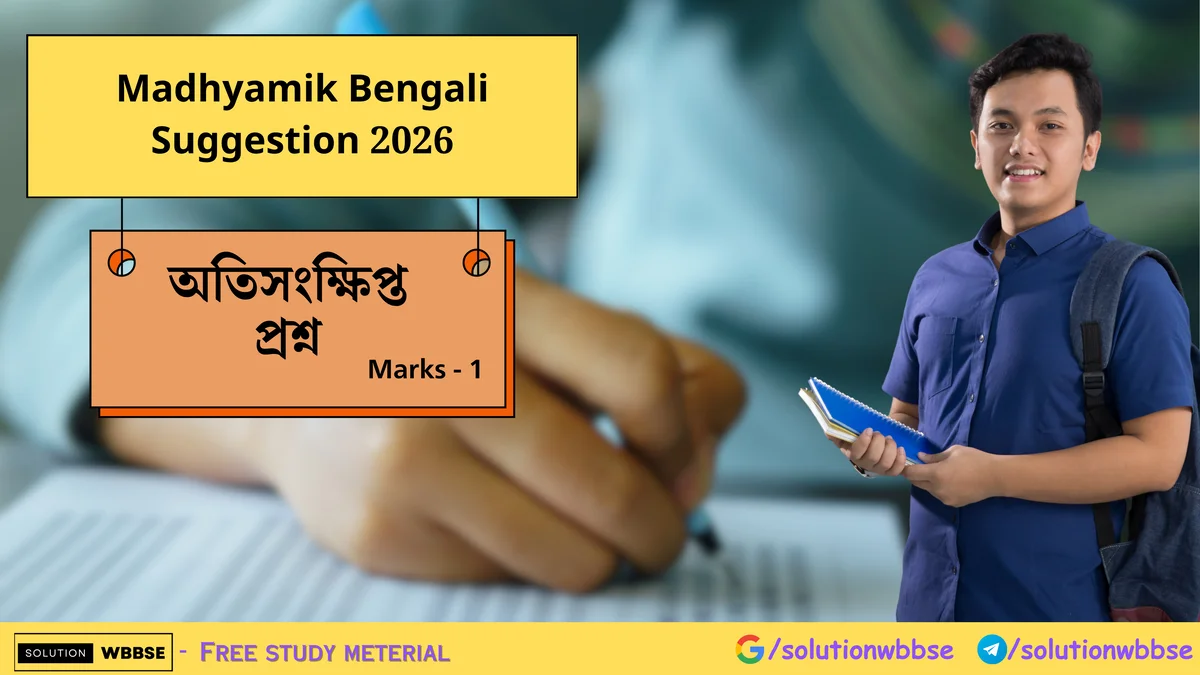
Madhyamik Bengali Suggestion 2026 – অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
গল্প
জ্ঞানচক্ষু
“ভালো হবে না বলছি।” – কোন্ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বক্তার এমন উক্তি?
তপনের প্রথম লেখা গল্পটি অন্য কোনো জায়গা থেকে ‘টুকলিফাই’ করেছে কিনা, ছোটোমাসির সেকথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে তপন এমন উক্তি করেছে।
তপন মামার বাড়িতে কেন এসেছিল?
ছোটোমাসির বিয়ে উপলক্ষে তপন মামার বাড়িতে এসেছে এবং স্কুলের ছুটি চলছে বলে মামার বাড়িতেই থেকে গেছে।
“শুধু এই দুঃখের মুহূর্তে গভীরভাবে সংকল্প করে তপন” – সংকল্পটি কী?
দুঃখের মুহূর্তে তপন সংকল্প করে যে, যদি কখনো লেখা ছাপাতে দিতে হয় তো সে নিজে গিয়ে তার ‘কাঁচা লেখা’ ছাপাতে দেবে। তাতে লেখা ছাপা হোক বা না হোক।
“আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন।” – বক্তার কোন্ দিনটি সবচেয়ে দুঃখের?
কারেকশনের নামে তপনের লেখা গল্পটি বদলে ছোটোমেসোর নিজের লেখা গল্প ছাপা হয়েছিল “সন্ধ্যাতারা” পত্রিকায়। এই গল্প তপন যেদিন পড়ল সেই দিনটিই ছিল তার কাছে সবচেয়ে দুঃখের।
“সূচিপত্রেও নাম রয়েছে” – সূচিপত্রে কী লেখা ছিল?
“সন্ধ্যাতারা” পত্রিকার সূচিপত্রে লেখা ছিল – ‘প্রথম দিন’ (গল্প) শ্রীতপনকুমার রায়।
“একটু কারেকশন” করে ইয়ে করে দিলে ছাপতে দেওয়া চলে।’ – কেকী ছাপানোর কথা বলেছেন?
লেখক ছোটোমেসোকে দেখে তপনের লেখক হওয়ার প্রবল ইচ্ছা জাগে ও সে গল্প লেখে। তপনের লেখা গল্প পড়ে ছোটোমেসো প্রশংসা করেন এবং বলেন একটু কারেকশন করে দিলেই গল্পটা ছাপাতে দেওয়া যাবে।
তপনের গল্প পড়ে ছোটোমাসি কী বলেছিল?
তপনের ‘বন্ধুসম’ ছোটোমাসি তপনের লেখা গল্পে একটু চোখ বুলিয়েই প্রশংসা করে এবং জানতে চায় গল্পটি কোথাও থেকে টুকলি করে লেখা কিনা।
“হঠাৎ ভয়ানক একটা উত্তেজনা অনুভব করে তপন” – এখানে কোন্ উত্তেজনার কথা বলা হয়েছে?
প্রথম গল্পটি ছোটো মেসোমশাই ছাপানোর জন্য নিয়ে যাওয়ার পর তপন আরও একটা গোটা গল্প লিখে ফেলে। সেই গল্প লেখার ফলে সৃষ্ট আনন্দজনিত উত্তেজনার কথাই এখানে বলা হয়েছে।
“যেন নেশায় পেয়েছে।” – কোন্ নেশার কথা বলা হয়েছে?
নতুন লেখক-মেসোকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তপন একটি গল্প লিখে ফেললে ছোটোমাসির উৎসাহে ছোটোমেসো সেটা ছাপিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এরপর থেকে তপনের গল্প লেখাটা নেশা হয়ে দাঁড়ায়।
“গল্প ছাপা হলে যে ভয়ংকর আহ্লাদটা হবার কথা, সে আহ্লাদ খুঁজে পায় না।” – উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আহ্লাদিত হতে না পারার কারণ কী?
‘জ্ঞানচক্ষু’ গল্পে তপনের লেখা গল্প ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকাতে ছাপা হলেও সে আহ্লাদিত হতে পারে না, কারণ তার গল্পটা কারেকশান করতে গিয়ে ছোটোমেসো সেটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছিলেন।
“তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই,” – কোন্ দুঃখের কথা বলা হয়েছে?
তপনের লেখা গল্পটি ছোটোমেসোমশাই সুপারিশ করে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন এবং লেখাটি প্রকাশের সময় তিনি কারেকশান স্বরূপ গল্পটি একপ্রকার নতুন করে লেখেন, যার দ্বারা তপন উপলব্ধি করে অন্যের দয়ায় গল্প ছাপানো যেমন অপমানের তেমনি গল্পের মধ্যে নিজের লেখা খুঁজে না পাওয়াও চরম দুঃখের। সেই দুঃখের কথাই এখানে বলা হয়েছে।
“কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল।” – কোন্ কথা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গিয়েছিল?
তপনের ছোটো মেসোমশাই বই লেখেন এবং সেই বই ছাপা হয় – এ কথা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গিয়েছিল।
“এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল তপনের” – কোন্ বিষয়ে তপনের সন্দেহ ছিল?
লেখকরা যে তপনের বাবা, ছোটোমামা বা মেজোকাকুর মতো একজন সাধারণ মানুষ এই বিষয়টি তপন বিশ্বাস করত না, তাই তার সন্দেহ ছিল।
নতুন মেসোকে দেখে কী জেনেছিল তপন?
ছোটোবেলা থেকে গল্প পড়া ও লেখার সুবাদে তপন গল্প জিনিসটা কী তা ভালোই জানে। কিন্তু গল্প লেখকরা তার মামা, কাকার মতো সাধারণ মানুষ – এটা সে নতুন মেসোকে দেখে জেনেছিল।
“তপন অবশ্য মাসির এই হইচইতে মনে মনে পুলকিত হয়” – তপন কেন মনে মনে পুলকিত হয়েছিল?
ছোটোমাসির হইচইয়ের ফলে তপনের লেখাটি লেখক ছোটোমেসোর হাতে পৌঁছোলে লেখাটির প্রকৃত মূল্য তিনি বুঝতে পারবেন – এই ভেবেই তপন মনে মনে পুলকিত হয়েছিল।
“এমন সময় ঘটল সেই ঘটনা” – কোন্ ঘটনার কথা বলা হয়েছে?
মামার বাড়ি থেকে ফেরার বেশ কিছুদিন বাদে ছোটোমাসি ও মেসো হঠাৎ উপস্থিত হন তপনদের বাড়িতে, তাদের হাতে ছিল তপনের দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফল ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পটি। এখানে সেই ঘটনার কথাই বলা হয়েছে।
“পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে?” – অলৌকিক ঘটনা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
তপনের লেখা গল্পটি তার নামসহ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার ঘটনাটিকে ‘অলৌকিক ঘটনা’ বলা হয়েছে।
“ক্রমশ ও কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে।” – কোন্ কথা ছড়িয়ে পড়ল?
তপনের লেখা গল্পটা ছোটো মেসোমশাই কারেকশান করে দেওয়ার পর ‘সন্ধ্যাতারা’ পত্রিকায় ছাপার কথা, অর্থাৎ ছোটো মেসোমশাইয়ের ‘কারেকশান’ করার কথা ছড়িয়ে পড়ল।
বহুরূপী
“এবার মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভান্ডার।” – কথাগুলো কে কাদের বলেছিলেন?
আলোচ্য কথাগুলি ‘বহুরূপী’ গল্পের মুখ্য চরিত্র হরিদা তার প্রতিদিনের সঙ্গী গল্পকথক ও তার বন্ধু অনাদি, ভবতোষদের বলেছিল।
“আক্ষেপ করেন হরিদা।” – হরিদার আক্ষেপের কারণ কী?
জগদীশবাবুর বাড়িতে আসা সর্বত্যাগী হিমালয়বাসী এক মস্ত বড়ো সন্ন্যাসীর কথা শুনে হরিদা তাঁর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সন্ন্যাসী চলে যাওয়ায় হরিদার সেই ইচ্ছে আক্ষেপে পরিণত হয়।
“কিন্তু ওই ধরনের কাজ হরিদার জীবনের পছন্দই নয়।” – কী ধরনের কাজ হরিদার অপছন্দ?
হরিদার সংসার অভাবে পরিপূর্ণ। ইচ্ছে করলেই তিনি কোনো অফিসের কিংবা কোনো দোকানের বিক্রিওয়ালার কাজ পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু সময় বেঁধে আর নিয়ম করে রোজই একটা চাকরি করা হরিদার অপছন্দ।
“মাস্টারমশাই একটুও রাগ করেননি। বরং একটু তারিফই করলেন।” – ‘তারিফ’ করার কারণ কী?
পুলিশের আসল পরিচয় জানতে পেরে মাস্টারমশাই রাগ করতে পারেননি। কারণ হরিদার শিল্পীসত্তায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বরং ‘তারিফ’ করে হরিদাকে প্রশংসা করেছিলেন।
“আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়ো?” – বক্তা একথা কাকে বলেছিলেন?
এক সন্ধ্যায় হরিদা বিরাগীর ছদ্মবেশে জগদীশবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হন। জগদীশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বিরাগীকে অভ্যর্থনা জানানোয় হরিদা তাঁকে আলোচ্য কথাটি বলেছিলেন।
“সপ্তাহে বড়জোড় একটি দিন বহুরূপী সেজে পথে বের হন হরিদা।” – বহুরূপী কাকে বলে?
যিনি নানা রূপ ধারণ করেন তাকেই বলে বহুরূপী। অনেকেই বহুরূপী সেজে জীবিকা নির্বাহ করেন। ‘বহুরূপী’ গল্পে হরিদা বহুরূপী সেজে উপার্জন করতেন।
“হরিদার জীবন এইরকম বহুরূপের খেলা দেখিয়েই একরকম চলে যাচ্ছে।” – কীরকম খেলা দেখিয়ে হরিদার জীবন চলে যাচ্ছে?
সন্ধ্যায় ব্যস্ততামুখর শহরের রাস্তায় হঠাৎ ঘুঙুরের মিষ্টি রুমঝুম শব্দ করে এক রূপসী বাইজি নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে। নবাগতরা অবাক হয়ে দেখে। এইভাবে পাগল, কাপালিক, পুলিশ, কাবুলিওয়ালা ইত্যাদি রূপে হরিদার জীবন একরকম চলে যাচ্ছে।
জগদীশবাবু তীর্থ ভ্রমণের জন্য কত টাকা বিরাগীকে দিতে চেয়েছিলেন?
জগদীশবাবু তীর্থ ভ্রমণের জন্য বিরাগীকে একশো এক টাকা দিতে চেয়েছিলেন।
জগদীশবাবু হিমালয় থেকে আগত সন্ন্যাসীকে কী কী উপহার দেন?
জগদীশবাবু সন্ন্যাসীর পদধুলি গ্রহণের জন্য তাঁকে একজোড়া সোনার বোল লাগানো খড়ম উপহার দেন। পরে সন্ন্যাসী বিদায় গ্রহণকালে জগদীশবাবু তাঁকে জোর করে একশো টাকার একটা নোট প্রদান করেন।
বিরাগী জগদীশবাবুকে কী উপদেশ দেন?
বিরাগী জগদীশবাবুকে বলেন ধন জন যৌবন সব কিছুই অর্থহীন। এগুলি এক-একটি সুন্দর সুন্দর বঞ্চনা। মনপ্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষা শুধু একজনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলে এই সৃষ্টির সকল ঐশ্বর্য লাভ করা সম্ভব হয়।
“চমকে ওঠে ভবতোষ।” – কী দেখে চমকে ওঠে ভবতোষ?
জগদীশবাবুর বাড়িতে বিরাগীকে প্রত্যক্ষ করে কথক ও তার বন্ধুরা নিশ্চিত ছিল যে, তিনি হরি নন। এমতাবস্থায় হরির বাড়িতে প্রবেশ করেই যখন তারা বুঝতে পারে যে বিরাগী আসলে তাদের হরিদাই ছিলেন তখন বিস্মিত হৃদয়ে ভবতোষ চমকে ওঠে।
“অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।” – হরিদার কোন্ ভুলের কথা এখানে বলা হয়েছে?
জগদীশবাবুর বাড়িতে হরিদা বিরাগী সেজে গিয়ে জগদীশবাবুর দেওয়া একশো এক টাকা প্রণামী অবলীলায় ফিরিয়ে দেওয়াকে গল্পকথক ‘ভুল’ বলে উল্লেখ করেছেন।
“সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস।” – কোন্ জিনিস সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে?
জগদীশবাবুর বাড়িতে যে ‘উঁচু দরের সন্ন্যাসী’-র আগমন ঘটেছিল সেই হিমালয়বাসী সন্ন্যাসী শুধুমাত্র জগদীশবাবু ভিন্ন আর কাউকে তাঁর পদধুলি গ্রহণ করতে না দেওয়ায় তাঁর পদধুলি সম্পর্কেই আলোচ্য মন্তব্যটি করা হয়েছে।
“খুব উঁচু দরের সন্ন্যাসী।” – কার সম্পর্কে এই ধারণা তৈরি হয়?
জগদীশবাবুর বাড়িতে সাতদিন অতিবাহিত করা হিমালয়ের গুহাবাসী এক সন্ন্যাসী সম্পর্কে কথকদের মনে এই ধারণা তৈরি হয়।
‘পরম সুখ’ বলতে বিরাগী কী বুঝিয়েছেন?
বিরাগীর মতানুযায়ী ‘পরম সুখ’ হল অনন্ত শান্তি ও মুক্তির নামান্তর। সকল জাগতিক সুখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনন্তের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারলেই ‘পরম সুখ’ লাভ করা যায়।
“বাঃ, এ তো বেশ মজার ব্যাপর।” – বক্তার কোন্ ব্যাপারকে মজার ব্যাপার বলে মনে হয়েছে?
হিমালয় থেকে আগত সন্ন্যাসী কাউকে তার চরণধুলি প্রদান করেন না। অথচ জগদীশবাবু খড়ম পরানোর অছিলায় তাঁর পদধূলি গ্রহণ করতে পারে জেনেও সোনার বোল লাগানো খড়মটি পরিধান করতে স্বীকৃত হন ও জগদীশবাবুও তাঁর পদধূলি লাভ করেন – এই ব্যাপারটাকেই বক্তা হরির মজার ব্যাপার বলে মনে হয়েছে।
পুলিশ সেজে হরি কী করে?
পুলিশ সেজে প্রথমে হরি দয়ালবাবুর লিচুবাগানের ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকে, পরে স্কুলের চারটে ছেলেকে ধরে। শত অনুরোধ সত্ত্বেও ছেলেগুলিকে না ছেড়ে মাস্টারের কাছ থেকে আট আনা ঘুস নিয়ে তারপর তাদের অব্যাহতি দেয়।
“চমকে উঠলেন জগদীশবাবু”। – কেন?
বারান্দার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে জগদীশবাবু এক শুভ্রবসন পরিধানকারী, সাদা চুলওয়ালা যোগী পুরুষকে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর আদুড় গা, ধুলোমাখা পদযুগল, হাতে একটি ঝোলা ও শান্ত-উদাত্ত-উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে চমকে ওঠেন জগদীশবাবু।
পথের দাবী
“মিথ্যেবাদী কোথাকার!” – উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কেন মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে?
উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ গিরীশ মহাপাত্রের হাতে গাঁজা খাওয়ার যথেষ্ট প্রমান থাকা সত্ত্বেও সে নিমাইবাবুর কাছে অস্বীকার করলে জগদীশবাবু একথা বলেছিলেন।
‘অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ছিল’ – অপূর্ব কী দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল?
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’ রচনাংশ অনুসারে অপূর্ব মুগ্ধ হয়ে গিরীশ মহাপাত্রের অদ্ভুত দুটি চোখের দিকে চেয়েছিল।
“আর যাই হোক যাঁকে খুঁজছেন তাঁর কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।” – কার খোঁজ করা হচ্ছিল?
পোলিটিকাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিকের খোঁজ করা হচ্ছিল।
“বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।” – বুড়োমানুষের কোন কথা শুনতে বলা হয়েছে?
দারোগা নিমাইবাবু গিরীশ মহাপাত্রের ভগ্ন চেহারার মধ্যে গাঁজা খাওয়ার লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। তার শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করেই নিমাইবাবু গাঁজা খেতে নিষেধ করেছিলেন।
ভামো যাত্রায় ট্রেনে অপূর্বর কে কে সঙ্গী হয়েছিল?
ভামো যাত্রাকালে ট্রেনে অপূর্বর সঙ্গী হয়েছিল আরদালি এবং অফিসের-একজন হিন্দুস্তানি ব্রাহ্মণ পিয়াদা।
“তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?” – কোন্ বস্তুটি পকেটে ছিল?
বস্তুটি আর কিছুই নয়, একটি গাঁজার কলকে। পুলিশস্টেশনে তল্লাশির সময় গিরীশ মহাপাত্রের পকেটে এই বস্তুটি পাওয়া গিয়েছিল।
“ইহা যে কত বড়ো ভ্রম তাহা কয়েকটা স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল।” – ‘ভ্রম’-টি কী?
ভামো যাত্রাকালে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী অপূর্বর মনে ভরসা ছিল রাতে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে না। এটাই ছিল অপূর্ব ভ্রম কারণ সেই রাতেই ব্রিটিশ পুলিশ তিনবার তার ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।
‘দেখি তোমার ট্যাকে এবং পকেটে কী আছে?’ – গিরীশ মহাপাত্রের ট্যাকে ও পকেটে কী কী পাওয়া গিয়েছিল?
গিরীশ মহাপাত্রের ট্যাক থেকে পাওয়া যায় একটি টাকা ও গন্ডা ছয়েক পয়সা। পকেট থেকে পাওয়া যায় একটা লোহার কম্পাস ও ফুটরুল। এ ছাড়া বিড়ি-দেশলাই ও গাঁজার কলকেও পাওয়া যায়।
‘পরকে সেজে দি, নিজে খাইনে’ – কখন এমন উক্তি করা হয়েছে?
‘পথের দাবী’ রচনাংশ অনুসারে খানাতল্লাশির সময় গিরীশ মহাপাত্রের কাছে একটি গাঁজার কলকে পাওয়া যায়। গিরীশ জানায় যে, সে বন্ধুবান্ধবদের গাঁজা দিলেও নিজে খায় না। তার এ কথায় চটে গিয়ে জগদীশবাবু প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটি করেছিলেন।
‘অপূর্ব রাজি হইয়াছিল।’ – কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে?
‘পথের দাবী’ পাঠ্যাংশে অপূর্বর সহকর্মী তলওয়ারকরের স্ত্রীর অনুরোধ ছিল অপূর্বর বাড়ির কেউ না-আসা পর্যন্ত অপূর্বকে তার হাতে তৈরি মিষ্টান্নে জলযোগ সম্পন্ন করতে হবে। সে-কথায় অপূর্ব রাজি হয়েছিল।
‘তিনি আমার আত্মীয়, আমার পিতার বন্ধু।’ – ‘তিনি’ বলতে যাঁর কথা বলা হয়েছে, তাঁর পরিচয় দাও।
উদ্ধৃতাংশে ‘তিনি’ বলতে থানার বড়োবাবু নিমাইবাবুকে বোঝানো হয়েছে। তিনি অপূর্বর বাবার বন্ধু তাই তার পিতৃস্থানীয়। নিমাইবাবুর চাকরির পিছনে অপূর্বর বাবার অবদান ছিল।
‘তিনি ঢের বেশি আমার আপনার।’ – কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করা হয়েছে?
এক্ষেত্রে ‘তিনি’ হলেন বিপ্লবী সব্যসাচী মল্লিক। ইংরেজ পুলিশ নিমাইবাবু অপূর্বর আত্মীয়স্থানীয় হলেও দেশপ্রেমিক সব্যসাচীকে। দেশভক্ত অপূর্বর বেশি আপন বলে মনে হয়েছে।
‘মনে হল দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।’ – কোন্ কথা মনে করে অপূর্বর এই মনোবেদনা?
অপূর্ব বিনাদোষে ফিরিঙ্গি যুবকদের হাতে মার খাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত ভারতীয়রা অভ্যাসবশত এর কোনো প্রতিবাদ করেনি। এই কথা মনে করেই অপূর্বর এই মনোবেদনা।
‘ও নিয়ম রেলওয়ে কর্মচারীর জন্য’ – কোন্ নিয়ম রেলওয়ে কর্মচারীর জন্য?
শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ রচনাংশ থেকে গৃহীত প্রশ্নের অংশটিতে উক্তিটি করেছে বর্মা পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর। বাঙালি যুবক অপূর্ব তার অফিসের বড়োসাহেবের নির্দেশে প্রথম শ্রেণির যাত্রী হিসেবে ভামো যাচ্ছিল। তল্লাশির নাম করে পুলিশ যখন বারবার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল তখন প্রতিবাদ করে অপূর্ব বলে সে প্রথম শ্রেণির যাত্রী। তখন পুলিশ আলোচ্য উক্তি করেছিল।
‘পুলিশ স্টেশন প্রবেশ করিয়া দেখা গেল’ – কে, কী দেখল?
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘পথের দাবী’ পাঠ্যাংশের আলোচ্য অংশে দেখা গেল, পুলিশস্টেশনের সামনের হলঘরে জনা-ছয়েক বাঙালি বসে আছে তার পুলিশ তাদের মালপত্র তল্লাশি করছে।
‘লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল।’ – লোকটির পরিচয় দাও।
‘পথের দাবী’-তে লোকটি বলতে গিরীশ মহাপাত্রের ছদ্মবেশধারী রাজবিদ্রোহী সব্যসাচীর কথা বলা হয়েছে। সন্দেহবশত পুলিশ তাকে আটক করলেও পরে আচার-আচরণ ‘ও বেশভূষা দেখে পুলিশ গিরীশকে ছেড়ে দেয়।
গিরিশ মহাপাত্রের গায়ে কোন্ ধরনের পোশাক ছিল?
‘পথের দাবী’ রচনাংশ অনুসারে গিরীশ মহাপাত্রের গায়ে ছিল জাপানি সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি আর তার বুকপকেট থেকে একটি বাঘ-আঁকা রুমালের কিছুটা দেখা যাচ্ছিল। তবে কাঁধে উত্তরীয়ের কোনো বালাই ছিল না।
‘তার আমি জামিন হতে পারি।’ – কে, কীসের জামিন হতে চেয়েছে?
নিমাইবাবু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গিরিশ মহাপাত্রকে আটক করলেও তার বেশভূষা ও আচরণ দেখে অপূর্বর ধারণা হয় সে সব্যসাচী মল্লিক নয়। তাই অপূর্ব উক্ত বিষয়ে জামিন হতে চায়।
‘নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।’ – নিমাইবাবু কেন চুপ করে থাকলেন?
গিরীশ মহাপাত্র যে রাজদ্রোহী সব্যসাচী নয়, অপূর্বর এই আশ্বাসে নিমাইবাবু আস্থা রাখলেও সব্যসাচীর প্রখর বুদ্ধি সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। তাই নিশ্চিত না-হলেও তিনি চুপ থেকেছেন।
অদল বদল
“এসো, আমরা কুস্তি লড়ি।” – কে, কার সঙ্গে কুস্তি লড়তে চেয়েছিল?
পান্নালাল প্যাটেল রচিত ‘অদল বদল’ গল্পে কালিয়া অমৃতের সঙ্গে কুস্তি লড়তে চেয়েছিল।
‘হঠাৎ অমৃতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল’ – ‘বুদ্ধিটা কী ছিল?
‘অদল বদল’ গল্পাংশে বুদ্ধিটি হল অমৃত ইসাবকে টেনে নিয়ে ওদের বাড়ির মাঝখানে ঢুকে জামাটা অদল বদল করে নিতে চাইলো, যাতে ইসাব তার বাবার কাছে ধরা পড়ে মার না খায়।
“অমৃত ফতোয়া জারি করে দিল।” – অমৃত কী “ফতোয়া” জারি করেছিল?
অমৃত ফতোয়া জারি করেছিল যে, ঠিক ইসাবের মতো জামা না পেলে সে স্কুলে যাবে না।
“অদল বদলের গল্প” গ্রামপ্রধানের কানে গেলে তিনি কী ঘোষণা করেছিলেন?
“অদল বদলের গল্প” গ্রামপ্রধানের কানে গেলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এরপর থেকে সকল গ্রামবাসী অমৃতকে অদল ও ইসাবকে বদল বলে ডাকবে।
“এসো, আমরা কুস্তি লড়ি।” – কে, কাকে বলেছিল?
ছেলেছোকরার দল থেকে কালিয়া নামের একজন ছেলে এসে অমৃতের গলা জড়িয়ে ধরে কুস্তি লড়ার প্রস্তাব দেয়।
“অদল বদল” গল্পটি কে বাংলায় তরজমা করেছেন?
“অদল বদল” গল্পটি বাংলায় তরজমা করেছেন অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত।
‘ইসাবের মেজাজ চড়ে গেল।’ – কখন ইসাবের মেজাজ চড়ে গিয়েছিল?
অমৃত কুস্তি লড়তে না চাওয়ায় কালিয়া অন্যায়ভাবে অমৃতকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেয়, তা দেখে ইসাবের মেজাজ চড়ে গিয়েছিল।
‘বলতে গেলে ছেলে দুটোর সবই একরকম, তফাত শুধু এই যে’ – তফাৎটা কী?
অমৃত আর ইসাবের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও তফাত ছিল অমৃতের বাবা-মা আর তিন ভাই রয়েছে, আর ইসাবের শুধু বাবা রয়েছে।
‘উনি ঘোষণা করলেন’ – কে, কী ঘোষণা করেছিলেন?
অমৃত ও ইসাবের পারস্পরিক ভালোবাসার কাহানি শুনে মুগ্ধ হয়ে গ্রাম প্রধান ঘোষণা করলেন যে, অমৃতকে ‘অদল’ আর ইসাবকে ‘বদল’ বলে ডাকা হবে।
অমৃতের বুক ভয়ে ঢিপঢিপ করছিল কেন?
জামা না ছেঁড়ার জন্য অমৃতের মা অমৃতকে সাবধান করে দিয়েছিল। তবুও জামা ছিঁড়ে যায়, আর ছেঁড়া জামা পরে বাড়ি ফিরলে মায়ের কাছে মার খেতে হবে ভেবে অমৃতের বুব ভয়ে ঢিপঢিপ করছিল।
‘ওরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল’ – ওরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল কেন?
কালিয়ার সাথে কুস্তি করতে গিয়ে ইসাবের নতুন জামার পকেট ও ছ’ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। ফলে ইসাবের বাবা হয়তো ইসাবকে শাস্তি দিতে পারেন এই আশঙ্কায় ওরা দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।
‘আমার সঙ্গে আয়’ – অমৃত ইসাবকে এমন নির্দেশ দিল কেন?
কালিয়ার সঙ্গে কুস্তি লড়ে ইসাবের জামা ছিঁড়ে যাওয়ার ইসাবের বাবা যাতে ইসাবকে না মারতে পারেন, অমৃত তাই নিজের জামার সাথে বদল করার জন্য এমন নির্দেশ দিয়েছিল।
‘ও আমাকে শিখিয়েছে খাঁটি জিনিস কাকে বলে।’ – ‘খাঁটি জিনিস’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
আলোচ্য অংশে ‘খাঁটি জিনিস’ বলতে পার্থিব কোনো বস্তু নয়-অমৃতের মায়ের ওপর অগাধ ভরসা অমৃতকে তার বন্ধুর প্রতি সহৃদয় হতে সাহায্য করেছিল।
‘উনি আসল ঘটনাটা জানেন’ – কে, কোন্ ঘটনাটা জানেন?
ইসাবের বাবা অমৃত ও ইসাবের মধ্যে জামা অদল বদলের আসল ঘটনাটা জানেন।
‘ছেলের দল আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল’ – কী কারণে আনন্দ হয়েছিল?
অমৃত ও ইসাব কুস্তি লড়তে রাজি না হওয়ায় কালিয়া জোর করে অমৃতকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। উপস্থিত ছেলের দল ধরে নেয় কালিয়ার জয় আর অমৃতের পরাজয় হয়েছে। তাই তারা আনন্দে চিৎকার করতে থাকে।
নদীর বিদ্রোহ
“আরও বেশি অপরিচিত মনে হইল।” – উদ্দিষ্টকে ‘বেশি অপরিচিত’ মনে হওয়ার কারণ কী?
পাঁচদিন আগের পঙ্কিল নদীটি জলপুষ্ট হয়ে ফুলে ফেঁপে চঞ্চল বেগে ছুটে চলেছে। নদীর সেই ভয়ংকর রূপ নদের চাঁদের কাছে ‘বেশি অপরিচিত’ মনে হয়েছিল।
“বড়ো ভয় করিতে লাগিল নদেরচাঁদের।” – নদেরচাঁদের ভয়, করার কারণ কী?
ইট, সুরকি, সিমেন্ট, লোহালক্কড় দিয়ে তৈরি ব্রিজের ওপর বসেও নদীকে দেখে ভয় লেগেছিল নদের চাঁদের। কারণ পাঁচদিনের অবিশ্রান্ত বর্ষণে নদী ফুলে ফেঁপে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছিল।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম কী?
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
“নদেরচাঁদ সব বোঝে,” – নদেরচাঁদ কী বোঝে?
তিরিশ বছর বয়সী নদেরচাঁদ একজন স্টেশনমাস্টার। এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব যার কাঁধে, নদী নিয়ে পাগলামি তাকে মানায় না – একথা নদের চাঁদ বোঝে।
“এক একখানি পাতা ছিঁড়িয়া দুমড়াইয়া মোচড়াইয়া জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল।” – উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কীসের পাতা জলে ফেলতে লাগল?
পাঁচদিনের অবিশ্রান্ত বর্ষণে কর্মস্থলে আবদ্ধ নদেরচাঁদ স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বিরহপূর্ণ পাঁচ পাতার যে চিঠি লিখেছিল তার পাতাগুলি ছিঁড়ে জলে ফেলতে লাগল।
“নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইয়া গেল।” – নদেরচাঁদের স্তম্ভিত হওয়ার কারণ কী?
ব্রিজের কাছে এসে নদীর দিকে প্রথমবার তাকিয়ে নদীর উন্মত্ত চেহারা দেখেই নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হয়ে গেল।
“জলপ্রবাহকে আজ তাহার জীবন্ত মনে হইতেছিল।” – কেন নদেরচাঁদের নদীর জলপ্রবাহকে জীবন্ত মনে হল?
বৃষ্টির জল পেয়ে নদীর জলপ্রবাহ উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। আর এই উন্মত্ততার জন্যই নদেরচাঁদের নদীর জলপ্রবাহকে জীবন্ত বলে মনে হল।
“নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে।” – নদীর বিদ্রোহের কারণ নদেরচাঁদ বুঝতে পারল কীভাবে?
শুকনো নদী পাঁচদিনের বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। উন্মত্ত নদীর তীব্র স্রোতযুক্ত জলধারা দেখে নদেরচাঁদ নদীর বিদ্রোহের কারণ বুঝতে পারল।
“নদেরচাঁদ গর্ব অনুভব করিয়াছে” – নদেরচাঁদ কীসের জন্য গর্ব অনুভব করেছে?
স্টেশনের কাছে নতুন রং করা ব্রিজটির জন্য নদেরচাঁদ গর্ব অনুভব করেছিল।
“আজও সে সেইখানে গিয়ে বসল” – কোথায় গিয়ে বসল?
নদেরচাঁদ ব্রিজের মাঝামাঝি ইট, সুরকি আর সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা ধারকস্তম্ভের শেষপ্রান্তে গিয়ে বসল।
“নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে” – নদীর বিদ্রোহের কারণ কী ছিল?
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে আমরা দেখি, নদেরচাঁদ অনুভব করে নদীর ওপরে ব্রিজ তৈরি করা ও বাঁধ দেওয়ার কারণেই নদী যেন বিদ্রোহ করেছে।
“ট্রেনটি নদেরচাঁদকে পিযিয়া চলিয়া গেল” – কোন্ ট্রেনটি?
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্প থেকে নেওয়া আলোচ্য অংশে ৭ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কথা বলা হয়েছে।
“নদেরচাঁদ ছেলেমানুষের মতো ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল।” – কেন তার এমন বোধ হয়েছিল?
নদীকে না দেখতে পেয়ে নদেরচাঁদের অবস্থা ছেলেমানুষের মতো হয়ে গিয়েছিল। সে ছোটোছেলের মতো উতলা হয়ে উঠেছিল নদীকে দেখার জন্য।
“নদীকে এভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত নদেরচাঁদ দিতে পারে।” – নদেরচাঁদের নদীকে ভালোবাসার কৈফিয়ত কী ছিল?
নদেরচাঁদ নদীর ধারে জন্মেছে, নদীর ধারেই মানুষ হয়েছে, নদী যেন তার চিরপরিচিত আপনজন। এই বিষয়টিকেই নদেরচাঁদ নদীর প্রতি তার ভালোবাসার সহজ কৈফিয়ত হিসেবে তুলে ধরতে পারে।
“দেখিয়া সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল” – সে কী দেখে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল?
নদেরচাঁদের দেশের ক্ষীণস্রোতা নদীটি অনাবৃষ্টির বছরে প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে সে কেঁদে ফেলেছিল।
কবিতা
অসুখী একজন
“ঘাস জন্মালো রাস্তায়” – কখন রাস্তায় ঘাস জন্মালো?
চিলিতে যুদ্ধ হওয়ায় মানুষের মৃত্যুর সাথে কথকের স্মৃতি মলিন হয়ে যায়, বৃষ্টিতে তাই পায়ের দাগ ধুয়ে যাওয়ায় ঘাস জন্মেছিল।
“যেখানে ছিল শহর” – সেখানকার কী অবস্থা হল?
‘অসুখী একজন’ কবিতায় যেখানে ছিল জীবন্ত শহর, যুদ্ধের ভয়ংকরতায় সেখানে ছড়িয়ে রইল কাঠকয়লা, দোমড়ানো লোহা, মৃত পাথরের মূর্তির বীভৎস মাথা আর জমাট রক্তের একটা কালো দাগ।
“তারপর যুদ্ধ এল” – যুদ্ধ কেমনভাবে এল?
ভয়ংকর প্রাণঘাতী যুদ্ধ এল রক্তের এক আগ্নেয় পাহাড়ের মতো। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করে দিয়েছিল।
‘অসুখী একজন’ কবিতাটি কে বাংলায় তরজমা করেছেন?
পাবলো নেরুদার লেখা ‘অসুখী একজন’ কবিতাটি বাংলায় তরজমা করেছেন নবারুণ ভট্টাচার্য্য।
“শিশু আর বাড়িরা খুন হলো” – ‘শিশু আর বাড়িরা’ খুন হয়েছিল কেন?
প্রাণঘাতী যুদ্ধ এল রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড়ের মতো। এই যুদ্ধের আগুনে ধ্বংস হল মানব-মানবী, ভস্মীভূত হল গৃহ থেকে দেবালয়।
“বছরগুলো/নেমে এল তার মাথার ওপর” – তাৎপর্য লেখো।
কবিতায় উক্ত মেয়েটির প্রিয়জন ছেড়ে যাওয়ার বেদনা গুরুভার হয়ে বসেছিল তার বুকে। বছরের পর বছর তার এই দুঃসহ দুঃখ বহন করাকেই উক্ত চরণে প্রতিকায়িত করা হয়েছে।
“তারপর যুদ্ধ এল” – যুদ্ধ কীভাবে এল?
শান্ত স্থিতধী সমাজের শান্তি আর সহাবস্থানের বুক চিরে যুদ্ধ এল চূড়ান্ত রক্ত ক্ষরণের মধ্য দিয়ে। যাকে রক্তের আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
যুদ্ধের পরিণতিতে মেয়েটির কী অবস্থা হল?
‘অসুখী একজন’ কবিতায় যুদ্ধের পরিণতিতে ঘরবাড়ি শিশুসহ প্রায় সমস্ত শহর ধ্বংস হলেও শুধু মেয়েটি বেঁচে রইল তার অপেক্ষা নিয়ে।
‘অসুখী একজন’ কবিতায় ‘হাজার বছর’ ধরে ধ্যানে মগ্ন ছিল কারা?
‘অসুখী একজন’ কবিতায় ‘শান্ত হলুদ’ দেবতারা হাজার বছর ধরে ধ্যানে মগ্ন ছিল।
“সেই মিষ্টি বাড়ি” – কবির সাধের ‘মিষ্টি বাড়ি’-র কী হল?
কবির সাধের সাজানো ও মনোরম বাড়িটি যুদ্ধের ধ্বংসের তান্ডবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল বলেই কবি আপশোস করেছেন।
‘অসুখী একজন’ কবিতার বক্তা মিষ্টি বাড়ির বারান্দায় কী করতেন এবং যুদ্ধে বাড়িটির কী পরিণতি হয়েছিল?
‘অসুখী একজন’ কবিতার বক্তা নিজের মিষ্টি বাড়ির বারান্দায় ঝুলন্ত বিছানায় মাঝে মাঝে ঘুমোতেন। যুদ্ধের তান্ডবের কারণে সেই বাড়িটি নষ্ট হয়ে যায় বলে বক্তা উল্লেখ করেছেন।
পাবলো নেরুদা কোথাকার কবি ছিলেন এবং কোন্ ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন?
‘অসুখী একজন’ কবিতাটি নোবেল জয়ী সাহিত্যিক পাবলো নেরুদার ‘Extravagaria’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
‘অসুখী একজন’ কবিতায় কে, কাকে, কোথায় ছেড়ে গিয়েছিল?
পাবলো নেরুদার ‘অসুখী একজন’ কবিতায় বক্তা তার পরিচিত এক মেয়েকে দরজার সামনে অপেক্ষমান রেখে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।
“সে জানত না…” – সে কী জানত না?
কবি পাবলো নেরুদা রচিত ‘অসুখী একজন’ কবিতার বক্তার আর ফিরে না আসার কথাটি জনৈকা মেয়েটি জানত না বলে মন্তব্য করেছেন।
কখন এবং কেন বক্তার পায়ের দাগ ধুয়ে গেল?
বক্তার দীর্ঘদিন অনুপস্থিতিতে রাস্তায় তার পায়ের দাগগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি
“পৃথিবী হয়তো গেছে মরে” – পৃথিবী সম্পর্কে এমন বলার কারণ কী?
সাধারণ মানুষের বিপন্নতার কথা, তাদের সর্বস্ব হারানোর কথা কেউ মনে রাখে না। একটু আশ্রয়, একটু খাদ্যের জন্য সর্বহারাদের বারোমাস ভিখারি থাকতে হয়। আজ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই বলেই কবি এরূপ আশঙ্কা করেছেন।
‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতাটির রচয়িতা কে?
‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতাটির রচয়িতা শঙ্খ ঘোষ।
“ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে” – কী ছড়ানো রয়েছে?
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সর্বগ্রাসী ক্ষুধার শিকার সাধারণ মানুষ। এই সর্বহারা বিপন্ন মানুষের কাছে দূরে অর্থাৎ, চারপাশে ছড়ানো রয়েছে শিশুদের শব।
“আমাদের পথ নেই আর” – তাহলে আমাদের করণীয় কী?
যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে মানুষের চলার পথ রুদ্ধ। এই অবস্থায় বেঁচে থাকার জন্য কবি সম্মিলিত হতে বলেছেন। জোট বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই উচিত।
“আমাদের ইতিহাস নেই।” – এ কথা বলা হয়েছে কেন?
সাধারণ বঞ্চিত মানুষের দুঃখকষ্ট-বঞ্চনার কথা ইতিহাসে স্থান পায় না। যদিও ইতিহাস লেখা হয়, সে ইতিহাসে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করা থাকে। তাই উক্ত কথাটি আক্ষেপের সঙ্গে বলা হয়েছে।
“আয় আরো হাতে হাত রেখে” – এই পঙক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী?
‘হাতে হাত রেখে’ অর্থাৎ, পারস্পরিক সহানুভূতির বন্ধন দৃঢ় করে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান এই পঙক্তিটিতে কবি করেছেন।
“আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি” – কাদের উদ্দেশ্যে কবির এই আহ্বান?
অবক্ষয়মান সমাজব্যবস্থার প্রতিকূলতার মধ্যে যারা সংগ্রাম করে টিকে আছে তাদের উদ্দেশ্যে কবির এই আহ্বান।
“আমাদের মাথায় বোমারু” – ‘বোমারু’ শব্দটির অর্থ কী?
‘বোমারু’ শব্দটির অর্থ যা বোমা নিক্ষেপ করে বা বর্ষণ করে। এখানে যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত বোমারু বিমানকে বোঝানো হয়েছে।
বিপন্ন মানুষের ঘর কীভাবে উড়ে গেছে?
যুদ্ধ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক সন্ত্রাসে বিপন্ন মানুষের ঘর অর্থাৎ মাথার উপরের আচ্ছাদন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা আশ্রয়হীন হয়েছে।
‘শিশুদের শব’ কোথায় কীভাবে ছড়ানো রয়েছে?
যুদ্ধ, দাঙ্গার মধ্যে পড়ে যেসব মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছে, সেইসব বিপন্ন মানুষের চারপাশে কাছে দূরে শিশুদের শব ছড়নো রয়েছে।
কবি শঙ্খ ঘোষ কেন ‘বেঁধে বেঁধে’ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন?
বিপন্ন মানুষজনের চারিদিকের পথ বন্ধ তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কবি শঙ্খ ঘোষ ‘বেঁধে বেঁধে’ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।
“আমাদের পথ নেই কোনো” – কেন এরকম অবস্থা?
আমাদের ডানদিকে ধস আর বামদিকে গভীর গিরিখাত, শুধু তাই নয়, মাথার উপরে বোমারু বিমানের হানা আর চলতে গেলে বাধা সৃষ্টি করে হিমানীর বাঁধ। তাই আমাদের কোনো পথ নেই।
“এ-মুহূর্তে মরে যাব না কি?” – এই আশঙ্কা কেন?
সাধারণ মানুষের চলার পথ অবরুদ্ধ, তাদের বাসস্থান ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের শিশুরা মারা গেছে অপুষ্টি আর রোগভোগে – এমন পরিস্থিতিতে তাদেরও বেঁচে থাকাটা নিশ্চিত নয়। তাই তাদের এরূপ আশঙ্কা।
“আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি” – বেঁধে থাকার কারণ কী?
অবক্ষয়মান পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিবন্ধকতাকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করার কারণে বেঁধে থাকার কথা বলা হয়েছে।
আফ্রিকা
“কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে” – আলোর কৃপণতার কারণ কী?
প্রাক্-সভ্যতায় আফ্রিকা তমসাবৃত রূপটি নিয়ে জেগে উঠেছিল। আলো সেখানে নির্বাধ নয়, কুণ্ঠিত ও কৃপণ ছিল তার প্রকাশ। অর্থাৎ, ‘কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে’ বলতে তমসাবৃত আফ্রিকাকেই বোঝানো হয়েছে।
“বলো ক্ষমা করো” – কীসের জন্য এই ক্ষমা প্রার্থনা?
ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক শাসকের নির্লজ্জ, নির্মম অত্যাচারে কলঙ্কিত আফ্রিকা মহাদেশ। কবি মনে করেন, এজন্য পৃথিবীর সুশীল সভ্যসমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত আফ্রিকার কাছে।
‘সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।’ – ‘সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী’টি কী?
মানহারা-মানবীর প্রতি তীব্র অসম্মানের জন্য অপমানিতের দ্বারে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাওয়াকেই কবি ‘সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী’ বলেছেন।
“এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,” – ‘ওরা’ কারা?
‘ওরা’ বলতে কবি লোহার হাতকড়িধারী এবং প্রভুত্বকামী ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের বুঝিয়েছেন। ‘ওরা’ নেকড়ের চেয়ে তীক্ষ্ণ নখযুক্ত; সূর্যহারা অরণ্যের চেয়েও গর্বে অন্ধ।
“বিদ্রুপ করেছিলে ভীষণকে” – কীভাবে ‘বিদ্রুপ’ করেছিল?
আফ্রিকা ভীষণকে বিদ্রুপ করেছিল বিরূপের ছদ্মবেশে। প্রতিস্পধী ক্ষমতার ছদ্ম আবরণই হল ‘বিরূপের ছদ্মবেশ’।
“এসো যুগান্তর কবি” – কবির ভূমিকাটি কী হবে?
দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যার শেষ রশ্মিটুকু যখন আপতিত হবে, তখনই যুগান্তর কবির আবির্ভাব হবে অশুভ পশুশক্তিকে দমন করার জন্য।
আফ্রিকা কীভাবে ভীষণকে অবজ্ঞা করেছিল?
আফ্রিকা নিজেকে উগ্র ও বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায় তুলে ধরে ভীষণকে অবজ্ঞা করেছিল। অর্থাৎ, বন্য দুর্গম প্রকৃতির বিরূপতাকে আফ্রিকা যেন ভয়ের সৌন্দর্য দিয়েই জয় করতে চেয়েছিল।
“অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ” – কেন অপরিচিত ছিল?
‘আফ্রিকা’ দুর্গম ও রহস্যময়তার জন্য স্বতন্ত্র থেকেছে পৃথিবীর অন্য অংশের কাছে। প্রকৃতির বিরূপতা ও আদিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের কারণে সভ্য জগৎ আফ্রিকার মানুষদের প্রতি ছিল চরম উদাসীন।
“এল মানুষ-ধরার দল” – কারা, কেন এসেছিল?
‘মানুষ-ধরার দল’ বলতে ‘আফ্রিকা’ কবিতায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের কথা বলা হয়েছে। এরা ইউরোপ থেকে এসেছিল আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদ লুঠ করতে।
‘সুন্দরের আরাধনা’ কোথায় ধ্বনিত হচ্ছিল?
আফ্রিকার বিপরীত প্রান্তে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় দেশের কবিদের সংগীতে স্বাভাবিকভাবেই ‘সুন্দরের আরাধনা’ চলছিল।
“অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল” – ‘দিনের অন্তিমকাল’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তির আফ্রিকাকে করায়ত্ত করে স্বাধীনতা হরণ করার সময়কালকে কবি ‘দিনের অন্তিমকাল’ বলে অভিহিত করেছেন।
যুগান্তর কবির কাছে ‘আফ্রিকা’ কবিতার কবি কী অনুরোধ রেখেছেন?
‘আফ্রিকা’ কবিতার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফ্রিকার অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সভ্য সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে যুগান্তর কবিকে ক্ষমা চাইতে বলেছেন।
“উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে” – কথাটির বিশেষ অর্থ কী?
কথাটির বিশেষ অর্থ হল – আদিম যুগ উদ্ভ্রান্ত অর্থাৎ তখন সভ্যতায় বিন্যাস পর্বের সূচনা হয়নি। প্রকৃতি আদিমতায় আচ্ছন্ন ছিল।
‘আফ্রিকা’ কবিতায় কেন সৃষ্টিকর্তা নতুন সৃষ্টিকে বারবার বিধ্বস্ত করছিলেন?
‘আফ্রিকা’ কবিতায় স্রষ্টা নিজের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না, তাই তিনি নিজেই নিজের নতুন সৃষ্টিকে বারবার বিধ্বস্ত করছিলেন।
‘হায় ছায়াবৃতা’ – আফ্রিকাকে ‘ছায়াবৃতা’ বলার কারণ কী?
‘আফ্রিকা’ ভূখণ্ড ছিল বনস্পতির ছায়ায় আবৃত; আর এই ভূখণ্ডের দুর্গমতা, জঙ্গলাকীর্ণ বিভীষিকাময় প্রকৃতির রহস্য ছিল বহিজর্গতের অজানা। তাই একে ‘ছায়াবৃতা’ বলা হয়েছে।
“সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি” – নিভৃত অবকাশে কী করছিল?
‘আফ্রিকা’ কবিতা অনুযায়ী মূল ভূখণ্ড থেকে আফ্রিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে বনস্পতির আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। মূল জনজীবন থেকে নিভৃতে থেকে সে সংগ্রহ করছিল রহস্যঘেরা দুর্গমতা, আর বুঝে নিতে চাইছিল প্রকৃতির দুর্বোধ্য সংকেত ও মন্ত্রধ্বনি।
অভিষেক
“নাদিলা কর্বূরদল হেরি বীরবরে,” – ‘কর্বূরদল’ শব্দটির অর্থ কী?
‘কর্বূর’ কথাটির অর্থ রাক্ষস, আর কর্বূরদল কথাটির অর্থ হলো রাক্ষসদল।
“হা ধিক্ মোরে।” – বক্তা নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন কেন?
রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিৎ রাজধানী থেকে দূরে নারীকুল মাঝে বিনোদনে রত ছিলেন অথচ অপরদিকে লঙ্কাপুরী শত্রুর পদভারে কম্পমান, তার পরের ভাই কালসমরে হত হয়েছে, পিতা প্রতিশোধকল্পে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হচ্ছেন – তাই নিজের এহেন নির্বুদ্ধিতার জন্য তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন।
“এ কলঙ্ক, পিতঃ ঘুষিবে জগতে।” – বক্তা কোন কলঙ্কের কথা বলেছেন?
ইন্দ্রজিৎ লঙ্কেশ্বর রাবণের যোগ্য সন্তান। এমন সন্তান থাকতে পিতা রাবণ যুদ্ধে গেলে সমগ্র জগতে নিন্দা-ধ্বনি উঠবে। বক্তা ইন্দ্রজিৎ এই কলঙ্কের কথাই বলেছেন।
“হায়, বিধি বাম মম প্রতি।” – বক্তার এমন মন্তব্যের কারণ কী?
বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে ভেঙে পড়েছিলেন লঙ্কাধিপতি রাবণ। প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে পাঠিয়ে পুনরায় পুত্রশোক পেতে চান না তিনি। রাবণের মনে হয়েছে বিধাতা তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন বলেই এমন পরিণতি হয়েছে।
“ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা” – কেন ইন্দ্রজিতের কাছে এসেছিলেন?
অম্বুরাশি-সুতা অর্থাৎ লঙ্কার কুললক্ষ্মী ইন্দ্রজিতের ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে প্রমোদ কাননে ইন্দ্রজিতের কাছে এসেছিলেন বীরবাহুর মৃত্যু ও রাবণের যুদ্ধপ্রস্তুতির সংবাদ দিতে।
“কে কবে শুনেছে পুত্র ভাসে শিলাজলে,” – বক্তার এমন মন্তব্যের কারণ কী?
শ্রীরামচন্দ্র বানরবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের উপর শিলাদ্বারা সেতু নির্মাণ করেছিলেন। শিলা জলে ভাসা অসম্ভব। কিন্তু রামচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়েছে একথাই রাবণ মেঘনাদকে বলেছেন।
“হাসি উত্তরিলা/মেঘনাদ” – মেঘনাদ কী উত্তর দিয়েছিলেন?
রাবণপুত্র মেঘনাদ তার প্রিয় পত্নীর ভালোবাসাপূর্ণ কথা শুনে হেসে উত্তর দিয়েছিলেন যে, প্রমীলা যে বাঁধনে তাকে বেঁধেছে তা ছেঁড়ার সাধ্য কারো নেই। তাই তিনি তার কাজ শীঘ্র সম্পন্ন করে আবার প্রমীলার কাছে ফিরে আসবেন।
“কাঁপিলা লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি।” – লঙ্কার এমন অবস্থার কারণ কী?
মেঘনাদ তাঁর প্রিয়নুজের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তার আগমন সংকেত ও ধনুকের টংকারে আকাশ-বাতাস কম্পমান। মেঘনাদের বিভীষণ পদচারণাজাত আগমন বার্তাই লঙ্কা ও জলধি মাঝে কম্পন সৃষ্টি করে।
“নাদিলা কর্তৃরদল” – কর্তৃরদলের এরূপ আচরণের কারণ কী?
যুদ্ধে প্রস্তুত কর্তৃরদল অর্থাৎ রাক্ষসবাহিনী মেঘনাদকে দেখতে পেয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে চিৎকার করে ওঠে।
“কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে শিলা জলে,” – এখানে কোন্ প্রসঙ্গের উপস্থাপন হয়েছে, তা লেখো।
শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর বানর বাহিনী সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় পৌঁছোতে শিলা দিয়ে যে সেতু নির্মাণ করে তার কথা এখানে বলা হয়েছে। আসল রামচন্দ্রের নামাঙ্কিত শিলা লঘুভার হয়ে গিয়ে জলের ওপর ভাসতে থাকে আর তার উপর দিয়ে সৈন্যদল লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে। এখানে রাবণ মেঘনাদের সঙ্গে কথোপকথনকালে সেই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ করেছেন।
“কহিলা রাক্ষসপতি” – রাক্ষসপতি কী বলেছিলেন?
রাক্ষসপতি রাবণ বলেছিলেন যে, ভাই কুম্ভকর্ণকে তিনি অকালে ঘুম থেকে জাগিয়েছিলেন এবং তাই তার মৃতদেহ বজ্রাঘাতে পতিত তরুর মতো সিন্ধুতীরে পড়ে আছে।
“কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী/ইন্দ্রজিৎ” – ইন্দ্রজিৎ কনক-আসন ত্যাগ করেছিলেন কেন?
ইন্দ্রজিৎ ধাত্রীর চরণে প্রণাম জানানোর জন্য ও লঙ্কার কুশল সংবাদ শোনার জন্য কনক-আসন ত্যাগ করেছিলেন।
“জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;” – এই বিস্ময়ের কারণ কী?
রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ রামচন্দ্রকে নিশারণে হত্যা করার পর কে বীরবাহুকে হত্যা করল, তা ভেবে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।
“তবে/এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা,” – এখানে ‘অদ্ভুত বারতা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
মহাবাহু মেঘনাদ তার ধাত্রী জননীরূপী দেবী রমার কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে, তার প্রিয়ানুজ বীরবাহু যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। অথচ যার হাতে তিনি প্রাণ বিসর্জন করেছেন তাকে ইন্দ্রজিৎ নিশারণে খন্ড খন্ড করে কেটে হত্যা করেছিলেন। তাই এই বার্তাকে তার ‘অদ্ভুত বারতা’ বলে মনে হয়েছে।
“তব শরে মরিয়া বাঁচিল।” – কে, কার শরে মরেও বাঁচল?
সীতাপতি রামচন্দ্র রাবণপুত্র মেঘনাদের শরে মরে গিয়েও বেঁচে উঠেছিলেন।
“হৈমবতীসূত তথা নাশিতে তারকে/মহাসুর” – উপমাটি ব্যবহার করা হয়েছে কোন্ ঘটনার অনুষঙ্গে?
ভাই বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর মেঘনাদের যুদ্ধযাত্রার জন্য ‘বীর-আভরণে’ সজ্জিত হওয়ার দৃশ্যটি দুর্গা-পুত্র কার্তিকের তারকাসুর বধের সময়কার যুদ্ধসাজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
প্রলয়োল্লাস
“ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?” – কবি ধ্বংসকে ভয় পেতে নিষেধ করেছেন কেন?
কবি এ প্রশ্ন করেছেন অগ্রদূতের উদ্দেশ্যে। প্রলয় যেমন ধ্বংসলীলা ঘটায় তেমনি প্রলয়ের মাধ্যমেই নতুনের সৃষ্টি হয়। তাই কবি অগ্রদূতকে অভয় দিয়ে বলেছেন প্রলয় চিরসুন্দর।
“এবার মহানিশার শেষে” – কে আসবে?
মহানিশার শেষে আসবে ঊষার হাসি। দীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার নিশাবসান ঘটবে এবং স্বাধীনতার নতুন সূর্যোদয় ভারতবর্ষের আকাশকে আলোকিত করে তুলবে।
“প্রলয় বয়েও আসছে হেসে” – ‘প্রলয়’ বহন করেও হাসির কারণ কী?
নবযুগের বার্তাবাহক মহাকাল বা নবীন বিপ্লবীশক্তিই জীবনহারা অসুন্দরকে ছেদন করে চিরসুন্দরকে গড়ে তুলবে। তাই সে প্রলয় বয়েও মধুর হাসি হাসছে।
“ওরে ওই স্তব্ধ চরাচর!” – ‘চরাচর’ স্তব্ধ কেন?
ভয়ংকরের আগমন বার্তায় মুক্তিকামী মানুষের মনে আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। তাই ‘চরাচর’ স্তব্ধ।
‘দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় ‘দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা’ বলতে ভাবী প্রলয়ের প্রচণ্ডতাকেই বুঝিয়েছেন। নবযুগের সূচনাকারী ভয়ংকর প্রলয় বারোটি সূর্যের ন্যায় দীপ্ত ও তীব্র। সূর্যচক্রের বারোটি অরা (Aura) বা জ্যোতির মিলিত শক্তির দিকেও কবি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন।
“ওরে ওই স্তব্ধ চরাচর।” – চরাচর কেন স্তব্ধ হয়ে গেছে?
জোয়ার ও ভাটার মধ্যবর্তী সময়ে যেমন জল স্থিরতা লাভ করে, ঠিক তেমনি ভয়ংকরের আগমন বার্তায়, ধ্বংসের সম্ভাবনায় প্রকৃতিও যেন স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাই বিশ্ব সেই অনাগত ধ্বংসের জন্য নিশ্চল হয়ে গেছে।
“এবার মহানিশার শেষে/আসবে ঊষা অরুণ হেসে/করুণ বেশে।” – অন্তর্নিহিত অর্থ লেখো।
দীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার অমানিশা ছেদ করে প্রলয়ের আগমনে স্বাধীনতার নবারুণ জেগে উঠবে করুণভাবে হাসতে হাসতে। সেই হাসি করুণ, কেন-না দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ শাসনে আমাদের হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তি হারিয়ে যেতে বসেছে।
“দিগম্বরের জটায় হাসে শিশু-চাঁদের কর” বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
‘দিগম্বর’ শব্দের অর্থ হল বস্ত্রহীন অবস্থা তবে এখানে মহাদেবকে বোঝানো হয়েছে। তাঁর জটায় যেন শিশু-চাঁদ আশ্রয় নিয়েছে। সে স্বাধীনতার, পরাধীনতার বন্ধনমুক্তির হাসি নিয়ে যেন দেশবাসীর সামনে প্রকাশিত হবে।
“আসছে নবীন-জীবনহারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন।” – এই নবীন কারা?
‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম যে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন তা সংঘটিত করবে তরুণ বিপ্লবীরা এরাই কবির ভাষায় ‘নবীন’। কবি সমাজ পরিবর্তনের দ্বায়ভার নবীনদের উপর সমর্পণ করেছেন।
“বধূরা প্রদীপ তুলে ধর” – কবি বধূদের উদ্দেশ্যে কেন এই আহ্বান জানিয়েছেন?
কবি প্রলয় বেশী যে চিরসুন্দরের কল্পনা করেছেন তাকে স্বাগত জানাতে তিনি বধূদের প্রদীপ তুলে ধরতে আহ্বান জানিয়েছেন। কবি চান পুরুষদের জয়ধ্বনির পাশাপাশি সমাজের মহিলারাও যেন সমাজ পরিবর্তনে অংশ নেয়।
“তোরা সব জয়ধ্বনি কর” – কবি কাদের জয় জয়ধ্বনি করতে বলেছেন?
কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় পরাধীন দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের জয়ধ্বনি করতে আহ্বান জানিয়েছেন।
‘কালবোশেখির ঝড়’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ‘কালবোশেখির ঝড়’ বলতে বৈশাখ মাসের বিকালবেলায় আকাশ কালো করে যে ভীষণ ঝড়ের লীলা চলে তাকে বুঝিয়েছেন। এই ‘কালবোশেখি ঝড়’ ধ্বংসের বার্তাবাহী।
“নূতনের কেতন ওড়ে” – কীভাবে নূতনের কেতন ওড়ে?
কবি নজরুল ইসলাম রচিত ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতা অনুযায়ী ‘নূতনের কেতন’ কালবৈশাখীর ঝড়ের দাপটে ওড়ে।
“ওরে ওই হাসছে ভয়ংকর” – ভয়ংকর হাসছে কেন?
পরাধীনতার অচলায়তনের অন্ধকারকে হনন করে নবদিগন্তে নবারুণের বার্তা বহন করে নিয়ে আসছে বলে ভয়ংকর হাসছে।
সিন্ধুতীরে
“সিন্ধুতীরে দেখি দিব্যস্থান।” – ‘দিব্যস্থান’ কেমন ছিল?
সমুদ্রকন্যা পদ্মাবতীর দিব্যস্থান ছিল সমুদ্রের তীরবর্তী পাহাড়ের নীচে দুঃখ-ক্লেশহীন, মনোরম, সত্যধর্ম এবং সদাচারবিশিষ্ট।
“সিন্ধুতীরে রহিছে মাঞ্জস।” – ‘মাঞ্জস’ শব্দের অর্থ কী?
‘মাঞ্জস’ শব্দের অর্থ মান্দাস বা ভেলা (নৌকা)।
“সখী সবে আজ্ঞা দিল” – বক্তা তার সখীদের কী আজ্ঞা দিয়েছিলেন?
সমুদ্রকন্যা পদ্মা উদ্যানে ভ্রমণকালে সমুদ্রতীরে অচৈতন্য পদ্মাবতী ও তাঁর সখীদের দেখতে পেয়ে নিজ-সখীগণকে আজ্ঞা করেন, সেই পঞ্চকন্যাকে বসনে ঢেকে সযত্নে উদ্যানে আনার জন্য।
“কন্যারে ফেলিল যথা” – কন্যাকে কোথায় ফেলা হবে?
সিন্ধুর জলের মাঝে অবস্থিত দেবী পদ্মার পুরী, যেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই; সর্বদা সত্য ধর্ম ও সদাচার পালিত হয়। সেখানে অচৈতন্য অবস্থায় পদ্মাবতী পড়েছিলেন।
“দেখিয়া রূপের কলা বিস্মিত হইল বালা অনুমান করে নিজ চিতে।” – ‘বালা’ কী অনুমান করেছিল?
সমুদ্রতীরে অচৈতন্য অবস্থায় পদ্মাবতীকে পড়ে থাকতে দেখে ‘বালা’ অর্থাৎ সমুদ্রকন্যা পদ্মা অনুমান করেছিলেন হয়তো দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপে কোনো বিদ্যাধরী স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে ভূমিতে পড়ে আছেন।
“বিস্মিত হইল বালা” – কে এবং কেন বিস্মিত হয়ে পড়েন?
সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের ‘পদ্মাসমুদ্র খন্ড’ -এ সিন্ধুর তীরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকা পদ্মাবতীকে দেখে সমুদ্রকন্যা পদ্মা বিস্মিত হয়ে পড়েন।
“ইন্দ্রশাপে বিদ্যাধরি/কিবা স্বর্গভ্রষ্ট করি” – ‘বিদ্যাধরি’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
বিদ্যাধরি বলতে বাগদেবী সরস্বতীকে বোঝানো হয়েছে। সিন্ধুনদের তীরে অচৈতন্য অবস্থায় পদ্মাবতীকে পড়ে থাকতে দেখে সমুদ্রকন্যা পদ্মা তাকে দেবরাজ ইন্দ্রের শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধরি অর্থাৎ সরস্বতী বলে কল্পনা করেছেন।
“মোহিত পাইয়া সিন্ধু-ক্লেশ” – এ কথা বলার কারণ কী?
রত্নসেন ও তার স্ত্রী পদ্মাবতী সিন্ধুনদে নৌকাডুবির বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন অর্থাৎ প্রবল বায়ুপ্রবাহের দরুন সৃষ্ট ঢেউয়ে তাদের দিগ্ভ্রম ঘটে। তবুও ক্লেশক্লিষ্ট পদ্মাবতীর মধ্যে সিন্ধুক্লেশ মোহনীয় রূপলাবণ্য সৃষ্টি করেছে।
সমুদ্রকন্যা সখীদের কী আজ্ঞা দান করেন?
সমুদ্রকন্যা পদ্মা ওরফে লক্ষ্মী সিন্ধুতীরে পদ্মাবতীর সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে তাঁর সখীদের পদ্মাবতী ও তাঁর সখীদের যত্ন করে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।
“পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন” – পঞ্চকন্যা কীভাবে চেতনা ফিরে পেলেন?
সামুদ্রিক ঝড়ে বিপন্ন পদ্মাবতী ও তাঁর চার সখীকে উদ্ধার করে পদ্মা ও তাঁর সখীরা আগুনের তাপ দিয়ে, তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগে ও ওষুধ খাইয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলেন। এভাবেই তাঁরা চেতনা ফিরে পান।
‘সিন্ধুতীরে’ কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
আরাকান রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের অন্তর্গত ‘পদ্মাসমুদ্র খন্ড’ -এর অন্তর্গত প্রথম কবিতা ‘সিন্ধুতীরে’।
“কন্যারে ফেলিল যথা” – কোন্ কন্যার কথা বলা হয়েছে?
‘পদ্মাবতী’ কাব্যের নায়িকা সিংহলরাজের কন্যা পদ্মাবতী, যাঁকে সমুদ্রতীরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন সমুদ্রকন্যা পদ্মা ও তাঁর চারজন সখী তাঁর কথাই এখানে বলা হয়েছে।
“সমুদ্রনৃপতি সুতা” – ‘সমুদ্রনৃপতি সুতা’ কাকে বলা হয়েছে?
‘সমুদ্রনৃপতি সুতা’ বলতে এখানে পদ্মা নাম্নী মেয়েটির কথা বলা হয়েছে। মুহম্মদ জায়সীর কাব্যে যাঁর নাম লক্ষ্মী কিন্তু ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে তাঁর নাম পদ্মা।
“নাহি তথা দুঃখ ক্লেশ” – এর পরিবর্তে সেখানে কী ছিল?
সমুদ্রের প্রবল বাতাস পদ্মাবতীকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল সেই মনোহর দেশটিতে দুঃখ-ক্লেশ ছিল না, পরিবর্তে সেখানে সর্ব সময় সত্যধর্ম পালিত হত।
‘টঙ্গি’ কথার অর্থ কী?
মঞ্চাদির উপর নির্মিত ক্ষুদ্র কুটির, বৃক্ষাবাস বা জলাশয়বক্ষে নির্মিত অট্টালিকা হল টঙ্গি। এখানে অবশ্য সিন্ধুতীরের উদ্যানে অবস্থিত সুলক্ষণযুক্ত বৃক্ষের উপর নির্মিত প্রাসাদ বা বাসস্থান বিশেষের কথা বলা হয়েছে।
‘তুরিত গমনে আসি’ – এসে পদ্মা কী দেখতে পেলেন?
সমুদ্ররাজ কন্যা পদ্মা সখীদের সঙ্গে উদ্যানে প্রাতভ্রমণ করতে গিয়ে চার সখীবেষ্টিত পদ্মাবতীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাঞ্জসে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন।
অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান
“তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান” – গান কোথায় বেড়াবে?
গান ঘুরে বেড়াবে নদীতে, দেশ-গাঁয়ে। আসলে যেখানেই অস্ত্রে রাঙানো ক্ষমতার দম্ভ, সেখানেই গান মানুষকে সঙ্গী করে ঘুরে বেড়াবে।
“রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে” – কথাটির অর্থ কী?
হিংসা আর যুদ্ধে মানব সভ্যতা রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে। মানবদরদী কবি জয় গোস্বামী গান দিয়ে সেই রক্ত মুছে ফেলতে চান।
“অস্ত্র ফ্যালো, অস্ত্র রাখো” – কোথায় অস্ত্র ফেলার কথা বলা হয়েছে?
মানবতাবাদী কবি জয় গোস্বামী অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য অস্ত্রকে পায়ে ফেলতে বলেছেন।
‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ – কবিতায় কবি মাথায় কী কী থাকার কথা বলেছেন?
সভ্যতার পক্ষে অশুভ শকুন ও চিল মাথায় থাকার কথা কবি ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় বলেছেন।
‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় ‘শকুন’ ও ‘চিল’ কীসের প্রতীক?
‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় ‘শকুন’ ও ‘চিল’ আগ্রাসী শক্তি ও হিংস্রতার প্রতীক।
“আমার শুধু একটা কোকিল” – কোকিল কোন কাজ সমাধা করবে বলে কবি আশা প্রকাশ করেন?
কোকিল শুভত্বের প্রতীক, জীবনের প্রতীক। তার গানের সুমধুর সুর অজস্র গানের জন্ম দেবে, যা মানুষকে শুভ বোধে জাগিয়ে তুলবে।
‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ – কবিতায় অস্ত্রকে কোথায় ফেলার কথা বলা হয়েছে?
‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় অস্ত্র পরিত্যাগ করার কথা বলতে গিয়ে কবি অস্ত্রকে পায়ে ফেলে প্রণত হওয়ার কথা বলেছেন।
“গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে” – ‘বর্ম’ কথাটির অর্থ কী?
বর্ম হল শত্রুপক্ষের আক্রমণরোধকারী এক ধরনের পোশাক। এটি লোহা বা চামড়ার তৈরি হতে পারে। বিশেষত, বক্ষদেশকে সুরক্ষিত রাখার ধাতু বা চামড়ার তৈরি আবরণ, কবচ বা তনুত্রাণ হল বর্ম।
ঋষিবালকের প্রধান কাজ কী?
জয় গোস্বামীর ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতায় ঋষিবালক অস্ত্রধারীকে তার অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়ে, গ্রাম নদীপথ পরিক্রমা করিয়ে শান্তির বার্তা বহন করে নিয়ে যায়।
“তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান” – ‘তোমায়’ বলতে কার কথা বলা হয়েছে?
এখানে ‘তোমায়’ বলতে অস্ত্রধারী আক্রমণকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
“তোমায় নিয়ে বেড়াবে গান/নদীতে, দেশগাঁয়ে” – কীভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে তুমি মনে করো?
মানবসভ্যতার ধ্বংসকারী শক্তি তাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি সমর্পণ করার পর বর্ম খুলে আদুর গায়ে দেখলে গানকে ঋষিবালকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। মাথায় ময়ূরপালক গোঁজা ঋষিবালক সদৃশ গানের সন্ধান লাভ করতে পারলেই প্রশ্নোদ্ধৃত পরিস্থিতি তৈরি হওয়া সম্ভব।
‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতাটি কার লেখা, কোন্ কাব্যের অন্তর্গত?
উত্তর আধুনিক কালের সমাজসচেতন কবি জয় গোস্বামীর লেখা ‘পাতার পোশাক’ কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ কবিতাটি গৃহীত হয়েছে।
অস্ত্রকে কেন ফেলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?
অস্ত্র যখন শত্রুকে বধ করে সভ্যতা বা দেশ রক্ষা করে তখন অস্ত্র আমাদের কাম্য। কিন্তু সেই অস্ত্র যখন মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করতে চায় তখন তাকে ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।
অস্ত্রকে কী দিয়ে কবি জয় করতে চান?
মানবতাবাদী কবি জয় গোস্বামী গানে ভুবন ভরিয়ে শত্রুর হৃদয় অর্থাৎ, অস্ত্রকে জয় করতে চেয়েছেন।
“এগিয়ে আসি, উঠে দাঁড়াই”-কে, কীভাবে এগিয়ে আসেন?
কবি জয় গোস্বামী উত্তমপুরুষের জবানিতে অস্ত্রের বিরুদ্ধে হাজারো মানুষের মনে প্রতিরোধ স্পৃহা গড়ে তুলে এগিয়ে যেতে চান।
“গানের বর্ম আজ পরেছি গায়ে” – গানের বর্ম পরিধান করে কবি কোন্ কাজ করতে পারেন?
গানের বর্ম গায়ে পরে কবি হাত নাড়িয়ে অনায়াসে বুলেট তাড়াতে পারেন।
“রক্ত মুছি শুধু গানের গায়ে” – কবি কেন এরূপ উক্তি করেছেন?
সমাজ সভ্যতা ধ্বংসকারী শক্তির অস্ত্রের আঘাতে মানব সভ্যতা রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে। কবি সেই রক্ত গান দিয়ে মুছে ফেলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চান।
প্রবন্ধ
হারিয়ে যাওয়া কালি কলম
“ইতিহাসে ঠাঁই কিন্তু তার পাকা।” – ইতিহাসে কার পাকা ঠাঁই?
ইতিহাসে কলমের ঠাঁই পাকা।
একসময়ে বিদেশে উন্নত ধরনের নিব বের হয়েছিল কীভাবে?
একসময় বিদেশে গোরুর শিং নয়তো কচ্ছপের খোল কেটে বিদেশে উন্নত মানের নিব তৈরির পদ্ধতি বের হয়েছিল।
‘কুইল’ কাকে বলে?
পালকের কলমের ইংরেজি নাম ‘কুইল’। এখন এই ‘বুইল’ কেবল পুরোনো দিনের ছবিতেই দেখা যায়।
‘আশ্চর্য, সবই আজ অবলুপ্তির পথে।’ – আজ কী অবলুপ্তির পথে?
‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ রচনায় বিভিন্ন ধরনের দামি ও কম্পিউটারের দৌরাত্ম্যে এসবের কোণঠাসা অবস্থা বোঝাতে মূল্যবান কলম প্রসঙ্গে আলোচনাকালে, বর্তমান যুগে প্রাবন্ধিকের এমন মন্তব্য।
“কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য।” – কাদের কাছে অস্পৃশ্য?
পকেটমারদের কাছে কলম এখন অস্পৃশ্য। বর্তমানে কলম অতি সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় পকেটমাররা কলম নিয়ে আর হাতসাফাইয়ের খেলা দেখায় না।
“অনেক ধরে ধরে টাইপ-রাইটারে লিখে গেছেন মাত্র একজন।” – কার কথা বলা হয়েছে?
টাইপ-রাইটারে অনেক ধরে ধরে লিখে গেছেন সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়।
“এই নেশা পেয়েছি আমি শরৎদার কাছ থেকে।” – কোন নেশার কথা বলা হয়েছে?
উদ্ধৃত অংশে ফাউন্টেন পেন সংগ্রহ করার নেশার কথা বলা হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এই নেশা পেয়েছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সংগ্রহে অন্তত ডজন দুয়েক ফাউন্টেন পেন ছিল।
“সোনার দোয়াত কলম যে সত্যই হতো” – বক্তা সোনার দোয়াত কলমের কথা কীভাবে জেনেছিলেন?
সুভো ঠাকুরের বিখ্যাত দোয়াত সংগ্রহ দেখতে গিয়ে লেখক শ্রীপান্থ জেনেছিলেন যে, সত্যিই সোনার দোয়াত কলম হতো।
“লাঠি তোমার দিন ফুরাইছে।” – কথাটি কে বলেছেন?
উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
“তাই নিয়ে আমাদের প্রথম লেখালেখি।” – কী নিয়ে লেখকদের প্রথম ‘লেখালেখি’?
বাঁশের কলম, মাটির দোয়াত, ঘরে তৈরি কালি আর কলাপাতা এই নিয়ে লেখকদের প্রথম লেখালেখির সূচনা হয়েছিল।
দোকানদার লেখককে কলম বিক্রি করার আগে কী জাদু দেখিয়েছিলেন?
লেখক যেদিন প্রথম দোকানে গেলেন ফাউন্টেন পেন কিনতে সেদিন দোকানদার জাপানি পাইলট কতটা টেকসই তা বোঝাতে পেনটির খাপ খুলে সার্কাসের ছুরির খেলা দেখানোর আদলে কার্ডবোর্ডের উপরে ছুঁড়ে মারেন, তারপর দেখান নিবটি অক্ষত আছে। লেখক এই জাদু পাইলটেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।
দুজন সাহিত্যিকের নাম করো যাঁদের নেশা ছিল ফাউন্টেন পেন সংগ্রহ করা।
সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় উভয়েরই ফাউন্টেন পেন সংগ্রহ করার নেশা ছিল।
লেখক শ্রীপান্থ ছোটোবেলায় কীসে ‘হোম-টাস্ক’ করতেন?
লেখক শ্রীপান্থ ছোটোবেলায় কলাপাতাকে কাগজের মতো করে কেটে নিয়ে তাতে ‘হোম-টাস্ক’ করতেন এবং সেগুলি বান্ডিল করে স্কুলে নিয়ে যেতেন।
“আমরা ফেরার পথে কোনও পুকুরে তা ফেলে দিয়ে আসতাম।” – বক্তা কেন তা পুকুরে ফেলে দিতেন?
ছোটোবেলায় হোমটাস্কের কলাপাতাগুলি লেখকরা পুকুরে ফেলে দিতেন, কারণ তা গোরু খেয়ে নিলে অমঙ্গল। প্রচলিত আছে, অক্ষরজ্ঞানহীনকে অক্ষর খাওয়ানো পাপ।
“হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” – এ বর্ণিত সবচেয়ে দামি কলমটির কত দাম?
“হারিয়ে যাওয়া কালি কলম” – এ বর্ণিত সবচেয়ে দামি কলমটির দাম ধার্য হয়েছিল আড়াই হাজার পাউন্ড (এক পাউন্ড সমান পঁচাত্তর টাকা)।
‘যার পোশাকি নাম স্টাইলাস’ – ‘স্টাইলাস’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? অথবা, ‘স্টাইলাস’ কী?
রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর জুলিয়াস সিজার যে-ব্রোঞ্জের শলাকা বা কলম ব্যবহার করতেন, তার পোশাকি নাম ছিল ‘স্টাইলাস’।
‘কুইল ড্রাইভারস’ কাদের বলা হত?
‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধ অনুসারে, পালকের কলমকে ইংরেজিতে বলা হয় ‘কুইল’। লর্ড কার্জন বাঙালি সাংবাদিকদের গরম গরম ইংরেজি দেখে তাঁদের ‘বাবু কুইল ড্রাইভারস’ আখ্যা দিয়েছিলেন।
‘দার্শনিক তাঁকেই বলি’ কাকে প্রাবন্ধিক দার্শনিক বলেন?
‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক তাঁকেই দার্শনিক আখ্যা দিয়েছেন, যিনি কানে কলম গুঁজে রেখে তা সারা দুনিয়ায় খুঁজে বেড়ান।
ক্যালিগ্রাফিস্ট কাদের বলে? অথবা, লিপিকুশলী কাদের বলা হত?
‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধ অনুসারে মধ্যযুগে এবং তার পরবর্তীকালে যাঁরা ছিলেন ওস্তাদ কলমবাজ বা লিপিকুশলী, যেসমস্ত লিপিকরদের লেখা পুঁথি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, তাদের বলা হত ক্যালিগ্রাফিস্ট।
‘সমানি সম শীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।’ – উদ্ধৃতিটির বাংলা অর্থ কী?
উদ্ধৃতিটির বাংলা অর্থ হল – ‘সব অক্ষর সমান, প্রতিটি ছত্র সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্ন।’
‘সম্ভবত শেষ পর্যন্ত নিবের কলমের মান মর্যাদা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন একমাত্র সত্যজিৎ রায়।’ – এ কথার যৌক্তিকতা কতখানি?
সত্যজিৎ রায়ের লিপিশিল্পের প্রতি আকর্ষণ সর্বজনবিদিত। তাঁর হস্তলিপির কুশলতা তাঁর অন্যান্য শিল্পকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই তিনিই কেবল নিবের কলমের মানমর্যাদা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।
‘মনে মনে সেই ফরাসি কবির মতো বলেছি’ – ফরাসি কবির মতো কী বলা হয়েছে?
প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ তাঁর ‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে ফরাসি কবির মতো বলেছেন – ‘তুমি সবল, আমি দুর্বল। তুম সাহসী, আমি ভীরু। তবু যদি আমাকে হত্যা করতে চাও, আচ্ছা, তবে তা-ই হোক। ধরে নাও আমি মৃত।’
‘কঙ্কাবতী’ এবং ‘ডমরুধর’ উপন্যাস দুটির লেখক কে বা কারা?
‘কঙ্কাবতী’ এবং ‘ডমরুধর’ উপন্যাস দুটিরই লেখক হলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
“সেই আঘাতেরই পরিণতি নাকি তাঁর মৃত্যু।” – কোন্ আঘাতের পরিণতিতে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে?
বাংলা সাহিত্যে ‘কঙ্কাবতী’ ও ‘ডমরুধর’ -এর স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় নিজের হাতের কলম অসাবধানতাবশত বুকে বিঁধে মারা যান। সেই ঘটনার কথা বলা হয়েছে।
“বাংলায় একটা কথা চালু ছিল” – কথাটি কী?
পাঠ্য রচনা অনুসারে চালু কথাটি হল, ‘কালি নেই, কলম নেই, বলে আমি মুনশি!’
লেখক ছোটোবেলায় কেমন করে কলম তৈরি করতেন?
‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধ অনুসারে লেখকেরা রোগা বাঁশের কঞ্চি কেটে কলম তৈরি করতেন। আর কলম শুধু সূঁচালো হলেই হত না, তার মুখটাও চিরে দিতে হত।
‘নামটা রবীন্দ্রনাথের দেওয়াও হতে পারে’ – রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নামটি কী?
রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ফাউন্টেন পেনের নামটি হল ঝরনা কলম।
‘রিজার্ভার পেন’ কী?
‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ রচনা অনুসারে আদিতে ফাউন্টেন পেনের নাম ছিল ‘রিজার্ভার পেন’। লুইস ওয়াটারম্যান তাকেই অনেক উন্নত করে ফাউন্টেন পেন তৈরি করেন।
লেখা শুকোনোর জন্য কী কী ব্যবহার করা হত? অথবা, একসময় লেখা শুকনো হত কী দিয়ে?
‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ রচনা অনুসারে একসময় লেখা শুকোনোর জন্য বালি ব্যবহার করা হত। পরে সেই কাজ হত ব্লটিং পেপারে।
‘না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।’ – কী না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত?
‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ রচনার লেখক শ্রীপান্থর মতে কাচ, কাট-গ্লাস থেকে ভেড়ার শিং কিংবা সোনার দোয়াত যে কত রকমের হয় তা না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।
“আর সেগুলি বান্ডিল করে নিয়ে যেতাম স্কুলে।” – ‘সেগুলি’ বলতে কীসের কথা বলা হয়েছে? অথবা, ‘সেগুলি বান্ডিল করে নিয়ে যেতাম স্কুলে।’ – কী নিয়ে যেতেন?
লেখকরা ছোটোবেলায় কলাপাতাকে কাগজের মতো করে কেটে তাতে স্কুলের কাজ করতেন। মাস্টারমশাইকে দেখানোর জন্য সেগুলি বান্ডিল করে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।
“আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই।” – কালি তৈরির পদ্ধতিটি কীরূপ ছিল? অথবা, লেখকেরা কীভাবে সহজ পদ্ধতিতে কালি তৈরি করতেন?
কড়াইয়ের ভুসো কালি জলে গুলে তাতে হরীতকী ঘষে বা আতপ চাল পোড়া মিশিয়ে, সবশেষে খুন্তিকে লাল করে পুড়িয়ে সেই জলে ছ্যাঁকা দিয়ে কালি তৈরি হত।
কালি তৈরির উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাচীনদের বলা ছড়া বা প্রচলিত প্রবাদটি উল্লেখ করো। অথবা, ‘প্রাচীনেরা বলতেন’ – প্রাচীনেরা কী বলতেন?
‘হারিয়ে যাওয়া কালি কলম’ প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রাচীনদের বলা ছড়াটি হল, ‘তিল ত্রিফলা শিমুল ছালা/ছাগ দুগ্ধে করি মেলা/লৌহপাত্রে লোহায় ঘষি/ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।’
“এত বছর পরে সেই কলম যখন হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম” – কলম হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম কেন?
শ্রীপান্থের মতে ফাউন্টেন, বল-পেন কিংবা ডট-পেনের বহুল প্রচলনের ফলে বাঁশের কলম আজ হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম।
‘আমরা এত কিছু আয়োজন কোথায় পাব?’ – ‘এত কিছু আয়োজন, বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ভালো কালি তৈরি করতে তিল, ত্রিফলা ও শিমুলের ডাল ছাগলের দুধে ফেলে লোহার পাত্রে রেখে, আর একটি লোহার খুন্তি দিয়ে ঘষে কালি বানাতে হত। এখানে এই আয়োজনের কথাই বলা হয়েছে।
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান
অবিখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের আগে কী সতর্কতা নেওয়া উচিত?
অবিখ্যাত লেখকের বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশের আগে সেটি অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে যাচাই করে নেওয়া উচিত।
“তার ফলে তাঁদের চেষ্টা অধিকতর সফল হয়েছে।” – ‘তার ফলে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
1936 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষাসমিতি নিযুক্ত করে। ‘তার ফলে’ বলতে সেই পরিভাষা সমিতিতে বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, সংস্কৃতজ্ঞপণ্ডিত এবং আরো অনেকের একযোগে কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কী ত্রুটি ছিল?
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পরিভাষা রচনায় একসঙ্গে কাজ না করে পৃথকভাবে করেছিলেন। ফলে বহু ত্রুটি হয়েছিল।
“বাংলায় বিজ্ঞান শেখা তাদের সংস্কারের বিরোধী নয়।” – কাদের পক্ষে এই শিক্ষা সংস্কার বিরোধী নয়?
প্রথম শ্রেণীর পাঠকদের পক্ষে এই শিক্ষা সংস্কার বিরোধী নয়।
“এতে রচনা উৎকট হয়।” – রচনা উৎকট হয় কীসে?
প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসুর মতে অনেক লেখক তাঁদের বক্তব্য ইংরেজিতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। ফলে তাঁদের রচনা হয় উৎকট।
প্রয়োজনমতো বাংলা শব্দ পাওয়া না গেলে কী করা উচিত বলে লেখক মনে করেছেন?
প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসুর মতে প্রয়োজনমতো বাংলা শব্দ পাওয়া না গেলে বৈজ্ঞানিক রচনায় ইংরেজি শব্দই বাংলা বানানে চালানো যেতে পারে।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন?
1936 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন।
ছেলেবেলায় রাজশেখর বসু কার লেখা জ্যামিতি বই পড়তেন?
ছেলেবেলায় প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু ব্রহ্মামোহন মল্লিকের বাংলা জ্যামিতি বই পড়তেন।
“যাদের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক বাংলা গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখা হয় তাদের মোটামুটি দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে।” – শ্রেণি দুটি কী কী?
শ্রেণি দুটি হল – প্রথম, যারা ইংরেজি জানে না বা অতি অল্প জানে। দ্বিতীয়, যারা ইংরেজি জানে এবং ইংরেজি ভাষায় অল্পাধিক বিজ্ঞান পড়েছে।
“আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ কথা বলেছেন।” – শব্দের ‘ত্রিবিধ’ কথা কী?
আলংকারিকগণের উল্লিখিত শব্দের ত্রিবিধ কথা হল অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা।
বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত পরিভাষা সমিতি নবাগত রাসায়নিক বস্তুর ইংরেজি নাম সম্বন্ধে কি বিধান দিয়েছিল?
বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত পরিভাষা সমিতি বিধান দিয়েছেন যে, নবাগত রাসায়নিক বস্তুর ইংরেজি নামই বাংলা বানানে চলবে। যেমন – অক্সিজেন, প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন।
পরিভাষার উদ্দেশ্য কী?
পরিভাষার উদ্দেশ্য ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করা এবং তার অর্থ সুনির্দিষ্ট করা।
‘বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ রচনায় ‘বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ’ বলতে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে।
‘পারিভাষিক শব্দ’ বলতে কী বোঝ?
‘পারিভাষিক শব্দ’ -এর অর্থ হল পরিভাষা সম্বন্ধীয়। পরিভাষা এক ধরনের সংজ্ঞাবিশেষ, যার কোনোরকম অর্থান্তর ঘটে না। ইংরেজিতে একে ‘Glossary’ বা ‘Technical term’ বলে।
কবে, কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয়বার পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত হয়েছিল?
1936 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন বিষয়ের দিপালদের নিয়ে যে-পরিভাষা সমিতি গঠন করা হয়েছিল, তাকেই দ্বিতীয়বারের পরিভাষা সমিতির নিযুক্তিকরণ বলা হয়।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত করেছিল?
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1936 সালে পরিভাষা সমিতি নিযুক্ত করেছিল।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির সঙ্গে কারা কাজ করেছিলেন?
1936 সালে নিযুক্ত পরিভাষা সমিতিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ববিদ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং কয়েকজন লেখককে নিযুক্ত করা হয়েছিল।
‘Sensitized Paper’ -এর অনুবাদ লেখকের মনে কী করলে যথাযথ হয়?
প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসুর মতে ‘Sensitized Paper’ -এর বাংলা ‘সুগ্রাহী কাগজ’ লিখলে যথাযথ হয়।
‘বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ বোঝা কঠিন।’ – কেন?
রাজশেখর বসুর মতে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রাথমিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় না থাকায় বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ বোঝা কঠিন।
অভিধা কাকে বলে?
অভিধা হল শব্দের আভিধানিক অর্থ। যেমন, ‘অরণ্য’ বলতে বোঝায় বন, জঙ্গল ইত্যাদি। এর চেয়ে বিশদ কোনো অর্থ বোঝায় না।
‘লক্ষণা’ বলতে কী বোঝ?
‘লক্ষণা’ হল শব্দের বৃত্তিবিশেষ। শব্দের মুখ্য অর্থের চেয়ে তার অন্য অর্থই যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তাকে বলে লক্ষণা। যেমন, ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ -র অর্থ অরণ্যবাসীদের রোজনামচা।
ব্যঞ্জনা কী?
‘ব্যঞ্জনা’ হল কাজের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশক বৃত্তি। অভিধা ও লক্ষণার দ্বারা যে-অর্থ বোঝানো সম্ভব হয় না, তা ব্যঞ্জনার দ্বারা বোঝানো হয়। যেমন, ‘অরণ্যে রোদন’ কথার অর্থ হল ‘নিষ্ফল আবেদন’।
লেখক বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে অলংকারের প্রয়োগ কম করতে বলেছেন কেন? অথবা, ‘বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে যত কম থাকে ততই ভালো।’ – কী কম থাকার কথা বলা হয়েছে?
লেখক রাজশেখর বসু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে অলংকারের প্রয়োগ কম করতে বলেছেন, কারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ভাষা হওয়া উচিত সহজসরল ও স্পষ্ট।
‘তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা সুসাধ্য হবে।’ – কখন সুসাধ্য হবে বলে লেখকের ধারণা?
ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রাথমিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত কম। এই দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তৃত হলে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যরচনা সুসাধ্য হবে বলে লেখকের মত।
‘এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়।’ – কোন্ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয় বলেছেন লেখক?
অনেকের মতে বিজ্ঞান আলোচনায় পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে সাধারণ শব্দ ব্যবহার করলে রচনা সহজ ও বোধগম্য হয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়।
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় কী বাধা আছে?
প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসুর মতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার এখনও নানারকম বাধা আছে। তার মধ্যে পারিভাষিক শব্দের অপ্রতুলতা, বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার অভাব, রচনাপদ্ধতির দুর্বলতা এবং ভাষার আড়ষ্টতা হল প্রধান।
‘একটি দোষ প্রায় নজরে পড়ে।’ – কোন্ দোষের কথা বলা হয়েছে?
বাংলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লেখক রাজশেখর বসু যে দোষটি প্রায়ই দেখতে পেয়েছেন, তা হল না-জেনে বা কম জেনে তথ্য পরিবেশন করা।
‘এই কথাটি সকল লেখকেরই মনে রাখা উচিত।’ – কোন্ কথাটি?
রাজশেখর বসুর ‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ প্রবন্ধ অনুসারে কথাটি হল, যে-কোনো বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল এবং স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।
বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থের পাঠকদের মধ্যে যারা লেখকের মতে প্রথম শ্রেণিভুক্ত, তাদের বিবরণ দাও।
বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থের পাঠকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিভুক্তরা ইংরেজি জানে না অথবা অতি অল্প জানে। সাধারণত কমবয়সি ছেলেমেয়ে, অল্পশিক্ষিত বয়স্ক লোকেরাই এই শ্রেণিতে পড়ে।
‘গুটিকতক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ হয়তো তারা শিখেছে’ শব্দগুলি কী কী?
‘বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ রচনা অনুসারে প্রথম শ্রেণির পাঠকেরা গুটিকতক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ শিখেছে; সেগুলি হল টাইফয়েড, আয়োডিন, মোটর, ক্রোটন, জেব্রা প্রভৃতি।
“এই শ্রেণির পাঠক ইংরেজি ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত।” – এই শ্রেণির বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসুর মতে যারা ইংরেজি জানে না বা খুবই কম জানে; সেই সমস্ত পাঠক ইংরেজি ভাষার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।
“আমাদের সরকার ক্রমে ক্রমে রাজকার্যে দেশি পরিভাষা চালাচ্ছেন,” – তাতে অনেকে মুশকিলে পড়েছেন কেন?
আমাদের সরকার রাজকার্যে যেভাবে দেশি পরিভাষা ক্রমশ ব্যবহার করাচ্ছেন তাতে অনেকে মুশকিলে পড়ছে, কেন-না তাদের নতুন করে সেগুলি শিখতে হচ্ছে।
‘তাঁদের নূতন করে শিখতে হচ্ছে।’ – কী শেখার কথা বলা হয়েছে?
সরকারি কাজকর্মে বাংলা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার শুরু হওয়ায় অনেক ইংরেজি জানা ব্যক্তি মুশকিলে পড়েছেন। কারণ তাঁদের সেই পরিভাষা নতুন করে শিখতে হচ্ছে।
ব্যাকরণ
কারক ও অ-কারক সম্পর্ক
বাংলায় কী দেখে কারক নির্ণয় করা হয়?
বাংলায় সমপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক দেখে কারক নির্ণয় করা হয়।
মুখ্য কর্মের একটি উদাহরণ দাও।
আমি চিঠি লিখছি। – এখানে ‘চিঠি‘ হলো মুখ্যকর্ম।
বিভক্তি কাকে বলে?
যে সমস্ত চিহ্ন (বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি) শব্দ কিংবা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদ গঠন করে কারক, অকারক ও ক্রিয়ার কাল নির্ণয়ে সাহায্য করে তাকেই বিভক্তি বলে। যেমন – দশম শ্রেণির ছাত্রদেরকে নিয়ে এসো।
দশম শ্রেণি + ‘র’ বিভক্তি
ছাত্রদের + ‘কে’ বিভক্তি
নিরপেক্ষ কর্তার একটি উদাহরণ দাও।
সূর্য উঠলে পদ্ম বিকশিত হয়। এখানে ‘উঠলে’ অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ‘সূর্য’ হল নিরপেক্ষ কর্তা।
ভাববাচ্যের একটি উদাহরণ দাও।
তপন গড়গড়িয়ে পড়ে যায়। (ভাববাচ্যে পরিণত করো)
তপনের গড়গড়িয়ে পড়া হয়। (ভাববাচ্য)
প্রযোজ্য কর্তার একটি উদাহরণ দাও।
বেদে সাপ নাচাচ্ছে। (বেদের প্রভাবে সাপ নাচছে।)
সেকালে বাবুরা পায়রা ওড়াতেন।
শূন্য বিভক্তি কাকে বলে?
যে শব্দবিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দকে পদে পরিণত করে কিন্তু নিজে অপ্রকাশিত থাকে, তাকে শূন্য বিভক্তি বলে। শূন্য বিভক্তির চিহ্ন হল ‘অ’।
সম্বন্ধ পদের বিভক্তি কী কী?
‘র’ এবং ‘এর’ হল সম্বন্ধপদের বিভক্তি।
একটি গৌণ কর্মের উদাহরণ দাও।
আমি তোমাকে বইটা দিলাম।
‘তোমাকে‘ গৌণ কর্ম (‘কাকে’ প্রশ্নর উত্তর)
নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো –
চিঠি পকেটে ছিল।
অধিকরণ কারকে ‘এ’ বিভক্তি।
তির্যক বিভক্তি কাকে বলে?
যে বিভক্তি সব কারকেই ব্যবহৃত হয় তাকে তির্যক বিভক্তি বলে। যেমন – ‘শূন্য’ বিভক্তি, ‘এ’ বিভক্তি।
সম্বন্ধপদ কারক নয় কেন?
সম্বন্ধ পদের সঙ্গে বাক্যস্থিত সমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না বলে, সম্বন্ধপদকে কারক বলা হয় না।
নিম্নরেখ শব্দটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো –
‘পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে।’
কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি।
বিভক্তি ও অনুসর্গের একটি পার্থক্য লেখো।
বিভক্তির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। অন্যদিকে, অনুসর্গের নিজস্ব অর্থ বর্তমান।
‘মন্দিরে বাজছিল পুজার ঘণ্টা‘ – নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
অধিকরণ কারকে, ‘এ’বিভক্তি।
শব্দ বিভক্তির একটি উদাহরণ দাও।
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা।
এখানে ‘মন্দির’ পদটির সঙ্গে ‘এ’ শব্দবিভক্তি যুক্ত হয়েছে।
প্রযোজ্য কর্তা কাকে বলে?
অপরের প্রভাবে কেউ কোনো কাজ করলে তাকে বলে প্রযোজ্য কর্তা। যেমন – বেদে সাপ নাচাচ্ছে।
এখানে বেদের প্রভাবে সাপ নাচছে।
নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো –
‘কহ দাসে লঙ্কার কুশল।
কর্মকারকে ‘শূন্য’ বিভক্তি।
সম্বন্ধ পদ কাকে বলে?
যার অধিকারে কোনো কিছু থাকে কিংবা যার সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর সম্বন্ধ থাকে, তাকেই বলে সম্বন্ধপদ। যেমন – গঙ্গার জল পবিত্র।
‘অস্ত্র রাখো’ – নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
কর্মকারকে ‘শূন্য’ বিভক্তি।
নিরপেক্ষ কর্তা কাকে বলে?
কোনো বাক্যে সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভিন্ন কর্তা থাকলে, অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাটিকে নিরপেক্ষ কর্তা বলে।
কর্মের বীপ্সা বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।
‘বীপ্সা’ শব্দের অর্থ ‘পুনরাবৃত্তি’। একই কর্ম একাধিকবার ব্যবহৃত হলে তাকে কর্মের বীপ্সা বলা হয়।
অকারক কাকে বলে?
বাক্যে এমন কিছু পদ থাকে যাদের ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনে সম্পর্ক নেই, অথচ বাক্যস্থিত অন্য কোনো বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় পদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। এই পদগুলিকে বলা হয় অকারক পদ আর বাক্যান্তর্গত এমন সম্পর্ককে কলা হয় অকারক সম্পর্ক।
ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তি বলতে কী বোঝ?
যে-বিভক্তি ধাতু বা ক্রিয়ামূলের (ক্রিয়াপদের মূল অবিভাজ অংশ পদে যুক্ত হয়ে ধাতুকে ক্রিয়াপদে পরিণত করে তাকে ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তি বলে। যেমন – ‘ইয়াছি’, ‘এন’ প্রভৃতি। আমি বই পড়ি (পড়্ ধাতু) + ই (বিভক্তি)।
সমধাতুজ কর্তা কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।
কর্তা এবং ক্রিয়া যখন একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, তখন সেই ক্রিয়াপদের কর্তাকে সমধাতুজ কর্তা বলে।
উদাহরণ – পড়ুয়ারা চেঁচিয়ে পড়ছে। কর্তা ‘পড়ুয়ারা’ এবং ক্রিয়া ‘পড়ছে’ একই ধাতু ‘পড়্’ থেকে উৎপন্ন।
ব্যতিহার কর্তা কাকে বলে? একটি উদাহরণ দাও।
কোনো ক্রিয়ার দুই কর্তার পারস্পরিক বিনিময় প্রতিযোগিতা বা বিবাদ বোঝালে সেই ক্রিয়ার দুই কর্তাকে ব্যতিহার কর্তা বলে।
উদাহরণ – রাজায় রাজায় যুদ্ধ বেধেছে।
অকারক পদ কতপ্রকার ও কী কী?
অকারক পদ দু-প্রকার – 1. সম্বন্ধপদ এবং 2. সম্বোধন পদ।
সম্বোধন পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
বাক্যে যে-পদের সাহায্যে কাউকে ডাকা হয়, তাই হল সম্বোধন পদ।
উদাহরণ – ‘ওরে, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাইরে।’ এই বাক্যটিতে সম্বোধন পদটি হল ‘ওরে’।
সম্বন্ধপদ ও সম্বোধন পদের একটি পার্থক্য লেখো।
সম্বন্ধপদ ও সম্বোধন পদের একটি পার্থক্য ক্ষ্ম –
সম্বন্ধপদ – সম্বন্ধপদগুলি সাধারণত ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন – ক্ষ্ম হাতের পাঁচ, মিছরির ছুরি প্রভৃতি।
সম্বোধন পদ – সম্বোধন পদ সচরাচর শূন্য বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন – ক্ষ্ম ও মা, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি।
‘তিলে তেল হয়’ এবং ‘তিলে তেল আছে’ – রেখাঙ্কিত পদ দুটি কোন্ কোন্ কারকের দৃষ্টান্ত?
প্রথমটি অপাদান কারক এবং দ্বিতীয়টি অধিকরণ কারকের দৃষ্টান্ত।
‘সেই নগরের নাম আমরা অলিনগর রাখি।’ – রেখাঙ্কিত পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
‘নগরের’ – সম্বন্ধপদে ‘এর’ বিভক্তি।
মুখ্যকর্ম এবং গৌণকর্ম কাকে বলে?V
কোনো বাক্যে দুটি কর্ম থাকলে তাকে দ্বিকর্মক বাক্য বলে। সাধারণত এই কর্ম দুটির একটি প্রাণীবাচক এবং অপরটি অপ্রাণীবাচক হয়। বিভক্তিযুক্ত প্রাণীবাচক কর্মকে গৌণকর্ম আর বিভক্তিহীন অপ্রাণীবাচক কর্মকে মুখ্যকর্ম বলে।
উদাহরণ – আমি তোমাকে কলমটা দিলাম।
গৌণকর্ম – আমি তোমাকে, মুখ্যকর্ম – কলমটা দিলাম
বাংলায় অকারক পদগুলি কারক নয় কেন?
বাংলায় অকারক পদগুলির (সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ) বাক্যস্থিত সমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকায় এরা কারক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। তাই এরা কারক নয়।
সমধাতুজ কর্তার দুটি উদাহরণ দাও।
সমধাতুজ কর্তার উদাহরণ – 1. বাজনা বাজল। (কর্তা ও ক্রিয়া ‘বাজ্’ ধাতু থেকে উৎপন্ন), 2. পড়ুয়ারা চেঁচিয়ে পড়ছে। (কর্তা ও ক্রিয়া ‘পড়্’ ধাতু থেকে উৎপন্ন)
অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তির একটি উদাহরণ দাও।
ট্রেনটি রানাঘাট ছাড়ল। (অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি)
‘সিঁড়ি থেকে নেমে এলে বৈরাগী।’ – নিম্নরেখ পদটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো।
‘সিঁড়ি থেকে’ – অপাদান কারকে ‘থেকে’ অনুসর্গ।
সহযোগী কর্তা কাকে বলে?
বাক্যে একাধিক কর্তার মধ্যে সহযোগিতার ভাব প্রকাশ পেলে তাকে সহযোগী কর্তা বলে।
উদাহরণ – বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।
‘সে অঙ্কে কাঁচা।’ – রেখাঙ্কিত পদটির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো।
‘অঙ্কে’ – অধিকরণ কারকে ‘এ’ বিভক্তি।
দ্বিকর্মক ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
সকর্মক ক্রিয়াযুক্ত বাক্যের দুটি কর্ম থাকলে তাকে দ্বিকর্মক বাক্য এবং ক্রিয়াটিকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।
উদাহরণ – মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এই বাক্যে দুটি কর্ম ‘শিশুকে’ ও ‘চাঁদ’। আর দ্বিকর্মক ক্রিয়া দুটির মধ্যে ‘শিশুকে’ গৌণ কর্ম এবং ‘চাঁদ’ হল মুখ্য কর্ম।
কারক কাকে বলে?
বাক্যের বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় নামপদের সঙ্গে বাক্যস্থিত সমাপিকা ক্রিয়াপদের যে-সম্বন্ধ, তাকেই কারক বলে।
অনুসর্গ বলতে কী বোঝ?
যে সমস্ত অব্যয় বা সার্থক শব্দ বিশেষ্য কিংবা বিশেষ্য স্থানীয় পদের পরে আলাদাভাবে বসে কারক চিহ্ন হিসেবে যুক্ত হয়ে তাদের পদে রূপান্তরিত করে, তাদেরকে বলা হয় অনুসর্গ। যেমন – জন্য, থেকে, দিয়ে প্রভৃতি। বাক্যে প্রয়োগ – আলমারি থেকে আনো।
নির্দেশক বলতে কী বোঝ?
বাক্যের পদাশ্রিত যেসব চিহ্ন একবচন বা বহুবচনকে স্পষ্ট করে তোলে তারাই হল নির্দেশক। একবচনকে বোঝাবার প্রয়োজনে সংখ্যাবাচক টি, টা, খান, খানি এবং বহুবচন বোঝাতে গণ, বৃন্দ, সব, সমূহ প্রভৃতি নির্দেশকও পদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।
উদাহরণ – ছেলেটি খুব ভালো।
শব্দবিভক্তি বলতে কী বোঝ?
যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দটিকে পদে রূপান্তরিত করে তাকে বাক্যে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলে তাকে শব্দবিভক্তি বলে। যেমন – ‘অ’, ‘কে’, ‘এ’, ‘তে’, ‘এর’ প্রভৃতি।
‘অন্ধজনে দেহ আলো।’ – ‘অন্ধজনে’ কী কারক ও কোন্ বিভক্তি?
‘অন্ধজনে’ – নিমিত্ত কারকে ‘এ’ বিভক্তি।
‘প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে।’ – রেখাঙ্কিত পদ দুটি কোন্ কর্মকারককে নির্দেশ করছে?
‘নাচন নাচলে’ – সমধাতুজ কর্মকারককে নির্দেশ করছে।
গায়ক গান গাইছে। – রেখাঙ্কিত পদটি কী ধরনের কর্তা?
রেখাঙ্কিত ‘গায়ক’ পদটি কর্তৃবাচ্যের কর্তার উদাহরণ।
সমাস
‘ঋষিবালক’ – পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
যিনি ঋষি তিনিই বালক – সাধারণ কর্মধারয় সমাস।
পাশের ব্যাসবাক্যটি সমাসবদ্ধ করে তার শ্রেণি নির্ণয় করো – ‘অন্ধ করে যে’ –
অন্ধকার – উপপদ তৎপুরুষ সমাস।
কোন্ সমাসে দুটি বিজাতীয় সমস্যমান পদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়?
রূপক কর্মধারয় সমাসে।
‘উপগ্রহ’ – কথাটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
ক্ষুদ্র গ্রহ – উপগ্রহ (অব্যয়ীভাব)।
‘অলোপ সমাস’ কাকে বলে?
সমাস নিষ্পন্ন হওয়ার পরেও পূর্বপদের বিভক্তি চিহ্ন লোপ না পেয়ে, সমস্যমান পদের মতো থেকে গেলে, তাকে অলোপ সমাস বলে। যেমন – মনের মানুষ – মনের মানুষ (মনমানুষ নয়)।
সমাস কাকে বলে?
পরস্পর অর্থসম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হয়ে যখন একটি নতুন পদ গঠন করে, তখন তাকে সমাস বলে। যেমন – বীণা পানিতে যার = বীণাপানি।
রত্নাকর শব্দটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
রত্নাকর = রত্নের আকর (সম্বন্ধ তৎপুরুষ)।
ক্ষুদ্র গ্রহ – ব্যাসবাক্যটিকে সমাসবদ্ধ করে সমাসের নাম লেখো।
ক্ষুদ্র গ্রহ = উপগ্রহ (অব্যয়ীভাব সমাস)।
একটি নিত্য সমাসের উদাহরণ দাও।
অন্য মনু = মন্বন্তর। অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর।
উপপদ তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে?
যে তৎপুরুষ সমাসে উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন – দিবা করে যে = দিবাকর।
অব্যয়ীভাব সমাসের একটি উদাহরণ দাও।
মিলের অভাব = গরমিল। হিংসার বিপরীত = প্রতিহিংসা।
বহুরূপী শব্দটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো।
বহু রূপ যার = বহুরূপী (বহুব্রীহি সমাস)
ব্যাসবাক্যসহ একটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ দাও।
মায়া ও মমতা = মায়ামমতা (দ্বন্দ্ব সমাস)
কান্না ও কাটি = কান্নাকাটি (দ্বন্দ্ব সমাস)
‘মেঘে ঢাকা’ শব্দটির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম উল্লেখ করো।
মেঘের দ্বারা ঢাকা = মেঘেঢাকা (অলোপ করণ তৎপুরুষ)।
অলোপ সমাস কী?
যে সমাসের সমাসবদ্ধ পদে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলোপ সমাস বলে। এটি স্বতন্ত্র সমাস নয়; দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহিতে অলোপের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়।
গৌর অঙ্গ যাহার – ব্যাসবাক্যটি সমাসবদ্ধ করে সমাসের নাম লেখো।
গৌর অঙ্গ যাহার = গৌরাঙ্গ (বহুব্রীহি সমাস)।
নিত্য সমাস কাকে বলে?
যে সমাসের সাধারণ নিয়মে ব্যাসবাক্য হয় না কিংবা ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে গেলে অন্য পদের প্রয়োজন পড়ে, তাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন – অন্য ভাষা = ভাষান্তর।
‘চরণ কমলের ন্যায়’ – ব্যাসবাক্যটি সমাসবদ্ধ করে সমাসের নাম লেখো।
চরণ কমলের ন্যায় = চরণকমল (উপমিত কর্মধারয়)।
সমাস কাকে বলে?
পরস্পরের মধ্যে অর্থগত সম্পর্ক রয়েছে এমন দুই বা ততোধিক পদের একপদীকরণকেই ব্যাকরণে সমাস বলা হয়।
‘বহুব্রীহি’ শব্দটির সাধারণ অর্থ কী? ব্যাকরণের কোন্ প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয়?
‘বহুব্রীহি’ শব্দটির সাধারণ অর্থ হল বহুব্রীহি (ধন) আছে যার। ব্যাকরণে সমাসের আলোচনায় সমাসের প্রকার হিসেবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
‘দৃঢ়প্রতিজ্ঞ’ শব্দটির ব্যাসবাক্য লিখে দেখাও।
‘দৃঢ়প্রতিজ্ঞ’ শব্দটির ব্যাসবাক্য – দৃঢ় হয়েছে প্রতিজ্ঞা যার।
‘লাভ-লোকসান’ এবং ‘ব্যবসা-বাণিজ্য’ দুটিই দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য কী?
‘লাভ-লোকসান’ এবং ‘ব্যবসা-বাণিজ্য’-এই দুটিই দ্বন্দ্ব সমাস। কিন্তু ‘লাভ-লোকসান’ -এর ক্ষেত্রে সমস্যমান পদ দুটি পরস্পর বিপরীতার্থক। অথচ ‘ব্যবসা-বাণিজ্য’ -এর ক্ষেত্রে সমস্যমান পদ দুটি পরস্পর সমার্থক।
‘ইন্দ্রজিৎ’ পদটির ব্যাসবাক্য নির্ণয় করে এখানে উপপদ কী আছে উল্লেখ করো।
‘ইন্দ্রজিৎ’ পদটির ব্যাসবাক্য ও উপপদ – সমস্ত পদ; ইন্দ্রজি; ব্যাসবাক্য – ইন্দ্রকে জয় করে যে, উপপদ – ইন্দ্র।
মধ্যপদলোপী কর্মধারয় এবং মধ্যপদলোপী বহুব্রীহির মধ্যে পার্থক্য কী?
মধ্যপদলোপী কর্মধারয় এবং মধ্যপদলোপী বহুব্রীহির মধ্যে পার্থক্য –
1. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় – পরপদ বা উত্তরপদের প্রাধান্য থাকে।
2. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি – পূর্বপদ বা উত্তরপদ-কোনোটিই নয়, বোঝানো হয় সম্পূর্ণ অন্য কোনো ব্যক্তি বা বিষয়কে।
ব্যাসবাক্যের ‘ব্যাস’ শব্দটির অর্থ লেখো এবং এর অন্য নাম উল্লেখ করো।
ব্যাসবাক্যের ‘ব্যাস’ শব্দটির অর্থ হল ‘বিস্তার’ এবং এর অন্য নাম হল বিগ্রহবাক্য বা বিস্তারবাক্য।
তৃতীয় বা অন্য পদের অর্থ প্রধান হয় কোন্ সমাসে?
বহুব্রীহি সমাসে তৃতীয় বা অন্যপদের অর্থ প্রধান হয়।
একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের একটি উদাহরণ দাও।
একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের একটি উদাহরণ হল – আমরা > তুমি ও আমি।
‘অলোপ বহুব্রীহি’ সমাসের একটি উদাহরণ দাও।
অলোপ বহুব্রীহি সমাসের একটি উদাহরণ হল – গায়েহলুদ = গায়েহলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে।
বাক্যাশ্রয়ী সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
কোনো বাক্যকে বা বাক্যখণ্ডকে সুসংহতরূপে একটিমাত্র শব্দে পরিণত করে, তাকে বিশেষ্য বা বিশেষণের রূপ দিলে বা কোনো সমাসবদ্ধ পদকে আশ্রয় করে একটি বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হলে তাকে বাক্যাশ্রয়ী সমাস বলে। যেমন – রক্তদানশিবির – রক্তের দান (সম্বন্ধ তৎ) তার জন্য শিবির (নিমিত্ত তৎ)।
নঞ্তৎপুরুষ নঞবহুব্রীহি সমাসের একটি পার্থক্য লেখো।
নঞবহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ ও উত্তরপদের বাইরে তৃতীয় অর্থ প্রধান হয়। যেমন – অনাদি – নেই আদি। কিন্তু নঞ্তৎপুরুষ সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হয়। যেমন – অরাজি – নয় রাজি।
পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় কোন্ সমাসে?
দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদের অর্থপ্রাধান্য ঘটে।
‘সে ও তুমি’ ব্যাসবাক্যটিকে সমাসবদ্ধ করে তার শ্রেণি নির্ণয় করো।
সে ও তুমি > তোমরা – এটি একশেষ দ্বন্দ্বের উদাহরণ।
সমস্তপদ বা সমাসনিষ্পন্ন পদ কাকে বলে?
পূর্বপদ ও উত্তর পদ মিলে সমাসের মাধ্যমে যে নতুন পদ গঠন করে তাকে বলে সমস্ত পদ।
সমস্যমান পদ ও সমস্তপদের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
সমস্যমান পদ ও সমস্তপদের মধ্যে পার্থক্য হল –
1. সমস্যমান পদ – যে পদগুলির মধ্যে সমাস হয় অর্থাৎ ব্যাসবাক্যের অন্তর্গত পদগুলিকে সমস্যমান পদ বলে। উদাহরণ – লোকের আলয় → লোকালয় সমস্যমান পদ
2. সমস্তপদ – সমাসের ফলে অর্থসম্পর্ক যুক্ত একাধিক পদ মিলিত হয়ে যে নতুন পদটি গঠন করে, তাকে সমস্তপদ বলে। উদাহরণ – লোকের আলয় → লোকালয় সমস্তপদ
‘দ্বিগু’ সমাসের সঙ্গে ‘সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি’ সমাসের পার্থক্য কী?
দ্বিগু সমাস ও সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি সমাসের পার্থক্য –
1. দ্বিগু সমাস – সমাসবদ্ধ পদটির দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্তু বা বিষয়ের সমাহার বোঝায়।
2. সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি সমাস – নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্তু বা বিষয়ের সমাহার যার মধ্যে ঘটেছে, সমাসবদ্ধ পদটি সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়।
উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের মধ্যে পার্থক্য কী?
উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের মধ্যে পার্থক্য –
উপমান কর্মধারয় –
1. এটি উপমান ও সাধারণ ধর্মের মধ্যে সমাস।
2. সাধারণ ধর্ম থাকে।
3. পূর্বপদ উপমান এবং পরপদ সাধারণ ধর্ম।
উপমিত কর্মধারয় –
1. এটি উপমিত ও উপমেয়র মধ্যে সমাস।
2. সাধারণ ধর্ম থাকে না।
3. পূর্বপদ উপমেয়, পরপদ উপমান।
অলোপ সমাসের ‘অলোপ’ নামকরণের কারণ কী?
অলোপ সমাসে সমাসবদ্ধ পদটিতে সমাসনিষ্পন্ন হওয়ার পরেও পূর্বপদ বিভক্তিলুপ্ত না হয়ে সমস্যমান পদের মতো থেকে যায়। তাই একে অলোপ সমাস বলা হয়।
বাক্য
‘সংগ্রহ করেছিল দুর্গমের রহস্য।’ – জটিল বাক্যে রূপান্তর করো।
যা সংগ্রহ করেছিল তা দুর্গমের রহস্য/যেটা সংগ্রহ করেছিল সেটা দুর্গমের রহস্য।
‘আমি ছিলাম কালিকলমের ভক্ত।’ – বাক্যটিকে প্রশ্নসূচক বাক্যে রূপান্তর করো।
আমি কি কালিকলমের ভক্ত ছিলাম না?
যোগ্যতাহীন বাক্যের একটি উদাহরণ দাও।
সে চোখ দিয়ে শোনে।
বিমলবাবুর ছেলে হেঁটে হেঁটে স্কুল যায়। – বাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ চিহ্নিত করো।
উদ্দেশ্য – বিমলবাবুর ছেলে
বিধেয় – হেঁটে হেঁটে স্কুলে যায়।
খাঁটি গোরুর দুধ খেতে হবে। – এটি বাক্য নয় কেন?
বাক্যটি আসত্তিহীন। কারণ বাক্যটির মধ্যে পদক্রম নির্দিষ্ট নয়।
‘কথাটা শুনে তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল’ – জটিল বাক্যে পরিবর্তন করো।
কথাটা যখন শুনল তখন তপনের চোখ মার্বেল হয়ে গেল।
চাঁদের পাহাড়ের গল্প কখনও ভুলব না। – বাক্যটিকে প্রশ্নসূচক বাক্যে রূপান্তর করো।
চাঁদের পাহাড়ের গল্প কি কখনো ভুলব?
উদ্দেশ ও বিধেয় অংশ চিহ্নিত করো – ‘ওরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।’
ওরা – উদ্দেশ্য
ভয়ে কাঠ হয়ে গেল – বিধেয়
সূর্য পশ্চিমদিকে উদিত হয়। – বাক্য নির্মাণের কোন্ শর্ত এখানে লঙ্ঘন করা হয়েছে?
উল্লিখিত অংশে বাক্য নির্মাণের ‘যোগ্যতা’-র শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে।
‘কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য।’ – জটিল বাক্যে পরিবর্তন করো।
যারা কলম ব্যবহার করত তাদের কাছে কলম আজ অস্পৃশ্য।
বিধেয় প্রসারকের একটি উদাহরণ দাও।
ছেলেটি পরীক্ষার আগে ঘরে বসে একমনে – বিধেয়র প্রসারক।
পড়ছে – বিধেয়।
‘ঠিক ইসাবের মতো জামাটি না পেলে ও স্কুলে যাবে না।’ – যৌগিক বাক্যে পরিণত করো।
‘ঠিক ইসাবের মতো জামাটি চাই নইলে ও স্কুলে যাবে না।’
সে তখন যেতে পারবে না – হ্যাঁ-বাচক বাক্যে পরিবর্তন করো।
সে তখন যেতে অপারগ।
নির্দেশক বাক্যের একটি উদাহরণ দাও।
অনেকবার বইটা পড়েছি। ভারি মজা হবে। বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা আছে।
বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলআনাই বজায় আছে। – সরল বাক্যে পরিণত করো।
বাবুটির স্বাস্থ্য গেলেও শখ ষোলো আনাই বজায় আছে।
আর কোনো ভয় নেই। – প্রশ্নোবোধক বাক্যে পরিবর্তন করো।
আর কি কোনো ভয় আছে?
‘আমি গ্রামের ছেলে’ – বাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ চিহ্নিত করো।
আমি – উদ্দেশ্য।
গ্রামের ছেলে – বিধেয়।
একটি অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের উদাহরণ দাও।
বাংলার এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করবেন না।
অসিতবাবু আর কোনো প্রশ্ন করলেন না – প্রশ্নবাচক বাক্যে পরিবর্তন করো।
অসিতবাবু কি আর কোনো প্রশ্ন করলেন?
বাক্য কাকে বলে?
যে পদ বা পদসমষ্টির দ্বারা বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় সেই পদ বা পদসমষ্টিকে বলে বাক্য।
বাক্য গঠনের শর্তগুলি কী কী?
বাক্য গঠনের শর্তগুলি হল – যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি।
অপ্রধান খণ্ডবাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
যে খণ্ডবাক্য বাক্যস্থিত অন্য খণ্ডবাক্যের ওপর নির্ভর করে ভাব প্রকাশ করে তাকে বলে অপ্রধান খণ্ডবাক্য।
উদাহরণ – মৈনাকবাবু জানেন না তাঁর ছেলে কোথায় গেছে। – এখানে ‘তাঁর ছেলে কোথায় গেছে’ এই খণ্ডবাক্যটি পূর্ববর্তী ‘মৈনাকবাবু জানেন না’ এই খণ্ডবাক্যের ওপর নির্ভর করে তার ভাব প্রকাশ করায় একটি একটি অপ্রধান খণ্ডবাক্য।
প্রধান খণ্ডবাক্য কাকে বলে? উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দাও।
বাক্যস্থিত যে খণ্ডবাক্য তার ভাব স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে, অন্য কোনো খণ্ডবাক্যের ওপর নির্ভরশীল ‘থাকে না তাকে বলে প্রধান খণ্ডবাক্য।
উদাহরণ – এখানে ‘মৈনাকবাবু জানেন না’ এই খণ্ডবাক্যটি নিজেই তার ভাব স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারায় এটি একটি প্রধান খণ্ডবাক্য।
গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – সরলবাক্য, জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য ও মিশ্রবাক্য।
ওখানে যেও না। – এটি কী ধরনের বাক্য তা বুঝিয়ে লেখো।
এটি সরলবাক্য। সরলবাক্য গঠনের নিয়মানুসারে একটি মাত্র কর্তা ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োজন। প্রদত্ত বাক্যটিতে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (যেও) বর্তমান। যদিও বাক্যটিতে কর্তা (উদ্দেশ্য) উহ্য আছে।
সরলবাক্য কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র বিধেয় অর্থাৎ, একটিমাত্র কর্তা ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে বলে সরলবাক্য।
উদাহরণ – সে বাড়ি গেল। প্রদত্ত বাক্যটিতে একটি মাত্র উদ্দেশ্য (সে) ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (গেল) আছে। তাই বাক্যটি সরলবাক্যের উদাহরণ।
অর্থানুসারে বাক্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
অর্থানুসারে বাক্যকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – নির্দেশক বাক্য, প্রশ্নবোধক বাক্য, আজ্ঞাসূচক বাক্য, প্রার্থনা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য, সন্দেহবাচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য, আবেগসূচক বাক্য এবং শর্তসাপেক্ষ বা কার্যকারাত্মক বাক্য।
অন্ত্যর্থক বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
যে নিদের্শক বাক্যে কোনো বিবৃতি বা নির্দেশের অনুমোদন বা সমর্থন বোঝায় তাকে বলে অস্ত্যর্থক বাক্য।
উদাহরণ – জল ঢালু পথে বয়ে চলেছে। গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে।
নাস্ত্যর্থক বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
যে নিদের্শক বাক্যে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের অস্বীকৃতি বা নিষেধ বোঝায় তাকে বলে নাস্ত্যর্থক বাক্য।
উদাহরণ – আজ তার খেলতে ভালো লাগছে না। ওর আজ পড়ায় মন বসছে না।
বিদ্যাসাগরের মতো সত্য কথা বলতে অল্প মানুষকেই দেখা যায়। – বাক্যটি অর্থগত দিক থেকে কোন্ শ্রেণির?
বাক্যটি অর্থগত দিক থেকে নির্দেশক বাক্য।
উদাহরণ সহযোগে প্রার্থনাসূচক বাক্য ও অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
প্রার্থনাসূচক বাক্যে বক্তার মনোগত যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় তার ভঙ্গি অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ভঙ্গির থেকে আলাদা। বিশেষ করে অনুগ্রহ প্রকাশ কালে প্রার্থনাসূচক বাক্যের সুর পরিবর্তিত হয়।
এ কী বিপদ! – এটি অর্থগত দিক দিয়ে কোন প্রকারের বাক্য?
এটি অর্থগত দিক দিয়ে বিস্ময়বোধক বাক্য।
কারও পক্ষে তার কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। বাক্যটিকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করো।
বাক্যটিকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করলে হয় – কেউ যে তার কথা সহজে বিশ্বাস করবে এমন ব্যাপার অসম্ভব।
নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যটি পরিবর্তন করো – বৃথা আশা মরিতে মরিতে মরে না। (যৌগিক বাক্যে)
বৃথা আশা মরিতে চায় কিন্তু মরিতে পারে না।
তা হতে পারে না। – বাক্যটিকে অন্ত্যর্থক বাক্যে রূপান্তরিত করো।
বাক্যটিকে অস্ত্যর্থক বাক্যে রূপান্তরিত করলে হয় – তা হওয়া অসম্ভব।
নির্মেঘ আকাশেও বৃষ্টি হচ্ছে। – বাক্যটিকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তিত করলে কী হয়?
বাক্যটিকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তিত করলে হয় – আকাশ নির্মেঘ অথচ বৃষ্টি হচ্ছে।
বিপদে অধৈর্য হোয়ো না। – বাক্যটির নির্দেশক বাক্যে পরিবর্তিত রূপটি লেখো।
বাক্যটির নির্দেশক বাক্যে পরিবর্তিত রূপটি হল – বিপদে অধৈর্য হতে নেই।
বাক্যের আকাঙ্ক্ষা বলতে কী বোঝ?
বাক্যের খানিকটা অংশ বললে বাকি অংশটুকু বলা বা শোনার জন্য যে আগ্রহ তৈরি হয়, তাকেই বাক্যের আকাঙ্ক্ষা বলা হয়।
অর্থ ও গঠন অনুসারে বাক্যকে ক-টি ভাগে ভাগ করা যায়?
বাক্যকে অর্থ অনুসারে সাতটি এবং গঠন অনুসারে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।
যোগ্যতা বলতে কী বোঝো?
বাক্যে পরস্পর সন্নিবিষ্ট পদগুলির মিলিত অর্থ আমাদের জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা ও যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হওয়াকে বাক্যের যোগ্যতা বলে। যেমন – ছেলেটি পা দিয়ে ভাত খাচ্ছে (যোগ্যতাহীন)। ছেলেটি হাত দিয়ে ভাত খাচ্ছে (যোগ্যতাপূর্ণ)।
বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। – বাক্যটির উদ্দেশ্য অংশ ও বিধেয় অংশ পৃথক করে লেখো।
বাক্যটির উদ্দেশ্যে অংশ হল – বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। বাক্যটির বিধেয় অংশ হল – বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।
পিকু ভাত খায়। – বাক্যটির বিধেয় অংশ সম্প্রসারিত করে পুনরায় লেখো।
বাক্যটির বিধেয় অংশ সম্প্রসারিত করলে হয় – পিকু দাদার সঙ্গে দুপুরে মাছ-ভাত খায়।
মোহন বিকেলে খেলা করে। – বাক্যটির উদ্দেশ্য অংশ চিহ্নিত করে তা সম্প্রসারিত করো।
বাক্যটির উদ্দেশ্য অংশ হল – মোহন। এই উদ্দেশ্য অংশের সম্প্রসারিত রূপ হল – বারাসতের ছোট্ট মোহন।
পদগুচ্ছ বা পদখণ্ড বলতে কী বোঝো?
পদগুচ্ছ হল কতকগুলি অর্থবহ শব্দসমষ্টি যার কোনো উদ্দেশ্য ও বিধেয় নেই। একে বলা যেতে পারে আপেক্ষিক একক অনুসারে গোষ্ঠীবদ্ধ পদসমষ্টি।
বিশেষণ ও বিশেষ্য যোগে একটি বিশেষ্য খণ্ড তৈরি করে বাক্যে ব্যবহার করো।
বিশেষণ ও বিশেষ্য যোগে তৈরি একটি বিশেষ্য খণ্ড হল –
বিশেষণ – আমার বান্ধবী
বিশেষ্য – ইশিতা
বিশেষ্যখণ্ড
বাক্যে ব্যবহার – আমার বান্ধবী ইশিতা আমাদের বাড়িতে পড়তে এসেছে।
স্বাধীন বা নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
যে খণ্ডবাক্যগুলি পরস্পর স্বাধীনভাবে অবস্থান করে তাদের বলা হয় স্বাধীন বা নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্য।
উদাহরণ – সে বাড়ি গেল এবং ভাত খেল। – এখানে ‘সে বাড়ি গেল’, ‘(সে) ভাত খেল’ উভয়ই স্বাধীন খণ্ডবাক্য যা ‘এবং’ সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়েছে। এই বাক্যগুলি ভাব প্রকাশের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়।
বাচ্য
‘এসো যুগান্তের কবি।’ – ভাববাচ্যে পরিণত করো।
যুগান্তের কবির আসা হোক।
কর্মবাচ্যের একটি উদাহরণ দাও।
পুলিশ কর্তৃক চোরটি ধৃত হয়েছে।
সিঁড়ি থেকে নামা হল। – বাক্যটিকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করো।
সিঁড়ি থেকে নামলাম।
‘নদীর ধারে তার জন্ম হইয়াছে।’ – কর্তৃবাচ্যে পরিণত করো।
নদীর ধারে সে জন্মাইয়াছে। (কর্তৃবাচ্য)
কর্তৃবাচ্য কাকে বলে?
যে বাচ্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে এবং ক্রিয়া কর্তার অধীন হয়, তাকে কর্তৃবাচ্য বলে।
যেমন – তুহিন গান ভালোবাসে।
‘তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।’ – ভাববাচ্যে পরিবর্তন করো।
তাদের আর স্বপ্ন দেখা হল না। (ভাববাচ্য)।
কর্মকর্তৃবাচ্য কাকে বলে?
যে বাচ্যে কর্তার উল্লেখ থাকে না এবং কর্ম কর্তার মতো কাজ করে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে।
যেমন – পাতা নড়ে। বাঁশি বাজে। ঢোল বাজে।
বুড়ো মানুষের কথাটা শুনো। – কর্মবাচ্যে পরিণত করো।
বুড়ো মানুষ কর্তৃক উক্ত কথাটা শোনা হোক।
কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তনের অন্তত একটি পদ্ধতি উল্লেখ করো।
দ্বিকর্মক ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যের গৌণকর্মের রূপ একই থাকে আর মুখ্য কর্মটি বিভক্তিশূন্য হয়। যেমন – মা বোনকে ভূগোল পড়াচ্ছেন। (কর্তৃবাচ্য) – মায়ের দ্বারা বোনকে ভূগোল পড়ানো হচ্ছে।
কর্তৃবাচ্যের কর্তার সঙ্গে ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি বসে ও কর্তার পরে ‘দ্বারা’ বা ‘কর্তৃক’ অনুসর্গ যুক্ত হয়। যেমন – বিকাশ খাবার খেয়েছে (কর্তৃবাচ্য) – বিকাশের দ্বারা খাবার খাওয়া হয়েছে। (কর্মবাচ্য)
‘এ কার লেখা?’ – কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন করো।
এ কে লিখেছে? (কর্তৃবাচ্য)।
কর্মবাচ্যে বলতে কী বোঝ?
যে-বাচ্যে কর্মপদটিই প্রধান এবং ক্রিয়া তার অনুগামী হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন – পুলিশের হাতে চোর ধরা পড়েছে।
কর্মবাচ্যে ক্রিয়া কার অনুগামী হয়ত?
কর্মবাচ্যে ক্রিয়াটি কর্মপদের অনুগামী হয়।
ভাববাচ্য বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।
যে বাক্যবিন্যাসে সাধারণত ক্রিয়ার ভাবটিই প্রধান বলে বিবেচিত হয়, তাকে ভাববাচ্য বলে।
ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের একটি নিয়ম লেখো।
রামের ঘুমানো হচ্ছে। (ভাব)
রাম ঘুমোচ্ছে। (কর্তৃ)
ভাববাচ্যে ক্রিয়ার ভাবটির প্রাধান্য থাকে। যেমন – উপরের উদাহরণে ‘হচ্ছে’ ক্রিয়াপদটি ‘ঘুমানো’কে বোঝাচ্ছে। ‘ঘুমানো’ পদটি ক্রিয়ার ভাব। ভাবটির প্রাধান্য লোপ করে কর্তার উপর ক্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেই কর্তৃবাচ্যে পরিণত হবে।
কর্তাহীন ভাববাচ্যের একটি দৃষ্টান্ত দাও।
এত গরম জলে স্নান করা যায় না। (কর্তাহীন ভাববাচ্য)
আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু। – ভাববাচ্যে পরিণত করো।
আমি এখন তবে রওনা হলাম কাকাবাবু। (ভাববাচ্য)
তপনের বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকানো হয়। – কর্তৃবাচ্যে পরিণত করো।
তপন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায়। (কর্তৃবাচ্য)
জয়ন্তকে ডাকা হোক। – কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করো।
জয়ন্তকে ডাকো। (কর্তৃবাচ্য)
“ঘুড়ি ওড়ে।’ – এটি কী ধরনের বাচ্য?
‘ঘুড়ি ওড়ে।’ – এটি কর্মকর্তৃবাচ্য।
সে বলিল না। (ভাববাচ্যে পরিণত করো)।
তার বলা হইল না। (ভাববাচ্য)
সম্বন্ধ কর্তা ভাববাচ্যের একটি উদাহরণ দাও।
তমালের আজ বেরোনো হবে না।
গৌণ কর্ম-কর্তা ভাববাচ্যের একটি উদাহরণ দাও।
অমিতকে এবার দিল্লি যেতে হবে।
ভাববাচ্যে কর্তা লুপ্ত অবস্থায় আছে (লুপ্ত কর্তা ভাববাচ্য) – এরকম একটি বাক্য লেখো।
বোর্ডের খেলাটা খেলা যাক।
‘আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।’ – কর্তৃবাচ্যটিকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করো।
আমার দ্বারা তাকে ছেড়ে দেওয়া হল (কর্মবাচ্য)।
‘আপনার কি খাওয়া হবে?’ – বাক্যটি কোন্ বাচ্যে উদাহরণ?
প্রশ্নে উদ্ধৃত বাক্যটি ভাববাচ্যের উদাহরণ।
কর্তৃবাচ্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
কর্তৃবাচ্যের দুটি বৈশিষ্ট্য –
1. কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি সকর্মক ও অকর্মক দু-রকমই হতে পারে। যেমন – তোমরা আসছ কখন? (অকর্মক), মৃন্ময় কি ভাত খেয়েছে? (সকর্মক)
2. কর্তৃবাচ্যে সাধারণত শূন্য বিভক্তি হলেও ক্ষেত্রবিশেষে ‘এ’ বা ‘তে’ বিভক্তিও বসে। যেমন – মাটিতে সকলেই বসবে। (মাটি + ‘তে’ বিভক্তি)
কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে রূপান্তরের একটি নিয়ম লেখো।
কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার মূল ধাতুর সঙ্গে ‘আ’ প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবিশেষ্য পদ গঠন করা হয় এবং এরপর কোথাও ‘হ্’বা ‘যা’ ধাতুর প্রয়োগ ঘটে। যেমন – ওখানে বেশ বেড়ালাম। (কর্তৃবাচ্য) > ওখানে বেশ বেড়ানো হল। (ভাববাচ্য)।
‘অসত্যের দ্বারা সত্য বিনষ্ট হয় না।’ – বাক্যটির বাচ্য উল্লেখ করে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করো।
‘অসত্যের দ্বারা সত্য বিনষ্ট হয় না।’ (কর্মবাচ্য) > অসত্য সত্যকে বিনষ্ট করতে পারে না। (কর্তৃবাচ্য)
কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরের একটি নিয়ম লেখো।
‘কর্মবাচ্যের যৌগিক ক্রিয়ার সমাপিকা অংশটিতলোপ পায়ত এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে কর্তৃপদের পুরুষ ও বচন বিভক্তিযুক্ত করে কর্তৃবাচ্যের একপদী ক্রিয়া গঠন করা হয়। যেমন – শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক এই পরামর্শে সম্মতি দেওয়া হল। (কর্মবাচ্য) > শিক্ষক মহাশয় এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। (কর্তৃবাচ্য)
কোন্ বাচ্যের রূপান্তর সম্ভব নয়?
কর্মকর্তৃবাচ্যের রূপান্তর সম্ভব নয়।
বাচ্য বলতে কী বোঝ?
ক্রিয়ার যে প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে জানা যায় যে, ক্রিয়ার সঙ্গে এই বাক্যের কর্তা, কর্ম না ক্রিয়ার ভাবটিই প্রাধান্য পেয়েছে-বাক্যের সেই প্রকাশভঙ্গিকেই বাচ্য বলে।
যেমন – কথা আমিই বলব।
ক্রিয়ার রূপভেদ (প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য)
কথাটা আমাকেই বলতে হবে।
সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে বাচ্য কতপ্রকার?
সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে বাচ্য চারপ্রকার – 1. কর্তৃবাচ্য, 2. কর্মবাচ্য, 3. ভাববাচ্য ও 4. কর্মকর্তৃবাচ্য।
2026 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের বাংলা বিষয়ের অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সাজেশন এখানেই শেষ হলো। এই প্রশ্নগুলি তোমাদের কতটা সাহায্য করলো বা অন্য কোনো বিষয়ের সাজেশন প্রয়োজন কিনা, তা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানিও। আর্টিকেলটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না!
এছাড়াও, টেলিগ্রামের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন—আমরা আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।



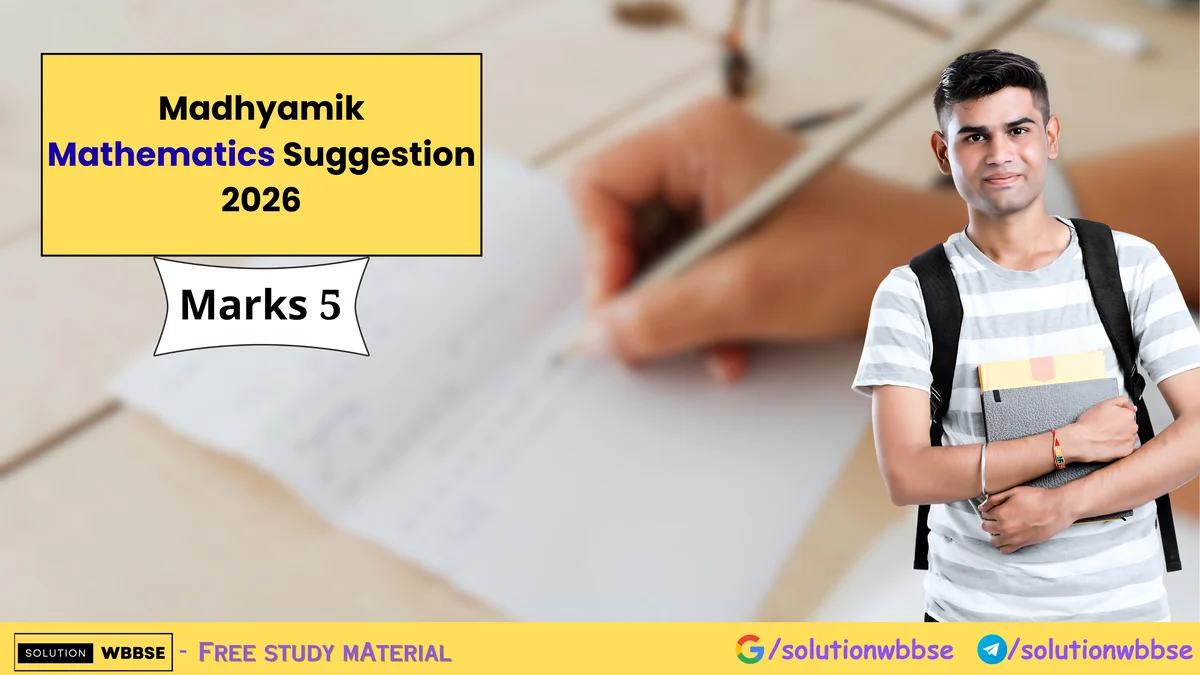
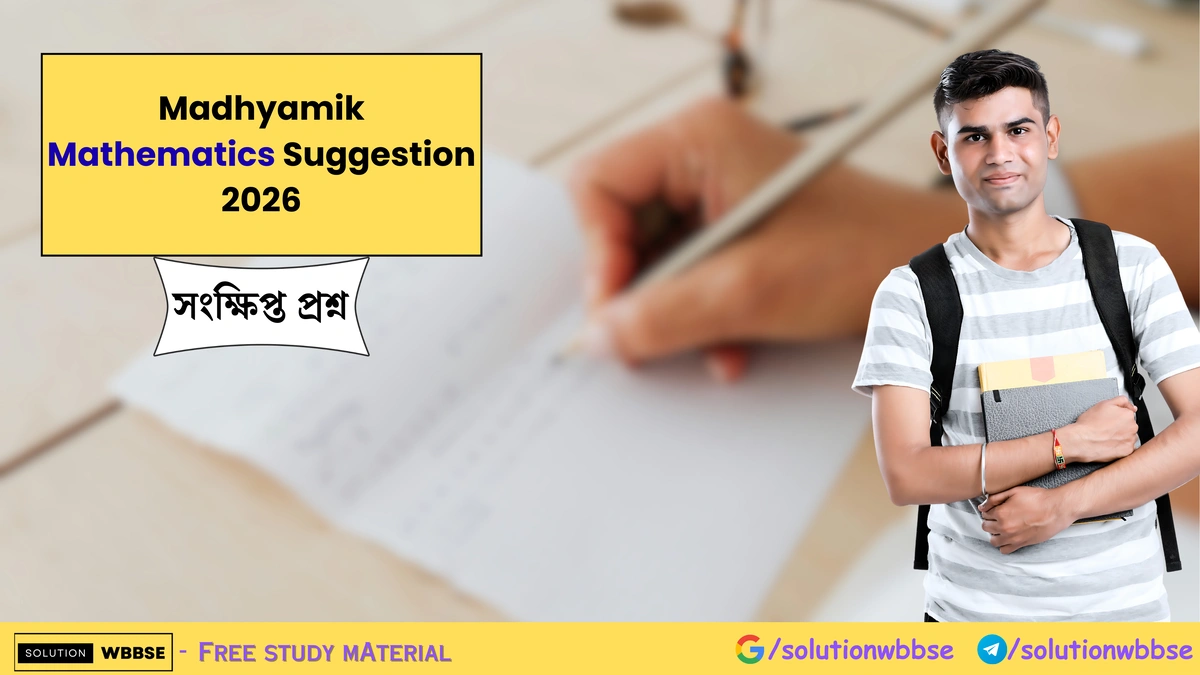

মন্তব্য করুন