এই আর্টিকেলে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাসের নমুনা প্রশ্ন ও উত্তরপত্র নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ষষ্ঠ শ্রেণীর পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই আসতে দেখা যায়।
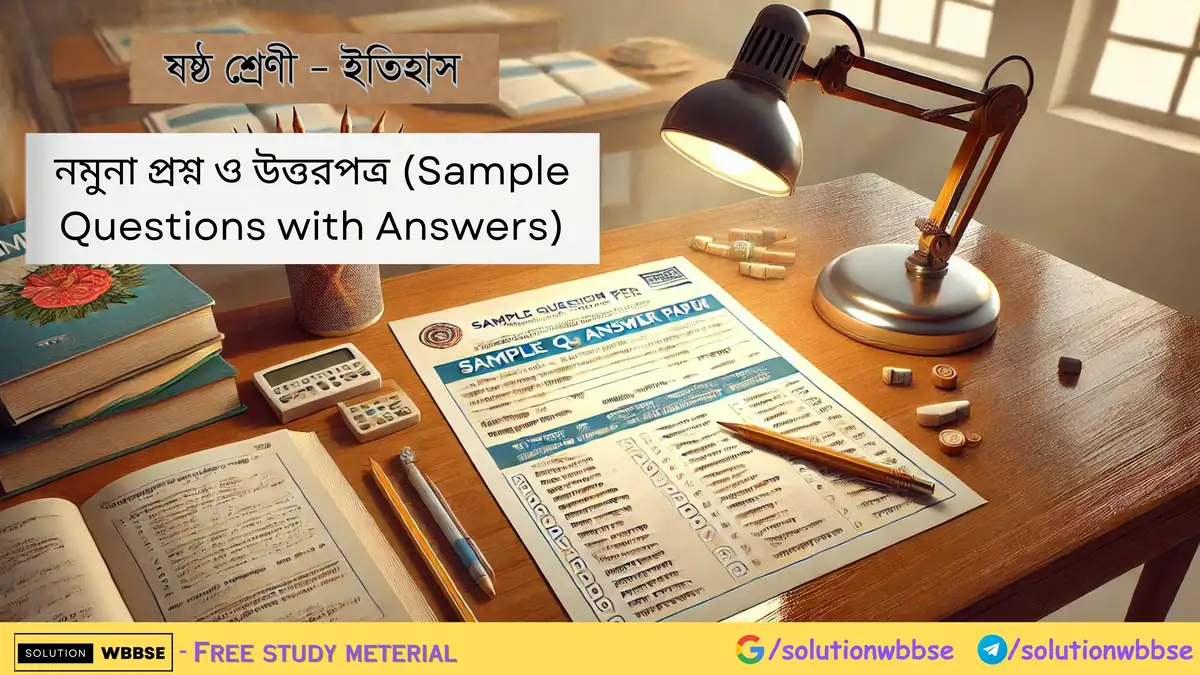
প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পূর্ণমান – ১৫
ঠিক উত্তরটি বেছে নাও (১×৩=৩)
প্রধাFনত কীসের আকার থেকে আদিম মানুষের নানারকম ভাগ করা হয়?
a. মস্তিষ্কের
b. পায়ের
c. হাতের আঙুলের
d. মেরুদণ্ডের
উত্তর – a. মস্তিষ্কের।
হরপ্পা সভ্যতার বাড়িগুলি কী দিয়ে তৈরি হত?
a. কাদামাটি দিয়ে
b. কাঠ দিয়ে
c. পোড়া ইট দিয়ে
d. পাথর দিয়ে
উত্তর – c. পোড়া ইট দিয়ে।
কোনটি আদিম মানুষের সংস্কৃতির অংশ ছিল না?
a. পাথরের ভোঁতা হাতিয়ার বানানো
b. গাছের ছাল গায়ে জড়ানো
c. পাথর ঠুকে আগুন জ্বালানো
d. পোড়া ইটের বাড়ি বানানো
উত্তর – d. পোড়া ইটের বাড়ি বানানো।
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো (চার-পাঁচটি শব্দ বা একটি বাক্যের মধ্যে) (১×২=২)
ভীমবেটকার গুহায় পুরোনো পাথরের যুগের মানুষেরা থাকত। – ঠিক না ভুল লেখো।
উত্তর – ঠিক।
কালিবঙ্গান, মেহেরগড়, ধোলাবিরা, বানাওয়ালি। – বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো।
উত্তর – মেহেরগড়।
নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর লেখো (দু-তিনটি বাক্যের মধ্যে) (২×১=২)
আদিম মানুষ এক সময়ে যাযাবর ছিল কেন?
আদিম মানুষরা চাষবাস জানত না। তাই তারা পশুশিকার করে কাঁচামাংস ও ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করত। ক্রমে তারা পশুপালন শেখে। তাই নিজেদের খাবার ও পালিত পশুর খাদ্যের (মূলত ঘাস) সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। এজন্যই আদিম মানুষ যাযাবর জীবনযাপন করত।
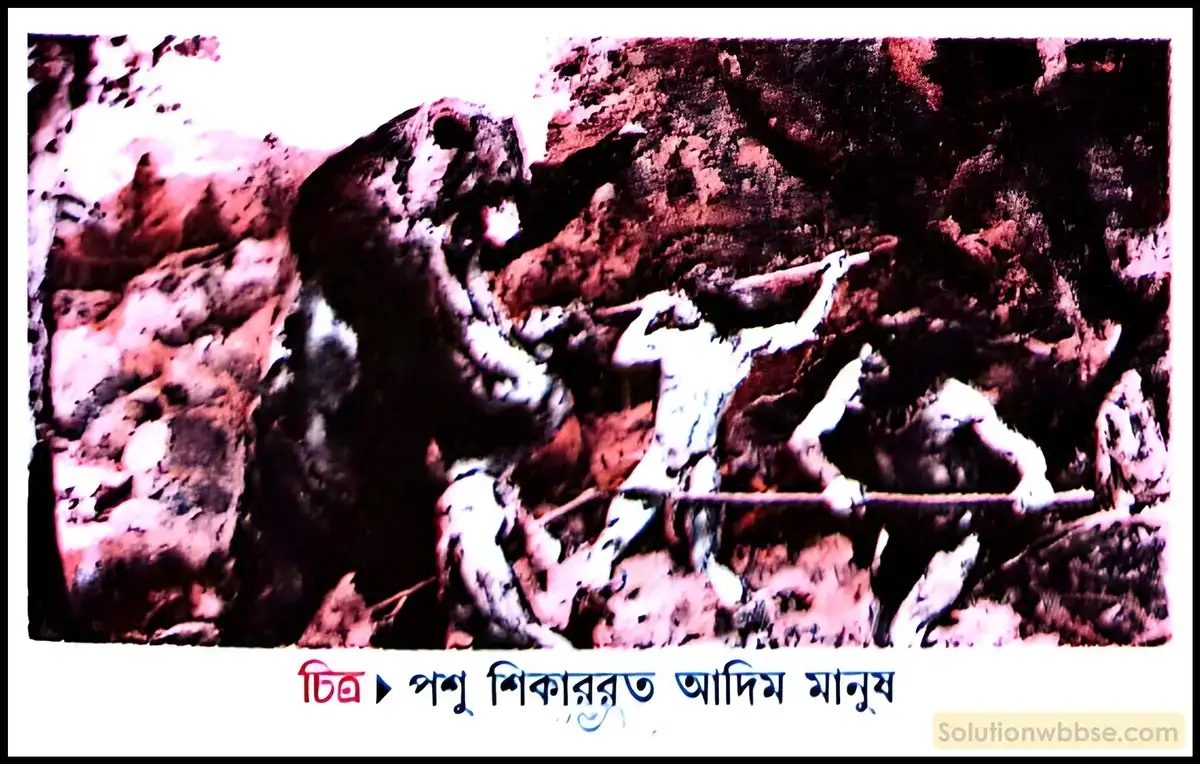
হরপ্পা সভ্যতাকে প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা বলা হয় কেন?
হরপ্পা সভ্যতাকে প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা বলা হয়, কারণ এযুগে লিপির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা আজ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করা যায়নি।
নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর লেখো (চার-পাঁচটি বাক্যের মধ্যে) (৩×১=৩)
আগুনের ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবনে কী কী পরিবর্তন এসেছিল?
প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই আগুন জ্বালাতে ও ব্যবহার করতে পারে। আগুন জ্বালাতে শেখার ফলে –
- আদিম মানুষেরা প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে রক্ষা পায়।
- আগুনকে যেহেতু বন্য পশুরা ভয় পায়, সেহেতু এদের আক্রমণের হাত থেকে আদিম মানুষরা রক্ষা পায়।
- তখন থেকে তারা কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে খাওয়া শুরু করে। এর ফলে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। শরীরে জোর বাড়ে ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। অন্যদিকে দেহাবয়বেও নানা পরিবর্তন হতে শুরু করে। চোয়াল সরু হয়, সামনের ধারালো উঁচু দাঁত ছোট হতে থাকে।
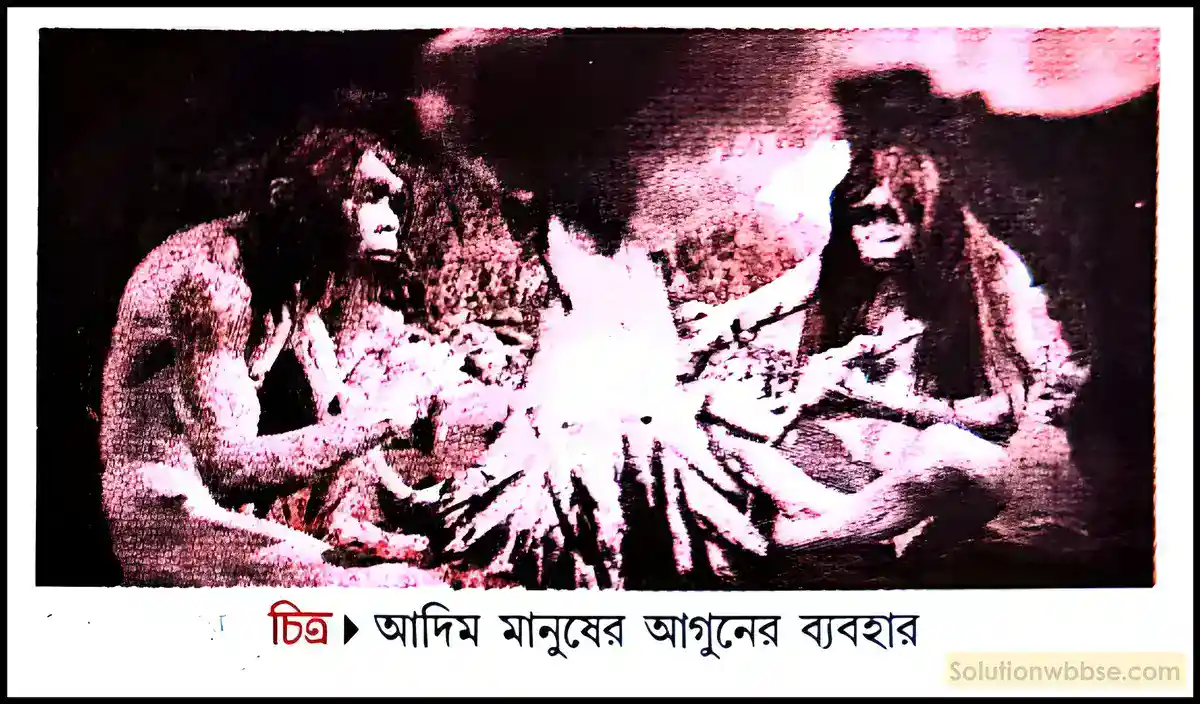
হরপ্পা সভ্যতার লিপি – টীকা লেখো।
সিন্ধুসভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতাকে বলা হয় ভারতের প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা। কারণ এযুগের মানুষ লিপির ব্যবহার জানত। যদিও আজ অবধি এই লিপিগুলি পাঠোদ্ধার করা যায়নি। এই লিপিগুলি হল ভারতের সর্বপ্রাচীন লিপি। এগুলি হল সাংকেতিকধর্মী। তাতে 375-400টির মতো চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। লিপিগুলি লেখা হত ডানদিক থেকে বামদিকে।
লিপিগুলি থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সেসময় হরপ্পাবাসীগণ যথেষ্ট লেখাপড়া জানত। লিপিগুলির দ্বারা লেখাপড়ার কথা বিস্তারিত জানা না গেলেও অনুমান করা হয় যে, তারা দ্রাবিড় ভাষায় একে অপরের সঙ্গে কথা বলত।
নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর লেখো (আট-দশটি বাক্যের মধ্যে) (৫×১=৫)
আদিম মানুষ জোট বেঁধেছিল কেন? জোটবাঁধার কী সুফল হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?
আদিম মানুষ নানা কারণে জোট বেঁধে থাকত। কারণ –
- তাতে তাদের পশু শিকারের কাজ সহজ হত।
- হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণের হাত থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারত।
- জোট বেঁধে থাকার ফলে আদিম মানুষের খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ হত।
জোট বাঁধার ফল – জোট বেঁধে থাকার ফলে আদিম মানুষের অনেক লাভ হয়েছিল। যেমন –
- তাদের মধ্যে সামাজিকতা গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।
- অনেকের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা গড়ে ওঠে।
- বিভিন্ন জীবিকার উদ্ভব হয়।
- হিংস্র পশুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা ও পশু শিকারের কাজ সহজ হয়।
- একসঙ্গে অনেক মানুষ থাকার ফলে কাজ ভাগ করে নেওয়া সহজ হয়।
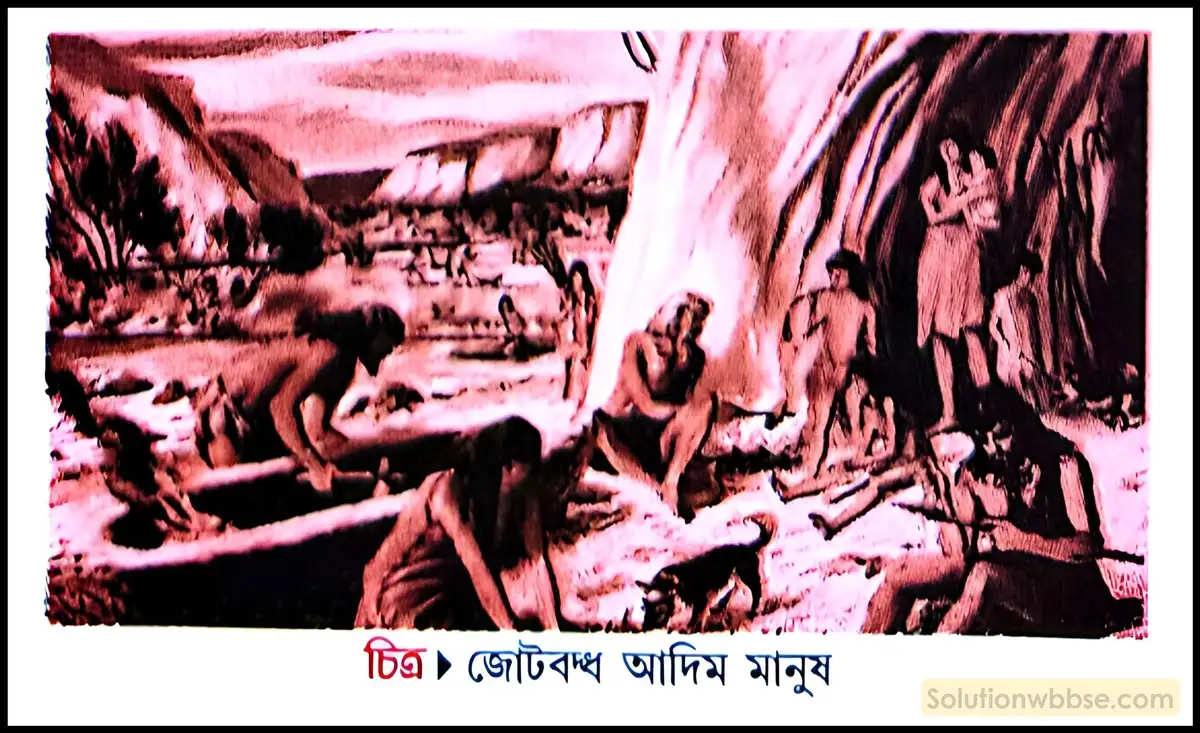
হরপ্পা সভ্যতার মানুষ স্বাস্থ্যসচেতন ও পরিবেশ-সচেতন ছিল – মন্তব্যটি যুক্তি দিয়ে আলোচনা করো।
হরপ্পা সভ্যতার মানুষ যে স্বাস্থ্যসচেতন ও পরিবেশ-সচেতন ছিল তার অনেক প্রমাণই পাওয়া গেছে, নিম্নে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হল –
স্বাস্থ্য সচেতনতা – সিন্ধু উপত্যকা খনন করে পোড়ামাটির ইটের তৈরি অনেক ঘরবাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ঘরগুলির ওপরের দিকে একটি করে পাথরের ঝাঁঝরি (ভেন্টিলেটর) ব্যবহার করা হত। যাতে ঘরের মধ্যে বায়ু চলাচল স্বাভাবিক থাকে।
হরপ্পা সভ্যতার প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে কূপ পাওয়া গেছে। প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার এবং স্নানাগার থাকত। এর থেকে বোঝা যায় যে, সিন্ধুবাসীরা নিয়মিত স্নান করতেন। যাতে তাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে।
পরিবেশ চেতনা – নগরগুলিতে প্রশস্ত রাস্তা ছিল। এগুলি গড়ে উঠত সমান ও সমান্তরাল পদ্ধতিতে। আবার বড়ো বড়ো রাস্তাগুলি থেকে বেরিয়ে আসত ছোটো ছোটো গলি।
- বাড়ির আব্রুরক্ষাসহ বাড়িগুলিকে ধুলোবালির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাড়ির দরজা-জানালাগুলি বড়ো রাস্তার দিকে রাখা হত না।
- প্রত্যেক বাড়ির সামনে আবর্জনা ফেলার জন্য একটি করে ডাস্টবিন রাখা হত।
- তারা নগরগুলিতে সুন্দর নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। নর্দমাগুলিতে ম্যানহোলের ব্যবস্থা ছিল।
দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পূর্ণমান – ২০
ঠিক উত্তরটি বেছে নাও (যে কোনো পাঁচটি) (১×৫=৫)
মেগালিথ হল –
a. পাথরের গাড়ি
b. পাথরের সমাধি
c. পাথরের খেলনা
d. পাথরের বাড়ি
উত্তর – b. পাথরের সমাধি।
এর কোনটি বর্ণাশ্রমের অংশ নয়?
a. ব্রাহ্মণ
b. ক্ষত্রিয়
c. শূদ্র
d. নৃপতি
উত্তর – d. নৃপতি।
জৈন ধর্মের প্রধান প্রচারককে বলা হত –
a. কেবলিন
b. মহাবীর
c. তীর্থংকর
d. পার্শ্বনাথ
উত্তর – c. তীর্থংকর।
ষোড়শ মহাজনপদের সময়ে মগধের কৃষির উন্নতি হয়েছিল, কারণ –
a. সবাই কৃষিকাজ করত
b. রাজারা কৃষিকাজের জন্য সকলকে বাধ্য করতেন
c. লোহার লাঙল ব্যবহার করা হত
d. সব জায়গায় জমি খুব উর্বর ছিল
উত্তর – c. লোহার লাঙল ব্যবহার করা হত।
সুয়ান জাং চিন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন –
a. ভারতীয় উপমহাদেশ বেড়ানোর জন্য
b. বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করার জন্য
c. হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য
d. হর্ষবর্ধনের শাসন বিষয়ে বই লেখার জন্য
উত্তর – খ. বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করার জন্য।
কুষাণ-মুদ্রায় সম্রাটদের মাথার পিছনে একরকমের জ্যোতির্বলয় বানানো হত –
a. সম্রাট ও দেবতা একই বোঝানোর জন্য
b. সম্রাটরা আসলে দেবতা ছিলেন, তা বোঝানোর জন্য
c. কুষাণ সম্রাটরা জাদুবিদ্যা জানতেন, তা বোঝানোর জন্য
d. সম্রাটদের শক্তিশালী বোঝানোর জন্য
উত্তর – a. সম্রাট ও দেবতা একই বোঝানোর জন্য
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো (যে-কোনো পাঁচটি) (১×৫=৫)
অশ্বমেধ, বাজপেয়, শতমান, রাজসূয় – বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো।
উত্তর – শতমান।
আদি বৈদিক যুগের কোন্ প্রতিষ্ঠানে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারতেন?
উত্তর – আদি বৈদিক যুগের নারীরা সমিতিগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারতেন।
বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের প্রধান ভাষা ছিল সংস্কৃত। – ঠিক না ভুল লেখো।
উত্তর – ভুল।
ষোড়শ মহাজনপদের সময়ের একটি গণরাজ্যের নাম লেখো।
উত্তর – ষোড়শ মহাজনপদের সময়ের একটি গণরাজ্যের নাম হল বৃজি।
শকরাজ রুদ্রদামনের সম্পর্কে জানবার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শিলালেখ ___। – শূন্যস্থান পূরণ করো।
উত্তর – জুনাগড়।
গুপ্ত সম্রাটরা বড়ো বড়ো উপাধি ব্যবহার করতেন কেন?
উত্তর – তাঁদের বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ইত্যাদি বোঝানোর জন্য।
নীচের যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর লেখো (দু-তিনটি বাক্যের মধ্যে) (২×২=৪)
চিত্রিত ধূসর মাটির পাত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।
চিত্রিত ধূসর মাটির পাত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল –
- এগুলির রং ছিল ধূসর এবং
- এগুলির গায়ে নানা ধরনের চিত্র আঁকা হত।
বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্ন কী কী?
বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্ন হল – বুদ্ধ, ধম্ম ও সংঘ।
শক-সাতবাহনদের লড়াই -এর কারণ কী ছিল?
শক ও সাতবাহন রাজাদের মধ্যে লড়াইয়ের প্রধান কারণ ছিল –
- মালব ছিল সেসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। তাই মালবের অধিকার নিয়ে শক ও সাতবাহন শাসকদের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়।
- এই লড়াইয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মালবের কোসায় অবস্থিত হিরার খনি দখল করা।
- এ ছাড়া পশ্চিম মালব ও দাক্ষিণাত্যের উপকূল দিয়ে বাণিজ্য করার জন্য উভয় শক্তির লড়াই হয়।
নীচের যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর লেখো (চার-পাঁচটি বাক্যের মধ্যে) (৩×২=৬)
চতুরাশ্রম – টীকা লেখো।
বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জীবন চারটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এই পর্যায়গুলিকেই একত্রে বলা হয় চতুরাশ্রম। এগুলি হল –
- ব্রহ্মচর্য – ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করা।
- গার্হস্থ্য – শিক্ষালাভের পর প্রত্যেকের বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করে সংসার জীবনযাপন করা ছিল গার্হস্থ্য।
- বাণপ্রস্থ – সংসার জীবন ত্যাগ করে, ধর্মচর্চার জন্য বনে বাস করাই বাণপ্রস্থ।
- সন্ন্যাস – সংসারের মায়া কাটিয়ে ঈশ্বর চিন্তায় শেষ জীবন কাটানো হল সন্ন্যাস আশ্রম।
নব্যধর্ম আন্দোলন ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের নব্যধর্ম আন্দোলন ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক। এই মন্তব্যটির পক্ষে বলা যায় যে –
- যে সময় নব্যধর্মের উদ্ভব হয়েছিল, সে সময়টি ছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। এই সময়েই ভারতে দ্বিতীয় নগরায়ণ হয়। এই সময় উত্তর ভারতে 16টি মহাজনপদের উদ্ভব হয়। এ ছাড়া ভারতের নানা প্রান্তে অসংখ্য ছোটো-বড়ো জনপদ গড়ে ওঠে।
- মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ দু-জনেই প্রথম জীবনে ছিলেন নগরবাসী। তাঁরা নগরগুলিতে ধর্মপ্রচারও করেন। মহাবীর ধর্মপ্রচার করেন মগধ ও কোশলে। অন্যদিকে গৌতম বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করেন সারনাথ ও রাজগৃহে। এই দুই ধর্মপ্রচারকের মৃত্যুও হয় নগরেই।
- তা ছাড়া নগরের মানুষরা লেখাপড়া জানত। সংস্কৃত ভাষা জানত। তাই তাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অসারতা বুঝতে দেরি হয়নি।
- অন্যদিকে সেইসময় অনেক রাজাই নব্যধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ফলে প্রতিবাদী ধর্ম সহজেই নগরগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।
হর্ষবর্ধন ও দ্বিতীয় পুলকেশির লড়াই -এর ফল কী হয়েছিল?
থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এই তথ্য জানা যায় আইহোল লেখ থেকে। জানা যায়, হর্ষবর্ধন দ্বিতীয় পুলকেশির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ফলে দক্ষিণ দিকে তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল নর্মদা নদী পর্যন্ত। এ ছাড়া তিনি নিজ কন্যাকে চালুক্য রাজের হাতে অর্পণ করেন।
নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর লেখো (আট-দশটি বাক্যের মধ্যে) (৫×১=৫)
বৈদিক সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা ও সামাজিক ভেদাভেদ কেন খারাপ, সে বিষয়ে আলোচনা করে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।
শিয়াখালা, হুগলি,
13/12/22
প্রিয় বিনয়,
কেমন আছো? আমি এখানে একপ্রকার আছি। অনেকদিন হল তোমার কোনো খবর নেই। তাই চিঠি লেখা। জানো আমি ছুটিতে প্রাচীন বৈদিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। কী জানলাম, সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাই-বা কী হল তা তোমায় চিঠির মাধ্যমে জানালাম।
জানো তো, বৈদিক সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। যথা – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সমাজে ব্রাহ্মণদের দারুণ মর্যাদা ও প্রভাব ছিল। তারা যাগযজ্ঞ করত, পূজা করত। বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণরা প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিল। সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত ছিল শূদ্ররা। এরা বাকি তিন বর্ণের সেবা করত। তাদের শিক্ষাদীক্ষা ছিল না। তাদের নামমাত্রও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তারা এতটাই অচ্ছুৎ ছিল যে, তারা গ্রামের এক কোণায় বসবাস করত। সমাজের সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজগুলি করে তারা জীবিকানির্বাহ করত।
ভাগ্যিস এই বর্ণপ্রথা এখন নেই। থাকলে কী হত তা বোঝাই যায়। তখন যদি এই সামাজিক ভেদাভেদ না থাকত, তাহলে ভালো হত। কারণ তাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয়েরই উন্নতি হত। সবাই সব কাজ করত। কেউ কাউকে ঘৃণা করত না।
আজ এই পর্যন্তই লিখলাম। আমার ভালোবাসা নিয়ো। তোমার বাবা-মাকে আমার প্রণাম জানিয়ো।
ইতি-
অত্রি
ঠিকানা –
ডানলপ, কলকাতা
মগধের উত্থান প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য সম্ভব হয়েছিল – মগধ মহাজনপদটির ভৌগোলিক অবস্থান আলোচনা করে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।
মগধ রাজ্যের উত্থান প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য সম্ভব হয়েছিল। তার কারণ –
- মগধ রাজ্যটি গঙ্গা, শোন ও গণ্ডক – এই তিনটি নদীর উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল। ফলে এখানকার মাটি ছিল খুব উর্বর। তাই এখানে খুব ভালো ফসল ফলত।
- পাহাড় ঘেরা মগধের রাজধানী রাজগৃহ ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। তাই বাইরের কোনো শক্তি একে আক্রমণ করতে পারেনি।
- মগধের কৃষি ও ব্যাবসাবাণিজ্য ছিল খুবই উন্নত। নদীপথে মগধের বণিকরা ব্যাবসাবাণিজ্য করত।
- মগধের উন্নতির মূলে ছিল তার খনিজ সম্পদ। মগধ রাজ্য ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। এখানে তামা ও লোহার খনি ছিল। লোহার তৈরি লাঙলের ফাল দিয়ে মগধবাসীরা কৃষিতে বিপ্লব ঘটায়। আবার লোহার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র মগধের সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।
গুপ্ত ও বাকাটক প্রশাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো।
গুপ্ত ও বাকাটক শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা –
সাদৃশ্য –
- উভয় শাসনব্যবস্থাতেই বিকেন্দ্রীকরণ নীতি চালু ছিল। যেমন – সমগ্র সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল কতকগুলি প্রদেশে। প্রদেশগুলি বিভক্ত ছিল জেলায় এবং জেলাগুলি আবার গ্রামে বিভক্ত ছিল।
- উভয় ব্যবস্থায় অমাত্য বা সচিব বলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী ছিলেন।
বৈসাদৃশ্য –
- গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় সম্রাট ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধান। অপরদিকে বাকাটক শাসনব্যবস্থায় সাম্রাজ্যের প্রধানকে বলা হত মহারাজ।
- গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় প্রদেশগুলিকে বলা হত ভুক্তি। অপরদিকে বাকাটক শাসনব্যবস্থায় প্রদেশগুলিকে বলা হত রাজ্য।
- গুপ্ত শাসনব্যবস্থায় প্রদেশের শাসনভার দেখাশোনা করতেন রাজপুত্ররা। অপরদিকে বাকাটক শাসনব্যবস্থায় প্রদেশের শাসনভার ছিল সেনাপতির ওপর।
তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পূর্ণমান – ৭০
ঠিক উত্তরটি বেছে নাও (১×১৪=১৪)
ইন্দো-আর্য ভাষার সবথেকে পুরোনো সাহিত্য –
a. ঋকসংহিতা
b. ব্রাহ্মণ
c. মহাভারত
d. বেদান্ত
উত্তর – a. ঋকসংহিতা।
এর মধ্যে কোন্ জায়গাতে চিত্রিত ধূসর রঙের মাটির পাত্র পাওয়া যায় না?
a. অত্রঞ্জিখেরাতে
b. হস্তিনাপুরে
c. অহিচ্ছত্র -এ
d. মেহেরগড়ে
উত্তর – d. মেহেরগড়ে।
মেগালিথ পাওয়া গেছে এমন একটি জায়গা হল –
a. হস্তিনাপুর
b. বুরজাহোম
c. হরপ্পা
d. লোথাল
উত্তর – b. বুরজাহোম।
দক্ষিণ ভারতের একমাত্র মহাজনপদ ছিল –
a. অবন্তি
b. মগধ
c. কোশল
d. অস্মক
উত্তর – d. অস্মক।
সুদ গ্রহণ করা কোন্ ধর্মে নিন্দার বিষয় ছিল?
a. ব্রাহ্মণ্য
b. বৌদ্ধ
c. জৈন
d. আজীবিক
উত্তর – a. ব্রাহ্মণ্য।
সেলিউকাস নিকেটর সেনাপতি ছিলেন –
a. বিম কদফিসেস -এর
b. আলেকজান্ডার -এর
c. দিয়োদোরাস -এর
d. এলডার পোরোস -এর
উত্তর – b. আলেকজান্ডার -এর।
লুম্বিনী গ্রামের ‘বলি’ নামক কর সম্রাট অশোক ছাড় দিয়েছিলেন। কারণ –
a. লুম্বিনী অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না
b. লুম্বিনীর সাধারণ মানুষ বিদ্রোহী ছিল
c. গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল
d. লুম্বিনীর প্রজারা কৃষিকাজ করত না
উত্তর – c. গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল।
গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমিদানকে বলা হত –
a. সামন্ত ব্যবস্থা
b. কার্ষাপণ
c. অগ্রহার ব্যবস্থা
d. বণিকগ্রাম
উত্তর – c. অগ্রহার ব্যবস্থা।
ফাসিয়ানের মতে, নগরের বাইরে থাকত –
a. বৈশ্যরা
b. রত্নিনরা
c. অমাত্যরা
d. চণ্ডালরা
উত্তর – d. চণ্ডালরা।
এর মধ্যে কোনটি হর্ষবর্ধনের লেখা নয়?
a. অমরকোশ
b. রত্নাবলী
c. প্রিয়দর্শিকা
d. নাগানন্দ
উত্তর – a. অমরকোশ।
শুশ্রুত সংহিতায় প্রধান যন্ত্র বলা হয়েছে –
a. হাতুড়িকে
b. ছুঁচকে
c. হাতকে
d. লাঙলকে
উত্তর – c. হাতকে।
এর মধ্যে কোনটি মহাকাব্য নয়?
a. রামায়ণ
b. মণিমেখলাই
c. মহাভাষ্য
d. শিলপ্পাদিকারম
উত্তর – c. মহাভাষ্য।
সেন্ট থমাস খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন কার আমলে?
a. আলেকজান্ডার
b. মিনান্দার
c. গন্ডোফারনেস
d. টলেমি
উত্তর – c. গন্ডোফারনেস।
এদের মধ্যে কে ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত রূপে পরিচিত ছিলেন না?
a. বুদ্ধযশ
b. কুমারজীব
c. পরমার্থ
d. হাল
উত্তর – d. হাল।
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো (চার-পাঁচটি শব্দ বা একটি বাক্যের মধ্যে) (১×১৪=১৪)
স্তম্ভ দুটি মেলাও
| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |
| 1. দয়েব | a. বৈদিক মুদ্রা |
| 2. শতমান | b. বৌদ্ধ সংগীতি |
| 3. সমাধি | c. জাতক |
| 4. যশ | d. জেন্দ অবেস্তা |
| 5. পালি ভাষা | e. ইনামগাঁও |
উত্তর –
| ‘ক’ স্তম্ভ | ‘খ’ স্তম্ভ |
| 1. দয়েব | d. জেন্দ অবেস্তা |
| 2. শতমান | a. বৈদিক মুদ্রা |
| 3. সমাধি | e. ইনামগাঁও |
| 4. যশ | b. বৌদ্ধ সংগীতি |
| 5. পালি ভাষা | c. জাতক |
দমঅর্ত উপাধি নেন কনিষ্ক। – ঠিক না ভুল লেখো।
উত্তর – ভুল।
সকলোত্তরপথনাথ বলা হত হর্ষবর্ধনকে। – ঠিক না ভুল লেখো।
উত্তর – ঠিক।
প্রাচীন ভারতে দ্বিতীয় নগরায়ণ কবে দেখা গিয়েছিল?
উত্তর – প্রাচীন ভারতে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দ্বিতীয় নগরায়ণ দেখা গিয়েছিল।
তামিলনাড়ুর ___ বন্দরে দূরপাল্লার বাণিজ্য হত। – শূন্যস্থান পূরণ করো।
উত্তর – কাবেরীপট্টিনম।
ব্রাহ্মী, সংস্কৃত, খরোষ্ঠী, দেবনাগরী। – বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো।
উত্তর – সংস্কৃত।
মথুরা শিল্পের মূল বিষয়বস্তু কী ছিল?
উত্তর – মথুরা শিল্পের মূল বিষয়বস্তু ছিল – বৌদ্ধ ধর্ম ও বুদ্ধের মূর্তি।
চলন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে পিছনে ঘুরে তির ছোঁড়ার কায়দা ভারতে কারা প্রচলন করে?
উত্তর – চলন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে পিছনে ঘুরে তির ছোঁড়ার কায়দা পহ্লবরা প্রচলন করেছিল।
ফো-কুয়ো-কি বইয়ের বিষয়বস্তু কী?
উত্তর – ফো-কুয়ো-কি বইয়ের বিষয়বস্তু ভারতবর্ষ ভ্রমণের বিবরণ বা অভিমত।
প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রকে কী বলা হত?
উত্তর – প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রকে বলা হত উপবেদ।
গ্রিসের একটি নগর-রাষ্ট্রের নাম কী?
উত্তর – গ্রিসের একটি নগর-রাষ্ট্রের নাম এথেন্স।
কোন্ গুপ্ত সম্রাটকে ‘ভারতের রক্ষাকারী’ বলা হয়?
উত্তর – গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তকে ‘ভারতের রক্ষাকারী’ বলা হয়।
আইহোল প্রশস্তি কার লেখা?
উত্তর – আইহোল প্রশস্তি দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি রবিকীর্তির লেখা।
ব্রহ্মসিদ্ধান্ত গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর – ব্রহ্মগুপ্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত গ্রন্থটি রচনা করেন।
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো (দু-তিনটি বাক্যের মধ্যে) (২×৬=১২)
স্নাতক কাদের বলা হত?
বৈদিক যুগে শিক্ষার্থীরা 12 বছর ধরে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন করত। সেখানে তারা গুরুর কাছে শিক্ষা নিত। শিক্ষা শেষে এক বিশেষ স্নান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্নান করত। এই স্নান থেকেই ‘স্নাতক’ শব্দটি এসেছে। বর্তমানে গ্র্যাজুয়েটদের বলা হয় স্নাতক। তখন এক অনুশীলনের মাধ্যমে এই স্নাতক ডিগ্রি দেওয়া হত।
অথবা,
সপ্তসিন্ধু অঞ্চল বলতে কী বোঝায়?
প্রথম পর্বে বৈদিক সভ্যতা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বিস্তারলাভ করেছিল। সাতটি নদী অধ্যুষিত অঞ্চল সপ্তসিন্ধু নামে পরিচিত ছিল। এই সাতটি নদী হল – সিন্ধু, সরস্বতী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, ইরাবতী এবং বিপাশা।
আর্যসত্য কী?
গৌতম বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। এই কষ্টের হাত থেকে মুক্তির জন্য তিনি চারটি মহান সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। এগুলি হল –
- পৃথিবী দুঃখময়।
- মানুষের কামনা-বাসনা থেকেই সৃষ্টি হয় দুঃখ।
- তা দূর করতে পারলেই মোক্ষ বা নির্বাণ পাওয়া যায়।
- এই মুক্তি পেতে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ‘মার্গ’ বা পথ অনুসরণ করতে হবে।
অথবা,
দ্বাদশ অঙ্গ কী?
আনুমানিক 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাটলিপুত্রে প্রথম জৈন সংগীতি আহূত হয়। এখানে স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে মহাবীর প্রচারিত জৈনধর্ম মোট 12টি অঙ্গে সংকলিত হয়। একেই বলা হয় দ্বাদশ অঙ্গ।
যজ্ঞ না করেও মৌর্য সম্রাটরা নিজেদের দেবতাদের মতোই সম্মানীয় কীভাবে প্রতিপন্ন করতেন?
মৌর্য সম্রাট অশোক সর্বপ্রথম তাঁর লেখতে নিজের নামের আগে দেবানংপিয় বা প্রিয়দর্শী বা দেবতাদের প্রিয় কথাগুলি ব্যবহার করেছেন। এইভাবে যজ্ঞ না করেও মৌর্য সম্রাটরা নিজেদের দেবতাদের মতোই সম্মানীয় প্রতিপন্ন করতেন।
অথবা,
ক্ষত্রপ কাদের বলা হত?
কুষাণ যুগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষত্রপ বলা হত। আবার ভারতে রাজত্বকারী শক রাজারা নিজেদের ওই নামে অভিহিত করতেন।
ইন-তু কী?
খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে অর্থাৎ, সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চিনা পর্যটক সুয়ান জাং ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণে ভারতবর্ষকে ইন-তু বলা হয়েছে।
মুদ্রারাক্ষস নাটকের বিষয়বস্তু কী?
মুদ্রারাক্ষস নাটকটি রচনা করেন বিশাখদত্ত। এই নাটকের বিষয়বস্তু হল নন্দরাজকে কীভাবে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসন লাভ করেছেন তার ঘটনা।
অথবা,
প্রাচীন যুগে পরিবেশের ওপর চাপ কম পড়ত কেন?
প্রাচীন যুগে পরিবেশের ওপর চাপ কম পড়ার কারণ ছিল –
- প্রাচীনকালের রাজারা পরিবেশ রক্ষার কাজে বিশেষ নজর দিতেন। এব্যাপারে সম্রাট অশোকের নাম অগ্রগণ্য।
- প্রাচীনকালে জনসংখ্যা ছিল কম এবং জনগণ নির্বিচারে বৃক্ষছেদন করত না। ফলে সেসময় পরিবেশ ছিল সুরক্ষিত।
হিদুষ কী?
পারসিকরা সিন্ধুনদকে বলত হিদুষ। কারণ তাদের বর্ণ বা উচ্চারণে ‘স’ এর স্থান নেই। তারা ‘স’ -এর উচ্চারণ করে ‘হ’। তারা সিন্ধু অঞ্চলকে বলত হিদুষ।
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো (চার-পাঁচটি বাক্যের মধ্যে) (৩×৫=১৫)
বৈদিক সাহিত্য – টীকা লেখো।
বেদ শব্দটি এসেছে ‘বিদ’ বা জ্ঞান থেকে। বেদের অপর নাম শ্রুতি কারণ ঈশ্বরের বাণী (অপৌরুষেয়) ‘বেদ’ -এর কোনো লিখিত রূপ ছিল না; তা শুনে শুনে মুখস্থ করা হত। আদি বৈদিকযুগে লিখিত হয় ঋগবেদ। পরবর্তী বৈদিক যুগে রচিত হয়েছে সাম, যজু ও অথর্ব বেদ। প্রত্যেক বেদের চারটি অংশ, যথা – সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ বা বেদান্ত। উপনিষদ বেদের শেষ ভাগ তাই তা বেদান্ত নামে খ্যাত। বেদ -এর মূল তত্ত্ব সংক্ষেপিত হয়েছে সূত্রসাহিত্যে। সূত্রসাহিত্য বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন নিয়ে গঠিত। বেদাঙ্গের 6টি ভাগ, যথা – শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প। কল্পসূত্রের 3টি ভাগ যথা – শ্রেণি, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র। দর্শন-সাহিত্যেরও 6টি ভাগ আছে।
অথবা,
বৌদ্ধ সংগীতি – টীকা লেখো।
গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর উপদেশ ও বৌদ্ধ সংঘের নিয়মগুলি নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। এজন্য বৌদ্ধ পণ্ডিতরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিয়ে যে বৌদ্ধ ধর্মসম্মেলন করতেন তাকেই বলা হয় বৌদ্ধ সংগীতি। এরূপ মোট চারটি বৌদ্ধ সংগীতি আহূত হয়, যেমন –
- প্রথম – সম্রাট অজাতশত্রুর আমলে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এর পৌরোহিত্য করেন মহাকাশ্যপ। এখানে সুত্ত ও বিনয়পিটক সংকলন করা হয়।
- দ্বিতীয় – মগধরাজ কালাশোকের রাজত্বে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি আহূত হয়। এখানে মহাসাংঘিক ও খেরাবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।
- তৃতীয় – সম্রাট অশোকের রাজত্বে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বৌদ্ধ সংঘের নিয়মগুলি কঠোরভাবে মানার ওপরে জোর পড়ে। সংঘের মধ্যে ভাঙন আটকাবার চেষ্টা হয়।
- চতুর্থ – চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি আহূত হয় কাশ্মীরে, সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বে। এখানে বৌদ্ধ ধর্ম হীনযান ও মহাযান – এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।
এলাহাবাদ প্রশস্তি গুরুত্বপূর্ণ কেন?
এলাহাবাদ প্রশস্তি হল একটি শিলালেখ। এটি রচনা করেন গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ। লিপিটি লেখা হয়েছে ব্রাহ্মীলিপিতে। এর ভাষা হল সংস্কৃত।
এই প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের গুণকীর্তন ও রাজ্যবিস্তারের কাহিনি লেখা আছে। জানা যায়, তিনি আর্যাবর্তের (উত্তর ভারত) 9 জন রাজা ও দক্ষিণ ভারতের 12 জন রাজাকে পরাজিত করেন। এই লিপি থেকেই, সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তার নীতি সম্পর্কে জানা যায়। জানা যায়, দক্ষিণ ভারতে রাজ্যবিস্তার নীতির ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ মোক্ষ অনুগ্রহ নীতি গ্রহণ করেন। এই রাজ্যগুলিকে তিনি পরাজিত করে তাদের বশ্যতা আদায় করে নেন। তিনি এই রাজ্যগুলিকে সরাসরি গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি।
এ ছাড়া জানা যায় যে, তিনি সীমান্তবর্তী আরও 5 জন রাজার বশ্যতা আদায় করেন। এ ছাড়া ভারতবর্ষের অনেক উপজাতি রাজন্যবর্গেরও তিনি বশ্যতা আদায় করেন।
অথবা,
সাতবাহন প্রশাসন কেমনভাবে চলত?
সাতবাহন রাজারা ছিলেন (যেমন – গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী) রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক। একাধারে তাঁরা ছিলেন রাজা, অন্যদিকে তারা ছিলেন সেনাপতি। তাঁরাই ছিলেন রাজ্যের প্রধান বিচারক।
শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সাতবাহন রাজারা রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। এর প্রধান প্রশাসক ছিলেন অমাত্যগণ। উৎপন্ন ফসলের \( \frac14 \) অংশ বলি কর এবং \( \frac16 \) অংশ ভাগ নামক ভূমিরাজস্ব নেওয়া হত। এ ছাড়া তাঁরা বণিকদের কাছ থেকে বাণিজ্য কর এবং কারিগরদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেন।
কুষাণ আমলে অর্থনীতিতে নতুন কী কী দিক দেখা গিয়েছিল?
কুষাণ যুগে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ায় ভারতীয় বাণিজ্য প্রসারিত হয়। কুষাণ যুগে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন হলে বহির্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কুষাণ যুগেই বিখ্যাত ‘রেশমপথ’ গড়ে ওঠে। চিনের রেশম মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের মধ্যদিয়ে ইরান ও রোমে রফতানি করা হত। কুষাণ রাজারা ‘রেশম পথের’ বণিকদের কাছ থেকে প্রচুর শুল্ক আদায় করত। মিলিন্দপঞহো থেকে জানা যায় যে, মিনান্দারের রাজধানী সাকলে (বর্তমানে পাকিস্তানের শিয়ালকোট) ভারতীয় পণ্যের বাজার গড়ে উঠেছিল। তখন তাম্রলিপ্ত ছিল পূর্ব ভারতের বিখ্যাত বন্দর। খ্রিস্টীয় 45 অব্দে আলেকজান্দ্রিয়া, রোম ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন চলত।
অথবা,
গুপ্ত যুগের মুদ্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
গুপ্ত যুগে নানা প্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। তবে তা ছিল সবই সোনার মুদ্রা। সমুদ্রগুপ্তের ‘বীণাবাদনরত’ স্বর্ণমুদ্রার কথা জানা যায়। তাঁর ওপর একটি মুদ্রা থেকে তাঁর বীরত্ব ও দেহ সৌষ্ঠবের কথা জানা যায়। বীণাবাদনরত মুদ্রা থেকে সমুদ্রগুপ্তের সংগীত অনুরাগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্ত যুগের মুদ্রা থেকে গুপ্তাব্দ প্রচলনের কথা জানা যায়। আবার সমুদ্রগুপ্তের পর কিছু গুপ্ত সম্রাট তাঁদের মুদ্রায় লক্ষ্মী, কার্তিক প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি ব্যবহার করতেন।
পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের সোনার মুদ্রাগুলিতে খাদ মেশানো শুরু হয়। যা সেযুগের দুর্বল অর্থনীতির কথা প্রমাণ করে।
সংগম সাহিত্য কী?
তামিল ভাষায় সংগম কথার অর্থ একত্রিত হওয়া। জানা যায় প্রাচীন যুগে মাদুরাই নগরীতে তিনটি সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল সেজন্য তামিল সাহিত্যকে সংগম সাহিত্য বলা হয়।
অথবা,
প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চায় আর্যভট্টের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
গুপ্ত যুগে গণিত শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত ছিলেন এযুগের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। মনে করা হয় যে, আর্যভট্ট ত্রিকোণমিতির সাইন ও কোসাইন -এর উদ্ভাবক ছিলেন। আর্যভট্ট তাঁর সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রকাশ করেন। 365 দিনে যে এক বছর এই হিসাব আর্যভট্টই করেছিলেন। দশমিক পদ্ধতির প্রয়োগ তিনিই করেছিলেন।
তাম্রলিপ্ত – টীকা লেখো।
তাম্রলিপ্ত ছিল প্রাচীন বাংলার একটি জনপদ তথা নদীবন্দর। এটির বর্তমান নাম তমলুক। যা বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন লিখিত ঐতিহাসিক উপাদানে এর নাম উল্লেখ আছে। মৌর্য যুগে এই বন্দরের শ্রীবৃদ্ধির কথা জানা যায়। জানা যায়, এই বন্দর দিয়ে প্রাচীন ভারতের বহির্বাণিজ্য চলত। এখান দিয়ে তামা ব্রহ্মদেশে রফতানি করা হত।
গুপ্ত যুগে তাম্রলিপ্ত বন্দর ছিল একটি উন্নত বাণিজ্য কেন্দ্র। কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে এই বন্দরের নাম উল্লেখ আছে। পাল ও সেন যুগেও এটি ছিল একটি উন্নত বাণিজ্যক্ষেত্র।
অথবা,
রেশমপথ – টীকা লেখো।
নানা কারণে ভারতে হুন আকমণের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী।
ভারতে হুন আক্রমণের ফল –
- গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন – বারংবার হুন আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন হয়।
- সম্পদধ্বংস – নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু হুনদের আক্রমণে ভারতের বহু মন্দির, মঠ তথা স্থাপত্য-ভাস্কর্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
- আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব – হুন আক্রমণের সূত্র ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কিছু আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব হয়।
- মিশ্রজাতির উদ্ভব – পরবর্তী সময়ে এই হুনরা ভারতীয় জনজীবনে মিশে যাওয়ার ফলে এক মিশ্রজাতির উদ্ভব হয়। যারা রাজপুত জাতি নামে খ্যাত।
- রাজপুত শাখার উদ্ভব – ফলস্বরূপ উত্তর ভারতের নানা স্থানে প্রতিহার, পারমার, চৌহান, গাহড়বাল, চান্দেল, শোলাঙ্কি প্রভৃতি রাজপুত শাখার উদ্ভব হয়।
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো (আট-দশটি বাক্যের মধ্যে) (৫×৩=১৫)
মৌর্য সম্রাট ও গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদার তুলনা করো।
মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদার তুলনা –
| মৌর্য সম্রাট | গুপ্ত সম্রাট |
| মৌর্য সম্রাটরা ভালোভাবে শাসনকাজ চালানোর চেষ্টা করতেন। | গুপ্ত সম্রাটরাও ভালোভাবে শাসনকাজ চালানোর চেষ্টা করতেন। |
| বিচারব্যবস্থার ঊর্ধ্বে ছিলেন স্বয়ং মৌর্য সম্রাট। | বিচারব্যবস্থার উর্ধ্বে ছিলেন স্বয়ং গুপ্ত সম্রাট। |
| দেবতাদের প্রিয় উপাধি ব্যবহার করে মৌর্য সম্রাটরা তাঁদের ক্ষমতা জাহির করতেন। | বিরাট ক্ষমতা বোঝানোর জন্য গুপ্ত সম্রাটরাও নানা উপাধি ব্যবহার করতেন। |
| মৌর্য সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন মৌর্য সম্রাট। | গুপ্ত সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন গুপ্ত সম্রাট। |
অথবা,
কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলাফল ছিল অশোকের ধম্ম – যুক্তিসহ মন্তব্যটি আলোচনা করো।
কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলাফলের সঙ্গে সম্রাট অশোকের ধম্মের সম্পর্ক ছিল গভীর। কারণ এই যুদ্ধে অশোক জয়ী হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু যুদ্ধে মানুষের মৃত্যু, রক্তের স্রোত ও স্বজনহারা মানুষের কান্না দেখে তাঁর নিদারুণ কষ্ট হয়। এই যুদ্ধের জন্য তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হন। তাই তিনি যুদ্ধনীতি ত্যাগ করে ধর্মবিজয় নীতি অর্থাৎ, মানুষের মন ভালোবাসার দ্বারা জয় করার নীতি গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, এবার থেকে শান্তি ও অহিংসার পথে চলবেন।

ধম্মের প্রভাব –
সম্রাট অশোকের শাসনব্যবস্থায় তাঁর ধম্মের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। যেমন –
- নতুন কর্মচারী নিয়োগ – কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক যুদ্ধনীতি ত্যাগ করে ধর্মবিজয় নীতি গ্রহণ করে। এ ছাড়া প্রজারা যাতে শান্তিতে ধর্ম পালন করতে পারে তার জন্য তিনি ধর্মমহামাত্র নামে এক প্রকার নতুন রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন।
- মৃত্যুদণ্ড রদ – তিনি বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড রদ করেন।
- বিভিন্ন কর্মসূচি – প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি নানান কর্মসূচির উদ্যোগ নেন। রাস্তাঘাট, চিকিৎসালয়, সরাইখানা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এককথায় প্রজাকল্যাণই ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থার মূলভিত্তি।
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়ে কোন্ কোন্ পেশার মানুষদের কথা তুমি জানতে পেরেছ, তার তালিকা তৈরি করো। তার মধ্যে কোন্ কোন্ পেশা আজও দেখা যায়?
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় যষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে মানুষের যে যে পেশার কথা জানা যায়, তা নীচে লেখা হল –
| পেশার নাম | কাজ |
| যোদ্ধা | যুদ্ধ করা |
| গুপ্তচর | গুপ্তচর বৃত্তি |
| পণ্ডিত | শিক্ষাদান করা |
| চিকিৎসক | চিকিৎসা |
| ধোপা | কাপড় কাচা |
| নাপিত | চুল-দাড়ি কাটা |
| কৃষক | কৃষি |
| পশুপালক | পশুপালন |
| কারিগর | কারিগরি |
| ব্যবসায়ী | ব্যাবসা |
| দোকানদার | দোকানদারি |
| রাজকর্মচারী | রাজার কাজে সাহায্য করা |
উপরের লিখিত সব পেশাই বর্তমানকালে দেখা যায়।
অথবা,
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়কালের মধ্যের প্রাচীন ভারতে বাণিজ্যের বিবর্তনের দিকগুলি চিহ্নিত করো।
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যে নানা বিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন –
- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৈশ্যরা বাণিজ্য করত। শ্রেষ্ঠিন ছিল ধনী বণিক সম্প্রদায়।
- এসময় অর্থ ঋণ করার বিষয়টি চালু হয়। এর সত্যতা প্রমাণ করে কুশীদ (যিনি ঋণ দেন) শব্দ থেকে।
- এযুগে মুদ্রার প্রচলন ঘটে (কৃঞ্চল ও শতমান)। এগুলি ছিল স্বর্ণমুদ্রা। পরে কার্যাপণ নামে একপ্রকার মুদ্রার প্রচলন ঘটে।
- বাণিজ্যের স্বার্থে ও বণিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে এযুগে গিল্ড বা বণিকদের সংঘ গড়ে ওঠে। ক্রমে ভাণ্ডাগারিক নামে কারিগরদের একটি সম্মিলিত শ্রেণি গড়ে ওঠে। আবার পালি সাহিত্যে ভ্রাম্যমাণ বণিকদের কথাও জানা যায়।
- মৌর্য যুগে বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। কুষাণ যুগে বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গড়ে ওঠে ‘রেশমপথ’।
মৌর্য ও গুপ্ত আমলের শিল্পচর্চার মধ্যদিয়ে ধর্মীয় ধারণার তফাতের ছাপ ফুটে উঠেছে – উদাহরণসহ মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।
মৌর্য ও গুপ্ত যুগের শিল্পগুলি থেকে দুই যুগের ধর্মীয় ধ্যানধারণার তফাত লক্ষ করা যায়।
- মৌর্য যুগে প্রচুর স্তূপ ও চৈত্য নির্মিত হয়। সম্রাট অশোক স্বয়ং বহু সংখ্যক স্তূপ নির্মাণ করেন। স্তূপ ও চৈত্যগুলি বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং এগুলি থেকে মনে করা যায় যে, মৌর্য সম্রাটগণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী।
- অন্যদিকে গুপ্ত যুগে অসংখ্য মন্দির স্থাপত্য গড়ে ওঠে। গুপ্ত যুগে মন্দির শিল্পে অনেক রীতির চল ছিল। যেমন – নাগর, বেসর ও দ্রাবিড়। এর থেকে মনে করা যায় যে, গুপ্ত যুগে বৌদ্ধ ধর্মের বদলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আবার, এযুগে অনেক বিষ্ণু ও শিবের মন্দির তৈরি হয়। অন্যদিকে গুপ্ত যুগের শিল্পচর্চায় বৌদ্ধ ধর্মের ছাপ ছিল স্পষ্ট। কারণ মন্দিরের গায়ে ভগবান বুদ্ধের চিত্র আঁকা হয়েছিল।
অথবা,
প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসের উপাদান হিসেবে চরক সংহিতা ও শুশ্রুত সংহিতার গুরুত্ব আলোচনা করো।
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে রয়েছে অসংখ্য সাহিত্যিক উপাদান। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কারণ প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য দলিল হল চরক সংহিতা ও শুশ্রুত সংহিতা।
- চরক সংহিতা – চরক সংহিতা রচনা করেন আয়ুর্বেদজ্ঞ চরক। তিনি কুষাণ যুগের মানুষ ছিলেন। এই গ্রন্থে 700টি ঔষধি গাছ-গাছড়ার নাম লেখা হয়েছে। কোন্ রোগের কী ওষুধ তার কথাও লেখা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাধি ও লক্ষণ কী সে সম্পর্কেও এই গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া এই গ্রন্থে একটি আদর্শ চিকিৎসাকেন্দ্র বা হাসপাতাল কী হওয়া উচিত তাও এতে বলা হয়েছে।
- শুশ্রুত সংহিতা – শূশ্রুত সংহিতা হল একটি শল্য চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। এটি রচনা করেন প্রাচীন যুগের বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক শুশ্রুত। এই গ্রন্থে কারিগরদের হাতের কাজের প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে হাতই হল মানুষের প্রধান যন্ত্র।
এই আর্টিকেলে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাসের নমুনা প্রশ্ন ও উত্তরপত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সহায়ক হবে, কারণ এগুলো প্রায়ই পরীক্ষায় আসে। আশা করি, এই নিবন্ধটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে, তবে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত। ধন্যবাদ!


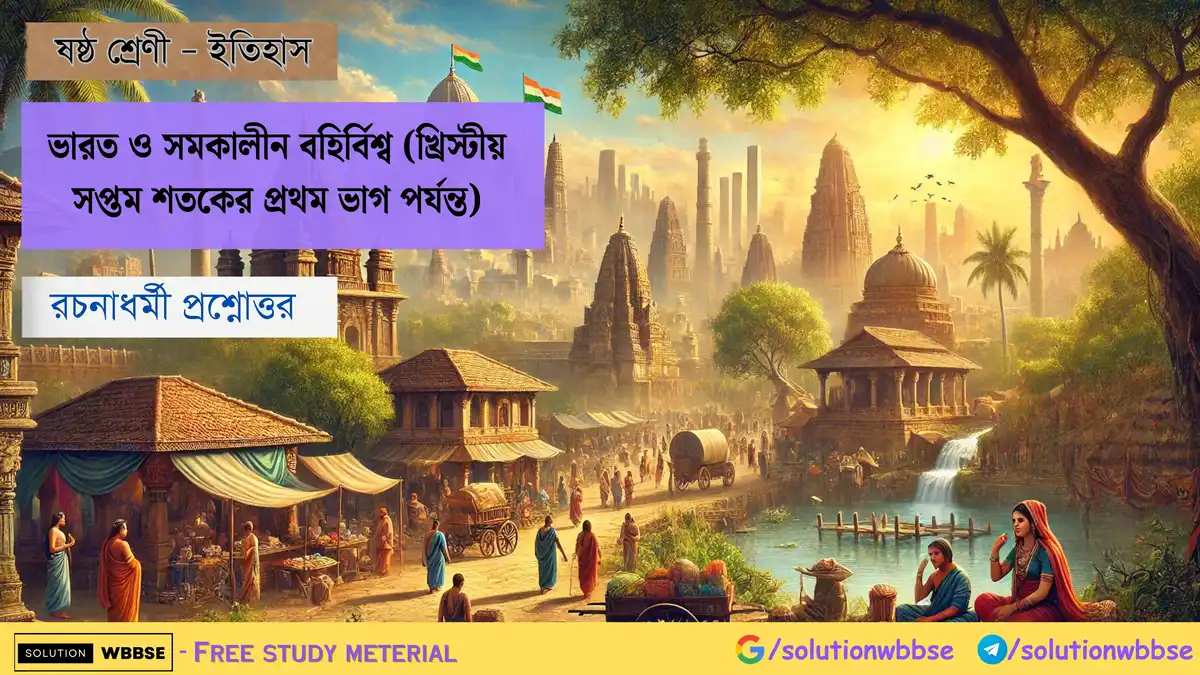
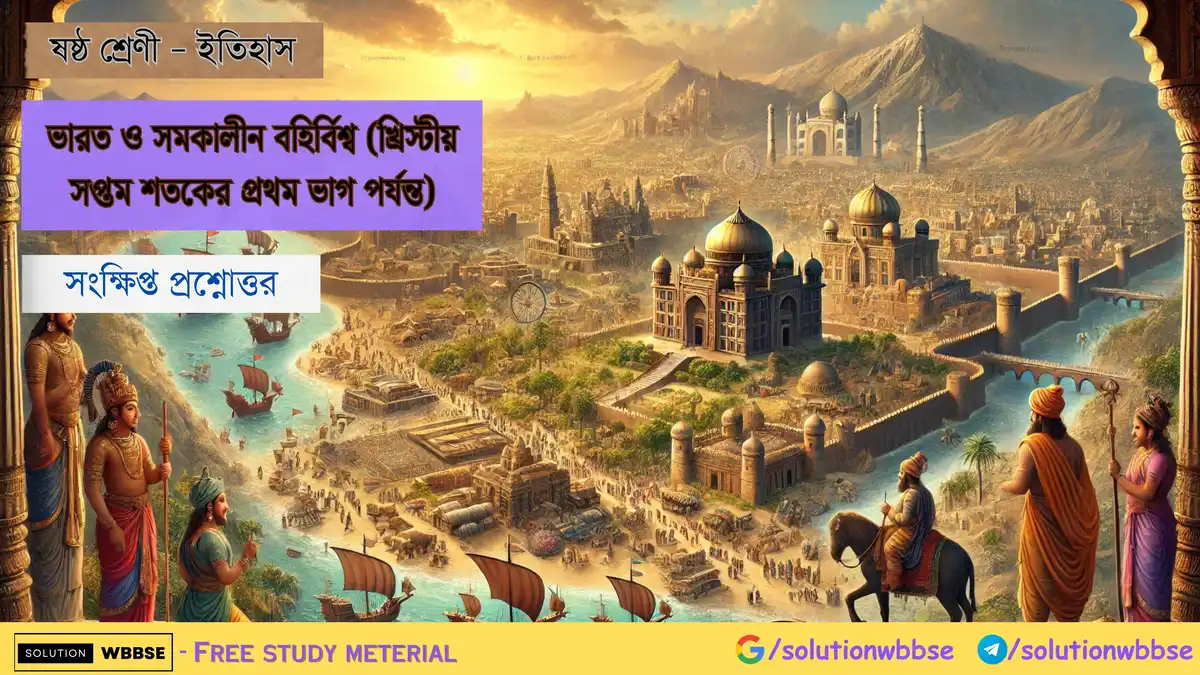
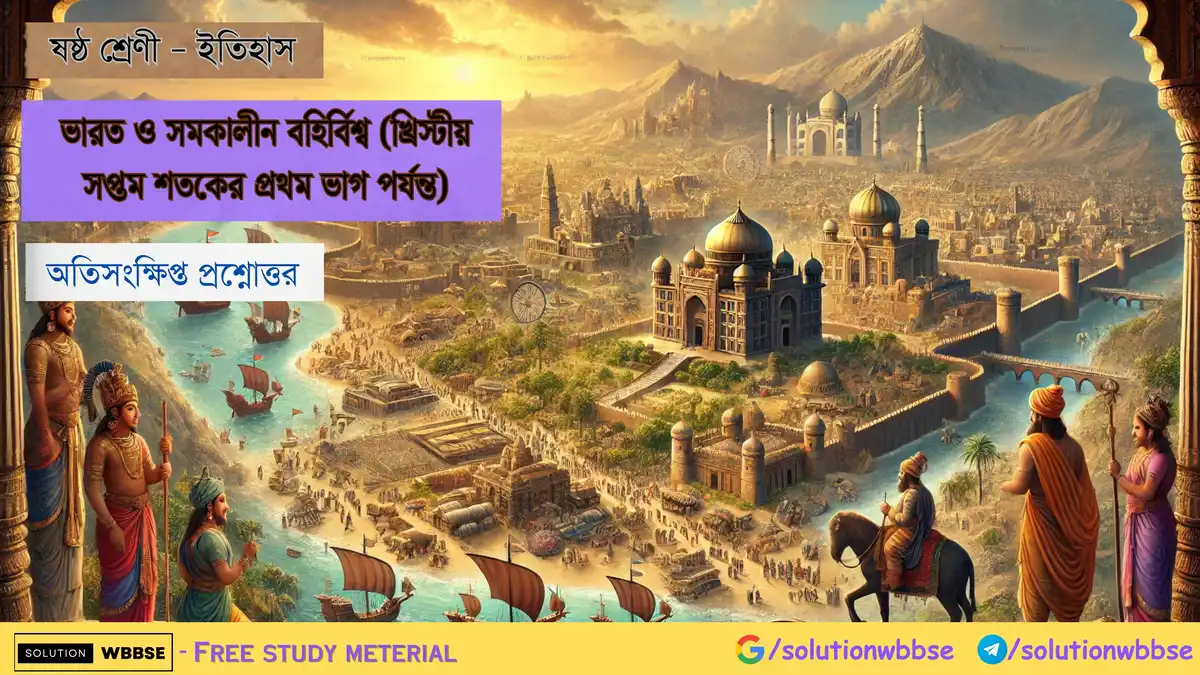

মন্তব্য করুন