এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের চতুর্থ পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘আকাশে সাতটি তারা’ -এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে কবির পরিচিতি, কবিতার উৎস, কবিতার পাঠপ্রসঙ্গ, কবিতার সারসংক্ষেপ, কবিতার নামকরণ এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এই আর্টিকেলটি আপনাদের ‘আকাশে সাতটি তারা’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবে এবং কবিতাটি ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া, নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে কবি ও কবিতার সারসংক্ষেপ সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে, তাই এই তথ্যগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
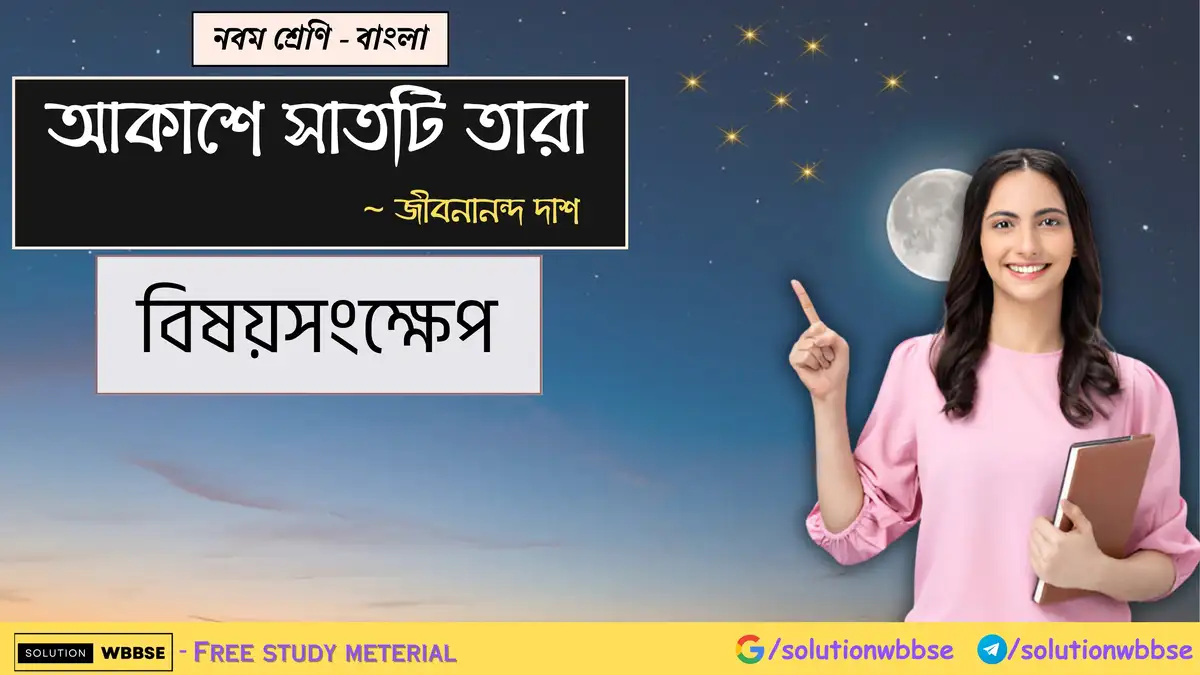
‘আকাশে সাতটি তারা’ কবিতার কবি পরিচিতি
“সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি – কেন-না তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য বিকিরণ তাদের সাহায্য করেছে।”
‘কবিতার কথা’ – জীবনানন্দ দাশ।
জন্ম এবং শৈশব
1899 খ্রিস্টাব্দের 18 ফেব্রুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন জীবনানন্দ দাশ। বরিশালেই তাঁর বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। পিতামহ সর্বানন্দ ঢাকা বিক্রমপুরের আদিনিবাস ছেড়ে এসে বরিশালে বসতি স্থাপন করেন। পরে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। পূর্বে এই বৈদ্য পরিবারের পদবি ছিল দাশগুপ্ত; জাতিভেদহীন ব্রাহ্মসমাজে এসে সর্বানন্দ হলেন গুপ্তহীন, কেবল দাশ। সর্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্র সত্যানন্দের প্রথম পুত্র কবি জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মিক শিষ্য। অন্যদিকে জীবনানন্দের মাতা কুসুমকুমারী দেবীও ছিলেন সেযুগের অন্যতম মহিলা কবি।
জীবনানন্দ দাশের ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন –
আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বরিশাল স্কুলে আর কলেজে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়ে কলকাতায় আসেন প্রেসিডেন্সি কলেজে সাম্মানিক ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হয়ে। ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাস করে কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। অবশ্য কিছুদিন পরে তাঁর সেই চাকরি চলে যায়। তারপর দিল্লিতে এক কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করে ফিরে যান বরিশালে। সেখানকার ব্রজমোহন কলেজে দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছিলেন। দেশভাগের পরে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। এবার যোগ দেন হাওড়া গার্লস কলেজে।
জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যজীবন
জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতায় কেবল স্মরণযোগ্যই নন, রবীন্দ্র পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিও বটে। রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই বাংলা কাব্যে কবিভাষার নতুন রূপ ও বর্ণ সৃষ্টি করে আমাদের অনুভূতির জগৎকে নতুন নতুন আস্বাদনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাঁর কবিমন গঠনে – “আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে” – মাতৃরচিত কবিতা তথা কাব্যবোধ বিস্তর ভূমিকা নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কবির অনুজা শ্রীমতী সুচরিতা দাশ জানিয়েছেন – “বাবা যদি দিয়ে থাকেন তাঁকে সৌরতেজ-প্রাণবহ্নি, মা তাঁর জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছেন স্নেহমমতার বনচ্ছায়া, মৃত্তিকাময়ী সান্ত্বনা।’
এমন বাস্তুভূমির স্নিগ্ধ ছায়ার সঙ্গে তাঁর মনে-মননে নিবিড়-নির্জন প্রকৃতির অনুভব প্রগাঢ়ভাবে মিলেমিশে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। উপরন্তু ইংরেজি সাহিত্যপাঠের একনিষ্ঠতায় ইয়েটসের কাব্যরীতি, এলিয়টীয় কালচেতনা জীবনানন্দের ‘বোধ’ -এর জগতে যে অনুরণন তুলেছিল-তা তাঁর কবিতায় বিলম্বিত ছায়া ফেলে গেছে।
জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভার
তাঁর কাব্যসাধনাকে মোটামুটিভাবে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় – এক, বরিশালের প্রকৃতি প্রভাবিত প্রথম যুগ; দুই, কলকাতার নাগরিকতা প্রভাবিত দ্বিতীয় যুগ। প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলি হল – ‘ঝরাপালক’ (প্রকাশকাল – 1927 খ্রিস্টাব্দ), ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (1936 খ্রিস্টাব্দ), ‘রূপসী বাংলা’ (রচনাকাল – 1936-1937 খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশকাল – 1959 খ্রিস্টাব্দ), ‘বনলতা সেন’ (রচনাকাল – 1925-1939 খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশকাল – 1942 খ্রিস্টাব্দ) ‘মহাপৃথিবী’ (রচনাকাল – 1929-1941 খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশকাল – 1944 খ্রিস্টাব্দ)। দ্বিতীয় যুগের কাব্যগ্রন্থ-‘সাতটি তারার তিমির’ (রচনাকাল – 1928-1943 খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশকাল – 1948 খ্রিস্টাব্দ) এবং ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ (রচনাকাল – 1927-1943 খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশকাল – 1961 খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর প্রথম যুগের কবিভাষা ছিল হৃদয়াবেগ প্রধান, দ্বিতীয় যুগের কবিভাষা মননাবেগ প্রধান।
লেখক জীবনানন্দ
কবি জীবনানন্দের উপন্যাস, ছোটোগল্পের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। প্রথম উপন্যাস – ‘পূর্ণিমা’ (রচনাকাল – 1931-1932 খ্রিস্টাব্দ), ‘কল্যাণী’ (রচনাকাল – 1932 খ্রিস্টাব্দ), ‘বিভা’ (রচনাকাল – 1933 খ্রিস্টাব্দ), ‘প্রেতিনীর রূপকথা’ (রচনাকাল – 1933 খ্রিস্টাব্দ), ‘জীবন প্রণালী’ (রচনাকাল – 1933 খ্রিস্টাব্দ), ‘কারুবাসনা’ (রচনাকাল – 1933 খ্রিস্টাব্দ), ‘বাসমতীর উপাখ্যান’ (রচনাকাল – 1948 খ্রিস্টাব্দ), ‘জলপাইহাটি’ (রচনাকাল – 1948 খ্রিস্টাব্দ), ‘মাল্যবান’ (রচনাকাল – 1948 খ্রিস্টাব্দ, অসম্পূর্ণ)। যদিও ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না, তা বলাবাহুল্য। তবে তিনি উপন্যাসে যে ভাষারীতি প্রয়োগ করেছেন তা অনেকাংশেই ভিন্ন এক শৈলীর জন্ম দিয়েছে। জীবনানন্দের ভাষার ‘অধরা মাধুরী’, কথনরীতি আজকের কবি সাহিত্যিকদের ভাষাচেতনার অগ্রজাতক এ কথা ভেবে বিস্ময় জাগে।
কবি জীবনানন্দ
‘বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি’, ‘প্রকৃতির কবি’, ‘প্রেমের কবি’, ‘মৃত্যুচেতনার কবি’, ‘কালচেতনার কবি’, ‘ধূসরতার কবি’ – এ-সকল বাক্যাংশ একই কবি অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বিশ শতকীয় ব্যর্থতা-বেদনা, আকাঙ্ক্ষার অপমৃত্যু, পলাতক জীবনের নিঃশেষে উধাও হয়ে যাওয়া এইসব জীবনানন্দের কবিচিত্তকে করেছে পীড়িত, অন্ধকারাচ্ছন্ন, বেদনাহত। তবু ‘আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে’ – এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসে তিমির হননের গান গাওয়াই জীবনানন্দের চরম অঙ্গীকার। নিরবচ্ছিন্ন কালপ্রবাহে অনাদি অন্ধকার থেকে তমোঘ্ন আলোকে উত্তরণের চিরন্তন সত্যই তাঁর কাব্যের আলোকবর্তিকা।
কাব্য নির্মিতিতেও তিনি অনন্যসাধারণ। তাঁর বাক্সীতির অভিনবত্ব একদা আক্রমণস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল; কারণ তাঁর প্রতীক, রূপকল্প, চিত্রকল্প ব্যবহারের সংগতিযোগ সকল পাঠকের কাছে দৃষ্টিগোচর হয়নি। কিন্তু তাঁর মনমেজাজ, প্রতীকীবাদ, কথনপদ্ধতির সঙ্গে গভীর পরিচয়েই তাঁর কবিতার রূপ-রস-গন্ধের আস্বাদ পাওয়া সম্ভব।
উপসংহার
কলকাতায় একটি ট্রাম দুর্ঘটনায় 1954 খ্রিস্টাব্দের 22 অক্টোবর তাঁর মৃত্যু ঘটে।
“…সকল মাটির গন্ধ আর সব নক্ষত্রের আলো যে পেয়েছে, – সকল মানুষ আর দেবতার কথা যে জেনেছে-আর এক ক্ষুধা তবু-এক বিহ্বলতা তাহারও জানিতে হয়! এই মত অন্ধকারে এসে!-জেগে-জেগে যা জেনেছ,-জেনেছ তা-জেগে জেনেছ তা,-নতুন জানিবে কিছু হয়তো বা ঘুমের চোখে সে!”
‘আকাশে সাতটি তারা’ কবিতার উৎস
‘আকাশে সাতটি তারা’ কবিতাটি কবি জীবনানন্দ দাশের ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যটি প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর তিন বছর পরে। কবির জীবনাবসান ঘটে 1954 খ্রিস্টাব্দে এবং কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল 1957 খ্রিস্টাব্দে।
‘আকাশে সাতটি তারা’ কবিতার পাঠপ্রসঙ্গ
‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি প্রথম থেকেই গাঢ় প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় নিয়ে পাঠকমহলে সমাদৃত। অথচ এই কাব্যের অণুপরমাণুর মধ্যে এক ধরনের বিরল ব্যতিক্রমী দেশপ্রেমও সঞ্চিত ছিল। এ কাব্যের কবিতাগুলির রচনাকাল 1934 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হলেও, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 1957 খ্রিস্টাব্দে জীবনানন্দের মৃত্যুর তিন বছর পরে। সমগ্র কাব্যটিতে কবির প্রকৃতি চেতনার পরিচয় স্পষ্ট। পরাধীন ভারতবর্ষে দেশীয় সংস্কৃতিকে ভুলে যাওয়াটাই যখন সমগ্র জাতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন জীবনানন্দ দাশের ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থে বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমত্ব আর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ অনুষঙ্গে কবি খুঁজে পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রাণের হদিস। রূপসী বাংলাদেশের রূপে মুগ্ধ কবির আর পৃথিবী খুঁজে সৌন্দর্য অন্বেষণের দরকার হয়নি। কবির সৌন্দর্য পিয়াসী মন বাংলাদেশের সন্ধ্যাকালীন সৌন্দর্যের অপরূপ বর্ণনা করেছে ‘আকাশে সাতটি তারা’ কবিতায়। সময়ের আবহমান হৃদয় থেকে বাংলাদেশের একটি বিশেষ সন্ধ্যাকে কবিতার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করে, তাকেই আবার আবহমান কালের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। বঙ্গপ্রকৃতির এই সান্ধ্য অধিবেশনে লেশমাত্র বৈভব আড়ম্বরের আয়োজন নেই, শুধুই সমাহিত শান্তির আশ্বাস তার রূপকে অতুলনীয় ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছে।
‘আকাশে সাতটি তারা’ কবিতার বিষয়সংক্ষেপ
সন্ধ্যার সূচনায় আকাশে সাতটি তারা ফুটে উঠলে কবি ঘাসের ওপর বসে থাকেন। গঙ্গাসাগরের ঢেউ -এর অস্তমিত সূর্যের আলোয় ভাসমান মেঘ যখন কামরাঙা লাল বর্ণ পায়, কবি তার সঙ্গে মিল খুঁজে পান মৃত মনিয়া পাখির। কবি প্রত্যক্ষ করেন শান্ত অনুগতভাবে বাংলাদেশে নেমে আসছে নীল সন্ধ্যা আর তার মায়াবী আলোয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বাংলার নিসর্গপ্রকৃতি। কবির মনে হয় এই মায়াময় সন্ধ্যা যেন কেশবতী কন্যা; যার চুল কবির চোখের উপর, মুখের উপর খেলা করছে। আসলে বঙ্গপ্রকৃতির সান্ধ্যসৌন্দর্যে কবি আবিষ্ট হয়ে যান। কবি বিশ্বাস করেন পৃথিবীর আর কোনো স্থান এ সৌন্দর্যের স্পর্শ পায় না। কবি আর কোথাও দেখেননি কেশবতী কন্যার অজস্র চুল অবিরত চুম্বন করে যাচ্ছে হিজল, কাঁঠাল কিংবা জামগাছকে। কবি জানেন না পৃথিবীর আর কোনো পথে রূপসী কেশবতী কন্যার চুলের বিন্যাসে এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে পড়ে কি না! সে গন্ধ কবি পান বাংলাদেশের নরম ধানে, কলমির মধ্যে। সে মৃদু ঘ্রাণ কবি অনুভব করেন হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা-সরপুঁটিদের সংস্পর্শে; সে ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা কবি উপলব্ধি করেন কিশোরের পায়ে দলা মুথাঘাসে কিংবা লাল লাল বটের ফলে। বঙ্গপ্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য এবং বিচিত্র গন্ধের মাঝে কবি অনুভব করেন বাংলাদেশের প্রাণের স্পন্দন।
‘আকাশে সাতটি তারা’ কবিতার নামকরণ
নামকরণের ইতিহাস
সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহিত্যের বিষয়কে আগাম ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলে তার নামকরণ। কবিতায় যেহেতু ব্যক্তি অনুভূতি প্রকাশ পায়, তাই নামকরণে অধিকাংশ সময়েই ব্যঞ্জনার আশ্রয় নেন কবি। কিন্তু মনে রাখতে হবে আলোচ্য কবিতাটির ‘আকাশে সাতটি তারা’ নামকরণ কবি জীবনানন্দ দাশ করেননি। কেবল এই কবিতা নয়, ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যের কোনো কবিতারই নামকরণ করেননি কবি; এমনকি মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই কাব্যের নামও কবির দেওয়া নয়। সুতরাং সংকলকের দেওয়া ‘আকাশে সাতটি তারা’ নামটি কবিতাটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে কিনা তা আলোচনার প্রয়োজন।
‘আকাশে সাতটি তারা’ কবিতার নামকরণের সার্থকতা
আলোচ্য কবিতাতে অপরূপ সৌন্দর্য এবং বিচিত্র গন্ধের মাঝে কবি বাংলাদেশের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছেন সান্ধ্যকালীন পরিবেশে। সন্ধ্যার সূচনালগ্নে আকাশে যখন দু-একটি তারা ফুটে ওঠে, তখন বাংলার নীল সন্ধ্যার মায়াবী আবেশে আপ্লুত হয়ে যান কবি। বঙ্গপ্রকৃতির তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুষঙ্গে কবি খুঁজে পান বাংলার প্রাণের সন্ধান। সময়ের আবহমান হৃদয় থেকে বাংলাদেশের একটি বিশেষ সন্ধ্যাকে কবিতার বিষয়রূপে নির্বাচন করে, তাকেই আবার আবহমান কালের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন কবি। বঙ্গপ্রকৃতির যে সান্ধ্য অধিবেশন পরিবেশিত হয়েছে আলোচ্য কবিতায়, সেখানে লেশমাত্র বৈভব-আড়ম্বরের আয়োজন নেই। শুধুই সমাহিত শান্তির আশ্বাস তার রূপকে অতুলনীয় ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছে। শিরোনামে ‘আকাশে সাতটি তারা’ শব্দবন্ধে আগত সন্ধ্যার ইঙ্গিত রচিত হয়েছে। ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যের কবিতাগুলির নামকরণে সম্পাদক বরাবরই বেছে নিয়েছেন কবিতার প্রথম চরণ কিংবা প্রথম চরণের একগুচ্ছ শব্দকে। আলোচ্য কবিতার নামকরণে ব্যবহৃত ‘আকাশে সাতটি তারা’শব্দবন্ধ সে নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়েও কবিতাটির বিষয়ের সঙ্গে মানানসই হয়েছে। এক কথায় বলা যায় কবিতাটির নামকরণ সার্থক।
এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের চতুর্থ পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘আকাশে সাতটি তারা’ -এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে কবির পরিচিতি, কবিতার উৎস, কবিতার পাঠপ্রসঙ্গ, কবিতার সারসংক্ষেপ, কবিতার নামকরণ এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আর্টিকেলটি আপনাদের ‘আকাশে সাতটি তারা’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছে এবং কবিতাটি ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া, নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে কবি পরিচিতি, কবিতার নামকরণ ও কবিতার সারসংক্ষেপ সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে, তাই এই তথ্যগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।






মন্তব্য করুন