আজকের আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়, “বিপ্লবী আদর্শ, নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ” -এর “বিষয়সংক্ষেপ” নিয়ে আলোচনা করব। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পড়ার সময় অধ্যায়টির কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বুঝতে সাহায্য করবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত বিবেচনা আপনাদের প্রস্তুতি আরও ভালো করতে সাহায্য করবে।
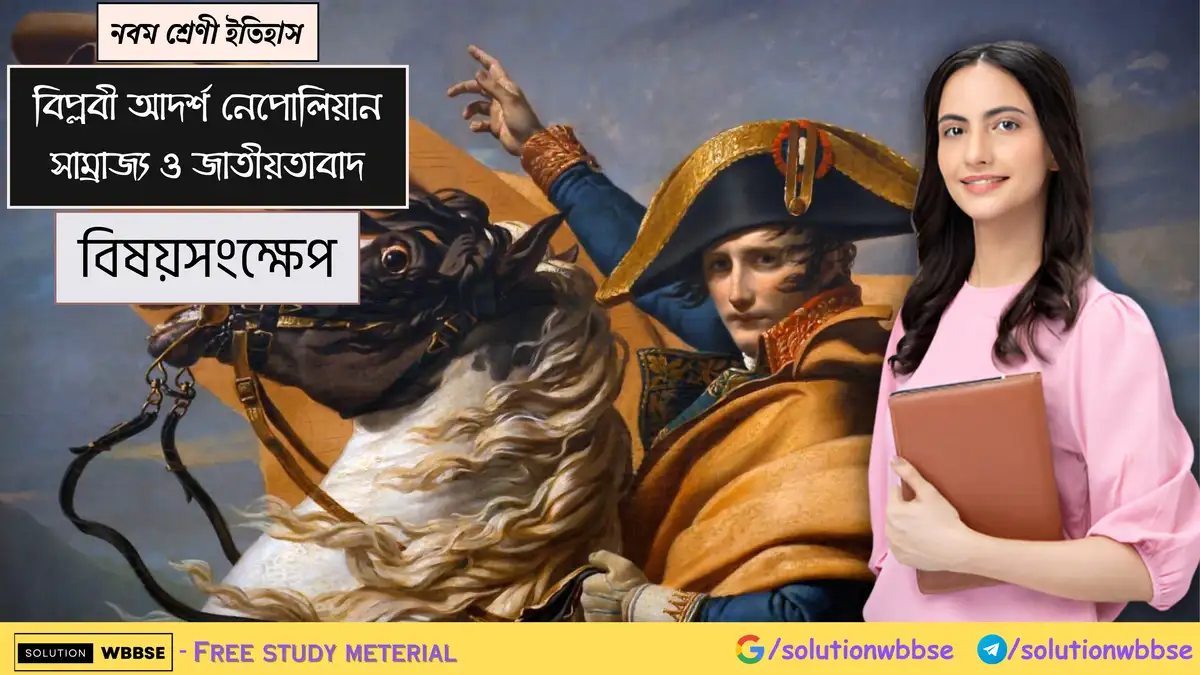
ডিরেক্টরি শাসন (Rule of Directory) –
সন্ত্রাসের শাসনের অবসানের পর ফ্রান্সে ডিরেক্টরি শাসনের সূচনা হয়। 1795 খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্বে রচিত সংবিধান অনুসারে ফ্রান্সের শাসনক্ষমতা পাঁচ সদস্যের একটি পরিষদ বা ডিরেক্টরির হাতে প্রদান করা হয়। ডিরেক্টরি শাসনের ভিত্তি ছিল উদীয়মান বিত্তবান বুর্জোয়া সম্প্রদায়। এরা মূলত ছিলেন অপদার্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই ডিরেক্টরির আমলে ফ্রান্সের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক ডেভিড থমসন (David Thomson) মনে করেন, ডিরেক্টরির শাসনই ফ্রান্সে বিপ্লবের ধ্বংসকে সম্পূর্ণ করেছিল (“…they presided over the final liquidation of the Revolution.”)
পাঁচজন ডিরেক্টর (Directors) –
- বারাস (Barras),
- লা র্যাভেলিয়ে (La Revelliere),
- লা তুর্নায়ের (Le Tourneur),
- রিউবেল (Rewbell) এবং
- কারনো (Carnot)।
‘বাসকুল’ নীতি রাজতন্ত্রী এবং জেকোবিন (Jacobin) – এই দুটি দল প্রথম থেকেই ডিরেক্টরির শাসনের বিরোধিতা করেছিল। তাই ডিরেক্টররা এই দুটি দলের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতিকেই ‘বাসকুল’ নীতি বলে।
বেবিউফ (Babeuf) -এর বিদ্রোহ –
দুর্নীতিগ্রস্ত ডিরেক্টরি শাসনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে যে একাধিক বিদ্রোহের উদ্ভব হয়, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 1796 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সংঘটিত ফ্রাঁসোয়া বেবিউফ (Babeuf) -এর বিদ্রোহ। ফ্রাঁসোয়া বেবিউফ ছিলেন ‘সোসাইটি অফ দ্য প্যান্থিয়ন’ (Society of the Pantheon) নামক বিপ্লবী সংস্থার সদস্য। তিনি নিজে ‘প্যাথিয়ন ক্লাব’ (Pantheon Club) নামে একটি দলের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ‘ট্রিবিউন’ (Tribune) পত্রিকায় সম্পাদনার কাজ করতেন। ডিরেক্টরির বিরুদ্ধে চক্রান্তের জন্য তাঁকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে কার্ল মার্কসের অগ্রদূত বলে মনে করেছেন।
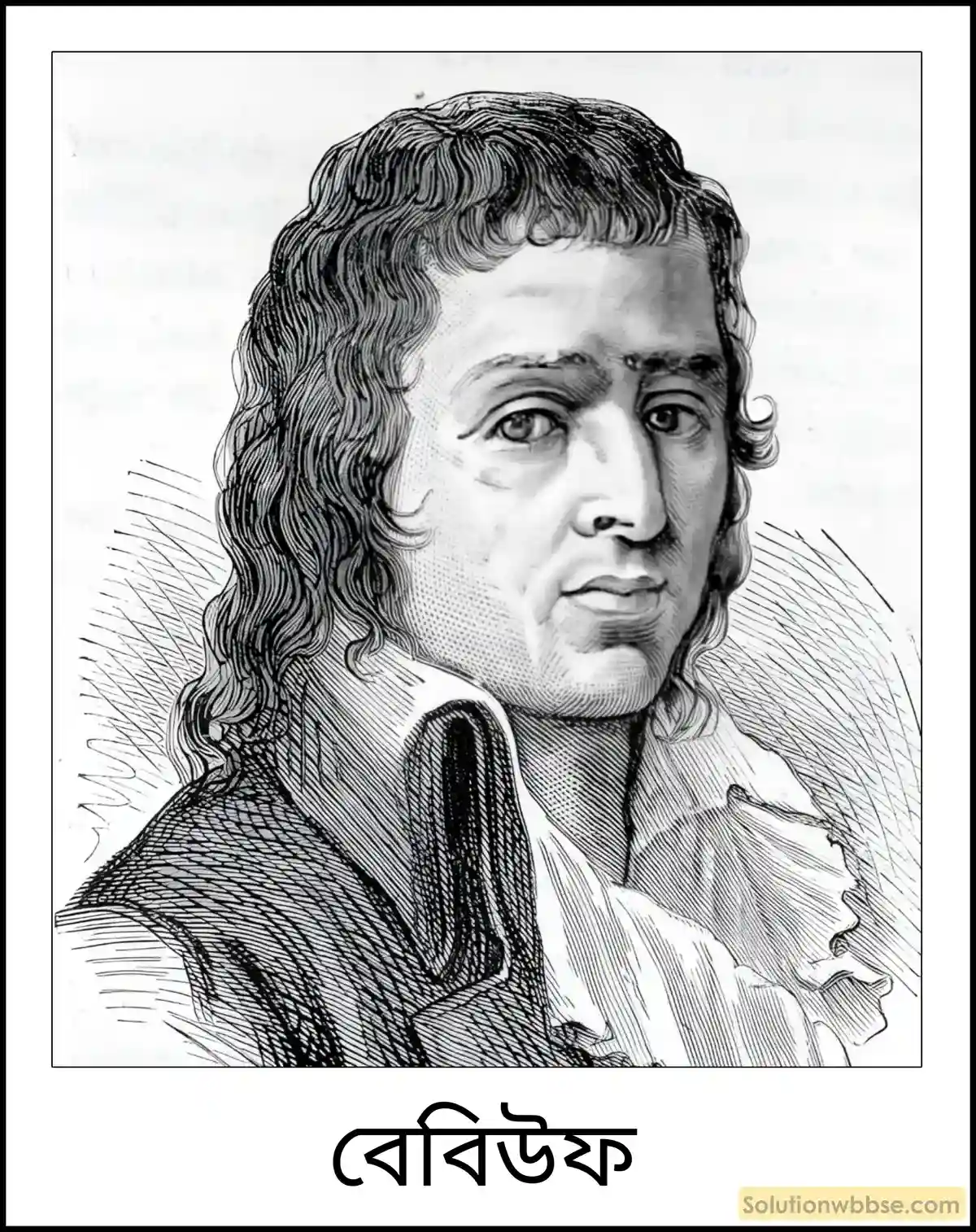
কনস্যুলেটের শাসন (Rule of Consulate) –
ডিরেক্টরির শাসন চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রান্সে ডিরেক্টরির শাসনের অবসান ঘটিয়ে কনস্যুলেটের শাসন প্রবর্তন করেন। এই শাসনব্যবস্থায় ৩ জন কনসালের হাতে শাসনক্ষমতা অর্পিত হয়। ফ্রান্সে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
তিনজন কনসাল (Consul) –
- নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Napoleon Bonapart),
- আবে সিয়েস (Abbe Sieyes) এবং ও
- রজার ডুকোস (Roger Ducos)।
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Napoleon Bonapart) –
নেপোলিয়ন 1769 খ্রিস্টাব্দের 15 আগস্ট ইটালির অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপের অ্যাজাক্কিও (Ajaccio) শহরে জন্মগ্রহণ করেন।
নেপোলিয়ন বংশসূত্রে কর্সিকান, কিন্তু জন্মসূত্রে ফরাসি নাগরিক ছিলেন, কারণ তাঁর জন্মস্থান কর্সিকা দ্বীপ ইটালির অন্তর্গত হলেও তাঁর জন্মের এক বছর আগে (1768 খ্রিস্টাব্দ) ফ্রান্স কর্সিকা দ্বীপ দখল করে নেয়।
- বাবা-মা – বাবার নাম – কার্লো বোনাপার্ট (পেশায় উকিল), মায়ের নাম – লেটিজিয়া বোনাপার্ট।
- শিক্ষালাভ – ব্রিওনি ও প্যারিসের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।
- চাকুরি – ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনীর সাব-লেফটেন্যান্ট পদে যোগ দেন। পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।
- পত্নী – জোসেফাইন। নেপোলিয়ন দ্বিতীয়বার অস্ট্রিয়ার রাজকন্যা মারিয়া লুইস-কে বিবাহ করেন (1810 খ্রিস্টাব্দে)।
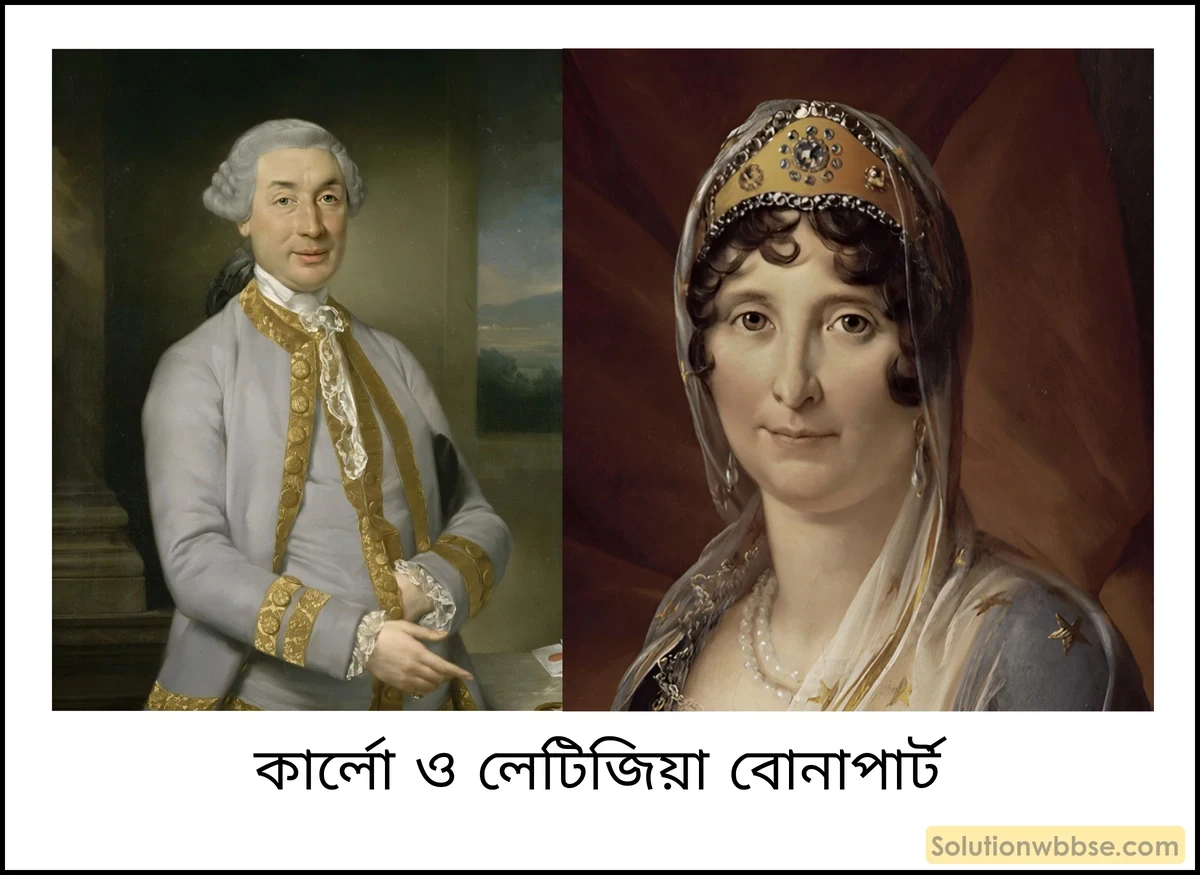
কনস্যুলেটের (Consulate) শাসান প্রথম কনসাল নেপোলিয়ন –
1799 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন ডিরেক্টরি শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে ‘কনস্যুলেট’ নামে এক নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এতে নেপোলিয়ন ছিলেন প্রথম কনসাল। অপর দুজন কনসাল ছিলেন আবে সিয়েস (Abbe Sieyes) ও রজার ডুকোস (Roger Ducos)।
- 1802 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তিনি নিজে সারাজীবনের জন্য কনসাল নিযুক্ত হন।
- কনস্যুলেটের শাসনে (1799-1804 খ্রিস্টাব্দ) নেপোলিয়ন ছিলেন সর্বেসর্বা। কনস্যুলেটের শাসনে একটি নতুন সংবিধান রচিত হয়েছিল (1799 খ্রিস্টাব্দ)। এটি ‘অষ্টম বর্ষের সংবিধান’ নামে পরিচিত, যার মূল ভিত্তি ছিল ‘কর্তৃত্ব উপরতলার আর আস্থা নীচুতলার’ (Authority from above and confidence from below)। এর রচয়িতা ছিলেন সংবিধান বিশেষজ্ঞ আবে সিয়েস।
- ফেলিক্স মার্কহাম তাঁর ‘নেপোলিয়ন অ্যান্ড দি অ্যাওয়েকেনিং অফ ইউরোপ’ (Napoleon and the Awakening of Europe) গ্রন্থে এই সংবিধানের প্রকৃতি প্রসঙ্গে একটি সুন্দর কথোপকথন উল্লেখ করেছেন। সংবিধানটি রচিত হওয়ার পর এটি জনগণকে শোনানো হয়েছিল। অনেকে তা মন দিয়ে শুনেছিলেন। সেসময় অনুপস্থিত এক মহিলা তার প্রতিবেশীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, নতুন সংবিধানে কী বলা হয়েছে? এর উত্তরে তার প্রতিবেশী বলেছিলেন, ‘নেপোলিয়ন’।
- আসলে নতুন সংবিধানে বিভিন্নভাবে প্রথম কনসাল বা নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত ক্ষমতাই জাহির করা হয়েছিল।
সম্রাট নেপোলিয়ন –
1804 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন নিজ ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ ঘটান। 1804 খ্রিস্টাব্দে সিনেট জাতীয় স্বার্থের নামে বংশগত সাম্রাজ্য গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এজন্য ফ্রান্সে গণভোট নেওয়া হয়। গণভোটের মাধ্যমে ফরাসি জনগণ নেপোলিয়নকে বেছে নেয়। এতে নেপোলিয়নের পক্ষে ভোট পড়েছিল 35,72,329টি এবং বিপক্ষে পড়েছিল 2,579টি।

- ফরাসি বিপ্লবের মূল আদর্শ ‘সাম্য’-কে গ্রহণ করলেও ‘স্বাধীনতা’-র আদর্শকে তিনি গুরুত্ব দেননি। তিনি বলেন – ‘ফরাসি জাতি স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র চায় না, তারা সাম্য চায়’ (What the nation wants is not Liberty but Equality)।
- 1804 খ্রিস্টাব্দের 2 ডিসেম্বর পোপ সপ্তম পায়াস (Pius VII) নোটরডাম চার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। 1804 খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন ‘ফরাসি জাতির সম্রাট’ উপাধি গ্রহণ করেন।
- নেপোলিয়নের উত্থানের ফলে ফ্রান্সের ইতিহাস হয় ইউরোপের ইতিহাস এবং ইউরোপের ইতিহাস হয় ফ্রান্সের ইতিহাস। এককথায় নেপোলিয়ন হয়ে উঠেছিলেন ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা। আর এভাবেই ‘নেপোলিয়নের যুগ’ শুরু হয়েছিল (1799-1815 খ্রিস্টাব্দ)।
- সম্রাট পদ লাভ করে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, “ফ্রান্সের রাজমুকুট মাটিতে পড়েছিল আমি তরবারির সাহায্যে তা তুলে নিয়েছি।” (I found the Crown of France lying on the ground and I picked it up with my Sword.)।
- নেপোলিয়ন ধর্মকেও একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলতেন, ‘…আমি মিশরে মুসলমান, ফ্রান্সে ক্যাথলিক….।’ (‘…I was a Mohammedan in Egypt, I shall be a Catholic here…’)
- নেপোলিয়ন ‘লিজিয়ন অফ অনার’ (Legion of Honour) নামে সম্মানসূচক পদবি প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।
- নেপোলিয়ন ‘কোড নেপোলিয়ন’ নামে একটি আইনবিধি সংকলন করেছিলেন। এজন্য নেপোলিয়নকে ‘দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান’ বলা হয়। 2287টি ধারা সংবলিত এই আইনবিধিকে ‘ফরাসি সমাজের বাইবেল’ বলা হয়।
- নেপোলিয়ন 1800 খ্রিস্টাব্দে ‘ব্যাংক অফ ফ্রান্স’ (Bank of France) প্রতিষ্ঠা করেন।
- কন্টিনেন্ট (Continent) মানে মহাদেশ। নেপোলিয়ন সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকে সামুদ্রিক অবরোধের আওতায় এনেছিলেন বলে এর নাম হয় ‘কন্টিনেন্টাল সিস্টেম’ (The Continental System) বা ‘মহাদেশীয় অবরোধ’।
- নেপোলিয়ন তাঁর নৌ-অধ্যক্ষ ট্রেভিল-কে (Treville) বলেছিলেন, ‘আমরা যদি ছ-ঘণ্টার জন্য ইংলিশ চ্যানেলের উপর কর্তৃত্ব করতে পারি, আমরা পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারি।’
মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা (Continental System) –
| খ্রিস্টাব্দ | ডিক্রি |
| 1806 খ্রিস্টাব্দের 11 নভেম্বর | বার্লিন ডিক্রি (Berlin Decree) |
| 1807 খ্রিস খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর থেকে নভেম্বর | মিলান ডিক্রি (Milan Decree) |
| 1807 খ্রিস্টাব্দ | ওয়ারশ ডিক্রি (Warshaw Decree) |
| 1810 খ্রিস্টাব্দ | ফন্টেনব্ল্যু ডিক্রি (Fontainebleau Decree) |
গ্র্যান্ড আর্মি (Grand Army) –
মূলত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন তাঁর ‘মহতী সৈন্যদল’ বা গ্র্যান্ড আর্মি (Grand Army) গঠন করেছিলেন। এই সৈন্যবাহিনী 1805 থেকে 1815 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। 1812 খ্রিস্টাব্দে এর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় 6 লক্ষ 75 হাজার। ফরাসি, জার্মানি, ওলন্দাজ, অস্ট্রিয়, ইতালীয়, প্রাশীয় ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির সৈন্য নিয়ে গঠিত এই সেনাবাহিনী নেপোলিয়নের হয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে লড়াই করেছিল।
ডাচি (Dutchy) –
ডাচি কথার অর্থ হল জমিদারি।
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মাধ্য হওয়া শক্তিজোটসমূহ (Coalitions) –
| শক্তিজোট | সময়কাল | কোন্ কোন্ দেশের মধ্যে |
| প্রথম শক্তিজোট (First Coalition) | 1793 খ্রিস্টাব্দ | অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ইংল্যান্ড, স্পেন, পোর্তুগাল, সার্ডিনিয়া। |
| দ্বিতীয় শক্তিজোট (Second Coalition) | 1799 খ্রিস্টাব্দ, 12 মার্চ | অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, নেপলস, পোর্তুগাল, তুরস্ক, ইংল্যান্ড। |
| তৃতীয় শক্তিজোট (Third Coalition) | 1805 খ্রিস্টাব্দ, জুলাই | অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, সুইডেন, ইংল্যান্ড। |
| চতুর্থ শক্তিজোট (Fourth Coalition) | 1813 খ্রিস্টাব্দ | রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংল্যান্ড, তুরস্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া। |
নেপোলিয়নের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ –
| যুদ্ধ | সময়কাল | প্রতিপক্ষ | জয়ী দেশ | যুদ্ধ শেষে সন্ধি |
| পিরামিডের যুদ্ধ (Battle of the Pyramids) | 1798 খ্রিস্টাব্দ, জুলাই | ফ্রান্স ও মিশর | ফ্রান্স | – |
| নীলনদের যুদ্ধ (Battle of the Nile) | 1798 খ্রিস্টাব্দ, আগস্ট | ইংল্যান্ড ওফ্রান্স | ইংল্যান্ড | – |
| ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধ (Battle of Marengo) | 1800 খ্রিস্টাব্দ, জুন | ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া | ফ্রান্স | লুনিভিলের সন্ধি (1801 খ্রিস্টাব্দ) |
| উলম্ -এর যুদ্ধ (Battle of Ulm) | 1805 খ্রিস্টাব্দ, 20 অক্টোবর | ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া | ফ্রান্স | |
| ট্রাফালগারের যুদ্ধ (Battle of Trafalgar) | 1805 খ্রিস্টাব্দ, 21 অক্টোবর | ইংল্যান্ড ওফ্রান্স | ইংল্যান্ড | |
| অস্টারলিজের যুদ্ধ (Battle of Austerlitz) | 1805 খ্রিস্টাব্দ, 2 ডিসেম্বর | ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া | ফ্রান্স | প্রেসবার্গের সন্ধি (1805 খ্রিস্টাব্দ, 26 ডিসেম্বর) |
| জেনার যুদ্ধ (Battle of Zena) ও অস্ট্যারডাটের যুদ্ধ (Battle of Austerdt) | 1806 খ্রিস্টাব্দ, 14 অক্টোবর | ফ্রান্স ও প্রাশিয়া | ফ্রান্স | স্কনবার্ন-এর সন্ধি (1806 খ্রিস্টাব্দ) |
| ফ্রিডল্যান্ডের যুদ্ধ (Battle of Friedland) | 1807 খ্রিস্টাব্দ, 14 জুন | ফ্রান্স ও রাশিয়া | ফ্রান্স | টিলসিটের সন্ধি(1807 খ্রিস্টাব্দ) |
| ওয়াগ্রামের যুদ্ধ (Battle of Wagram) | 1809 খ্রিস্টাব্দ, 5-6 জুলাই | ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া | ফ্রান্স | – |
| বোরোডিনোর যুদ্ধ (Battle of Borodino) | 1812 খ্রিস্টাব্দ, 7 সেপ্টেম্বর | ফ্রান্স ও রাশিয়া | ফ্রান্স | – |
| ড্রেসডেনের যুদ্ধ (Battle of Dresden) | 1813 খ্রিস্টাব্দ, আগস্ট | ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া | ফ্রান্স | – |
| লিপজিগের যুদ্ধ বা জাতিসমূহের যুদ্ধ (Battle of the Nations) | 1813 খ্রিস্টাব্দ, অক্টোবর | ফ্রান্স ও চতুর্থ শক্তিজোট (অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন ও রাশিয়া) | চতুর্থ শক্তিজোট ও মিত্রবাহিনী | ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রস্তাব (1813 খ্রিস্টাব্দ, 9 নভেম্বর) |
| ওয়াটারলুর যুদ্ধ (Battle of Waterloo) | 1815 খ্রিস্টাব্দ, 18 জুন | মূলত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স | ইংল্যান্ড ও প্রাশিয়া | – |
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি –
| স্বাক্ষরিত সন্ধি | স্বাক্ষরকারী | সন্ধির শর্তাবলি ও গুরুত্ব |
| ক্যাম্পো ফর্মিও-র সন্ধি (Treaty of Campo Formio), অক্টোবর, 1797 খ্রিস্টাব্দ | অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস -এর সঙ্গে নেপোলিয়নের | এই সন্ধির ফলে- 1. আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ, বেলজিয়াম ও অস্ট্রিয়াতে ফরাসি প্রাধান্য স্বীকৃতি পায়। 2. জার্মানির রাইন নদীর পূর্ব পর্যন্ত ফরাসি সাম্রাজ্যের সীমারেখা বিস্তৃত হয়। 3. অস্ট্রিয়ার প্রভাবমুক্ত ইটালিতে ‘সিস আলপাইন’ ও ‘লাই গুরিয়ান’ প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। |
| লুনিভিলের সন্ধি (Treaty of Lunéville), ফেব্রুয়ারি, 1801 খ্রিস্টাব্দ | ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে | এই সন্ধির ফলে- ফ্রান্স রাইন নদীর বামতীর পর্যন্ত তার অধিকার সম্প্রসারিত করায় বহু জার্মান মানুষ এবং বেশ কিছু জার্মান শহর, যথা – মেইনজ, আখেন প্রভৃতি ফ্রান্সের অধিকারে চলে যায় এবং ইটালিতে ফ্রান্স তার অধীনস্থ প্রজাতন্ত্রগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। |
| অ্যামিয়েন্সের সন্ধি (Treaty of Amiens), মার্চ, 1802 খ্রিস্টাব্দ | ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের | এই সন্ধির ফলে- ফ্রান্স মিশর, পোর্তুগাল ও দক্ষিণ ইটালি থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়, ইংল্যান্ড সিংহলে ও ত্রিনিদাদ বাদে সকল বিজিত অঞ্চল ফ্রান্স ও তার মিত্রদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এই সন্ধিতে ফ্রান্সের সকল ‘বৈদেশিক অধিকার’ অক্ষুণ্ণ থাকায় এবং ইংল্যান্ড বিনা ক্ষতিপূরণে সকল বিজিত অঞ্চল ত্যাগ করায় ইউরোপীয় রাজনীতিতে ফ্রান্স শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং সাময়িকভাবে দীর্ঘ 10 বছরের (1792-1802 খ্রিস্টাব্দ) ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। |
| প্রেসবার্গের সন্ধি (Treaty of Pressburg), ডিসেম্বর, 1805 খ্রিস্টাব্দ | ফ্রান্সের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার | এই সন্ধির ফলে- অস্ট্রিয়া ইটালির ভেনেসিয়া অঞ্চল ফ্রান্সকে, টাইরল ব্যাভেরিয়াকে, পশ্চিম জার্মানির একাংশ উইটনবার্গকে ছেড়ে দেয় এবং একটি দ্বিতীয় শ্রেণির শক্তিতে পরিণত হয় তথা জার্মান রাজ্যগুলিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য হ্রাস পায়। |
| টিলসিটের সন্ধি (Treaty of Tilsit), জুলাই, 1807 খ্রিস্টাব্দ | ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার | এই সন্ধিতে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য সংহত রূপ পায় এবং ফ্রান্সের সঙ্গে বেলজিয়াম, স্যাভয়, নিস প্রভৃতি যুক্ত হয় তথা নেপোলিয়ন তাঁর সামরিক গৌরবের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেন এবং রুশ-ফরাসি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ছাড়া রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধে যোগ দিতে বাধ্য হয়। |
| স্কনবার্নের সন্ধি (Treaty of Schönburnn), অক্টোবর, 1809 খ্রিস্টাব্দ | ফ্রান্সের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার | এই সন্ধির দ্বারা অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ইলিরিয়া প্রদেশ ফ্রান্সকে, পূর্ব ও পশ্চিম গ্যালিশিয়া যথাক্রমে রাশিয়া ও গ্র্যান্ড-ডাচি অফ ওয়ারশকে অর্পণ করে এবং রাজবংশ স্থাপনে আগ্রহী নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ রাজকন্যা মারিয়া লুইসকে বিবাহ করেন। |
| ফন্টেন্যুর সন্ধি (Treaty of Fontainebleau), এপ্রিল, 1814 খ্রিস্টাব্দ | নেপোলিয়নের সঙ্গে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ অর্থাৎ চতুর্থ শক্তিজোট | এই সন্ধির দ্বারা ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করে নেপোলিয়ন স্বাধীন শাসক হিসেবে এলবা দ্বীপে নির্বাসনে চলে যান এবং তাঁকে বছরে 2 মিলিয়ন ফ্রাংক করে বেতন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। |
| প্যারিসের প্রথম সন্ধি (Treaty of Paris), মে, 1814 খ্রিস্টাব্দ | চতুর্থ শক্তিজোট ও ফ্রান্সের মধ্যে | এই সন্ধির দ্বারা বুরবোঁ রাজা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষিত হন এবং ফ্রান্স তাঁর বিপ্লবপূর্ব সীমান্ত ফিরে পায় এবং বেলজিয়াম ও রাইন নদীর তীরবর্তী কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। |
| প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি (Treaty of Paris), নভেম্বর, 1815 খ্রিস্টাব্দ | চতুর্থ শক্তিজোট ও ফ্রান্সের মধ্যে | এই সন্ধির দ্বারা ফ্রান্স 1790 খ্রিস্টাব্দের হারানো সীমান্ত ফিরে পায় এবং ফ্রান্সকে 700 মিলিয়ন ফ্র্যাংক ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং বলা হয় আগামী 5 বছর মিত্রপক্ষের একদল সেনা ফ্রান্সে মোতায়েন থাকবে। |
ট্রাফালগারের যুদ্ধ (Battle of Trafalgar) –
ট্রাফালগারের যুদ্ধ হয়েছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌসেনাপতি নেলসন (Nelson) ফরাসি ও স্পেনীয় নৌবহরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। এই যুদ্ধে ফ্রান্স উপলব্ধি করে যে, সুদক্ষ নৌবাহিনী ছাড়া ইংল্যান্ডকে পরাজিত করা সম্ভব নয়।
কর্সিকা (Corsica Island) –
ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ইটালির অন্তর্গত একটি দ্বীপ। এক সময় ফ্রান্সও এই দ্বীপটি দখল করেছিল।
এলবা দ্বীপ (Elba Island) –
এলবা দ্বীপ ফ্রান্স ও ইটালির মাঝে ভূমধ্যসাগরের উত্তরে অবস্থিত। 1814 খ্রিস্টাব্দে এই দ্বীপেই নেপোলিয়ন প্রথমবার নির্বাসিত হন। সেখানে তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছিল।
ওয়াটারলু (Waterloo) –
বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের 10 মাইল দক্ষিণে ওয়াটারলু অবস্থিত। নেপোলিয়নের বাহিনী ওয়াটারলুর যুদ্ধে আর্থার ওয়েলেসলির (ডিউক অফ ওয়েলিংটন) হাতে পরাজিত হয়েছিল।
সেন্ট হোলনা (Saint Helena) –
আটল্যান্টিক মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসিত একটি দ্বীপ। এটি ফ্রান্স থেকে প্রায় 5 হাজার মাইল দূরে অবস্থিত।
1815 খ্রিস্টাব্দের 18 জুন ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর 15 জুলাই নেপোলিয়ন ধৃত ও বন্দি হন। এরপর নেপোলিয়নকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে সশস্ত্র প্রহরায় নির্বাসন দেওয়া হয়। এখানেই 1821 খ্রিস্টাব্দের 5 মে তাঁর মৃত্যু হয়।
নেপোলিয়নের আইন –
- Law of Minimum – দরিদ্র জনগণের বা শ্রমিকদের মজুরির সর্বনিম্ন পরিমাণ বেঁধে দেওয়া।
- Law of Maximum – দরিদ্র জনগণের সুবিধার জন্য জিনিসপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া।
নেপোলিয়নের আত্মজীবনী –
নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত থাকার সময় (1815-1821 খ্রিস্টাব্দ) তাঁর আত্মজীবনী লিখেছিলেন। একে Napoleonic Legend (নেপোলিয়নিক লেজেন্ড বা নেপোলিয়নের উপাখ্যান, নেপোলিয়নের কিংবদন্তি) বলা হয়। এই আত্মজীবনী গ্রন্থটি 1823 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন –
- আমিই বিপ্লব (I am the Revolution)।
- আমি ‘বিপ্লবের সন্তান’ (Child of Revolution)।
- আমি ‘বিপ্লবের ধ্বংসকারী’ (Destroyer of Revolution)।
নেপোলিয়ন ও ফরাসি বিপ্লব –
নেপোলিয়ন তাঁর আত্মজীবনীতে একদিকে যেমন নিজেকে বিপ্লবের সন্তান বলেছেন, ঠিক তেমনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি বিপ্লবকে ধ্বংস করেছেন। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে বিপ্লবের সাম্যনীতিকে গ্রহণ করে তিনি যাজক ও অভিজাতদের বিশেষ প্রাধান্য লোপ, সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের স্বীকৃতি, ব্যাবসাবাণিজ্যের উপর সরকারি কর্তৃত্বের বিনাশ, কোড নেপোলিয়ন -এর মাধ্যমে আইনের দৃষ্টিতে সমতা রক্ষা, বিপ্লবী আদর্শের প্রসার প্রভৃতির মাধ্যমে বিপ্লবকে রক্ষা করেন। এই দিক থেকে তিনি ছিলেন বিপ্লবের সন্তান।
কিন্তু অন্যদিকে তিনি বিপ্লবের অপর আদর্শ-স্বাধীনতাকে কঠোর হাতে দমন করে পররাজ্য গ্রাস করেন। গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে কঠোর হাতে দমন করে তিনি নিজেকে বিপ্লবের ধ্বংসকারীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন।
নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদী আদার্শর সহাবস্থান –
নেপোলিয়ন তাঁর সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – ইটালি ও জার্মানি। নেপোলিয়ন এই সকল রাষ্ট্রে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, অত্যাচারী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাশালী চার্চব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একই প্রকার করব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা ও কোড নেপোলিয়ন প্রবর্তন করে পুরাতনতন্ত্রের বিলোপসাধন করেছিলেন। নেপোলিয়নের এই উদ্যোগের ফলেই ইউরোপে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদেরও প্রসার ঘটে।
আজকের আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়, “বিপ্লবী আদর্শ, নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ” -এর “বিষয়সংক্ষেপ” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় অধ্যায়টির কাঠামো ও প্রধান বিষয়াবলি বুঝতে সাহায্য করবে, যা আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কিছুটা হলেও সহায়ক হয়েছে। যদি কোনো প্রশ্ন, মতামত বা সহায়তার প্রয়োজন হয়, নিচে মন্তব্য করে জানাতে পারেন কিংবা টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন—আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত।






মন্তব্য করুন