এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের ষষ্ঠ পাঠের তৃতীয় অধ্যায়, ‘চন্দ্রনাথ’ -এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে লেখকের পরিচিতি, গল্পের উৎস, গল্পের পাঠপ্রসঙ্গ, গল্পের সারসংক্ষেপ, গল্পের নামকরণ এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এই আর্টিকেলটি আপনাদের ‘চন্দ্রনাথ’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবে এবং গল্পটি ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া, নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে লেখক ও গল্পের সারসংক্ষেপ সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে, তাই এই তথ্যগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
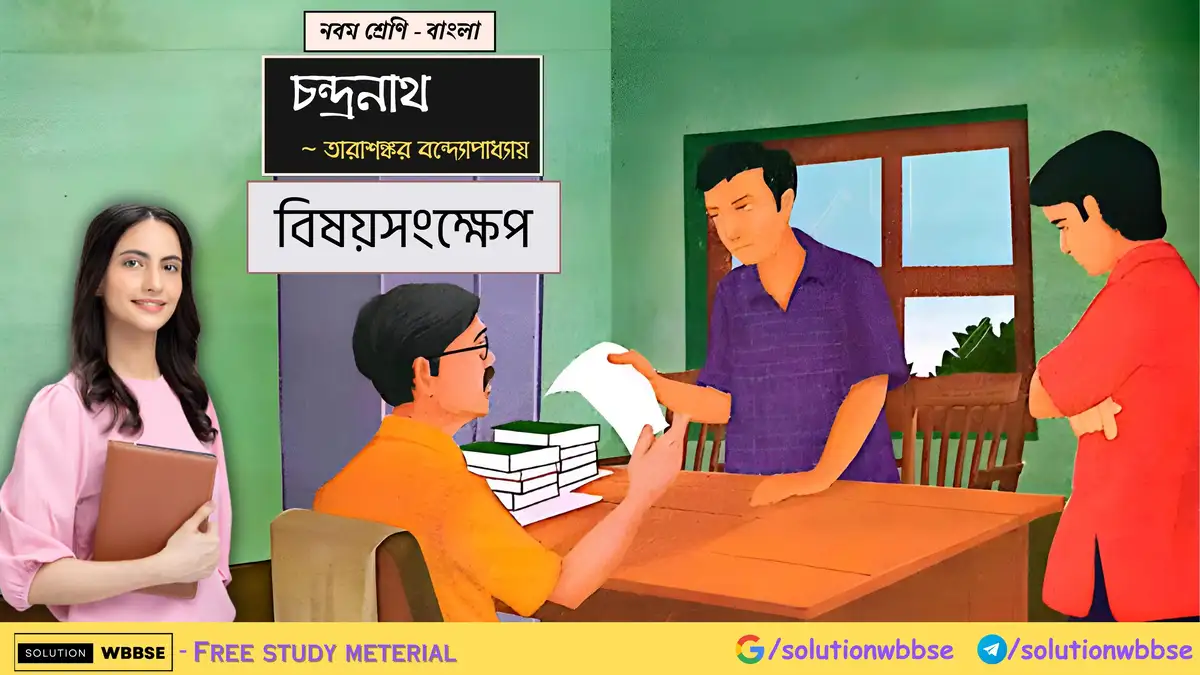
‘চন্দ্রনাথ’ গল্পের লেখক পরিচিতি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ও শিক্ষা –
রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। 1898 খ্রিস্টাব্দের 24 জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামের জমিদার পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তন্ত্রসাধক। মাতা প্রভাবতী দেবী ছিলেন আধুনিকমনস্ক, সাহিত্যানুরাগী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুরে যাদবলাল হাইস্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভরতি হন। এখানে পড়াকালীন বিপ্লবী দলে যুক্ত হওয়ার কারণে তাঁর পড়া শেষ হয়নি। বেশ কিছু সময় গৃহবন্দি থাকার পর তিনি 1918 খ্রিস্টাব্দে পুনরায় সাউথ সুবারবন কলেজে ভরতি হলেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাও অসমাপ্ত রেখে তাঁকে লাভপুরে চলে আসতে হয়।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ –
1322 বঙ্গাব্দে তিনি যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী উমাশশীকে বিবাহ করেন।
সাহিত্যিক তারাশঙ্কর –
মাতা প্রভাবতী দেবীর অনুপ্রেরণায় তারাশঙ্করের সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ তৈরি হয়। সাহিত্যজগতে তাঁর প্রবেশ ঘটে 1333 বঙ্গাব্দে ‘ত্রিপত্র’ কবিতা সংকলনটির প্রকাশের মধ্য দিয়ে। বীরভূমের রাঢ় মাটির গল্প, লোকজীবন তাঁর গল্প-উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছিল। ‘কল্লোল’ পত্রিকার আধুনিক সাহিত্যভাবনার অংশীদার হলেও তারাশঙ্কর একসময় নিজস্ব রীতি, মৌলিকতা নিয়ে স্বতন্ত্র হয়েছিলেন।
তাঁর গল্প-উপন্যাসে সমকালীনতা, বিশ্বযুদ্ধ এবং অবহেলিত, অন্ত্যজ, নিম্নবিত্তের মানুষের কথা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন – “জমিদার শ্রেণী ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনার প্রেরণাই হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল, বোধ করি এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ করে আগে লেখেননি বা লেখেন না বলে।” (‘আমার সাহিত্য জীবন’, 2য় খণ্ড)। তাঁর প্রথম গল্পটি হল ‘রসকলি’, 1334 বঙ্গাব্দে ‘কল্লোল’ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর ছোটোগল্প নানা সময়ে ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’, ‘উত্তরা’, ‘উপাসনা’, ‘বঙ্গশ্রী’, ‘প্রবাসী’ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্ব প্রকাশ, নিয়তির প্রভাব তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সম্ভার –
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সংখ্যা ষাট। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘চৈতালী ঘূর্ণি’ (1931 খ্রিস্টাব্দ)। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য হল – ‘পাষাণপুরী’ (1933 খ্রিস্টাব্দ), ‘রাইকমল’ (1934 খ্রিস্টাব্দ), ‘আগুন’ (1937 খ্রিস্টাব্দ), ‘ধাত্রীদেবতা’ (1939 খ্রিস্টাব্দ), ‘কালিন্দী’ (1940 খ্রিস্টাব্দ), ‘গণদেবতা’ (1942 খ্রিস্টাব্দ), ‘কবি’ (1944 খ্রিস্টাব্দ), ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ (1947 খ্রিস্টাব্দ), ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ (1952 খ্রিস্টাব্দ), ‘আরোগ্য নিকেতন’ (1953 খ্রিস্টাব্দ), ‘ডাকহরকরা’ (1958 খ্রিস্টাব্দ), ‘না’ (1960 খ্রিস্টাব্দ), ‘নিশিপদ্ম’ (1962 খ্রিস্টাব্দ), ‘কালবৈশাখী’ (1963 খ্রিস্টাব্দ), ‘মঞ্জরী অপেরা’ (1964 খ্রিস্টাব্দ), ‘ভুবনপুরের হাট’ (1964 খ্রিস্টাব্দ), ‘মহানগরী’ (1966 খ্রিস্টাব্দ), ‘শুকসারী কথা’ (1967 খ্রিস্টাব্দ), ‘স্বর্গমর্ত্য’ (1968 খ্রিস্টাব্দ), ‘ছায়াপথ’ (1969 খ্রিস্টাব্দ), ‘অভিনেত্রী’ (1970 খ্রিস্টাব্দ), ‘ফরিয়াদ’ (1971 খ্রিস্টাব্দ), ‘নবদিগন্ত’ (1973 খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সম্ভার –
তারাশঙ্করের গল্প সংখ্যা 190, গল্পগ্রন্থ 35টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – ‘ছলনাময়ী’ (1936 খ্রিস্টাব্দ), ‘জলসাঘর’ (1937 খ্রিস্টাব্দ), ‘রসকলি’ (1938 খ্রিস্টাব্দ), ‘তিনশূন্য’ (1941 খ্রিস্টাব্দ), ‘বেদেনী’ (1943 খ্রিস্টাব্দ), ‘যাদুকরী’ (1944 খ্রিস্টাব্দ), ‘হারানো সুর’ (1945 খ্রিস্টাব্দ), ‘ইমারত’ (1947 খ্রিস্টাব্দ), ‘মাটি’ (1950 খ্রিস্টাব্দ), ‘শিলাসন’ (1952 খ্রিস্টাব্দ), ‘বিস্ফোরণ’ (1955 খ্রিস্টাব্দ), ‘কালান্তর’ (1956 খ্রিস্টাব্দ), ‘বিষপাথর’ (1957 খ্রিস্টাব্দ), ‘মানুষের মন’ (1958 খ্রিস্টাব্দ), ‘রবিবারের আসর’ (1958 খ্রিস্টাব্দ), ‘অ্যাক্সিডেন্ট’ (1962 খ্রিস্টাব্দ), ‘চিন্ময়ী’ (1964 খ্রিস্টাব্দ), ‘তপোভঙ্গ’ (1966 খ্রিস্টাব্দ), ‘জায়া’ (1967 খ্রিস্টাব্দ), ‘পঞ্চকন্যা’ (1967 খ্রিস্টাব্দ), ‘শিবানীর অদৃষ্ট’ (1967 খ্রিস্টাব্দ), ‘এক পশলা বৃষ্টি’ (1967 খ্রিস্টাব্দ), ‘বিহঙ্গিনী’ (1970 খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি। তাঁর গল্পগুলি গঠনগত দিক থেকে মৌলিকত্বের দাবি রাখে। লেখক জীবন বাস্তবতাকে অকপটরূপে প্রকাশ করেছেন, ফলে তাঁর সাহিত্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরস্কার –
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের জন্য ‘শরৎ স্মৃতি পুরস্কার’ পেয়েছিলেন। বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পের জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন নানা সময়ে। ‘সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার’, ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’, ‘জ্ঞানপীঠ’ পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি। তারাশঙ্কর 1962 খ্রিস্টাব্দে ‘পদ্মশ্রী’ পুরস্কার পান এবং পরবর্তী 1969 খ্রিস্টাব্দে ভূষিত হন ‘পদ্মভূষণ’ পুরস্কারে।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু –
1971 খ্রিস্টাব্দের 14 সেপ্টেম্বর এই স্বনামধন্য কথাসাহিত্যের প্রয়াণ ঘটে। তাঁর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের এক অপূরণীয় ক্ষতি।
‘চন্দ্রনাথ’ গল্পের উৎস
‘চন্দ্রনাথ’ গদ্যাংশটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘আগুন’ উপন্যাসের প্রথমাংশের সম্পাদিত রূপ।
‘চন্দ্রনাথ’ গল্পের পাঠপ্রসঙ্গ
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চন্দ্রনাথ’ রচনাটি ‘আগুন’ উপন্যাসের অংশবিশেষ। ‘আগুন’ উপন্যাসে উনিশটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের সম্পূর্ণ ভাগ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের বেশ খানিকটা অংশ একত্র করে ‘চন্দ্রনাথ’ শিরোনামে ‘সাহিত্য সঞ্চয়ন’ বইতে সংকলন করা হয়েছে। পাঠ্য রচনায় ‘দুই’ চিহ্নিত অংশে মূল উপন্যাসের প্রথম ছয়টি অনুচ্ছেদ নেওয়ার পর তিনটে অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে। এরপর আরও কিছুটা অংশ সংকলন করা হয়েছে। মূল উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ নয়টি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে।
‘আগুন’ উপন্যাসটি যেখান থেকে আরম্ভ ‘চন্দ্রনাথ’ও সেখান থেকে শুরু করা হয়েছে। তাই এর পূর্বকথা বলে কিছু নেই। তবে প্রসঙ্গক্রমে ‘আগুন’ উপন্যাস সম্পর্কে কিছু কথা জেনে রাখা ভালো।
‘আগুন’ উপন্যাস প্রথমে ‘কালপুরুষ’ নামে ধারাবাহিক ভাবে সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় (1343 সনের 9 শ্রাবণ থেকে 21 কার্তিক পর্যন্ত) প্রকাশিত হয়। বই হিসেবে 1937 খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটি ‘আগুন’ নামে বের হয়।
‘আমার সাহিত্য জীবন’ বইয়ে তারাশঙ্কর লিখে গেছেন – ‘উনিশশো তেত্রিশ সালে ওই মনোহর পুকুর সেকেন্ড লেনে একখানি পাকা-দেয়াল টিনের ছাউনি ঘর ভাড়া করলাম। … এই ঘরখানিতেই কাটিয়েছিলাম প্রায় দেড় বছর। এরই মধ্যে অনেকগুলি ভালো গল্প এবং একখানি উপন্যাস লিখেছিলাম। … ‘আগুন’ উপন্যাসও এই ঘরে লেখা। তবে ‘আগুনে’র খসড়া তৈরি করেছিলাম বেহার প্রদেশের মগমা নামক স্থানে; বেহার ফায়ার ব্রিক্স্ কারখানায় – আমার পিসতুতো ভাইয়ের বাসায়।’
‘আগুন’ একটি চমৎকার, অভিনব ও উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাসের খ্যাতির আড়ালে এর চমৎকারিত্ব হারিয়ে গেছে।
‘চন্দ্রনাথ’ গল্পের বিষয়সংক্ষেপ
‘চন্দ্রনাথ’ কাহিনির সূচনা হয়েছে কথক তথা নরেশের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে। বিদ্যালয় জীবনের ঘটনা ও দুই সহপাঠী হীরু ও চন্দ্রনাথের সঙ্গে নরুর সম্পর্ক বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাহিনি ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। স্কুলের পরীক্ষায় বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করে আসা চন্দ্রনাথ শেষ বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়। অন্যায়ভাবে হীরুকে প্রথম করা হয়। হীরুর প্রথম হওয়াতে স্কুলের সহকারী শিক্ষক তথা গৃহশিক্ষকের অন্যান্য সহায়তা আছে বলে চন্দ্রনাথের বিশ্বাস। তা ছাড়া হীরু স্কুলের সেক্রেটারির ভাইপো বলেও সুবিধে পেয়েছে। চন্দ্রনাথের খাতা থেকেও সে টুকলি করেছে। এরই প্রতিবাদে চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে প্রধান শিক্ষককে চিঠি দেয়। দ্বিতীয় পুরস্কার গ্রহণ করা তার ডিগনিটির পক্ষে সমীচীন নয়, বরং অপমানজনক বলে সে তার দাদা নিশানাথকে জানায়। নিশানায় প্রত্যাখ্যানপত্র ফিরিয়ে নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে চন্দ্রনাথকে ক্ষম চাইতে বলেন। দু-ভাইয়ের প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়। কিন্তু চন্দ্রনাথ নিজেজ্ঞ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে। মতবিরোধের চূড়ান্ত পরিণতিতে দু-ভাইয়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটে।
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পরীক্ষাতেও হীরু চন্দ্রনাথকে পিছনে ফেলে দেয় এবং স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। হীবুর বাড়িতে উৎসবের আয়োজন হয়। সেখানে চন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হলেও সেদিনই সে কাউকে কিছু না বলে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। অনুপস্থিতির জন্য মার্জনা চেয়ে হীরুকে একটা চিঠি লিখে যায়। কিন্তু সে কোথায় যাচ্ছে তা কাউকে বলে যায় না।
‘চন্দ্রনাথ’ গল্পের নামকরণ
ভূমিকা –
সাহিত্যে নামকরণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শিরোনাম সাহিত্য ও পাঠকের মধ্যে একটি প্রারম্ভিক সেতু গঠন করে। সাহিত্যে নামকরণের নির্দিষ্ট কোনো রীতি প্রচলিত না থাকলেও মোটামুটিভাবে নামকরণ চরিত্রকেন্দ্রিক, বিষয়কেন্দ্রিক ও ব্যঞ্জনাধর্মী – এই তিন ধরনের হয়ে থাকে। আলোচ্য পাঠ্যাংশটি মূলত চরিত্রকেন্দ্রিক।
সম্পাদককৃত নামকরণ –
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আগুন’ উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের পুরোটা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অংশবিশেষ একত্র করে ‘চন্দ্রনাথ’ নামে পাঠ্য ‘সাহিত্য সঞ্চয়ন’ বইতে সংকলিত হয়েছে। সুতরাং চরিত্রপ্রধান ‘চন্দ্রনাথ’ পাঠ্যাংশটির নামকরণ লেখককৃত নয়, সম্পাদককৃত।
নামকরণের বিষয়বস্তু
মূল উপন্যাসের নায়ক এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র চন্দ্রনাথ। পাঠ্য গদ্যাংশের কাহিনিও চন্দ্রনাথকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। কাহিনির কথক নরেশ এবং তার দুই সহপাঠী হীরু আর চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথও এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। চন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই কাহিনির সূচনা। স্কুলের পরীক্ষায় অন্যায়ভাবে হীরুকে প্রথম স্থান দিয়ে চন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় করা হয়েছে বলে চন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানাতে দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রধানশিক্ষককে লেখা প্রত্যাখ্যানপত্র ফিরিয়ে নিয়ে ক্ষমা চাইতে বলেন চন্দ্রনাথের দাদা। কিন্তু চন্দ্রনাথ রাজি হয়নি। ফলে তার দাদার সঙ্গে চন্দ্রনাথের চিরবিচ্ছেদ ঘটে যায়। অভিমানী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আত্মবিশ্বাসী চন্দ্রনাথ গ্রাম ছেড়ে একা নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেয়।
নামকরণের সার্থকতা –
মেধাবী ও দরিদ্র চন্দ্রনাথের প্রতি নরেশ বিশেষ সমব্যথী। হীরু, নিশানাথ, প্রধানশিক্ষক কেউই চন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করতে পারেননি। সকলের আচার-আচরণ, ভাবনাচিন্তা ও কথাবার্তার কেন্দ্রে চন্দ্রনাথ বিরাজমান। পাঠ্য অংশটি শেষও হয়েছে হীরুকে লেখা চন্দ্রনাথের চিঠি এবং চন্দ্রনাথের প্রতি নরেশের সমীহপূর্ণ স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে।
অতএব, কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামেই আলোচ্য রচনাটির নামকরণ হয়েছে এবং এই নামকরণ যথার্থ।
এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের ষষ্ঠ পাঠের তৃতীয় অধ্যায়, ‘চন্দ্রনাথ’ -এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে লেখকের পরিচিতি, গল্পের উৎস, গল্পের পাঠপ্রসঙ্গ, গল্পের সারসংক্ষেপ, গল্পের নামকরণ এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আর্টিকেলটি আপনাদের ‘চন্দ্রনাথ’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছে এবং গল্পটি ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া, নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে লেখক পরিচিতি, গল্পের নামকরণ ও গল্পের সারসংক্ষেপ সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে, তাই এই তথ্যগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।






মন্তব্য করুন