এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের প্রথম পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ -এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে নাট্যকার পরিচিতি, নাটকের উৎস, নাটকের পাঠপ্রসঙ্গ, নাটকের সারসংক্ষেপ, নাটকের নামকরণ এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এই আর্টিকেলটি আপনাদের ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবে এবং নাটকটি ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া, নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে নাট্যকার পরিচিতি ও নাটকের সারসংক্ষেপ সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে, তাই এই তথ্যগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
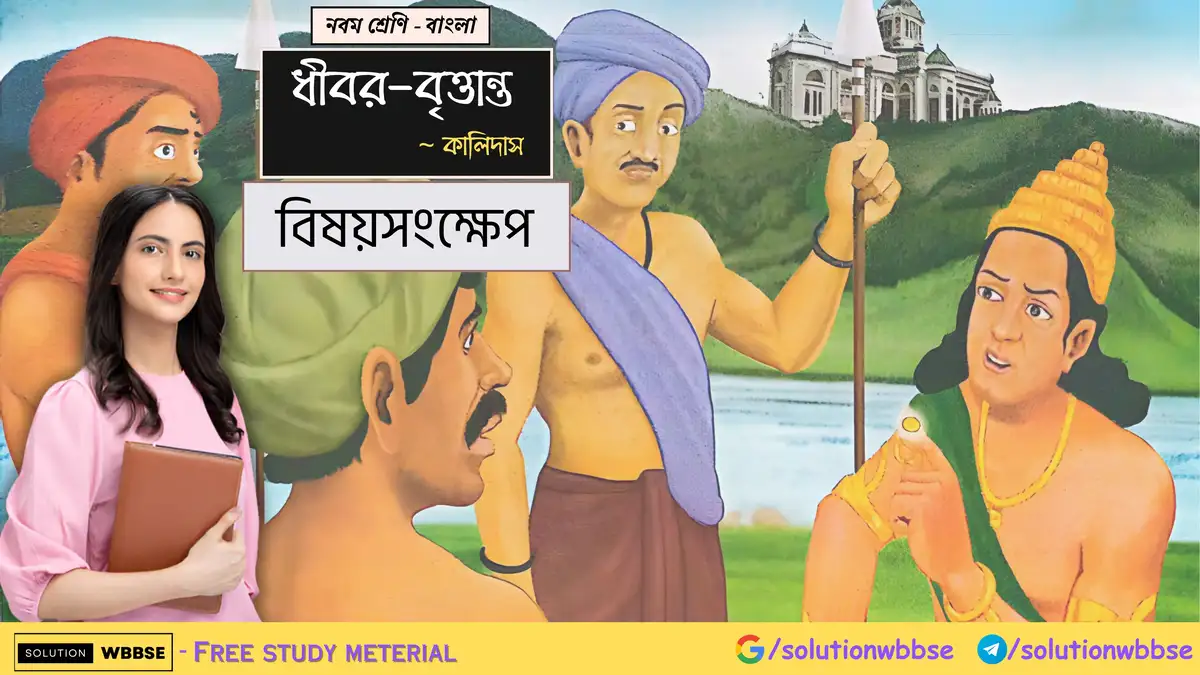
‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাটকের নাট্যকার পরিচিতি
কালিদাসের আবির্ভাবকাল ও জন্মস্থান –
সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মহাকবি হলেন কালিদাস। শুধুমাত্র ভারতভূমিতেই নয়, তাঁর সৃষ্টি বিশ্বসাহিত্য প্রাঙ্গণে প্রভূত সমাদর লাভ করেছে। কালিদাসের জন্মকাল এবং জন্মস্থান নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁর রচনারীতি বিশ্লেষণ করে গবেষকগণ এখনও কোনো স্থায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি।
কালিদাসের জন্মকাল নিয়ে তিনটি মত প্রচলিত রয়েছে – প্রথম মত, তিনি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে আবির্ভূত হন।
দ্বিতীয় মত, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে আবির্ভূত হন।
তৃতীয় মত, কালিদাসের আবির্ভাবকাল খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। কালিদাসের জন্মস্থানের ক্ষেত্রেও অস্পষ্টতা রয়ে গেছে –
- গবেষকদের একাংশের দাবি কালিদাস উজ্জয়িনীতে জন্মগ্রহণ করেন।
- কোনো কোনো মতানুযায়ী তিনি কাশ্মীর বা হিমালয়-সংলগ্ন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।
- আবার কেউ কেউ বলেন কালিদাস ছিলেন দক্ষিণ ভারত বা বিদর্ভ প্রদেশের লোক।
কোনো স্থির সিদ্ধান্তে না এলেও বহুপণ্ডিতের মতের ওপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে, কালিদাস হয়তো ‘উজ্জয়িনী’-তেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নয়তো তাঁর জীবনের এক বড়ো অংশ তিনি উজ্জয়িনীতে অতিবাহিত করেছিলেন।
কালিদাসের জনশ্রুতি –
কালিদাস সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। শোনা যায়, প্রথম জীবনে তিনি মহামূর্খ ছিলেন। কয়েকজন পণ্ডিত দেশের বিদুষী রাজকন্যার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কালিদাসের সঙ্গে কৌশলে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। কালিদাসের মূর্খতার পরিচয় পেয়ে তার পত্নী তাকে অপমান করে ত্যাগ করেন। এরপর দুঃখে কালিদাস আত্মহত্যা করতে গেলে স্বয়ং দেবী সরস্বতী তাকে রক্ষা করেন এবং ‘মহাকবি’ হওয়ার বর দান করেন। সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস রাজবাড়িতে এসে তার পত্নীর সঙ্গে দেখা করে বলেন – ‘অস্তি কশ্চিদ বাগবিশেষ’। এই বিখ্যাত বাণী থেকে পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর ‘কুমারসম্ভবম্’, ‘মেঘদূতম্’, ‘রঘুবংশম্’ ইত্যাদি অসাধারণ সাহিত্যসম্ভার।
কালিদাসের রচনা সমগ্র ও সাহিত্যে অবদান –
উজ্জয়িনীর সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সভাকবি কালিদাস সম্পর্কে জনশ্রুতি যাই থাকুক তাঁর সাহিত্যসৃজন থেকে মহাকবির পাণ্ডিত্য সম্পর্কে জানা যায়। শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের নানা পর্যায়ে কালিদাসের প্রভাব লক্ষণীয়। কালিদাসের রচনাগুলিতে সাহিত্যিক রীতি-র পাশাপাশি সমকালীনতা, বাস্তবতা এবং জীবনদর্শনের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। তিনি তিনটি দৃশ্যকাব্য বা নাটক রচনা করেছিলেন – ‘মালবিকাগ্নিমিত্রম্’, ‘বিক্রমোর্বশীয়ম্’, ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’। এ ছাড়া তাঁর রচিত দুটি মহাকাব্য হল – ‘কুমারসম্ভবম্’, ও ‘রঘুবংশম্’ এবং দুটি খণ্ড কাব্য হল- ‘ঋতুসংহারম্’ ও ‘মেঘদূতম্’। ‘মেঘদূতম্’-কে আবার দূতকাব্য বলা হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কালিদাসের প্রভাব দেখা যায়। গোবিন্দদাসের পদে, বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ বিবরণে সর্বত্রই কালিদাসের স্পর্শ রয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নানাভাবে কালিদাসের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত। কালিদাসের রচনাগুলি একাধিকবার ইংরেজি, জার্মান ভাষাতে অনূদিত হয়েছে। জার্মান কবি গ্যেটে ও হায়ডার কালিদাসের রচনার প্রশংসা করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপমা প্রয়োগ, শব্দ বিন্যাস, চিত্রকল্প নির্মাণ এবং চরিত্র সৃজনে কালিদাস বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন।
‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাটকের উৎস
সংস্কৃত মহাকবি কালিদাস বিরচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে পাঠ্যাংশের ‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশটি নেওয়া হয়েছে। নাটকটি বাংলায় তরজমা করেন সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী।
‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাটকের পূর্বকথা
হস্তিনাপুরের ভরতবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গিয়ে ঘটনাচক্রে। পথ ভুল করে মালিনী নদীতীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আসেন। সেখানে কম্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যান রাজা দুষ্মন্ত। শকুন্তলার সঙ্গলাভে উদ্গ্রিব রাজা কণ্বমুনির অনুপস্থিতিতে একদিন গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করেন এবং অভিজ্ঞানস্বরূপ তার নামাঙ্কিত আংটি উপহার দিয়ে রাজধানীতে ফিরে যান। বহুকাল অতিক্রম হলেও রাজা শকুন্তলাকে নিয়ে যেতে আসেন না। এদিকে দুষ্মন্ত-র চিন্তায় মগ্ন শকুন্তলা তপোবনে আগত ঋষি দুর্বাসাকে লক্ষ করেনি। এর ফলে অপমানিত ঋষি শকুন্তলাকে অভিশাপ দেন যে, যার চিন্তায় সে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতন হয়ে রয়েছে সেই ব্যক্তি শকুন্তলাকে চিরকালের জন্য ভুলে যাবে। শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদা ঋষি দুর্বাসার কাছে ভয়ানক অভিশাপ ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করলে সে জানতে পারে শকুন্তলাকে দেওয়া রাজার আংটি একমাত্র রাজার কাছে শকুন্তলার পরিচয় দিতে পারবে। কণ্বমুনি তপোবনে ফিরে এসে শকুন্তলার বিবাহ সম্পর্কে জানতে পেরে তাকে রাজার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। রাজধানীতে যাওয়ার পথে শকুন্তলার আংটি ঘটনাক্রম অনুসারে শচীতীর্থের জলে স্নানের পর অঞ্জলি দেওয়ার সময় পড়ে যায় এবং একটি মাছ তা খেয়ে নেয়। আংটি না থাকায় শকুন্তলা নিজের পরিচয় রাজাকে দিলেও রাজা তা বিশ্বাস করেন না এবং অপমানিত হয়ে শকুন্তলা মারীচের তপোবনে আশ্রয় নেয়।
অন্যদিকে কিছুকাল পর এক ধীবরের জালে ধরা পড়ে সেই মাছটি, যে শকুন্তলার আংটি খেয়ে ফেলেছিল। এরপরের অংশ নিয়েই আলোচ্য পাঠ্যাংশের ‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাটকটি রচিত।
‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাটকের বিষয়সংক্ষেপ
মহাকবি কালিদাস রচিত সংস্কৃত নাটক ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ থেকে আলোচ্য ‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশটি সংগৃহীত। মূল নাটক থেকে এই নাট্যাংশের অনুবাদ করেন সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। নাটকের অন্যতম মূলচরিত্র ও নায়িকা শকুন্তলা হলেও আলোচ্য নাট্যাংশটির মুখ্য চরিত্র হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে আপাত পরিচয়হীন ধীবর।
এই ধীবরের জালে ধরা পড়া রুই মাছের পেট থেকে পাওয়া যায়। রাজা দুষ্মন্ত নামাঙ্কিত মহামূল্যের আংটি। সেই আংটি বিক্রি করার সময় রাজ প্রহরী ও নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালকের হাতে চোর সন্দেহে ধরা পড়ে ধীবর। নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও রক্ষীরা তার কথা বিশ্বাস করে না। রাজশ্যালক তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনে রাজার কাছে আংটি নিয়ে যান সত্যতা প্রমাণ করতে। কিছু পরে তিনি ফিরে এসে জানান, ধীবর নির্দোষ এবং রাজা তাকে পুরস্কৃত করেছেন। উপরন্তু বলেন, আংটি পেয়ে রাজা শুধু খুশি হয়নি, কোনো গভীর চিন্তায় কিছু সময়ের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।
ধীবর মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছে এবং পুরস্কৃত হয়েছে দেখে রক্ষীরা ঈর্ষাণ্বিত হয়ে পড়ে। উদারমনস্ক ধীবর নিজের পাওয়া পুরস্কার থেকে অর্ধেক তাদের দিয়ে দেয়। ধীবরের এই আচরণে খুশি হয়ে নগর রক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক তাকে ‘বন্ধু’ বলে আপন করে নেয়।
‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাটকের নামকরণ
ভূমিকা –
নামকরণ যে-কোনো সাহিত্য নির্মিতিরই একটি প্রয়োজনীয় অংশ। বলা যেতে পারে, রচনাটি প্রাথমিকভাবে নামকরণ বা শিরোনামের কারণেই পাঠক মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠক নামকরণের মাধ্যমে রচনাটির বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। নামকরণ রচনাটিকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রতিটি সাহিত্যে নামকরণ উল্লেখযোগ্য বিষয়। সাধারণত কোনো ঘটনা, চরিত্র, বিষয়, বিশেষ ব্যঞ্জনা বা লেখকের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে নামকরণ করা হয়।
বিষয়কেন্দ্রিক নামকরণ –
আলোচ্য ‘ধীবর বৃত্তান্ত’ পাঠ্যাংশটি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ -এর ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে সংগৃহীত। পাঠ্যাংশের নামকরণ বিষয়কেন্দ্রিক। একজন ধীবরের সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের রাজধানীর নগররক্ষক ও রক্ষীদের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে উক্ত নাট্যাংশে। নাটকের পূর্বকথা থেকে জানা যায় শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের বিবাহের কথা শুনে কণ্বমুনি শকুন্তলাকে নিয়ে রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে শচীতীর্থের জলে শকুন্তলার কাছ থেকে রাজনামাঙ্কিত প্রতীকি আংটিটি পড়ে যায় এবং একটি মাছ তা খেয়ে নেয়। দুর্বাসার অভিশাপে রাজা শকুন্তলাকে ভুলে যান ও অভিজ্ঞান না থাকায় নিজের পরিচয় দিতে ব্যর্থ শকুন্তলা অপমানিত হয়ে ফিরে যায়।
অন্যদিকে আংটি খেয়ে নেওয়া মাছটি ধরা পড়ে একজন ধীবরের জালে। মাছ কেটে আংটি পাওয়া গেলে সামান্য ধীবর তা বিক্রির জন্য নগরে ঘুরতে থাকে। রাজনামাঙ্কিত মহামূল্যের আংটি ধীবরের কাছে দেখে তাকে চোর সন্দেহে নগররক্ষক ও প্রহরীরা ধরে আনেন। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে ব্যর্থ ধীরবকে তার বৃত্তি-জাতি নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহ্য করতে হয়। নগর রক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক আংটি নিয়ে সত্যতা যাচাই করার জন্য রাজার কাছে গেলে জানতে পারে ধীবর নিরপরাধী। আংটি পাওয়া গেলে রাজা ধীবরকে মুক্তি দেন ও সমমূল্যের উপহারে পুরস্কৃত করেন। শাস্তি না পেয়ে পুরস্কৃত ধীবরকে দেখে রক্ষীরা ঈর্ষাণ্বিত হলে উদারমনস্ক ধীবর তার নিজ প্রাপ্য থেকে অর্ধেক দিয়ে দেন। সত্যবাদী, সৎ ধীবরের আচরণে খুশি হয়ে রাজশ্যালক তাকে প্রিয় বন্ধুর মর্যাদা দেন।
নামকরণের সার্থকতা –
চোর সন্দেহে ধৃত ও পরে রাজার দ্বারা পুরস্কৃত ধীবর আলোচ্য পাঠ্যাংশের নায়ক ও মুখ্য চরিত্র। রাজনামাঙ্কিত আংটি নিয়ে নাটকটি শুরু হয়েছিল এবং নাটকের শেষে তা পুনরায় রাজার কাছে ফিরে যায় ধীবরের মাধ্যমে। ধীবরের সত্যবাদী, সৎ ও উদারমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধীবরকে কেন্দ্র করে নাট্যদৃশ্য আবর্তিত হয়। অতএব বলা যেতে পারে আলোচ্য নাটকটির বিষয়কেন্দ্রিক নামকরণ নিঃসন্দেহে যথার্থ ও সুপ্রযুক্ত হয়েছে।
এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের প্রথম পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ –এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে নাট্যকার পরিচিতি, নাটকের উৎস, নাটকের পাঠপ্রসঙ্গ, নাটকের সারসংক্ষেপ, নাটকের নামকরণ এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আর্টিকেলটি আপনাদের ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছে এবং নাটকটি ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া, নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে নাট্যকার পরিচিতি, নাটকের নামকরণ ও কবিতার সারসংক্ষেপ সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে, তাই এই তথ্যগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।






মন্তব্য করুন