এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “উনিশ শতকে লেখা ও রেখার মাধ্যমে কীভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটেছে? অথবা, উনিশ শতকে রেখায় ও লেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটেছিল – উক্তিটি আনন্দমঠ উপন্যাস এবং ভারতমাতা চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করো।” নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাস পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই “উনিশ শতকে লেখা ও রেখার মাধ্যমে কীভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটেছে? অথবা, উনিশ শতকে রেখায় ও লেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটেছিল – উক্তিটি আনন্দমঠ উপন্যাস এবং ভারতমাতা চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করো।“ প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায় “সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা“ -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়।
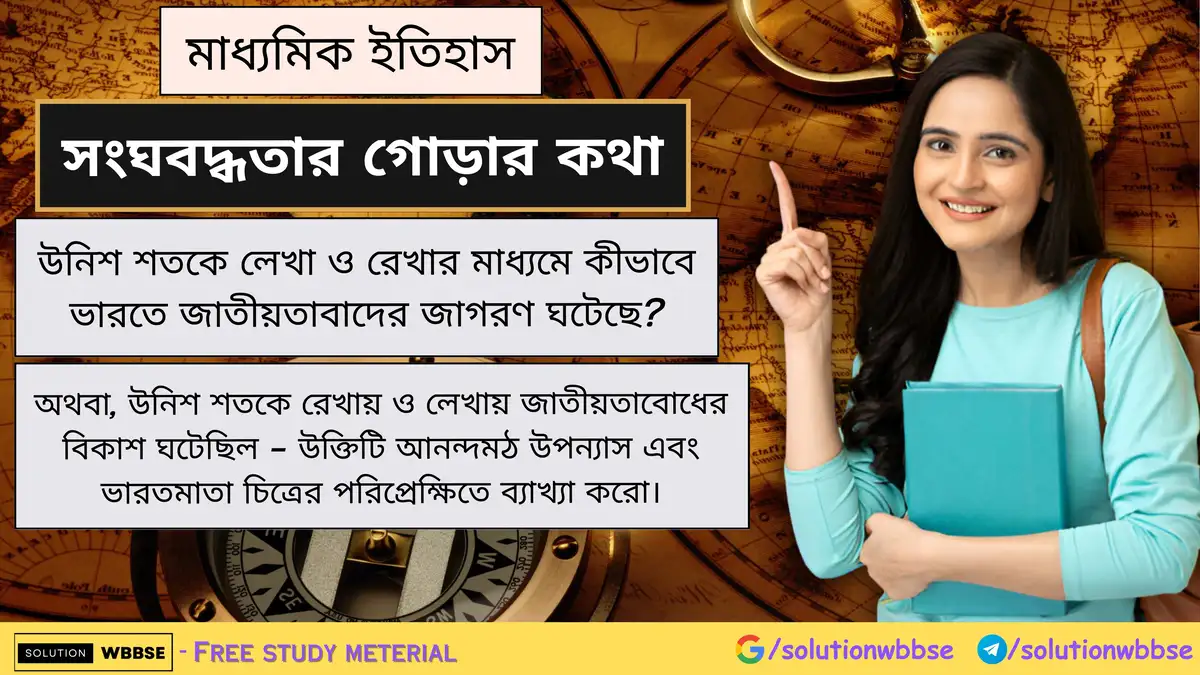
উনিশ শতকে লেখা ও রেখার মাধ্যমে কীভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটেছে?
অথবা, উনিশ শতকে রেখায় ও লেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটেছিল-উক্তিটি আনন্দমঠ উপন্যাস এবং ভারতমাতা চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করো।
পৃথিবীর যে-কোনো দেশে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশের সঙ্গে সেই দেশের দেশাত্মবোধক বা জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশাত্মবোধক সাহিত্যের বিকাশ ভারত ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ-সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই সেদিনের মূল সুর ছিল দেশপ্রেম। ভারতীয় চিত্রকলাতেও সেদিন লেগেছিল স্বাদেশিকতার ছোঁয়া। ভারতীয় জাতীয় জাগরণে এইসব গ্রন্থ এবং চিত্রকলার গুরুত্ব অপরিসীম।
লেখায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ
আনন্দমঠ বাংলা উপন্যাসে স্বদেশচিন্তা ও জাতীয়তাবোধের বিকাশের এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ।
আনন্দমঠ গ্রন্থের প্রকাশ –
1882 খ্রিস্টাব্দে আনন্দমঠ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
আনন্দমঠ গ্রন্থের বিষয়বস্তু –
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত আনন্দমঠ উপন্যাসে জনজীবনের কোলাহল থেকে দূরে এক নিভৃত স্থানে একটি মঠ গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই মঠে বসবাসকারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য নিবেদিত প্রাণ।
আনন্দমঠ গ্রন্থের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত –
‘আনন্দমঠ’-এ উল্লেখিত ‘বন্দেমাতরম্’ হল দেশপ্রেমের মহাসঙ্গীত, জাতীয়তাবাদের বেদ-বাইবেল-গীতা। এই ‘মা’ হলেন জননী-জন্মভূমি দেশমাতৃকা। তিনি মাতৃভক্ত সন্তানের একমাত্র আরাধ্যা। ‘বন্দোমাতরম্’ সঙ্গীত সশস্ত্র বিপ্লবীদের অন্যতম অভিমন্ত্রে পরিণত হয়।
আনন্দমঠ গ্রন্থের সন্তান দল –
‘আনন্দমঠ’-এ বঙ্কিমচন্দ্র সন্তানদলকে দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিত প্রাণ হিসাবে তুলে ধরেছেন। সন্তানদলের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব সমর্পনের আদর্শ পরবর্তীকালে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা জোগায়।’
রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাস –
1910 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হল উদার জাতীয়তাবাদের জাগরণ। ‘গোরা’র কেন্দ্রীয় চরিত্র গোরা (গৌরমোহন) একজন আইরিশ দম্পতির পুত্র। সে বিদেশি, বিধর্মী। নিজের জন্ম পরিচয় না জেনে একটি হিন্দু পরিবারে সে মানুষ হয়। নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসেবে সে ক্রমশঃ ইংরেজ বিদ্বেষী ও খ্রিস্ট-বিরোধি হয়ে ওঠে। কিন্তু একসময়ে সে তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে। কিন্তু এত বড়ো আঘাতেও গোরা ভেঙে পড়েনি বা অভিমানে দূরে সরে যায়নি। আত্মপরিচয় জানার পর তার সমস্ত সংকীর্ণতা নিমেষে ভেঙে যায় এবং পালিকা মাতা আনন্দময়ীর মধ্যেই খুঁজে পায় জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক শাশ্বত মাতৃহৃদয়কে।
‘গোরা’ উপন্যাসের জাতীয়তাবোধের জাগরণ –
সুবিশাল ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আনন্দময়ীর মতো ভারতমাতার কাছেও কোনো জাত-পাতের ভেদাভেদ নেই, জাত থাকলে ভারতবর্ষ যুগে যুগে ‘মহামানবের মিলনক্ষেত্রে’ হয়ে উঠত না। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে গোরার আত্মপোলব্ধির মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক সর্বভারতীয় রূপটি তুলে ধরেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।
বর্তমান ভারত –
স্বামীজির ‘বর্তমান ভারত’ প্রথমে পাক্ষিক ‘উদ্বোধন’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে 1905 খ্রিস্টাব্দে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
বর্তমান ভারত -এর বিষয়বস্তু –
‘বর্তমান ভারত’-এ স্বামীজি ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস মন্ধন করে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে সংহত আকারে প্রকাশ করেছেন।
বর্তমান ভারত -এর শূদ্রের জাগরণ –
‘বর্তমান ভারত’-এ স্বামীজি তাঁর বিশ্লেষণী লেখনীর মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাস সর্বদা শ্রেণি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। তাঁর মতে পৃথিবীর সর্বত্রই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র – এই চারটি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী শাসন করবে। প্রথম দুটি বর্ণের শাসনকাল শেষ হয়েছে, তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যের শাসনকালও সমাপ্তির মুখে। চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের শাসন অবশ্যম্ভাবী এবং তা ঐতিহাসিক সত্য।
বর্তমান ভারত -এর স্বদেশমন্ত্র –
গ্রন্থের উপসংহারে স্বামীজি দেশবাসীকে স্বদেশমন্ত্র উপহার দিয়েছেন। দেশের যুবসমাজের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান – ‘হে ভারত, ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত -ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।’ দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে অনবদ্য ভাষায় তিনি লিখেছেন – ‘ভারতবর্ষ আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ-ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ’। স্বামীজির স্বদেশপ্রেম এভাবেই পূর্ণতা পেয়েছে স্বদেশমন্ত্রে।
রেখায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতমাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভারতমাতা’ চিত্রটি দেশপ্রেমের এক মহাযজ্ঞ।
প্রেক্ষাপট –
1905 খ্রিস্টাব্দের স্বদেশি আন্দালনের উন্মাদনার দিনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কন করেন বঙ্গমাতার ছবি। পরে ভগিনি নিবেদিতা এর নাম দেন ‘ভারতমাতা’।
চিত্রবর্ণনা –
গৈরিক বস্ত্রে মণ্ডিতা এই মাতৃমূর্তি চতুর্ভুজা। তার চার হাতের এক-একটিতে ধরা আছে ধানের শিষ, শ্বেতবস্ত্র, পুস্তক এবং জপের মালা অর্থাৎ সন্তানের প্রতি মায়ের দান অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা ও দীক্ষা। ভারতমাতা যেন পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে, পশ্চাৎপটে সোনালি-হলুদ রঙের মোলায়েম কিন্তু দীপ্ত আবরন। মাথার পিছনে বৌদ্ধিক জ্যোতির্বলয়, রবিরশ্মির মতো উজ্জ্বল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পা দুখানি উজ্জ্বলতাবহ, পদপ্রান্তে প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্ম।
জাতীয়তাবোধের জাগরণ –
অবনীন্দ্রনাথের ‘ভারতমাতা’ নয়া জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হয়, দেশবাসী মাতৃমূর্তি পায়। স্বদেশি বাংলায় এই ছবি নিয়ে শোভাযাত্রা বের হত। এই চিত্রের মধ্য দিয়ে শান্তি, অভয় ও সমৃদ্ধিদানকারী মাতৃদেবীর রূপকে কল্পনা করা হয়েছে। ভারতমাতা এখানে একাধারে মানবী ও দেবী রূপে কল্পিত হয়েছেন।
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র –
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র সংকলনগুলির মধ্যে ‘বিরূপ বজ্র’, ‘নয়া হুল্লোড়’ ও ‘অদ্ভুত লোক’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আঁকা ব্যঙ্গচিত্রগুলির মধ্যে ‘জাতাসুর’, ‘পরভূতের কাকলি’, ‘বিদ্যার কারখানা’, ‘বাক্যন্ত্র’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।.
উচ্চবর্ণের সমালোচনা –
শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ‘জাতাসুর’ চিত্রে সমাজপতিদের দ্বারা নিম্নবর্ণের নিষ্পেষণের বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। চিত্রটিতে দেখা যায়, একটি বিরাট আকারের জাতার ওপর বসে হোম ও পূজা-আহ্নিক করছেন মুণ্ডিত মস্তক বিশিষ্ট এক ব্রাহ্মণ, যার হাতে রয়েছে পুঁথি। জাতাটি ঘোরাচ্ছে হাস্যরত এক নরকঙ্কাল, আর জাতার নীচে পিষ্ট হচ্ছে অসংখ্য নিম্নবর্ণের মানুষ। তাঁর ‘খলব্রাহ্মণ’ চিত্রেও তিনি জাত ব্যবস্থার ভণ্ডামির চিত্র তুলে ধরেছেন।
ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা –
বাঙালি সমাজের ইংরেজ প্রীতি এবং ঔপনিবেশিক শাসনের কঠোর সমালোচনা ধরা পড়েছে তাঁর বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্রে। ‘চোর’ চিত্রে দেখা যায় দশাশয়ী পুলিশ শীত বস্ত্রে সুরক্ষিত, কিন্তু ঠান্ডায় কাঁপছে স্বল্পবাসী দরিদ্র ভারতীয়। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর আঁকা ব্যঙ্গচিত্রেও ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।
মূল্যায়ন –
মধ্য-উনিশ শতকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ব্রিটিশ শাসনের এক অনিচ্ছাকৃত সুফল। ঔপনিবেশিক প্রশাসন সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যে কঠোর দমনমূলক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল, তার অনিবার্য ফলস্বরূপ ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী চেতনা ফুটে বেরোয় সাহিত্য ও চিত্রকলায়।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “আনন্দমঠ” উপন্যাসটি কীভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রভাবিত করেছিল?
“আনন্দমঠ” উপন্যাসে ‘বন্দেমাতরম্’ সঙ্গীত ও সন্তান দলের আদর্শ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের বার্তা ছড়িয়ে দেয়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “গোরা” উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের কী বার্তা রয়েছে?
“গোরা” উপন্যাসে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ঊর্ধ্বে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের ধারণা ফুটে উঠেছে। গোরা চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন।
স্বামী বিবেকানন্দের “বর্তমান ভারত” গ্রন্থে শূদ্রের জাগরণ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?
স্বামীজি বলেছেন যে ইতিহাসে শূদ্র (শ্রমিক শ্রেণি) শাসন আসন্ন এবং এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ভারতমাতা” চিত্রটির তাৎপর্য কী?
এই চিত্রে ভারতকে এক মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে, যিনি অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা প্রদান করেন। এটি স্বদেশি আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে।
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রগুলি কীভাবে ব্রিটিশ শাসন ও সমাজের সমস্যাগুলি তুলে ধরেছে?
তাঁর চিত্রগুলিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী কুসংস্কার ও ব্রিটিশ শোষণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন, “জাতাসুর” চিত্রে উচ্চবর্ণের শোষণ এবং “চোর” চিত্রে ঔপনিবেশিক অত্যাচার ফুটে উঠেছে।
উনিশ শতকে সাহিত্য ও শিল্প কীভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রভাবিত করেছিল?
সাহিত্য (যেমন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের রচনা) ও শিল্প (অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলা) মানুষের মনে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তুলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছিল।
“বন্দেমাতরম্” সঙ্গীতটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?
এটি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণাদায়ী সঙ্গীত ছিল এবং বিপ্লবীদের মনোবল বৃদ্ধি করেছিল।
স্বদেশি আন্দোলনে শিল্পীদের ভূমিকা কী ছিল?
শিল্পীরা চিত্র, ব্যঙ্গচিত্র ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করে জনগণকে জাগরিত করেছিলেন।
এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “উনিশ শতকে লেখা ও রেখার মাধ্যমে কীভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটেছে? অথবা, উনিশ শতকে রেখায় ও লেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটেছিল – উক্তিটি আনন্দমঠ উপন্যাস এবং ভারতমাতা চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করো।” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই “উনিশ শতকে লেখা ও রেখার মাধ্যমে কীভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটেছে? অথবা, উনিশ শতকে রেখায় ও লেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটেছিল – উক্তিটি আনন্দমঠ উপন্যাস এবং ভারতমাতা চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করো।” প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায় “সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা” -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকলে, আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তাছাড়া, নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।


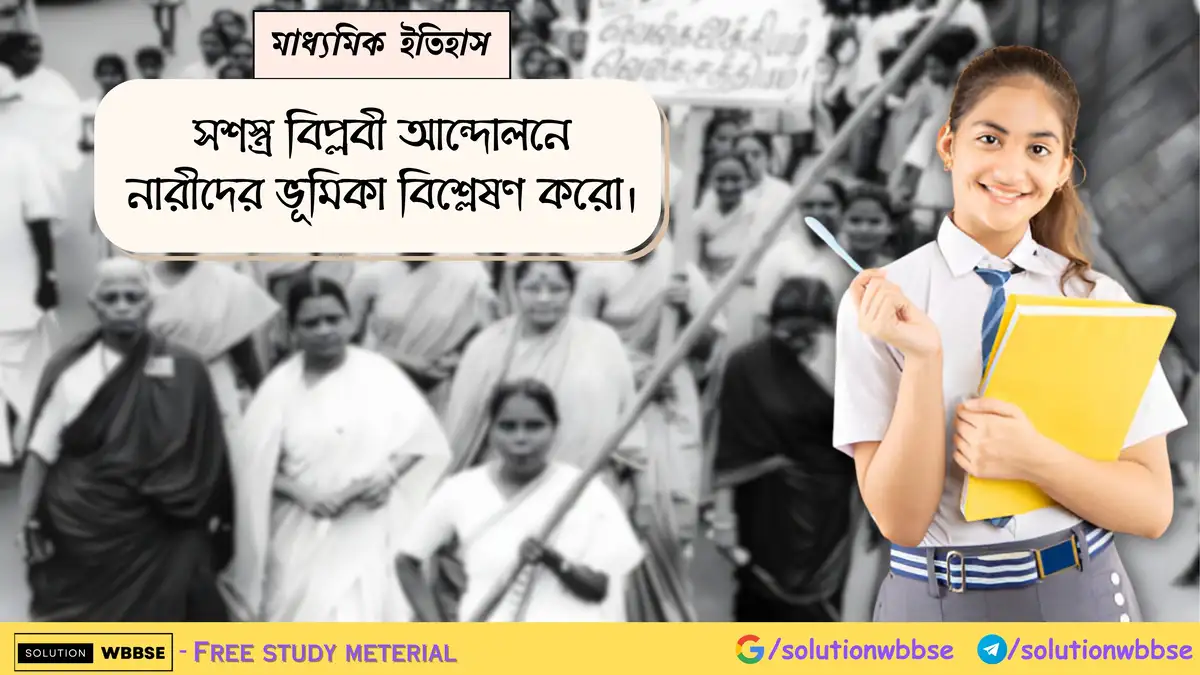
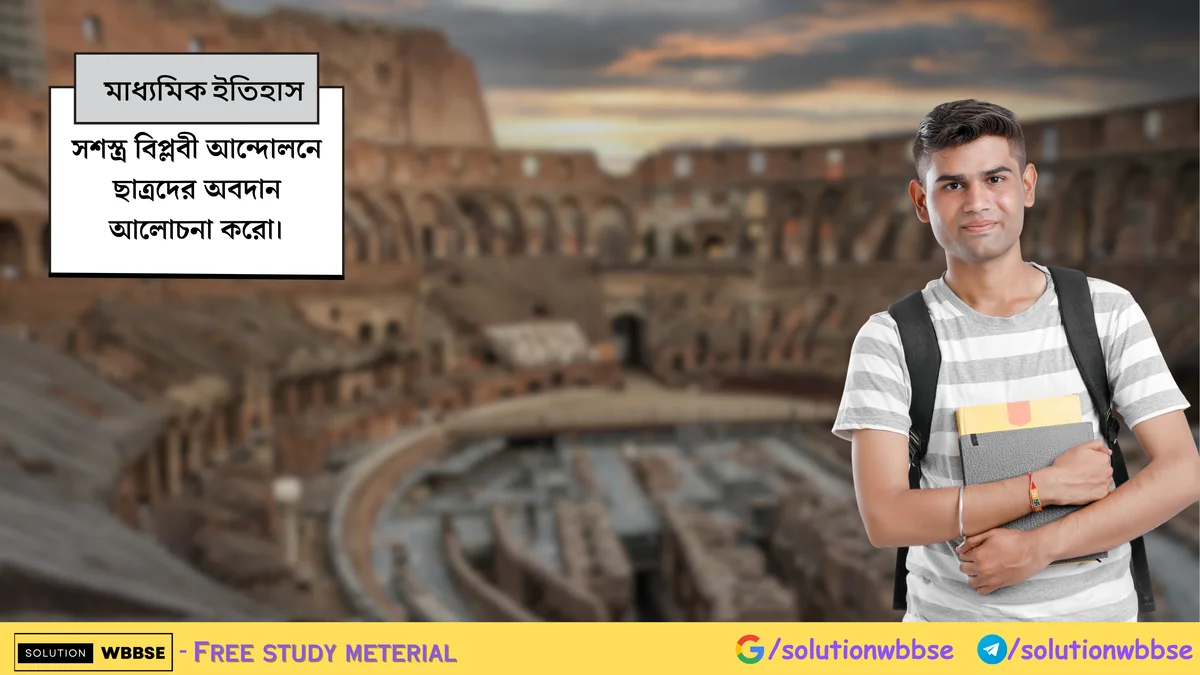
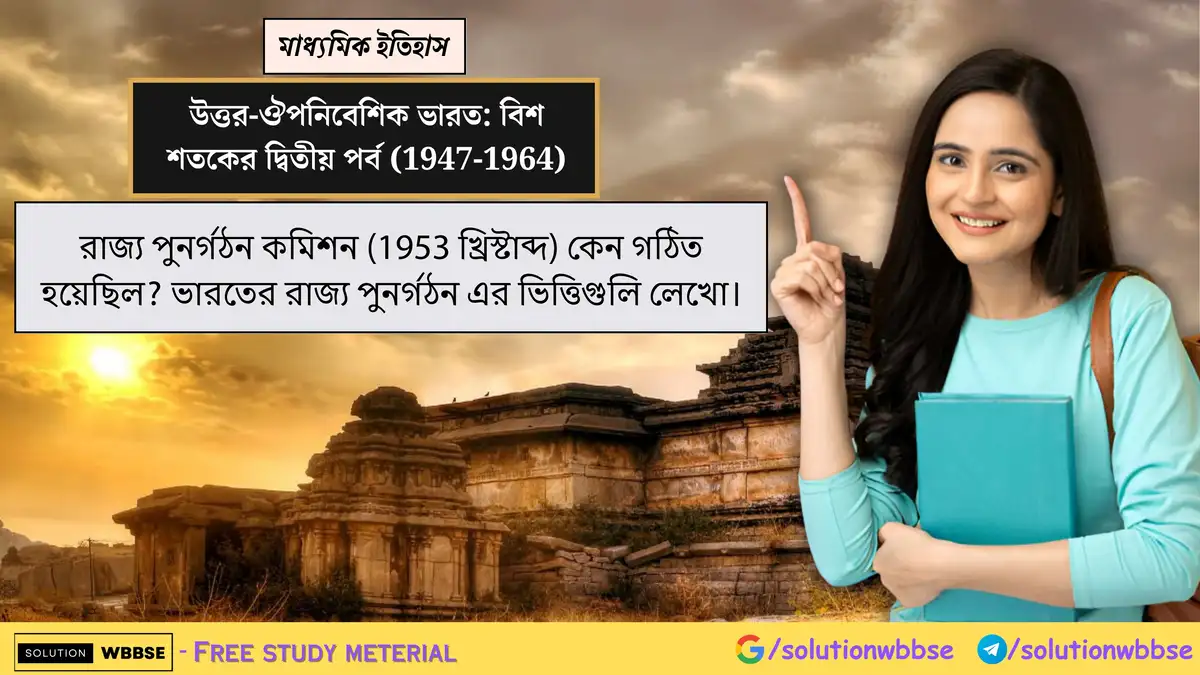

মন্তব্য করুন