এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “বাংলায় নবজাগরণের প্রকৃতি আলোচনা করো। এর সীমাবদ্ধতা কী ছিল?” নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাস পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই “বাংলায় নবজাগরণের প্রকৃতি আলোচনা করো। এর সীমাবদ্ধতা কী ছিল?“ প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় “সংস্কার – বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা“ -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়।
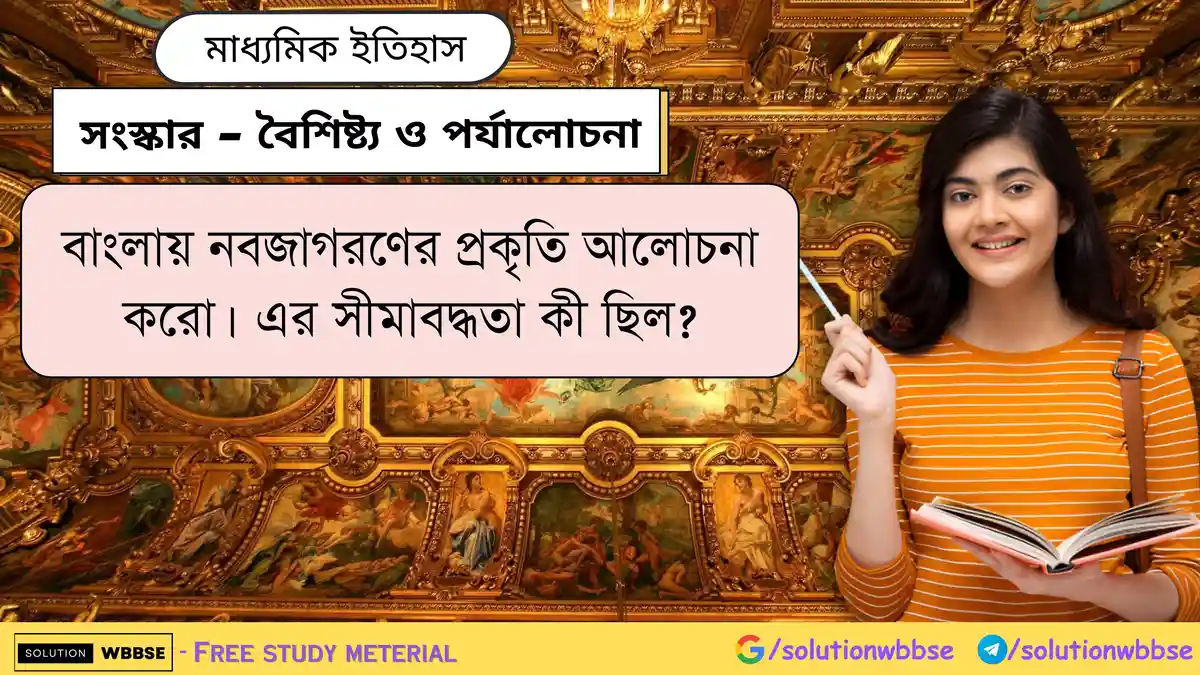
বাংলায় নবজাগরণের প্রকৃতি আলোচনা করো।
পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে এক যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী আলোড়ন দেখা যায়। তৎকালীন ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা-সাহিত্য-দর্শন-জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর সুগভীর প্রভাব অনুভূত হয়। পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের ইটালির নবজাগরণের সঙ্গে তুলনা টেনে অনেকেই উনিশ শতকের বাংলার এই জাগরণকে ‘বঙ্গীয় নবজাগরণ’ আখ্যা দিয়েছেন। তবে উনিশ শতকের এই জাগরণ, তার স্বরূপ, প্রকৃতি, সীমাবদ্ধতা, গুরুত্ব এমনকি এই জাগরণকে আদৌ ‘নবজাগরণ’ বা ‘রেনেসাঁ’ বলা যায় কিনা এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই।
নবজাগরণ -এর বাস্তবতা নিয়ে বিতর্ক
- পক্ষে মত – আচার্য যদুনাথ সরকার অতি সুস্পষ্ট ভাষায় এবং দ্বিধাহীনভাবে বাংলার এই জাগরণকে ‘নবজাগরণ’ বা ‘রেনেসাঁ’ আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ‘কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপে যে রেনেসাঁ দেখা দেয়, উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ছিল তদুপেক্ষা ব্যাপক, গভীর এবং অধিকতর বৈপ্লবিক। এই নবজাগরণ ছিল প্রকৃত একটি রেনেসাঁ।
- বিপক্ষে মত – অপরদিকে, ড. বিনয় ঘোষ, অশোক মিত্র, ড. বরুণ দে, ড. সুমিত সরকার প্রমুখ এই নবজাগরণকে ‘অতিকথা’ বা ‘মিথ’ এবং ‘ঐতিহাসিক প্রতারনা’ বলে অভিহিত করেছেন।
নবজাগরণের স্রষ্টা সংক্রান্ত বিতর্ক
নবজাগরণের স্রষ্টা কারা এই নিয়ে উঠে এসেছে নানান পরস্পর বিরোধী মন্তব্য –
- অনেকেই এই ব্যাপারে রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা ডিরোজিওর মতো ব্যক্তিবর্গকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন।
- মার্কিন গবেষক ডেভিড কফ্ বঙ্গীয় নবজাগরণের ব্যাপারে ভারতীয় মনীষীদের কোনো কৃতিত্ব দিতে রাজি নন। তাঁর মতে, ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ আসলে ব্রিটিশ প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ।
- মার্কিন ঐতিহাসিক ব্লুমফিল্ড বলেন যে, এই আন্দোলন ছিল ‘নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইংরেজ-সৃষ্ট তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণির আন্দোলন। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।’
- ড. সুমিত সরকারের মতে, বাংলার জাগরণ ইংরেজদের ‘নকলনবিশি’ ছাড়া কিছুই নয়। ড. বরুন দে-ও অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় এই জাগরণ গড়ে উঠেছিল।
ইটালির নবজাগরণের সঙ্গে তুলনা –
সাদৃশ্য –
- অন্ধকারের অবসান – ইটালির নবজাগরণ যেমন মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, জড়তা, অন্ধকার থেকে ইওরোপকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল বঙ্গীয় নবজাগরণও তেমনি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধকার থেকে ভারতকে তুলে আনে আধুনিকতার স্বর্ণদ্বীপ্ত ঊষার দ্বারপ্রান্তে।
- প্রেরণার উৎস – ইটালির নবজাগরণের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য। অনুরূপভাবে, বঙ্গীয় নবজাগরণ তার প্রেরণা পেয়েছিল প্রাচীন সংস্কৃত, মধ্যযুগীয় ফারসি ও আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য থেকে।
- যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী মানসিকতা – ইটালির নবজাগরণের যে স্বাধীন, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী ও অনুসন্ধানী মানসিকতা লক্ষ করা যায়, সেই মানসিকতা বাংলার নবজাগরণেও পরিলক্ষিত হয়।
- সাহিত্যে অগ্রগতি – ইটালির নবজাগরণে যেমন কথ্যভাষায় সাহিত্যের প্রসার ঘটে, বঙ্গীয় নবজাগরণেও তেমনি বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে।
বৈসাদৃশ্য –
- প্রেক্ষাপট – ড. অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন যে, ইটালির নবজাগরণ ও বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইওরোপের বাণিজ্য-বিপ্লব, নগর-বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনা ইটালির নবজাগরণের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। কিন্তু বাংলার নবজাগরণে এরূপ প্রেক্ষাপট অনুপস্থিত ছিল বলে তিনি মনে করেন।
- গতিবেগ – ইতালিয় তথা ইউরোপীয় নবজাগরণের যে প্রবল গতিবেগ, উদ্যম ও বহুমুখী সৃজনশীলতা লক্ষ করা যায়, সেই গতি, উদ্যম ও বহুমুখী সৃজনশীলতা বঙ্গীয় নবজাগরণে অনেকক্ষেত্রেই অনুপস্থিত ছিল।
- পরিবেশ – ফ্লোরেন্স নগরীকে কেন্দ্র করে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে ইটালির নবজাগরণ বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রিক বঙ্গীয় নবজাগরণের সময় কলকাতা তথা ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশের অধীন।
- ব্যাপকতা – ইটালির নবজাগরণ ছিল সার্বিক ও ব্যাপক। কিন্তু বঙ্গীয় নবজাগরণ ছিল ‘সীমাবদ্ধ’। এই নবজাগরণ কেবলমাত্র সমাজের উচ্চশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু সমাজের বৃহত্তর নিম্নবর্ণের মানুষ, কৃষক সমাজ বা মুসলিম সমাজের সঙ্গে নবজাগরণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ড. অনীল শীল তাই একে ‘এলিটিস্ট মুভমেন্ট’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
বাংলায় নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা কী ছিল?
ঐতিহাসিকদের একাংশ উনিশ শতকে বাংলার বৌদ্ধিক অগ্রগতিকে ‘নবজাগরণ’ বলে আখ্যায়িত করলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় –
বঙ্গীয় নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা –
শহুরে নবজাগরণ –
বাংলার নবজাগরণের ব্যাপ্তি ছিল খুবই সীমিত। তা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক, বিশেষত কলকাতা কেন্দ্রিক। গ্রাম বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নবজাগরণের কোনো সুফল পায়নি।
এলিটিস্ট মুভমেন্ট –
বঙ্গীয় নবজাগরণ কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার এই নবজাগরণের সঙ্গে গ্রাম-গঞ্জের হাজার হাজার দরিদ্র মেহনতী মানুষের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল না। এইজন্য অধ্যাপক অনীল শীল একে ‘এলিটিস্ট মুভমেন্ট’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
ব্রিটিশ নির্ভরতা –
বাংলার এই জাগরণ অতিমাত্রায় ব্রিটিশ নির্ভর হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নবজাগরণের নেতৃবৃন্দ মনে করতেন, ব্রিটিশ শাসনের দ্বারাই ভারতীয় সমাজের মঙ্গল সাধিত হবে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন – ‘ইংরেজদের দেওয়া সবচেয়ে বড়ো উপহার হল আমাদের উনিশ শতকের নবজাগরণ।’
হিন্দু জাগরণ –
বাংলার নবজাগরণ প্রকৃতপক্ষে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদে পর্যবসিত হয়েছিল। রাধাকান্ত দেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের কার্যকলাপে হিন্দু পুনর্জাগরণের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।
শ্লথগতি –
ইটালির নবজাগরণের গতিবেগ, উদ্যম ও বহুমুখী সৃজনশীলতা বঙ্গীয় নবজাগরণে বহুক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।
মূল্যায়ন –
পরাধীন দেশে, ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে বঙ্গীয় নবজাগরণ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারেনি-সত্য। তবুও পরিশেষে এর গতিশীলতা, সৃজনশীলতা ও ঐতিহাসিকতাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।
এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “বাংলায় নবজাগরণের প্রকৃতি আলোচনা করো। এর সীমাবদ্ধতা কী ছিল?” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই “বাংলায় নবজাগরণের প্রকৃতি আলোচনা করো। এর সীমাবদ্ধতা কী ছিল?” প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় “সংস্কার – বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা” -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকলে, আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করুন।


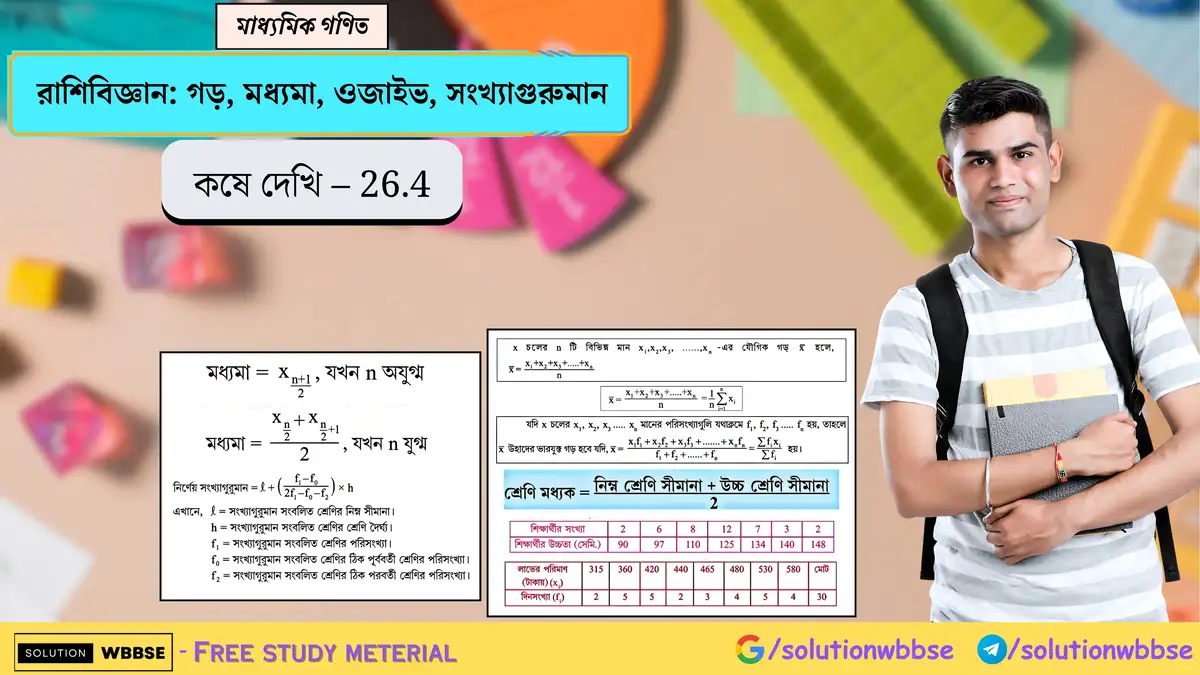
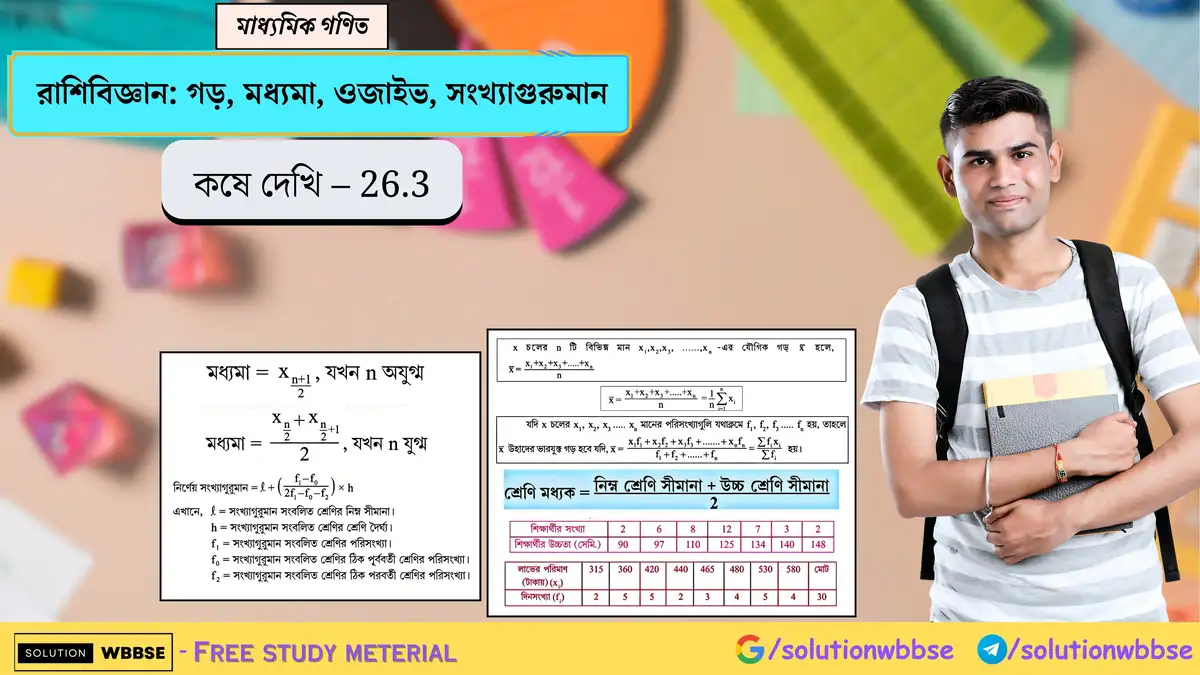
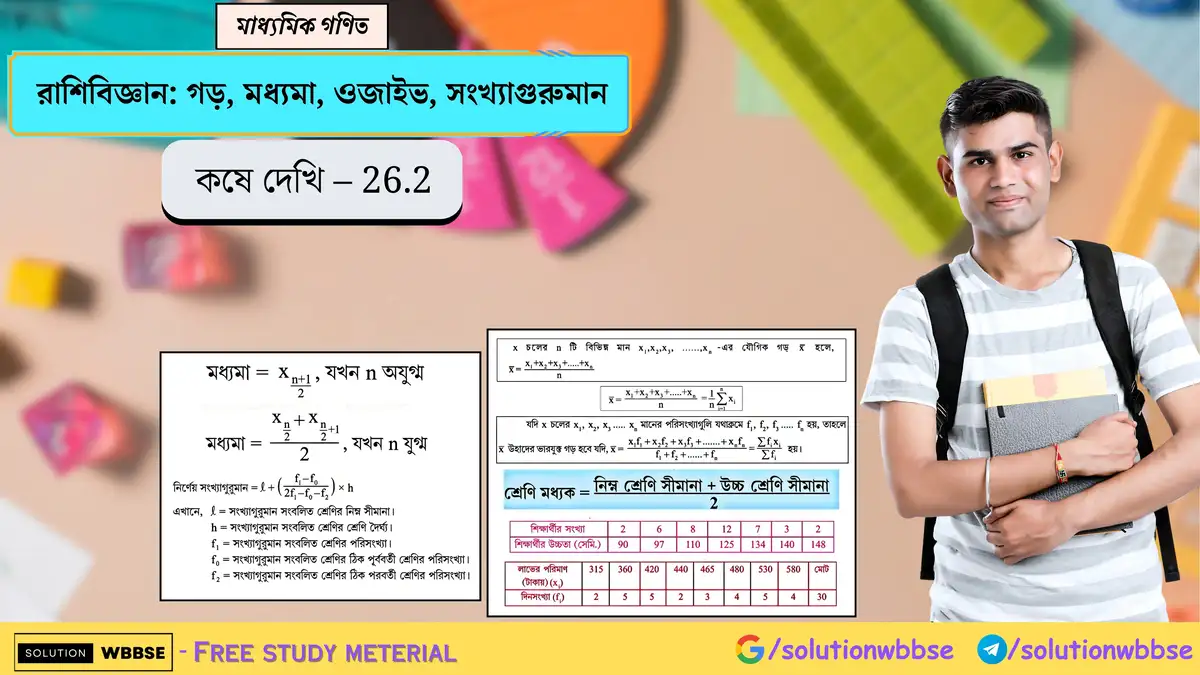

মন্তব্য করুন