এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “ভারতে ‘সভা-সমিতির যুগ’ -এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।” নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাস পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই “ভারতে ‘সভা-সমিতির যুগ’ -এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।“ প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায় “সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা“ -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়।
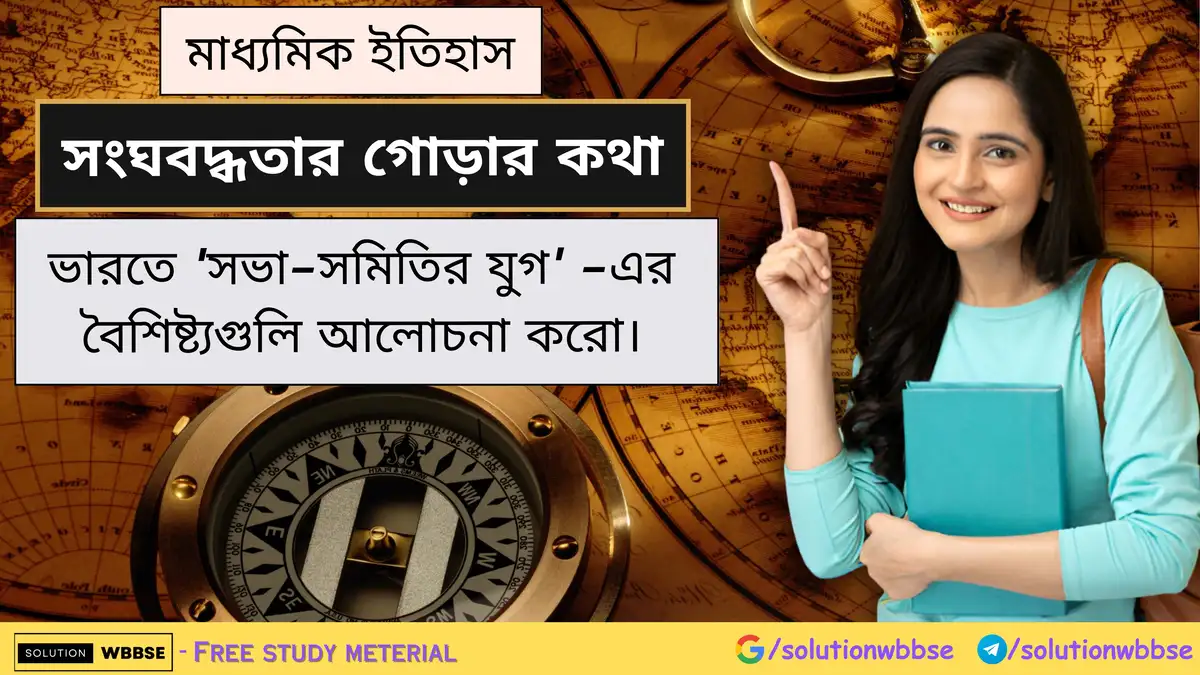
ভারতে ‘সভা-সমিতির যুগ’ -এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের সঙ্গে ভারতীয়রা উপলব্ধি করে যে, দেশের স্বার্থরক্ষার্থে তথা সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকেই উনিশ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য রাজনৈতিক সভা-সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। এইজন্য অধ্যাপক অনীল শীল উনিশ শতককে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন।
সভা-সমিতির যুগের বৈশিষ্ট্য
ইতিহাসসূত্র পর্যালোচনায় সভা-সমিতি যুগের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে –
বাংলায় প্রাথমিক বিকাশ –
ঔপনিবেশিক শাসনকালে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলির অধিকাংশ প্রাথমিক পর্বে বাংলাতেই বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলার অনুকরণে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতির আবির্ভাব লক্ষ করা যায়।
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব –
ইতিহাসের এই পর্বে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলির নেতৃত্ব মূলত ছিল ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের হাতে। সাধারণ সদস্যদের অধিকাংশও ছিলেন এই শ্রেণিভুক্ত। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ, এমনকি মুসলিম সমাজের সঙ্গে এই সভা-সমিতিগুলির সংযোগ ছিল অতি ক্ষীণ।
আঞ্চলিকতা –
ইতিহাসের এই পর্বে আবির্ভূত রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলির সবকটিই ছিল আঞ্চলিক এবং পেশাজীবি মানুষদের সংগঠন। উদাহরণস্বরূপ – বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, জমিদার সভা বা মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের নাম করা যেতে পারে। সভা-সমিতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে।
নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলনে বিশ্বাস –
প্রাথমিক পর্বের এই সকল রাজনৈতিক সভা-সমিতিগুলি সক্রিয় গণআন্দোলন অপেক্ষা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায়ে বেশি বিশ্বাসী ছিল। আবেদনপত্র প্রেরণ, স্মারকলিপি পেশ, পত্র-পত্রিকায় লেখনী ধারণ প্রভৃতির মধ্যেই এদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল।
ব্রিটিশ সুশাসনের প্রতি আস্থা –
সভা-সমিতিগুলির প্রায় কোনোটিই ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত ‘স্বরাজ’ বা ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’র দাবী উত্থাপন করেনি। ব্রিটিশের সভ্যতা, সংস্কৃতি তথা সুশাসনের প্রতি এগুলির নেতৃবৃন্দের ছিল সীমাহীন আস্থা ও শ্রদ্ধা। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশের অধীনেই ভারতবাসীর মঙ্গল সাধিত হবে। তাই পূর্ণ স্বাধীনতা অপেক্ষা ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অধীনে সীমিত স্বায়ত্তশাসন লাভই ছিল তাদের লক্ষ।
সভা-সমিতির যুগের মন্তব্য –
বস্তুতপক্ষে, তখন ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা যে স্তরে ছিল, তাতে প্রাথমিক পর্বে গড়ে ওঠা এই সভা-সমিতিগুলির সাফল্য সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। তথাপি জাতীয়তাবোধের জাগরণে এবং স্বাদেশিকতার উজ্জীবনে এগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর
সভা-সমিতির যুগ বলতে কী বোঝায়?
উনিশ শতকে ভারতীয়রা জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এই সময়কালকে ঐতিহাসিকরা ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলে চিহ্নিত করেছেন।
সভা-সমিতিগুলির প্রাথমিক বিকাশ কোথায় হয়েছিল?
এগুলির বেশিরভাগই বাংলায় প্রথম গড়ে ওঠে, যেমন – জমিদার সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা ইত্যাদি। পরে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।
ভারতে সভা-সমিতিগুলির নেতৃত্বে কারা ছিলেন?
প্রধানত ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় নেতৃত্ব দিতেন। মুসলিম সমাজ বা সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম।
সভা-সমিতিগুলির লক্ষ্য কী ছিল?
সভা-সমিতিগুলির মূল লক্ষ্য ছিল –
1. ব্রিটিশ শাসনে সুশাসন ও সংস্কার চাওয়া।
2. নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি (আবেদন, স্মারকলিপি) দিয়ে দাবি আদায়।
3. পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, বরং ব্রিটিশ শাসনের অধীনে অধিকারের দাবি করা।
ভারতে সভা-সমিতি সংগঠনগুলির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
এগুলি মূলত আঞ্চলিক ও পেশাজীবী মানুষদের সংগঠন ছিল, যেমন – মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন। এগুলির মধ্যে জাতীয় স্তরে কোনো সংযোগ ছিল না।
সভা-সমিতিগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি কী ছিল?
সভা-সমিতিগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি ছিল –
1. সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ কম ছিল।
2. কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থ তুলে ধরা হতো।
3. সশস্ত্র সংগ্রাম বা গণআন্দোলনের পরিবর্তে শুধু আবেদন-নিবেদনের উপর নির্ভরশীল ছিল।
সভা-সমিতি যুগের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?
যদিও এগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা চায়নি, তবুও –
1. জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ভূমিকা রাখে।
2. পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস -এর জন্মের পথ সুগম করে।
অধ্যাপক অনীল শীল কেন এই সময়কে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলেছেন?
কারণ এই সময়ে অসংখ্য রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, যা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে কাজ করেছিল।
সভা-সমিতি যুগের কিছু উল্লেখযোগ্য সংগঠনের নাম লেখো।
সভা-সমিতি যুগের কিছু উল্লেখযোগ্য সংগঠনের নাম হল – জমিদার সভা (1838), বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (1836), মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন (1852), বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন (1852)।
সভা-সমিতি যুগের সংগঠনগুলি কি ব্রিটিশবিরোধী ছিল?
তারা ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করলেও ব্রিটিশ সুশাসনে বিশ্বাস করত। তারা চেয়েছিল ব্রিটিশরাই ভারতের উন্নতি করবে, তাই পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের লক্ষ্য ছিল না।
এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “ভারতে ‘সভা-সমিতির যুগ’ -এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই “ভারতে ‘সভা-সমিতির যুগ’ -এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।” প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায় “সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা” -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকলে, আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তাছাড়া, নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।


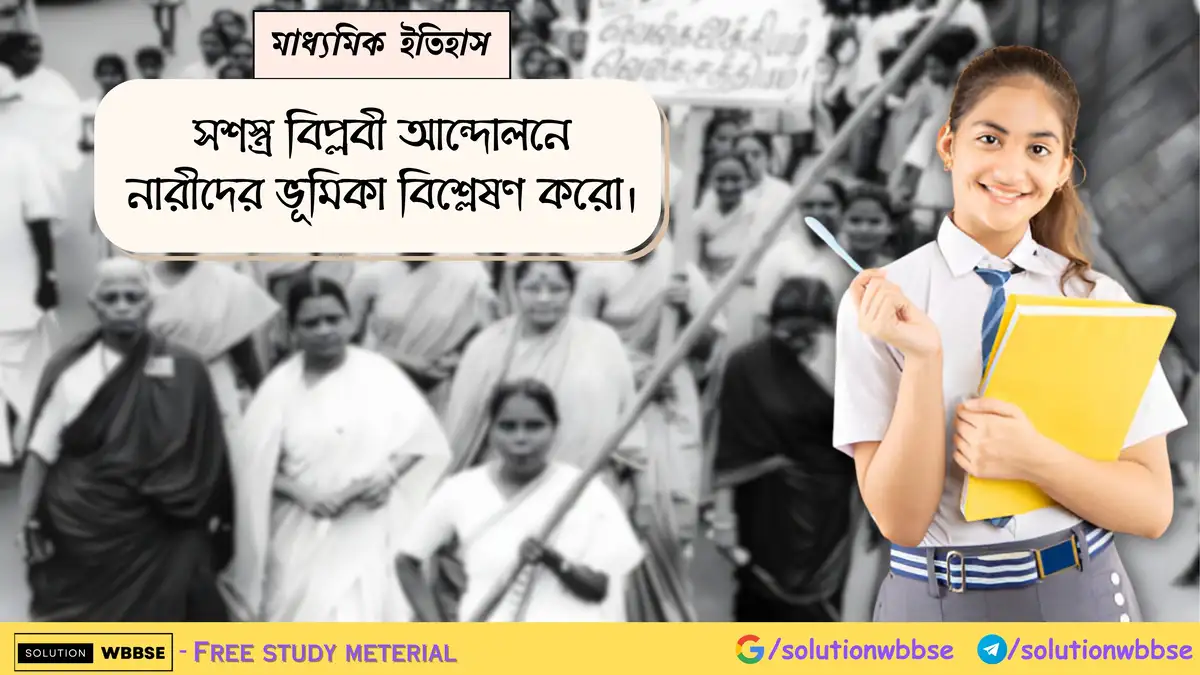
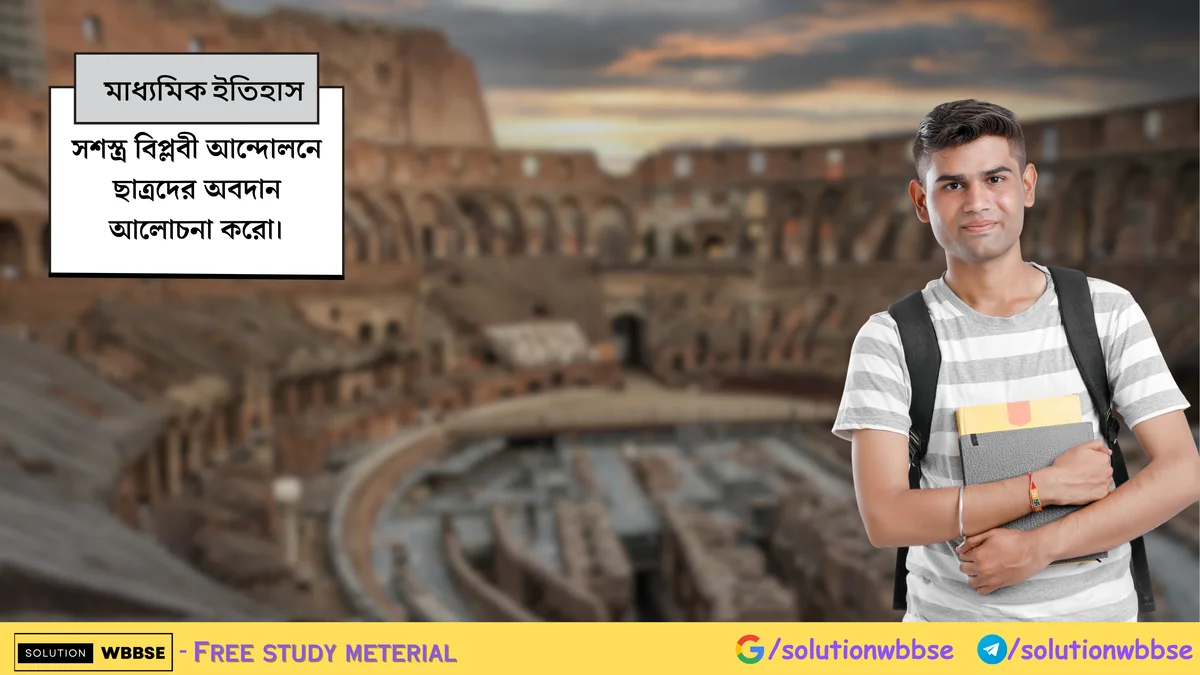
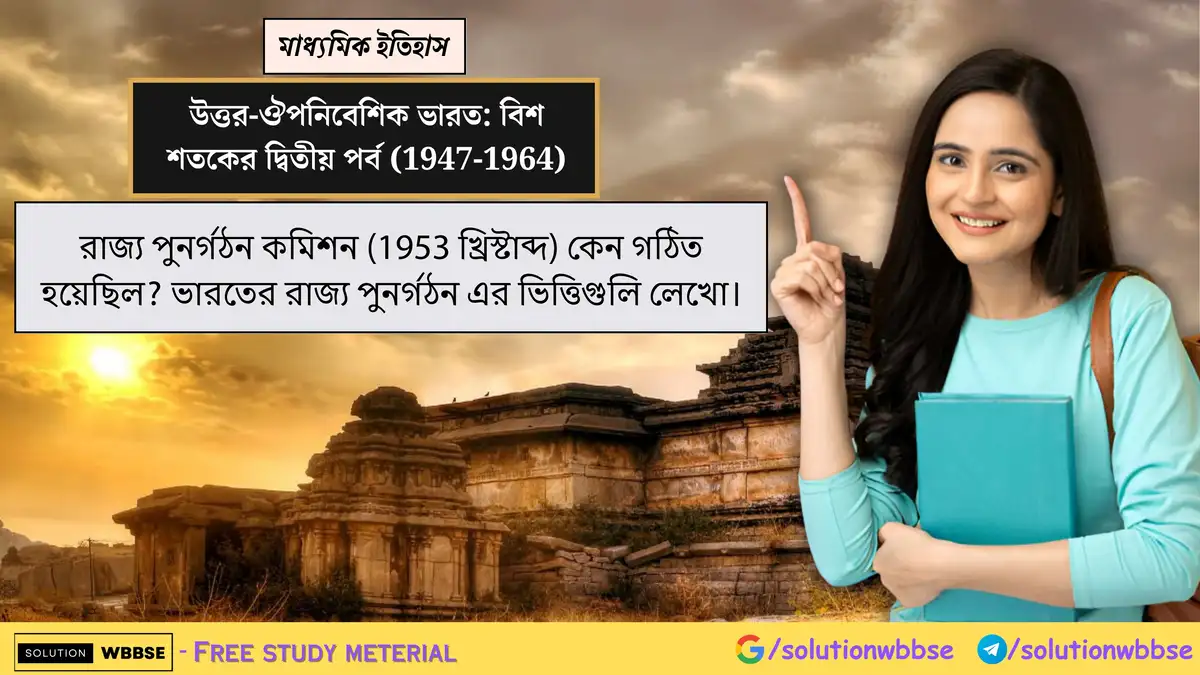

মন্তব্য করুন