আজকের আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক বাংলার চতুর্থ পাঠের প্রথম বিভাগ, ‘বহুরূপী,’ এর বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই পরীক্ষায় দেখা যায়। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য উপকারী হবে।
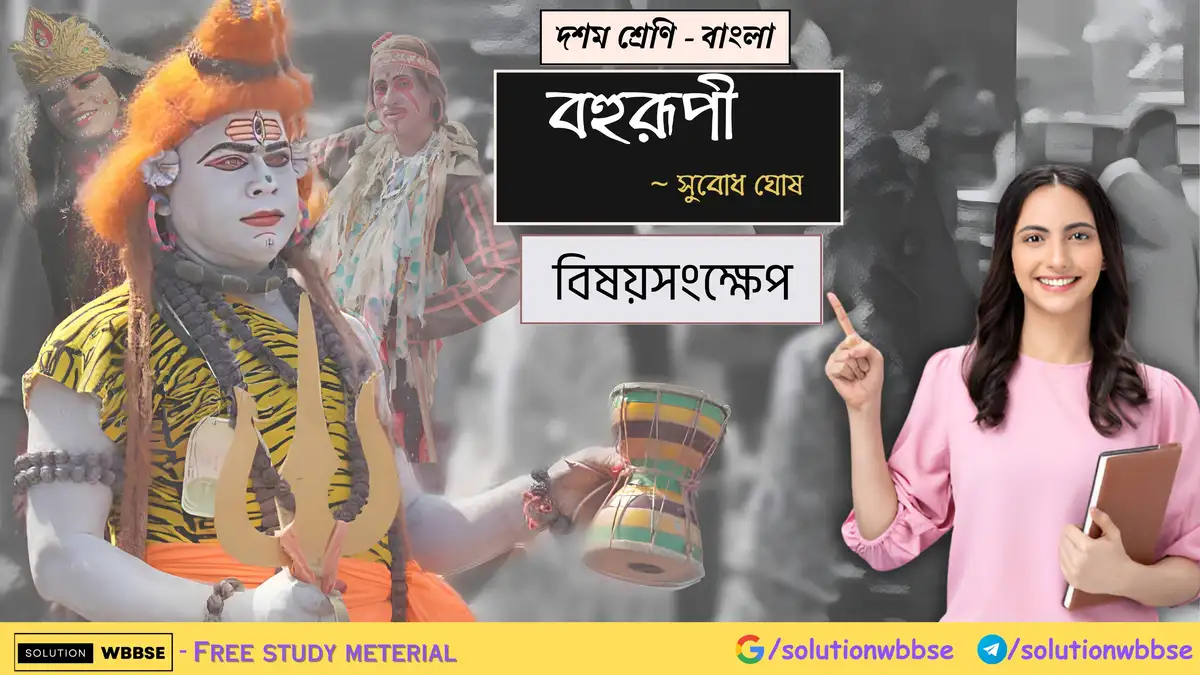
সুবোধ ঘোষের লেখক পরিচিতি
সুবোধ ঘোষের ভূমিকা –
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ এক স্মরণীয় নাম। সাহিত্যজগতে তাঁর প্রবেশ ঘটে কিছুটা দেরিতে হলেও, তিনি তাঁর মেধা, চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে বিভিন্ন কালজয়ী রচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন।
সুবোধ ঘোষের জন্ম ও শৈশব –
বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ 1909 সালের 14 সেপ্টেম্বর বিহারের হাজারিবাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি বাড়ি ছিল বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বহর গ্রামে।
সুবোধ ঘোষের শিক্ষাজীবন –
সুবোধ ঘোষ হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিশিষ্ট দার্শনিক ও গবেষক মহেশ ঘোষের লাইব্রেরিতে তিনি পড়াশোনা করতেন। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব এবং সামরিক বিদ্যায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল।
সুবোধ ঘোষের কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবন –
সুবোধ ঘোষের কর্মজীবন শুরু হয় বিহারের আদিবাসী অঞ্চলে বাসের কনডাক্টর হিসেবে। এরপর সার্কাসের ক্লাউন, মুম্বাই পৌরসভার চতুর্থ শ্রেণির কাজ, চায়ের ব্যাবসা, বেকারির ব্যাবসা, মালগুদামের স্টোরকিপার প্রভৃতি কাজে তিনি তাঁর জীবনের বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করেন। বহু পথ ঘুরে তিরিশের দশকের শেষে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে সহকারী হিসেবে যোগ দেন। তাঁর লেখালেখির সময়কাল 1940 থেকে 1980 খ্রিস্টাব্দ। 1946 খ্রিস্টাব্দের 16 আগস্ট দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে গান্ধিজির সহচর হিসেবে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। দাঙ্গা এবং দাঙ্গা-পরবর্তী সময়ের সাম্প্রদায়িকতা, হিংস্রতা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। সুবোধ ঘোষের প্রথম গল্প ‘অযান্ত্রিক’। তাঁর আর-একটি বিখ্যাত গল্প ‘থির বিজুরি’। শুধু গল্পকার হিসেবে নয়, ঔপন্যাসিক হিসেবেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখা একটি অন্যতম উপন্যাস হল তিলাঞ্জলি (1944 খ্রিস্টাব্দ)। কংগ্রেস সাহিত্যসংঘের মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর এই উপন্যাসে।
বিচিত্র জীবিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর কর্মজীবন। আনন্দবাজার পত্রিকা-র সহকারী হিসেবে তিনি যোগ দেন। ক্রমে সেখানকার সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর এবং তারপর অন্যতম সম্পাদকীয় লেখক হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল – ‘ভারত প্রেমকথা’ (মহাভারতের গল্প অবলম্বনে রচিত), ‘গঙ্গোত্রী’ (1947 খ্রিস্টাব্দ), ‘ত্রিযামা’ (1950 খ্রিস্টাব্দ), ‘ভালবাসার গল্প’, ‘শতকিয়া’ (1958 খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি। এ ছাড়াও তাঁর কয়েকটি গল্পসংকলন হল – ‘ফসিল’, ‘পরশুরামের কুঠার’, ‘জতুগৃহ’।
সুবোধ ঘোষের পুরস্কার –
সুবোধ ঘোষ তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য আনন্দ পুরস্কার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন।
সুবোধ ঘোষের জীবনাবসান –
1980 সালের 10 মার্চ এই বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক প্রয়াত হন।
‘বহুরূপী’ গল্পের উৎস
সুবোধ ঘোষের গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড থেকে ‘বহুরূপী‘ গল্পটি নেওয়া হয়েছে।
‘বহুরূপী’ গল্পের বিষয়সংক্ষেপ
বহুরূপী গল্পটি মূলত এক বহুরূপীর জীবন নিয়ে লেখা হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদা শহরের সবচেয়ে ছোটো গলির মধ্যেই বাস করতেন। সেখানে নিয়মিত আড্ডাও বসত। রোজকার চাকরি করতে যাওয়া হরিদার কখনই পোষাত না। তিনি ছিলেন এক বহুরূপী। মাঝেমধ্যে তিনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতেন — কখনও পাগল, কখনও বাউল, কখনও কাপালিক, আবার কখনও বোঁচকা কাঁধে বুড়ো কাবুলিওয়ালা, আবার কখনও পুলিশ। তাঁর এইসব রূপ দেখে অনেকে কিছু পয়সা দিতেন, যা ছিল তাঁর রোজগারের একটি উপায়। পুলিশ সেজে তিনি কখনও ঘুষও নিয়েছেন। তাঁর এইসব রূপ দেখে লোকজন কখনও বিরক্ত হতো, আবার কেউ কেউ আনন্দিত হতো, কেউ বিস্মিত হতো। বহুরূপী সেজে তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন। জগদীশবাবুর বাড়িতে হিমালয়ের গুহানিবাসী এক সন্ন্যাসীর আগমন এবং অভ্যর্থনার কথা শুনে মোটা রকমের উপার্জনের আশায় তিনি সন্ন্যাসী সেজে জগদীশবাবুর বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সৌম্য, শান্ত, জ্ঞানী মানুষ জগদীশবাবু। সাদা উত্তরীয় এবং ছোটো বহরের থান পরে এক বিরাগী মানুষের বেশ ধরে বহুরূপী হরিদা হাজির হন জগদীশবাবুর বাড়িতে। তাঁর সাজপোশাক, উদাত্ত শান্ত দৃষ্টি দেখে কেউ বুঝতেও পারেনি যে তিনি আসলে হরিদা। যেই রূপই তিনি ধারণ করতেন, সেই রূপের সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে যেতেন যে তাঁকে বহুরূপী বলে কেউ চিনতে পারত না। মনে হতো তিনি যেন সত্যিই সেই চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। এখানেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। হরিদা সত্যিই যেন বিরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তখন ধন, যৌবন, সংসার—সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাই জগদীশবাবু তাঁকে তীর্থভ্রমণের জন্য টাকা দিতে চাইলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। আসলে, এইভাবে তিনি তাঁর বহুরূপী পেশাটাকেই সম্মান দিয়েছিলেন। কারণ এই পেশা ছিল তাঁর ভালোবাসা।
‘বহুরূপী’ গল্পের নামকরণ
যে-কোনো সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই নামকরণ সাধারণত বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক, ভাবকেন্দ্রিক বা ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে থাকে। যে-কোনো সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবও এই নামকরণের মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলা হয়।
শহরের সবচেয়ে সরু গলির ভিতরের ছোট্ট ঘরটাই হরিদার জীবনের একমাত্র আশ্রয়। কোনো ছকে বাঁধা কাজ করতে তাঁর ভালো লাগে না। তবে তাঁর জীবনের নাটকীয় বৈচিত্র্য হলো এই যে, তিনি মাঝে মাঝে বহুরূপী সাজেন। এতে সামান্য কিছু রোজগারও হয় বটে। বহুরূপী সেজে তিনি কখনও বাসস্ট্যান্ডে, কখনও বাজারে, কখনও আবার অন্য উপায়ে তাঁর সাজ দেখিয়ে পয়সা রোজগার করেন। বহুরূপী সাজাটাই তাঁর পেশা। এই পেশাগত বিচারে গল্পের নামকরণ যথাযথ। কিন্তু সুবোধ ঘোষ গল্পের কাহিনিতে একটু বাঁক ফেরালেন জগদীশবাবুর বাড়িতে হরিদাকে এনে। হরিদা চেয়েছিলেন কৃপণ, ধনী জগদীশবাবুর কাছ থেকে বেশি করে টাকা আদায় করবেন। সেইমতো তিনি বিরাগীর বেশে সেজেও ছিলেন ভালো। জগদীশবাবু হরিদাকে বিরাগীর বেশে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। জগদীশবাবু বুঝতেই পারেন না যে, তাঁর বাড়িতে বিরাগীর বেশে আসা লোকটা আসলে একজন বহুরূপী। উপরন্তু, তিনি বিরাগী হরিদাকে একশো এক টাকার একটি থলি দিতে গেলে হরিদা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানান, বিরাগীর কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই। ত্যাগই তাঁর জীবনের ধর্ম। অর্থাৎ, বহুরূপী সাজলেও হরিদা তাঁর চরিত্রের আন্তরিকতা বজায় রেখেছেন। এখানেই হরিদার বহুরূপী পেশা পাঠকদের কাছে গৌরবের হয়ে উঠেছে। তাই বলা যায়, গল্পের নামকরণ কিছুটা বিষয়কেন্দ্রিক হলেও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে গল্পের নামকরণ ‘বহুরূপী’ সার্থক হয়েছে।
আজকে আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক বাংলার চতুর্থ পাঠের প্রথম বিভাগ, ‘বহুরূপী’, এর বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকে, তাহলে আমাকে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি সাহায্য করার চেষ্টা করব। এছাড়াও, এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ!


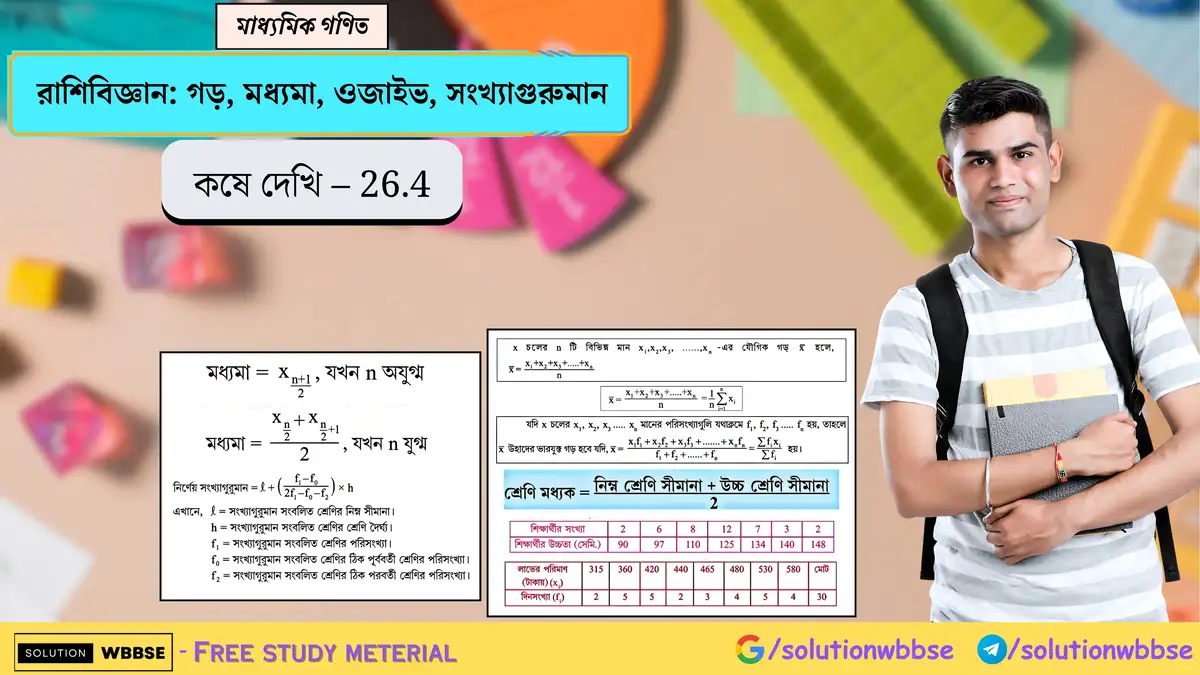
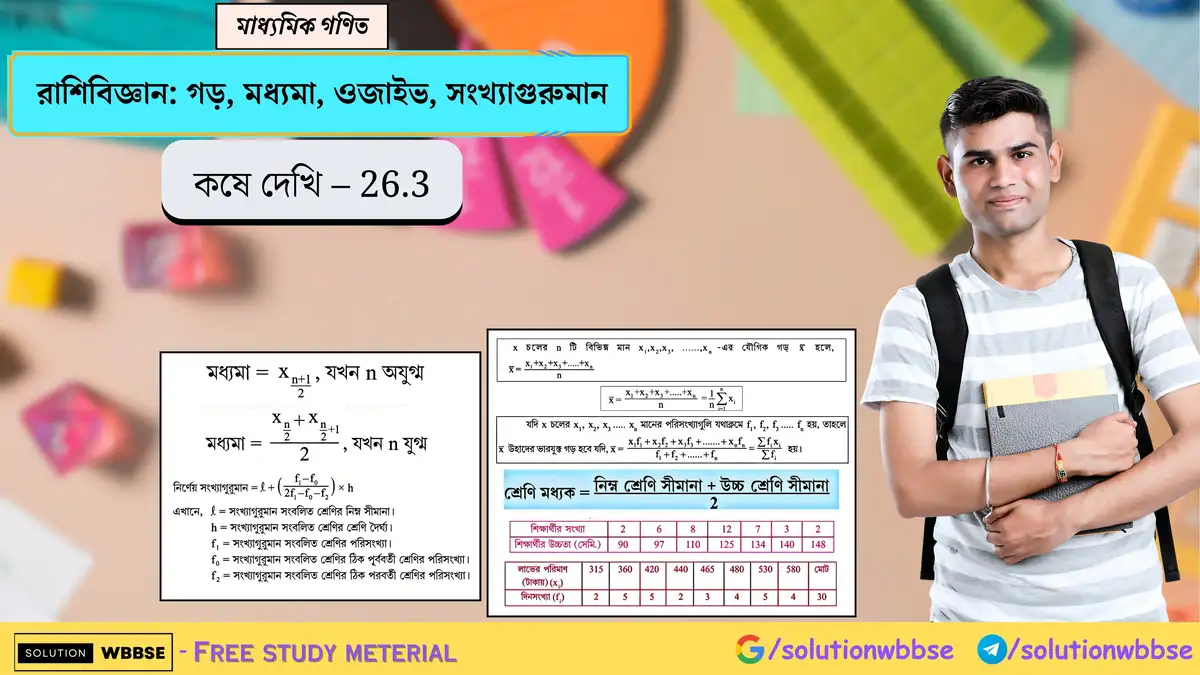
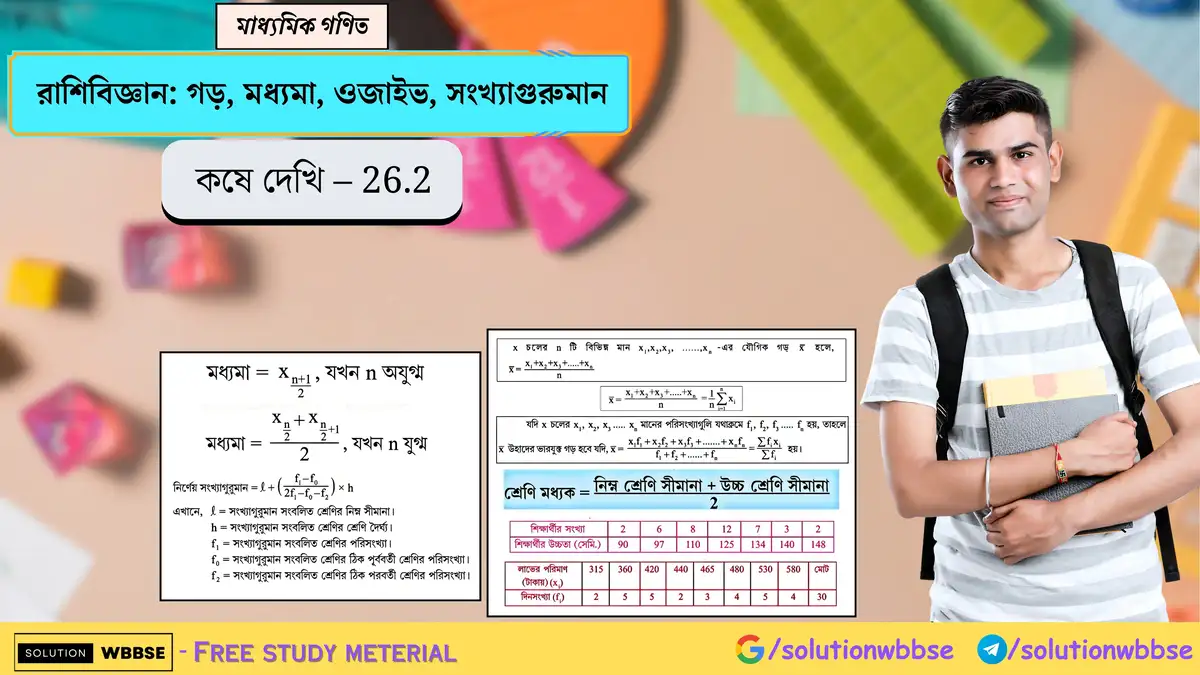

মন্তব্য করুন