আজকের আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যবইয়ের পঞ্চম পাঠের দ্বিতীয় অংশ, ‘সিরাজদ্দৌলা’, এর বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবো। এই অংশ থেকে আসা প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পূর্বে পরীক্ষায় এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই এসেছে। আশা করছি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।
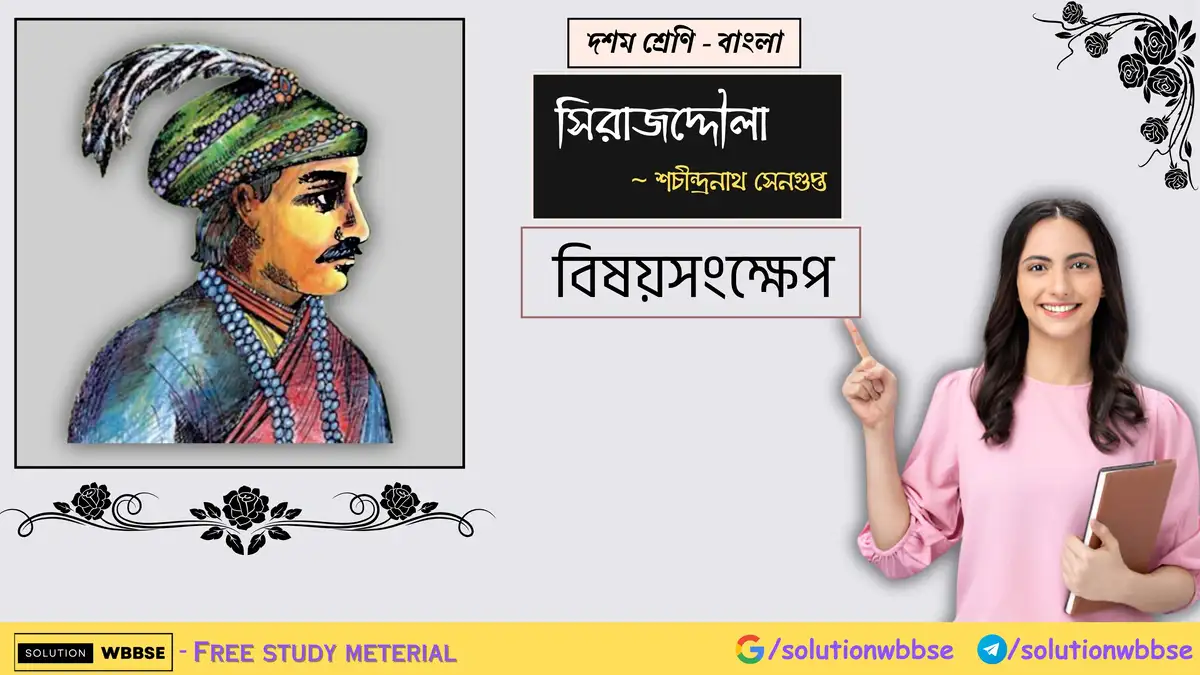
নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত -এর পরিচিতি
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত -এর ভূমিকা –
বিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত -এর শৈশব ও শিক্ষাজীবন –
বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 1892 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে (1299 বঙ্গাব্দের 4 শ্রাবণ) খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সত্যচরণ সেনগুপ্তের কর্মস্থল রংপুরে তিনি শিক্ষালাভ করেন। সেখানে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী ছিলেন তাঁর সহপাঠী। 1905 খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়ে শচীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত কলেজে বিএ পর্যন্ত পড়েন। পরে তিনি কটক মেডিকেল স্কুলে চিকিৎসাবিদ্যা ও ময়মনসিংহে কবিরাজি শেখেন।
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত -এর কর্মজীবন –
কর্মজীবনের শুরুতে শচীন্দ্রনাথ কিছুদিন একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন; পরে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন। তাঁর সাংবাদিকজীবনের শুরু দৈনিক কৃষক ও ভারত পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে। এ ছাড়া তিনি সাপ্তাহিক হিতবাদী বিজলী (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত), আত্মশক্তি প্রভৃতি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। বেসরকারি সাংস্কৃতিক দলের নেতা হিসেবে শচীন্দ্রনাথ রাশিয়া, নরওয়ে, পোল্যান্ড, চিন, সিংহল প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত -এর সাহিত্যজীবন –
শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক রচনার মধ্য দিয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নাটকের মূল বিষয়বস্তু হল দেশাত্মবোধ। সামাজিক নাটক রচনাতেও তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী তাঁর নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নাটকগুলি হল – গৈরিক পতাকা (1930 খ্রিস্টাব্দ), দেশের দাবি (1934 খ্রিস্টাব্দ), রাষ্ট্রবিপ্লব (1944 খ্রিস্টাব্দ), সিরাজদ্দৌলা (1938 খ্রিস্টাব্দ), ধাত্রীপান্না (1948 খ্রিস্টাব্দ), সবার উপরে মানুষ সত্য (1957 খ্রিস্টাব্দ), আর্তনাদ ও জয়নাদ (1961 খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক সিরাজদ্দৌলা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 1946 খ্রিস্টাব্দে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত রাষ্ট্রবিপ্লব নাটকটিও বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। গণনাট্যের আদর্শে বিশ্বাসী এই নাট্যকার তাঁর নাটকের মাধ্যমে পাঠক, দর্শকের মনকে জাগাতে চেয়েছিলেন। বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবেই তিনি নাট্য-আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। নাটককে হাতিয়ার করে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন তিনি। ফলে তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে উঠে এসেছে- কুমারীজীবনে মাতৃত্বের সমস্যা, দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, নারী স্বাধীনতার সুস্পষ্ট রূপ। এ ছাড়াও সমাজজীবনের নানান ভাঙন, ভণ্ড দেশপ্রেম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সার্বিক অবক্ষয় ইত্যাদি দিকগুলিও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। শচীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকগুলি তৎকালীন সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। রক্তকমল (1929 খ্রিস্টাব্দ), ঝড়ের রাতে (1931 খ্রিস্টাব্দ), নার্সিংহোম (1933 খ্রিস্টাব্দ), স্বামী-স্ত্রী (1937 খ্রিস্টাব্দ), তটিনীর বিচার (1939 খ্রিস্টাব্দ), মাটির মায়া, কাঁটা ও কমল, প্রলয়, জননী প্রভৃতি তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক। এসব নাটকেই ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর কিশোরদের জন্য লেখা নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি ও অনুবাদগ্রন্থ আছে।
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত -এর জীবনাবসান –
1961 খ্রিস্টাব্দের 5 মার্চ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জীবনাবসান হয়।
সিরাজদ্দৌলা নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
নবাব অলিবর্দি খাঁ-র কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। সেইজন্য তিনি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের 23 বছরের ছেলে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। এতে সিংহাসনের সম্ভাব্য অন্য দাবিদাররা সিরাজের প্রতি অখুশি হয়ে পড়েন। আলিবর্দির বড়ো মেয়ে মেহেরুন্নিসা, যিনি ঘসেটি বেগম নামেই বেশি পরিচিত, তাঁর বিয়ে হয় ঢাকার শাসনকর্তা নওয়াজিশ মুহম্মদ খান তথা শাহমৎ জঙ্গের সঙ্গে। তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। তখন তাঁরা সিরাজের ছোটো ভাই ইকরম উদ্দৌল্লাকে দত্তক নেন। কিন্তু কিছুদিন পরই ইকরম বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সন্তান হারানোর দুঃখে মৃত্যু হয় শাহমৎ জঙ্গের। বিধবা ঘসেটি বেগম একাই মতিঝিল প্রাসাদে তাঁর স্বামীর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। তাই সিরাজ সিংহাসন লাভ করলে ঘসেটি বেগমের ঈর্ষা হয়। তিনি আলিবর্দির মেজো মেয়ের পুত্র, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গকে সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা করতে থাকেন। এঁদের ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ। আর ঘসেটি বেগমের প্রাসাদ মতিঝিল ছিল এই যাবতীয় ষড়যন্ত্রের মূলকেন্দ্র। এই খবর পেয়ে সিরাজ বল প্রয়োগ করে ঘসেটি বেগমের যাবতীয় ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং নিজের মুরশিদাবাদ রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে তাঁকে নজরবন্দি করে রাখেন। এরপর শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করলেও ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সম্পর্কের চূড়ান্ত তিক্ততার কারণে তাঁকে মুরশিদাবাদে ফিরে আসতে হয়। শওকত জঙ্গকে হত্যা করেন সিরাজের সেনাপতি মোহনলাল। সিরাজের সিংহাসন লাভের সময় থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর তিক্ততা শুরু হয়। প্রথমত, সিরাজ যখন সিংহাসনে বসেন তখন চিরাচরিত প্রথা উপেক্ষা করে ইংরেজরা সিরাজকে কোনো নজরানা পাঠায়নি। এতে নবাব অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। দ্বিতীয়ত, সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগম ও শওকত জঙ্গের ষড়যন্ত্রের পিছনে ইংরেজদের সমর্থন আছে, এই খবর পেয়ে সিরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হন। তৃতীয়ত, ঘসেটি বেগমের প্রিয়পাত্র, ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের অভিযোগ উঠলে সিরাজ মুরশিদাবাদে এসে তাঁকে সব হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। রাজবল্লভের সহায়তায় ও বুদ্ধিতে তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাস প্রচুর ধনরত্ন-সহ ঢাকা থেকে পালিয়ে কলকাতায় এসে ইংরেজদের আশ্রয়ে গা-ঢাকা দেন। কলকাতার ইংরেজ গভর্নর ড্রেকের কাছে তাঁর আশ্রয় মেলে। তবে, নবাবের বারংবার নির্দেশ সত্ত্বেও ইংরেজরা কৃষ্ণদাসকে নবাবের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে। চতুর্থত, দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব শুরু হলে, তার অজুহাতে ফরাসি ও ইংরেজ উভয়পক্ষই বাংলায় দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। সিরাজ দুর্গনির্মাণ বন্ধ করার আদেশ জারি করলে ফরাসিরা তা পালন করলেও, নবাবের মুহুর্মুহু নির্দেশ সত্ত্বেও ইংরেজরা তা অগ্রাহ্য করে। এমনকি, নবাবের দূত নারায়ণ দাসকেও ইংরেজদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়, যা নবাবের পক্ষে ছিল অত্যন্ত অপমানজনক। তা ছাড়া কোম্পানির কর্মীরা দিল্লির সম্রাট ফারুকশিয়ার কর্তৃক কোম্পানিকে 1717 খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত ‘দস্তক’ বা ছাড়পত্র তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে ব্যবহার করা শুরু করে। সবমিলিয়ে ইংরেজরা সবক্ষেত্রে সিরাজের বিরোধিতা করতে থাকে।
এমন অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া ছাড়া সিরাজের অন্য কোনো উপায় ছিল না। ইংরেজ দমনের উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি তাদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করেন (4 জুন) এবং পরদিন কলকাতার দিকে অগ্রসর হন। 1756 খ্রিস্টাব্দের 20 জুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ- সহ সিরাজ কলকাতা অধিকার করে নেন এবং নবাব আলিবর্দি খাঁ-র নামানুসারে কলকাতার নাম রাখেন ‘আলিনগর’। এরপর মানিকচাঁদকে কলকাতার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তিনি ফিরে আসেন। এ-খবর মাদ্রাজে পৌঁছালে, তখনই কর্নেল ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে একটি নৌবহর কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং প্রায় বিনা বাধায় তারা পুনরায় কলকাতা দখল করে (2 জানুয়ারি, 1757 খ্রিস্টাব্দে)। এ-খবর পেয়ে আবার যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে পূর্ব ভারতে বহিরাক্রমণের আশঙ্কায় সিরাজ কয়েকদিন পর যুদ্ধ বন্ধ করে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন (9 ফেব্রুয়ারি)। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য, দুর্গনির্মাণ এবং নিজেদের নামাঙ্কিত মুদ্রা চালু করার অনুমতি পায়। পরোক্ষে এই সন্ধি সিরাজের অধিকারই খর্ব করে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে।
তবে এ সন্ধির মর্যাদা না রেখে, নবাবের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই ক্লাইভ ফরাসি ঘাঁটি চন্দননগর দখল করেন (23 মার্চ, 1757 খ্রিস্টাব্দ)। এইভাবেই ক্লাইভ ফরাসিদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পরাজিত করেন। পাশাপাশি তিনি কূটনীতির সাহায্যে ফরাসি ও নবাবের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের সম্ভাবনা দূর করেন। কিন্তু একইসাথে ফরাসিদের মুরশিদাবাদে আশ্রয়গ্রহণ এবং দাক্ষিণাত্যের ফরাসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নবাবের গোপন যোগাযোগ ক্লাইভের মনে ভয়ের জন্ম দেয় এবং তিনি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার ফিকির খুঁজতে থাকেন।
ইতিমধ্যে রাজদরবারেও জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, মীরজাফর, ইয়ার লতিফ প্রমুখ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ক্লাইভের সঙ্গে হাত মেলান। স্থির হয়, সিরাজকে অপসারিত করে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হবে, যার বিনিময়ে তিনি কোম্পানির স্বার্থ সুরক্ষিত করবেন।
ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি শেষ হলে ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে আলিনগরের সন্ধির শর্তভঙ্গের অভিযোগ এনে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন ও নবাবকে একটি চরমপত্র পাঠান। আবার চরমপত্রের উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই ক্লাইভ সসৈন্যে মুরশিদাবাদের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করেন। 1757 খ্রিস্টাব্দের 23 জুন মুরশিদাবাদ থেকে 23 মাইল দূরে নদিয়ার পলাশিতে দুই পক্ষের যুদ্ধ হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হয় এক চরম বিশ্বাসঘাতকের ফাঁদে পড়ে। সেইসঙ্গে বঙ্গের রাজনীতিতে শুরু হয় এক নতুন ঔপনিবেশিক অধ্যায়। সেই থেকে পরাধীন বাংলার দুঃখদুর্দশার শুরু, যার জের চলেছিল পরবর্তী দুশো বছর ধরে।
সিরাজদ্দৌলা নাটকের উৎস
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে নাট্যাংশটি গৃহীত হয়েছে। নাট্যকার নিজেই বলেছেন, “সিরাজদ্দৌলা নামটি নাকি সিরাজুদ্দৌলা হওয়া উচিত। কিন্তু সে পরিবর্তন করলাম না।” তাঁর সিদ্ধান্তকেই স্বীকৃতি দিয়ে এখানে যাবতীয় লেখাতে ‘সিরাজদ্দৌলা‘ বানানটিই অক্ষুণ্ণ রাখা হল।
সিরাজদ্দৌলা নাটকের বিষয়সংক্ষেপ
এই নাট্যাংশের শুরুতেই দেখা যায় মুরশিদাবাদে সিরাজদ্দৌলার সভাকক্ষের দৃশ্য। নাটকের প্রথমে আমরা দেখি, সিরাজ তাঁর দরবারের সদস্য, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটসকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে বহিষ্কৃত করছেন। আলিনগরের সন্ধির শর্তরক্ষা না করে ওয়াটসের প্ররোচনায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন যে কলকাতায় সৈন্যসমাবেশের উদ্যোগ নিচ্ছেন, তা ওয়াটসনের পাঠানো চিঠিতে জানতে পারেন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা। ফলে ওয়াটসকে বিতাড়িত হতে হয়। বাংলার ফরাসি বণিকদের পক্ষ থেকে মঁসিয়ে লা সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নবাবের সাহায্য চাইতে। তাদের অভিযোগ, নবাবের বিনা সম্মতিতেই তাঁর শাসনাধীন এলাকা চন্দননগরে ইংরেজরা ফরাসিদের হটিয়ে দিয়েছে এবং সমস্ত ফরাসি কুঠি যেন ইংরেজদের ছেড়ে দেওয়া হয়, এই দাবিও তারা জানিয়েছে। কিন্তু নবাব জানান, বিষয় সম্পর্কে তিনি অবগত হলেও এক্ষেত্রে কোনো সাহায্য তিনি করতে পারবেন না। কারণ, সদ্য কলকাতা জয়ের যুদ্ধে এবং শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়ার যুদ্ধে তাঁর বহু অর্থক্ষয়, লোকক্ষয় এবং শক্তিক্ষয় হয়েছে। তাই অল্পসময়ের ব্যবধানে কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এ কথা শুনে মঁসিয়ে লা তাঁকে বলেন যে, ফরাসিদের বঙ্গভূমি হয়তো ছাড়তে হবে, কিন্তু সেইসঙ্গে ধ্বংস হবে বাংলার স্বাধীনতা। এরপর মঁসিয়ে লা রাজসভা ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে ওয়াটসকে বহিষ্কার করা নিয়ে সভায় শোরগোল পড়ে যায়। সে সময় সিরাজের তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। এই সমালোচকদের দলে ছিলেন রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ এবং মীরজাফর। এই সময় সিরাজের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলেন মোহনলাল এবং মীরমদন। ইতিমধ্যেই সিরাজ মীরজাফরকে লেখা ওয়াটসনের একটি চিঠিও প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেন। স্বাভাবিকভাবেই, সভায় অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং সিরাজ যাঁদের ওপরে দোষারোপ করেন, তাঁরা সভা ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হন। তখন সিরাজ আন্তরিকভাবে সকলের কাছে সহায়তা প্রার্থনা করেন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য মরণপণ করে নিজেদের উৎসর্গ করতে বলেন। এরপরে দেখা যায়, সকলেই শপথ করেন যে, তাঁরা দেশের স্বার্থে প্রাণ বলি দিতেও রাজি। সকলে সভাস্থল ত্যাগ করার পর একা সিরাজ এবং গোলাম হোসেন পড়ে থাকেন। এসময়ে সেখানে প্রবেশ করেন ঘসেটি বেগম, সিরাজের মাসি। ঘসেটি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় সিরাজ তাঁর মতিঝিলের আবাসস্থল থেকে তাঁকে সরিয়ে নিজের প্রাসাদে এনে নজরবন্দি করে রাখেন। তাঁর পালিত পুত্র (আসলে তাঁর ভগ্নিপুত্র) শওকত জঙ্গকে নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার অপরাধে হত্যা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই, ঘসেটি ছিলেন সিরাজবিরোধী এবং তাই তিনি যত শীঘ্র সম্ভব, সিরাজের পতন কামনা করেন। সিরাজকে হত্যা করে নিজের প্রতিহিংসা মেটানোই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ফলে, সিরাজের দুঃসময়ে তিনি খুশি হয়ে ওঠেন। সিরাজকে শাপশাপান্ত করতে করতে ঘসেটি যখন মৃত্যুর অভিশাপও দিতে বসেছেন, তখন ছুটে আসেন লুৎফা, সিরাজের বেগম। তিনি ঘসেটি বেগমকে কোনোমতে এই কাজ থেকে বিরত করেন। কিন্তু সিরাজের সঙ্গে ঘসেটির উত্তপ্ত কথাবার্তা চলতেই থাকে। লুৎফার অনুরোধে সিরাজ শেষপর্যন্ত ঘসেটিকে অন্দরমহলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেও ঘসেটির অভিশাপ আর আগামী পলাশির যুদ্ধের পরিণতি ভেবে সিরাজের হাহাকার -এর মধ্য দিয়েই শেষ হয় নাটকটি।
সিরাজদ্দৌলা নাটকের নামকরণ
যে-কোনো সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নামকরণের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। নামকরণের মধ্য দিয়েই রচয়িতা তাঁর রচনাটি সম্পর্কে পাঠকের কাছে আগাম ধারণা দিয়ে থাকেন। পাঠ্য ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাট্যাংশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই নাট্যাংশটি গৃহীত হয়েছে যে মূল নাটকটি থেকে, তার নামও সিরাজদ্দৌলা। অর্থাৎ, পাঠ্যাংশটির এই নামকরণ মূল নাটকের নামেই। কিন্তু মূল নাটকে সিরাজই হয়ে থেকেছেন সমগ্র নাটকের কেন্দ্রশক্তি। ঠিক তেমনটাই ঘটেছে এই নাট্যাংশের ক্ষেত্রেও।
আলোচ্য নাট্যাংশের শুরুতেই তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে নাট্যকারের যে নির্দেশনা দেওয়া হয়, তাতে প্রথম যে মানুষটির অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া থাকে, তিনি সিরাজ। আবার এই নাট্যাংশের সর্বপ্রথম সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে সিরাজের মুখ থেকে। সমগ্র নাট্যাংশটিতে একটি কেন্দ্রীয় সমস্যাকে ক্রমশ নির্দেশ করেছেন সিরাজ, আবার সেই সমস্যার কোনো প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে হাহাকারও করতে হয়েছে তাঁকে। তিনি নবাব-তাই তাঁকে ঘিরেই যাবতীয় ষড়যন্ত্র, মুরশিদাবাদের রাজসভার সামগ্রিক রাজনীতি-কূটনীতি আবর্তিত হয়েছে। আর সেই আবর্তনের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে হাহাকার করে উঠেছেন স্বাধীন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লা। এই দুর্বিপাকের মধ্যে টলে উঠেছে তাঁর সিংহাসন। এই নাট্যাংশে সবসময়ই সিরাজ চরিত্রটির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যবনিকা পতনের আগে তাঁর মুখে বসানো নাটকের শেষ সংলাপেও আর-এক যবনিকা পতনের আভাসই প্রতিধ্বনিত হয়। সুতরাং এই নাট্যাংশের ভরকেন্দ্রই হলেন সিরাজ। সেই কারণেই এই নাট্যাংশের নামকরণ ‘সিরাজদৌল্লা’ যথাযথ ও সার্থক হয়েছে বলা যায়।
আজকের আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক বাংলার পঞ্চম পাঠের দ্বিতীয় অংশ ‘সিরাজদ্দৌলা’ এর বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো প্রায়ই মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসতে দেখা যায়। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য সহায়ক হয়েছে। যদি কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকে, তবে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন; আমি যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করবো। এছাড়া, এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জন বা যাদের এটির প্রয়োজন হতে পারে, তাদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ!


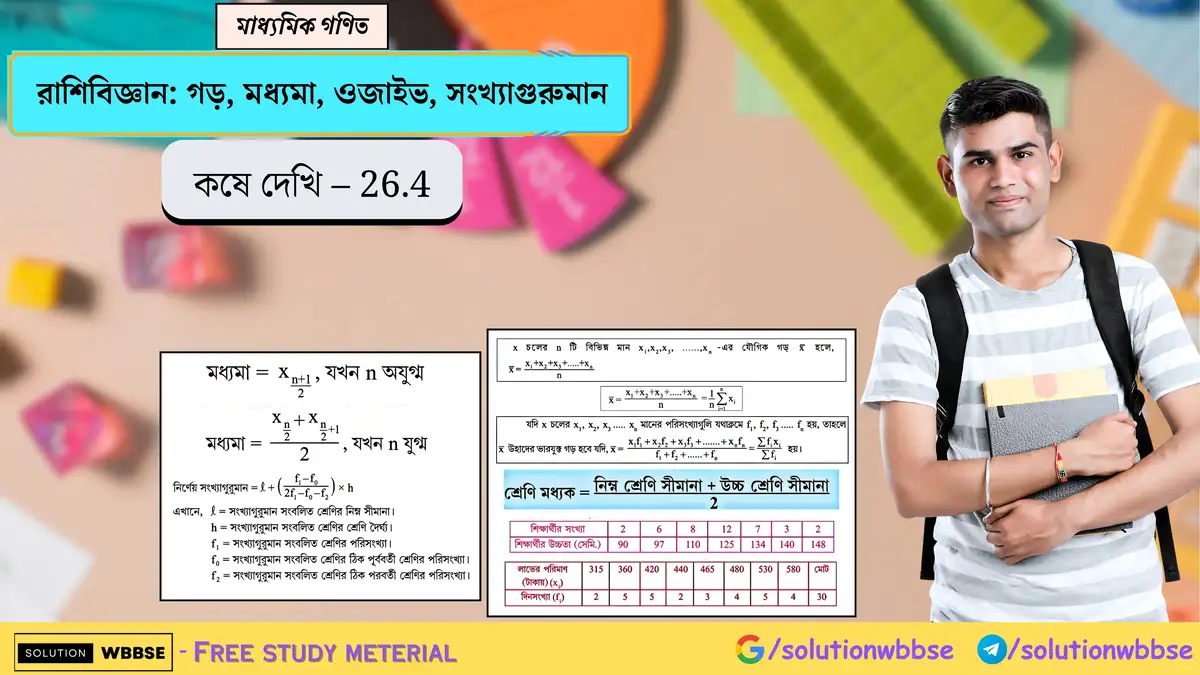
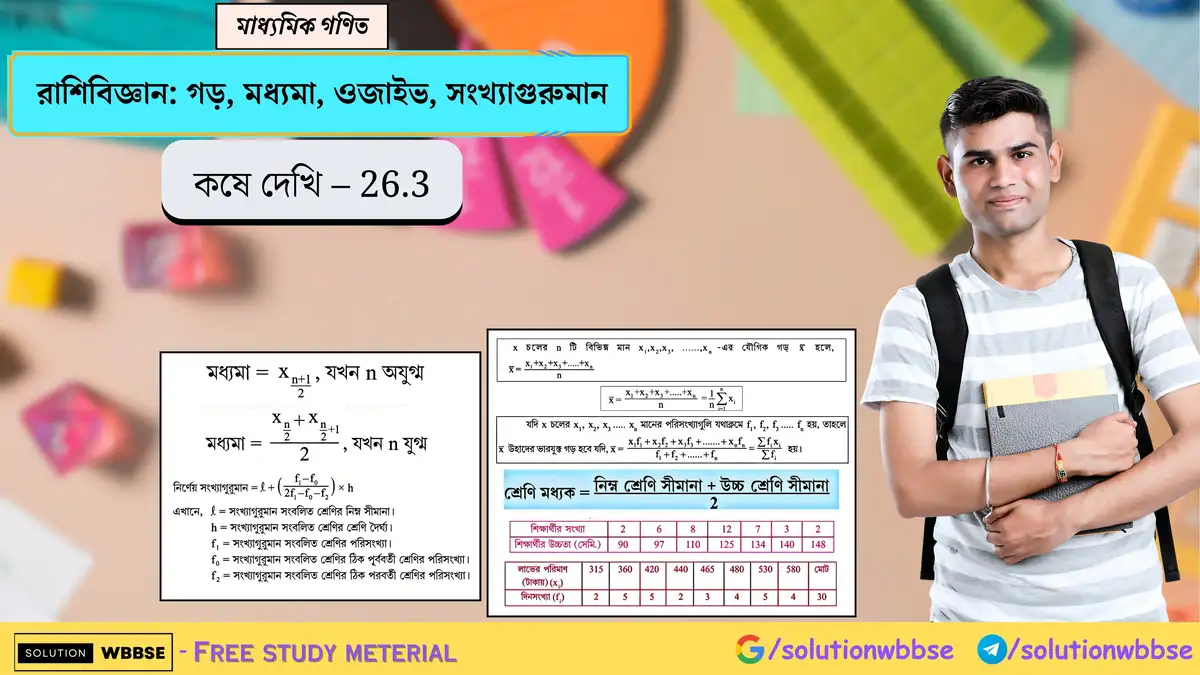
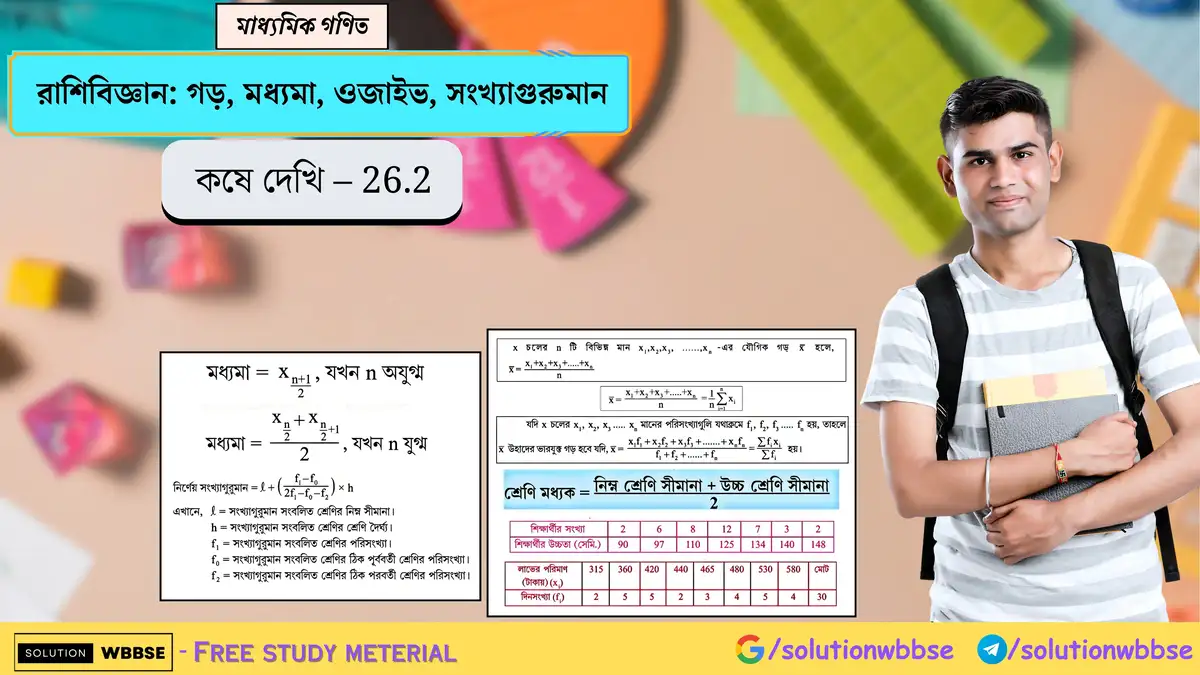

মন্তব্য করুন