আজকে আমরা এই আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণি) ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়, “সংস্কার: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা” এর কিছু “সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নোত্তরগুলি মাধ্যমিক বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই ধরনের প্রশ্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় প্রায়শই আসে।

আঠারো শতককে কেন অন্ধকার যুগ বলা হয়?
আঠারো শতকে বাংলা তথা ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংকট লক্ষণীয়।
আঠারো শতককে অন্ধকার যুগ বলার কারণ –
- রাজনৈতিক – এই সময় মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।
- সাংস্কৃতিক – রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংকটে পড়ে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গভীর সংকট দেখা দেয়। এই সমস্ত কারণে আঠারো শতককে ‘অন্ধকার যুগ’ বলা হয়।
উনিশ শতককে বাংলার প্রগতির যুগ বলা হয় কেন?
উনিশ শতকে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি প্রগতি পরিলক্ষিত হয়।
উনিশ শতককে বাংলার প্রগতির যুগ বলার কারণ –
- সামাজিক – বিভিন্ন মনীষীর উদ্যোগে এই সময় সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।
- রাজনৈতিক – এই সময় শাসনকাঠামো দৃঢ় হয়, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সাংস্কৃতিক – এই সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তার হয় এবং একাধিক ছাপাখানা গড়ে ওঠে। সাহিত্য সৃষ্টি হয় ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়।
এই সমস্ত কারণে উনিশ শতককে বাংলার ‘প্রগতির যুগ’ বলে।
উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাহিত্যের গুরুত্ব লেখো।
সামাজিক ইতিহাস জানার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংবাদপত্র ও সাহিত্য হল অন্যতম প্রধান উপাদান।
সংবাদপত্র ও সাহিত্যের গুরুত্ব –
- সামাজিক প্রতিফলন – সংবাদপত্র ও সাহিত্যে সামাজিক জীবনের প্রতিফলন ঘটে।
- জনমত গঠন – প্রকাশনা ও প্রসারের নিরিখে সংবাদপত্র ও সাহিত্য জনমত গঠনে প্রভাব বিস্তার করে।
এই নিরিখে সামাজিক ইতিহাস জানার জন্য সংবাদপত্র ও সাহিত্য হল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
উনিশ শতকের শুরুতে বাংলার নারীসমাজের অবস্থা কেমন ছিল?
উনিশ শতকের শুরুতে নারীসমাজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।
উনিশ শতকের শুরুতে বাংলার নারীসমাজের নারীর অবস্থা –
- শিক্ষার অভাব – এই সময় নারীশিক্ষা প্রায় ছিল না বললেই চলে। জমিদার বাড়িতে, বৈষ্ণবের আখড়ায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে সীমিত নারীশিক্ষা ছিল। মুরশিদাবাদ জেলায় মাত্র 9 জন নারী নাম লিখতে পারতেন বলে জানা যায়।
- নির্যাতন – বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ও বিভিন্ন কুসংস্কার নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।
বামাবোধিনী সভার দুটি উদ্দেশ্য লেখো।
উনিশ শতকে নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত বাংলার উল্লেখযোগ্য সমিতিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বামাবোধিনী সভা। 1863 খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্তের সুযোগ্য সহযোগিতায় বসন্তকুমার ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে বামাবোধিনী সভা।
বামাবোধিনী সভার উদ্দেশ্যসমূহ –
- শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার – বামাবোধিনী সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বামা অর্থাৎ নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার ঘটানো। নারীসমাজকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বামাবোধিনী সভার উদ্যোগে বাংলায় প্রায় 35টি বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হয়।
- কুসংস্কার দূরীকরণ – নারীদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করা ও সঠিক জ্ঞান প্রদান করাও ছিল এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য।
বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশের পটভূমি আলোচনা করো।
1863 খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত বামাবোধিনী পত্রিকা-ই হল নারীদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্রিকা।
বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশের পটভূমি –
- বামাবোধিনী সভা – উনিশ শতকে নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত বাংলার উল্লেখযোগ্য সমিতিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বামাবোধিনী সভা। বসন্তকুমার ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণয় গোস্বামী, বসন্তকুমার দত্ত প্রমুখের মিলিত প্রচেষ্টায় উমেশচন্দ্র দত্তের সুযোগ্য সহযোগিতায় 1863 খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে বামাবোধিনী সভা।
- বামাবোধিনী পত্রিকা – এই সভার মুখপত্র ছিল বামাবোধিনী পত্রিকা। শুধু বাংলায় নয়, ভারত তথা সমগ্র এশিয়ায় ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ ছিল একমাত্র নারীকেন্দ্রিক পত্রিকা।
কে, কবে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন?
উনিশ শতকের বাংলাদেশে নারী বিষয়ক পত্রিকা ছিল বামাবোধিনী পত্রিকা।
বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশনা –
- প্রকাশক – উমেশচন্দ্র দত্ত এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।
- প্রকাশকাল – 1863 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস বা 1270 বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।
বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কী ছিল?
বামাবোধিনী হল মহিলাদের জন্য প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা।
বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশের উদেশ্য –
- নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা – বাংলার নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ছিল এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।
- নারীদের মানসিক উন্নতি ঘটানো – বাংলার নারীদের বিশেষত গৃহবধূদের মানসিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটানো।
- নারীদের কুসংস্কার দূর করা – নারীদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করা ও সঠিক জ্ঞান প্রদান করা।
বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
অথবা, বামাবোধিনী পত্রিকার বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের দুটি বৈশিষ্ট্য হল –
- নারী বিষয়ক লেখা প্রকাশ – বামাবোধিনী পত্রিকা হল নারীদের জন্য প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা।
- আদর্শ নারীসমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা – বামাবোধিনী পত্রিকা আদর্শ নারীসমাজ গড়ে তোলার জন্য নারীর গুণাবলি, শিক্ষা, শিশুর যত্ন, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় প্রকাশ করে।
বামাবোধিনী পত্রিকার নামকরণ কতটা যথার্থ ছিল?
বামাবোধিনী পত্রিকার নামকরণ –
যে-কোনো নামকরণের একটি অর্থ থাকে। সেদিক থেকে বামাবোধিনী পত্রিকার নামকরণের যথার্থতা আছে। তা হল –
- নারী বিষয়ক – বামাবোধিনী শব্দের অর্থ হল নারীচেতনা। পত্রিকাটি ছিল সম্পূর্ণভাবে নারী বিষয়ক।
- নারীকল্যাণ – পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল নারীর সার্বিক কল্যাণসাধন। যথা – নারীশিক্ষার প্রসার, শিশুর যত্ন, বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণ, বিদুষী নারীদের আদর্শ প্রচার প্রভৃতি।
বামাবোধিনী পত্রিকার জনপ্রিয়তার কারণ কী?
1863 খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত বামাবোধিনী পত্রিকা হল নারীদের জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মাসিক পত্রিকা যা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।
বামাবোধিনী পত্রিকার জনপ্রিয়তার কারণ –
- নারীকেন্দ্রিক – বামাবোধিনী পত্রিকাটি ছিল সম্পূর্ণ নারী বিষয়ক। এখানে নারীর সার্বিক কল্যাণসাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।
- নারীশিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান – নারীকল্যাণের প্রথম পদক্ষেপ নারীশিক্ষার উপর এই পত্রিকায় জোর দেওয়া হয়। ফলে পত্রিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।
বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর কেন বন্ধ হয়ে যায়?
ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব –
ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ-বিরুদ্ধ কুচবিহার-বিবাহকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ শুরু হয়। এর ফলে 1878 খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় – কেশবচন্দ্র সেনের পরিচালিত নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ও শিবনাথ শাস্ত্রী পরিচালিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।
বামাবোধিনী পত্রিকার উপর প্রভাব –
বামাবোধিনীর সম্পাদক মহাশয় কেশবচন্দ্র সেনের গোষ্ঠী এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর গোষ্ঠী – কোন্ গোষ্ঠীর পক্ষ নেবেন তাই নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েন। এর ফলে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’র প্রকাশ প্রায় এক বছর বন্ধ থাকে।
নারীশিক্ষা বিস্তারে বামাবোধিনী পত্রিকার উদ্যোগ লেখো।
উনিশ শতকে বাংলাদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে বামাবোধিনী পত্রিকা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।
নারীশিক্ষা বিস্তারে বামাবোধিনী পত্রিকার উদ্যোগ –
- নারীদের পিছিয়ে পড়ার কারণ উল্লেখ – এই পত্রিকায় নারীদের শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হত।
- উৎসাহ দান – নারীকল্যাণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নারীশিক্ষার উপর এই পত্রিকায় জোর দেওয়া হত। বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রতি মাসে বিনামূল্যে পত্রিকার একটি করে সংখ্যা পাঠানো হত।
কে, কবে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা প্রকাশ করেন?
অথবা, হিন্দু প্যাট্রিয়ট -এর আবির্ভাব ঘটে কবে? সেই সময়ে এই পত্রিকার মালিক কে ছিলেন?
উনিশ শতকের বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী প্রধান পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল হিন্দু প্যাট্রিয়ট।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার প্রকাশনা –
- প্রকাশক – মধুসূদন রায় নামে কলকাতার একজন ব্যাংকার পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন। সেই সময় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
- প্রকাশকাল – 1853 খ্রিস্টাব্দের 6 জানুয়ারি কলকাতা থেকে এই সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কী ছিল?
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য –
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল –
- দরিদ্র চাষিদের উপর অত্যাচারের বিরোধিতা করা – হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা দরিদ্র চাষিদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিষয়ে লেখা প্রকাশ করে তার বিরোধিতা করত।
- সমাজসংস্কারে সহযোগিতা করা – হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা নারীশিক্ষার প্রসারে জনমত গড়ে তোলে এবং হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে সংস্কারকদের সমর্থন করে।
- ব্রিটিশ সরকারের অনিয়মগুলি প্রকাশ করা – এই পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম ছিল ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় বা নিয়মবিরুদ্ধ কাজগুলি জনগণের কাছে প্রকাশ করা।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার বৈশিষ্ট্য –
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল –
- ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা – হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা ছিল ভারতীয়দের দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা।
- দরিদ্র চাষিদের পক্ষ অবলম্বন – এই পত্রিকা অত্যাচারিত চাষিদের পক্ষ নিয়ে নীলকর সাহেবদের নির্মম শোষণের বিরোধিতা করেছিল।
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কীভাবে হিন্দু প্যাট্রিয়ট -এর সঙ্গে যুক্ত হন?
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 1855 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1861 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় –
মধুসূদন রায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার মালিক ছিলেন। পত্রিকাটি কিছুদিন প্রকাশ করার পর তিনি নিজের প্রেস বিক্রি করে হরিশচন্দ্রকে দিয়ে পশ্চিমে চলে গিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্র হিন্দু প্যাট্রিয়টকে ভবানীপুরে তুলে নিয়ে গিয়ে ভাই হারানচন্দ্রকে প্রেস ও কাগজের স্বত্বাধিকারী করে এই পত্রিকা চালাতে শুরু করেন।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা থেকে কী ধরনের সমাজচিত্র পাওয়া যায়?
পত্রপত্রিকায় যেহেতু সমকালীন বাংলার সমাজের প্রতিফলন ঘটে তাই হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা থেকে উনিশ শতকের বাংলার সমাজজীবনের বিভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা থেকে সামাজিক সমস্যাসমূহ –
- কুসংস্কার – সেসময় সমাজে প্রচলিত কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে এই পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখা হয়। এ ছাড়া নারীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের পক্ষেও প্রচার চালানো হয়।
- শোষণ ও দারিদ্র্য – দরিদ্র ভারতীয় কৃষকদের উপর করভার, শোষণ, কৃষকদের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ-বিদ্রোহ, তাদের দারিদ্র্য প্রভৃতির কাহিনি এই পত্রিকা তুলে ধরে।
সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রতি হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার কী মনোভাব ছিল?
উনিশ শতকের বাংলায় প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দু প্যাট্রিয়ট।
সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রতি হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার মনোভাব –
- 1855 খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতালদের দলবদ্ধ অভিযান, জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আধুনিক অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে তিরধনুক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রসজ্জিত সাঁওতালদের অসম যুদ্ধকাহিনি এই পত্রিকায় লেখা হয়।
- হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা পরাজিত সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের নৃশংস আচরণ সহানুভূতির সঙ্গে প্রচার করেছিল।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের কারণ বিষয়ে কী বলা হয়?
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় 1857 খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের কারণ –
- কার্তুজের ব্যবহার – গোরু ও শূকরের চর্বিমেশানো কার্তুজের ব্যবহার হিন্দু-মুসলিম সিপাহিদের বিদ্রোহী করে তোলে।
- সরকারি নীতি – বিদ্রোহের কারণ ছিল সরকারের বিভিন্ন নীতি। সিপাহিরা বিভিন্ন কারণে সরকারি নীতির উপরে বিক্ষুব্ধ ছিল।
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অত্যাচারী নীলচাষিদের কীরূপ সহযোগিতা করেন?
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সমাজজীবনে ঘটা সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছিল হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায়, যার সম্পাদক ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অত্যাচারিত নীলচাষিদের জন্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -এর উদ্যোগ –
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার মধ্যে দিয়ে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দরিদ্র চাষিদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিষয়ে লেখা প্রকাশ করে নীলচাষিদের দুর্দশার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরেন।
নারীসমাজের উন্নতির বিষয়ে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা কীরূপ উদ্যোগ নেয়?
উনিশ শতকের বাংলার সমাজজীবনের বিশেষত নারীসমাজের উন্নতির বিষয়ে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
নারীসমাজের উন্নতির বিষয়ে হিন্দু প্যাট্রিয়টের ভূমিকা –
- নারীশিক্ষার প্রসার – নারীসমাজের উন্নয়ন ও মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এই পত্রিকা নারীশিক্ষার প্রসারে জনমত গড়ে তোলে।
- কুসংস্কারের বিরোধিতা – এই পত্রিকা হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে সংস্কারকদের সমর্থন করে। এ ছাড়া সেসময় সমাজে। প্রচলিত কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে এই পত্রিকায়। বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখা হয়।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় সরকার বিরোধিতার কী পরিচয় পাওয়া যায়?
বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী প্রধান পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল হিন্দু প্যাট্রিয়ট। এই পত্রিকায় সরকার বিরোধিতার বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় সরকার বিরোধিতা –
- দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন – বড়োলাট লর্ড লিটন 1878 খ্রিস্টাব্দে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন জারি করেন। এর দ্বারা সরকারি নীতির সমালোচক এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদকের কারাবাসের ব্যবস্থা করা হলে হিন্দু প্যাট্রিয়ট এর প্রতিবাদ জানায়।
- ইলবার্ট বিল – 1883 খ্রিস্টাব্দে ইলবার্ট বিল রচিত হলে এর প্রতিবাদে ইংরেজরা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে এবং জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা বিলকে সমর্থন জানিয়ে পালটা আন্দোলন করে। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা এসময় জাতীয়তাবাদী মতকে সমর্থন জানায়।
উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদ প্রসারে হিন্দু প্যাট্রিয়ট -এর অবদান লেখো।
উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতে জাতীয়তাবাদ প্রসারে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।
উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদ প্রসারে হিন্দু প্যাট্রিয়ট -এর অবদান –
- ব্রিটিশ বিরোধিতা – 1860 খ্রিস্টাব্দে হিন্দু প্যাট্রিয়ট বাংলার নীলচাষিদের আন্দোলনকে সমর্থন ও নীলকরদের বিরোধিতা করে। এর সঙ্গে পত্রিকা ব্রিটিশ শাসননীতিরও বিরোধিতা করে।
- প্রতিবাদ – বিহার থেকে আসামে চা-শ্রমিক পাঠানোর বিরুদ্ধে এই পত্রিকা প্রতিবাদ জানায়। সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অত্যাচার ও দমননীতি হিন্দু প্যাট্রিয়ট -এ প্রকাশ পেয়েছিল।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা বিখ্যাত কেন?
হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা ছিল ভারতীয়দের দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক।
হিন্দু প্যাট্রিয়টের জনপ্রিয়তার কারণ –
- হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় তথা নিয়মবিরুদ্ধ কাজগুলি জনগণের কাছে প্রকাশ করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।
- দরিদ্র ভারতীয় কৃষকদের শোষণের কাহিনি প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক কাজেও এই পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
কে, কবে হুতোম প্যাঁচার নক্শা গ্রন্থটি প্রকাশ করেন?
হুতোম প্যাঁচার নক্শা গ্রন্থটি কলকাতার সমাজজীবনের একটি জীবন্ত দলিল।
হুতোম প্যাঁচার নক্শা গ্রন্থটির প্রকাশনা –
- গ্রন্থকার – কালীপ্রসন্ন সিংহ ‘হুতোম প্যাঁচা’ ছদ্মনামে এই ব্যঙ্গরচনাটি প্রকাশ করেন।
- রচনাকাল – 1861 খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি রচিত ও প্রকাশিত হয়। চলিত ও কথ্য বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের আসনে বসানোর প্রথম ও সার্থক প্রচেষ্টা হল এই গ্রন্থ রচনা।
হুতোম প্যাঁচার নক্শা – এরূপ নামকরণের কারণ কী?
হুতোম প্যাঁচার নক্শার নামকরণ –
হুতোম প্যাঁচার নক্শার রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহের ছদ্মনাম ছিল হুতোম প্যাঁচা।
- নক্শা শব্দের অর্থ হল ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে লেখা।
- ‘হুতোম প্যাঁচার নক্শা’ হল ব্রিটিশ আমলে বিভিন্নভাবে ফন্দিফিকির করে অর্থসম্পদে ধনী হয়ে ওঠা ধান্দাবাজ মানুষদের ব্যঙ্গ করে লেখা একটি কাহিনি। আর নিশাচর প্রাণী হিসেবে প্যাঁচা সমাজের রাত্রিকালীন অসৎ কর্মকাণ্ডের আদর্শ দর্শক। তাই যথার্থভাবেই এর নামকরণ হয়েছে হুতোম প্যাঁচার নক্শা।
হুতোম প্যাঁচার নক্শা – রচনার বৈশিষ্ট্য কী?
হুতোম প্যাঁচার নক্শা রচনার বৈশিষ্ট্য –
কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা হুতোম প্যাঁচার নক্শা রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি হল –
- কথ্যভাষায় রচিত – ‘হুতোম প্যাঁচার নক্শা’ কলকাতা ও তার আশপাশের শহরতলির কথ্যভাষায় লেখা।
- ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনা – এই গ্রন্থটি ব্রিটিশ আমলে ফন্দিফিকির করে ধনী হয়ে ওঠা সমাজের মানুষদের বিষয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র।
- সমাজের খারাপ দিক চিহ্নিত করা এবং সংশোধনের প্রচেষ্টা – এই গ্রন্থ রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল – এতে সমাজের কদর্য দিকগুলি তুলে ধরে সেগুলির সংস্কারসাধনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।
হুতোম প্যাঁচার নক্শা গ্রন্থের কোন্ ভাগে কীসের আলোচনা রয়েছে?
হুতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ 1861 খ্রিস্টাব্দে ‘হুতোম প্যাঁচার নক্শা’ গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থ থেকে উনিশ শতকের কলকাতার নাগরিক জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।
হুতোম প্যাঁচা নক্শা গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগ –
হুতোম প্যাঁচার নক্শা গ্রন্থে উনিশ শতকের কলকাতার বাঙালি সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থের প্রথমভাগে চড়ক পার্বণ, বারোয়ারি পূজা, মাহেশের স্নানযাত্রা এবং দ্বিতীয়ভাগে দুর্গোৎসব, রথযাত্রা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
হুতোম প্যাঁচার নক্শা থেকে কী ধরনের সমাজচিত্র পাওয়া যায়?
হুতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ ‘হুতোম প্যাঁচার নক্শা’ গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থ থেকে উনিশ শতকের কলকাতার নাগরিক জীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।
হুতোম প্যাঁচার নক্শার সমাজচিত্র –
- বাবু ও মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি – একদা ধনী ও অভিজাত শ্রেণির অবক্ষয় এবং নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনযাপন এই গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে। চড়ক, বারোয়ারি পূজা ইত্যাদি সামাজিক উৎসবে বাবুদের অর্থব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বর্ণিত হয়েছে।
- অন্যান্য শ্রেণি – এই গ্রন্থে ভৃত্য, কারিগর, গণিকা ও বিভিন্ন পেশার মানুষদের কথা বলা হয়েছে, তাদের জীবন ও জীবিকার বর্ণনাও আছে এখানে।
হুতোম প্যাঁচার নক্শার মাধ্যমে কলকাতার বাবুদের সম্পর্কে কী জানা যায়?
হুতোম প্যাঁচার নক্শার মাধ্যমে কলকাতার বাবু সম্প্রদায় –
উনিশ শতকের বাংলায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, যাকে বাবু সম্প্রদায় বলা হয়। অপরিমিত অর্থের আড়ম্বর দেখাতে বাবুরা বাইনাচ, পায়রা ও বুলবুলি পোষা, বিড়ালের বিবাহে লক্ষাধিক অর্থব্যয়ের জাঁকজমকপূর্ণ অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। কলকাতার আলো-আঁধারির আনাচকানাচে বাবুদের বিচরণ, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি অন্দরমহলের সজ্জাবিন্যাস সম্পর্কে নানান তথ্য হুতোম প্যাঁচার নক্শা গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।
হুতোম প্যাঁচার নক্শার মাধ্যমে কালীপ্রসন্ন সিংহ কীভাবে এক নতুন ভাষারীতির সূচনা করেন? উনিশ শতকে কলকাতায় বাবু চরিত্রচিত্রণে অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা হুতোমের নক্শা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
হুতোম প্যাঁচার নক্শার মাধ্যমে কালীপ্রসন্ন সিংহের নতুন ভাষারীতি –
কলকাতার আদি বাসিন্দাদের অপভাষাকে আশ্রয় করে এক নতুন ভাষারীতি উদ্ভাবন করার কৃতিত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রাপ্য। তাঁর রচনায় সাধুভাষার রীতিতে বদল এনে চলিত এবং কলকাতার কথ্যভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয়।
হুতোম প্যাঁচার নক্শার গুরুত্ব –
বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের ফলে আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে ‘বাবু’ শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। বাবু চরিত্রের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় নববাবুবিলাস ও আলালের ঘরের দুলাল নামের গ্রন্থ দুটিতে। পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির থেকে এটি অনন্য, কারণ এই গ্রন্থটিতেই বাবু চরিত্রচিত্রণে ব্যঙ্গবিদ্রুপের তীব্রতা লক্ষ করা যায়, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় না।
কে, কবে নীলদর্পণ নাটক রচনা করেন? নাটকটির গুরুত্ব কী ছিল?
উনিশ শতকের বাংলাদেশে নীলচাষিদের উপর নীলকর সাহেব ও জমিদারদের শোষণ-অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে নীলদর্পণ নাটকটি লেখা হয়।
নীলদর্পণ নাটকের প্রকাশনা –
- নাট্যকার – দীনবন্ধু মিত্র ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি রচনা করেন।
- রচনাকাল – 1860 খ্রিস্টাব্দে ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি রচিত ও প্রকাশিত হয়।
নীলদর্পণ নাটকের গুরুত্ব –
এই নাটকটির মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে নীলচাষিদের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়।
নীলদর্পণ নাটক থেকে কী ধরনের সমাজচিত্র পাওয়া যায়?
নীলদর্পণ নাটক থেকেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বাংলার সমাজ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়।
নীলদর্পণ নাটকের সমাজচিত্র –
- কৃষকদের দুর্দশা – বাংলার কৃষকদের এ সময় বিভিন্ন শোষণ, অত্যাচারের শিকার হতে হত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের নীলচাষ করতে বাধ্য করা হত। অগ্রিম দাদন, রাজি না হলে গোরু-ছাগল কেড়ে নেওয়া, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, নীলের দাম কম দেওয়া ইত্যাদি অবাধে চলত। সেই সামাজিক অত্যাচারের কাহিনি নাটকটিতে পাওয়া যায়।
- মধ্যবিত্তশ্রেণি – পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বাংলাদেশে যে মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় নাটকের কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।
নীলদর্পণ নাটকটি লেখকের স্বনামে প্রকাশিত হয়নি কেন?
1860 খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীলদর্পণ নাটকটি রচিত হয়। ‘কেনচিৎ পথিকেন’ এই ছদ্মনামে তিনি নাটকটি লেখেন।
নীলদর্পণ নাটকের স্বনামে প্রকাশিত না হওয়ার কারণ –
এই নাটকটি স্বনামে প্রকাশিত হয়নি, কারণ – দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন একজন সরকারি চাকুরে। আর এই নাটকটি ছিল বাংলার নীলচাষিদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্পর্কে। ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় তিনি স্বনামে নাটকটি প্রকাশ করেননি।
নীলদর্পণ নাটক প্রকাশের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল?
1860 খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের লেখা নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হওয়ার পর সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল।
নীলদর্পণ নাটকের প্রতিক্রিয়া –
- সমাজে ইংরেজবিরোধী মানসিকতা তৈরি – নীলদর্পণ নাটক পড়ে ও অভিনয় দেখে সাধারণ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে ইংরেজ ও নীলকরবিরোধী মানসিকতা তৈরি হয়।
- নীলচাষিদের পক্ষে জনমত তৈরি – নীলদর্পণ নাটক প্রকাশের ফলে অত্যাচারিত নীলচাষিদের পক্ষে জনমত তৈরি হয়।
- সরকারের কমিশন নিয়োগ – দেশে-বিদেশে নীলচাষিদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনি প্রচারিত হওয়ায় সরকার ইন্ডিগো কমিশন (1860 খ্রিস্টাব্দ) নিয়োগ করে অবস্থার তদন্ত করতে বাধ্য হয়।
নীলদর্পণ -এর জনপ্রিয়তার জন্য কোন্ কোন্ সহৃদয় ইউরোপীয় এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাদের পরিণতি কী হয়েছিল?
রেভারেন্ড জেমস লঙ –
ব্রিটিশ মিশনারিদের মধ্যে রেভারেন্ড জেমস লঙ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তাঁর যোগ্য তত্ত্বাবধানে ‘নীলদর্পণ’ নাটকটিকে মধুসূদন দত্ত ইংরেজিতে ভাষান্তর করেন বলে মনে করা হয়। জেমস লঙের বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং বিচারে তাঁর একমাস কারাদণ্ড ও 1000 টাকা জরিমানা হয়েছিল।
সিটন কার –
সিটন কার (Siton Carr) ছিলেন অপর-একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি যিনি বাংলায় ব্রিটিশ সরকারের সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁরই সহায়তায় নীলদর্পণ সরকারি ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছিল। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সমাজে সমালোচনার ঝড় ওঠে এবং তাঁকে বাংলা সরকারের সেক্রেটারি পদ ত্যাগ করতে হয়।
নীলদর্পণ নাটকটি বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কেন?
দীনবন্ধু মিত্র 1860 খ্রিস্টাব্দে নীলদর্পণ নাটকটি রচনা করেন। বাংলার ইতিহাসে এই নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম।
নীলদর্পণ নাটকটি বাংলার ইতিহাসের গুরুত্ব –
- নীলচাষিদের দুর্দশার প্রকাশ – নীলদর্পণ নাটকে বাংলার নীলচাষিদের দুর্দশা ও অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের সীমাহীন অত্যাচারের কাহিনি প্রচারিত হয়।
- শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি – নীলদর্পণ নাটক বাংলা ও ইউরোপের শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। রেভারেন্ড জেমস লঙ এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করার ফলে তাঁর জেল ও জরিমানা হয়।
দেশপ্রেমের উন্মেষে নীলদর্পণ নাটকের কী ভূমিকা ছিল?
1860 খ্রিস্টাব্দে নীলদর্পণ নাটকটি রচিত হয়। ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসে এই নাটক ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
দেশপ্রেমের উন্মেষে ‘নীলদর্পণ’ নাটকের ভূমিকা –
দেশপ্রেমের উন্মেষের নীলদর্পণ নাটকটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল –
- নীলকরদের অত্যাচার – এই নাটকে বাংলার নীলচাষিদের দুর্দশা ও অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের সীমাহীন অত্যাচারের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়।
- নীলচাষিদের প্রতিবাদ – নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নীলচাষিরা যে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেছিল তা এই নাটকে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এটি ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটাতে সাহায্য করে।
নীলদর্পণ নাটককে কে, কোন্ বিদেশি নাটকের সঙ্গে তুলনা করেন?
1860 খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীলদর্পণ নাটকটি প্রথম বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা বলে মানুষের মনে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিল।
এই নাটকটিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হ্যারিয়েট বিচার স্টোও (Harriet Beecher Stowe) -এর লেখা আঙ্কল টমস কেবিন (Uncle Tom’s Cabin) -এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।
নীল কমিশনের সামনে প্রধান সাক্ষী কে ছিলেন? নীল কমিশন কবে বসেছিল?
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সমাজজীবনে ঘটা গুরুত্বপূর্ণ সকল ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছিল হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায়। এরকম একটি ঘটনা ছিল নীল বিদ্রোহ।
নীল কমিশনের সামনে প্রধান সাক্ষী –
নীল কমিশনের সামনে প্রধান সাক্ষী ছিলেন হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
নীল কমিশন –
নীল কমিশন বসেছিল 1860 খ্রিস্টাব্দে।
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা কে প্রকাশ করেন? তিনি সুপরিচিত ছিলেন কী নামে?
উনবিংশ শতকে গ্রামবাংলার সমাজজীবনের কথা জানার জন্য গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকার প্রকাশনা –
- প্রকাশক – 1863 খ্রিস্টাব্দে হরিনাথ মজুমদার কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থেকে এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন।
- পরিচিতি – হরিনাথ মজুমদার কাঙাল হরিনাথ নামে সুপরিচিত ছিলেন।
হরিনাথকে কাঙাল হরিনাথ বলা হয় কেন?
উনিশ শতকে গ্রামবাংলার সমাজজীবনের দর্পণ ছিল গ্রামবার্তা প্রকাশিকা। 1863 খ্রিস্টাব্দে হরিনাথ মজুমদার বা ‘কাঙাল হরিনাথ’ এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন।
কাঙাল হরিনাথ নামের তাৎপর্য –
- উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে পরিকাঠামোগত সমস্যা, পুঁজির অভাব সত্ত্বেও দুঃখকষ্ট সহ্য করে হরিনাথ মজুমদার গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকাটি প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।
- স্কুলে শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে পত্রিকা প্রকাশে তিনি মনোনিবেশ করেন। এই কারণে শেষ জীবনে তাঁকে অর্থকষ্টে ভুগতে হয়েছিল। তিনি গ্রামবাংলার মানুষদের সমব্যথী ছিলেন। তাই তিনি ‘কাঙাল হরিনাথ’ নামে পরিচিত হন।
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকায় মূল কী বিষয়বস্তু প্রকাশিত হত?
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকায় মূল বিষয়বস্তু –
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হত। যেমন –
- কৃষকদের দুর্দশা – প্রধানত সুদখোর মহাজন, নীলকর, জমিদার কর্তৃক কৃষক শোষণের তথ্যভিত্তিক সংবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত।
- জ্ঞান-বিজ্ঞান – পত্রিকায় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা থাকত।
- নারীশিক্ষা – পত্রিকায় নারীশিক্ষা প্রসারের সংবাদ প্রকাশিত হত।
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদনায় হরিনাথ মজুমদারের ভূমিকা আলোচনা করো।
উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, পরিকাঠামোর অভাব, পুঁজি, পাঠক প্রায় সব কিছুরই অভাব ছিল। এই পরিস্থিতিতে দুঃখকষ্ট সহ্য করে পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন যারা, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হরিনাথ মজুমদার।
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদনায় হরিনাথের প্রভাব –
জমিদার, মহাজন, ইজারাদার প্রমুখের অত্যাচারের করুণ দৃশ্য জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন গ্রামবার্তা প্রকাশিকা। স্কুলে শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে পত্রিকা প্রকাশে তিনি মনোনিবেশ করেন। এই কারণেই শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁকে অর্থকষ্টে ভুগতে হয়েছিল।
পাবনার কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকায় কী ধরনের লেখা ছাপানো হত?
1872-1873 খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের পাবনায় কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে এবং বিদ্রোহী কৃষকদের সমর্থনে লেখা প্রকাশিত হয় গ্রামবার্তা প্রকাশিকা-য়।
গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য –
পত্রিকায় জমিদারি অত্যাচার, অতিরিক্ত আবওয়াব কর এবং জমিদারদের বাড়তি খাজনা আদায়ের জন্য নতুন জরিপ প্রণালী ইত্যাদি সব কিছুরই সমালোচনা করা হয়েছিল। এই পত্রিকায় বলা হয়েছিল যে, পাবনায় কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল জমিদারি অপশাসনের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নয়।
গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা কেন ব্যতিক্রমী ছিল?
উনিশ শতকে গ্রামবাংলার সমাজজীবনের কথা জানার জন্য গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হরিনাথ মজুমদার ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক।
গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা ব্যতিক্রমী হওয়ার কারণ –
বিভিন্ন কারণে এই পত্রিকাটি ব্যতিক্রমী ছিল –
- গ্রামীণ সমাজচিত্র – গ্রামবার্তা প্রকাশিকা গ্রাম্য সমাজজীবনের নানা চিত্র তুলে ধরে। এর আগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শহরের কথা থাকলেও গ্রামীণ সমাজের কথা সেভাবে পাওয়া যেত না। সেদিক থেকে এই পত্রিকাটি ছিল ব্যতিক্রম।
- মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা প্রকাশ – গ্রামের মানুষের দুঃখকষ্ট, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
দেশীয় শিক্ষা বলতে কী বোঝো?
দীর্ঘকাল ধরে ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে চালু ছিল।
দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা –
এই শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ হল –
- সংস্কৃত – পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, টোল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, ধর্মীয় আখ্যান ও বিধান শেখানো হত।
- আরবি-ফারসি – মক্তব ও মাদ্রাসায় আরবি ও ফারসি ভাষা, ধর্মীয় আখ্যান ও বিধিবিধান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত।
সরকারি উদ্যোগে দেশীয় শিক্ষার বিবরণ দাও।
ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন কারণে দেশীয় শিক্ষার উন্নতিতে সচেষ্ট হয়।
সরকারি উদ্যোগে দেশীয় শিক্ষা –
- কলকাতা মাদ্রাসা – 1781 খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস আরবি ও ফারসি ভাষাচর্চার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
- এশিয়াটিক সোসাইটি – 1784 খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম জোনস -এর উদ্যোগে প্রাচ্য ভাষাচর্চার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়।
- সংস্কৃত কলেজ – 1791 খ্রিস্টাব্দে জোনাথান ডানকান বেনারস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুদের সন্তুষ্ট করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।
উদ্দেশ্য যাই থাক, এই প্রতিষ্ঠানগুলির মান বেশ উঁচু ছিল। প্রাচীন ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট অবদান ছিল।
ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমদিকে কেন ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেয়নি?
ব্রিটিশদের ভারতে আগমনকালে ভারতীয়রা দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষালাভ করত। ভারতীয়রা দেশীয় শিক্ষার বাইরে ইউরোপীয় ধ্যানধারণা গ্রহণের একেবারেই পক্ষপাতী ছিল না। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও অনেক পরে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ না নেওয়ার কারণ –
ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমদিকে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেয়নি। কারণ –
- সরকারের বিরোধিতা – ব্রিটিশ সরকার মনে করত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করলে শাসকের বিরুদ্ধেই ভারতীয়দের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
- রাজনৈতিক সুদৃঢ়করণ – ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নিজেদের রাজনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ব্রিটিশরা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে তেমন উৎসাহ দেখায়নি।
প্রথম দিকে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কেন্দ্রের নাম লেখো।
প্রারম্ভিক পর্যায়ে কোম্পানি সরকার শুধুমাত্র দেশীয় শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টা করে এবং এ বিষয়ে তাদের উদ্যোগ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কেন্দ্রসমূহ –
- কলকাতা মাদ্রাসা – প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্যে 1781 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা মাদ্রাসা।
- এশিয়াটিক সোসাইটি – উইলিয়ম জোনসের উদ্যোগে 1784 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি।
- বেনারস সংস্কৃত কলেজ – বেনারসে 1791 খ্রিস্টাব্দে জোনাথন ডানকান প্রতিষ্ঠা করেন বেনারস সংস্কৃত কলেজ।
- ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ – এ ছাড়া লর্ড ওয়েলেসলি 1800 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।
উইলিয়ম জোনস কেন এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
অথবা, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
উইলিয়ম জোনস 1784 খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য –
- ভারতের প্রাচীন সভ্যতার চর্চা করা – ভারতের প্রাচীন সভ্যতার চর্চা করার জন্য তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।
- ভারতীয় সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ করা – তিনি ভারতীয় সাহিত্যকে আধুনিক ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এর ফলে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্ক দৃঢ় হবে।
গ্র্যান্টের অবজারভেশন কী?
বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হলেও কোম্পানি সরকার এদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। প্রথমদিকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত মিশনারিদের উদ্যোগেই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটে।
চার্লস গ্র্যান্টের অবজারভেশন –
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী চার্লস গ্রান্ট ‘অবজারভেশন’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন (1792 খ্রিস্টাব্দে)। এই পুস্তিকায় তিনি এদেশে সুসংবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার কথা বলেন। কিন্তু কোম্পানি সরকার এটি গ্রাহ্য করেনি।
লর্ড ওয়েলেসলি কেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
লর্ড ওয়েলেসলি 1800 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য –
তাঁর উদ্দেশ্য ছিল – ভারতে চাকরি করতে আসা ইউরোপীয়দের ভালো করে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর জন্য তিনি তাদের ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা দিতে চেয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।
কী কী কারণে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে?
ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনার পর ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ও প্রসার ঘটে।
ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের কারণ –
- খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটানো – খ্রিস্টান মিশনারিরা ভারতে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটানোর জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে উদ্যোগী হয়।
- প্রশাসনিক সুবিধা – ব্রিটিশ সরকার পাশ্চাত্য বা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মচারী তৈরি করে প্রশাসনিক সুবিধা লাভ করার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটায়।
ইভানজেলিস্ট কাদের বলা হয়?
ভারতবর্ষে প্রথম ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে প্রকৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেন খ্রিস্টান মিশনারিরা। বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মিশনারিরা এদেশে এসে বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।
ইভানজেলিস্ট –
ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি যে কয়েকজন খ্রিস্টান মিশনারি শিক্ষাবিদ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তারা হলেন – চার্লস গ্রান্ট, উইলবার ফোর্স প্রমুখ। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের পাশাপাশি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা দূরীকরণের কথাও তারা প্রচার করেন। এদেরকেই ইভানজেলিস্ট বলা হয়।
পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে আলেকজান্ডার ডাফ -এর উদ্যোগ উল্লেখ করো।
উনিশ শতকে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে আলেকজান্ডার ডাফ -এর উদ্যোগ –
স্কটিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ-এর উদ্যোগে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন (1830 খ্রিস্টাব্দ)। পরবর্তীকালে, 1835 খ্রিস্টাব্দে এটি ‘স্কটিশ চার্চ কলেজ’ নামে পরিচিতি লাভ করে। উল্লেখ্য, ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য 1830-1857 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় ‘ডাফের যুগ’ নামে পরিচিত ছিল।
জেসুইট মিশনারিদের উদ্যোগে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম লেখো।
বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হলেও কোম্পানি সরকার এদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়ায় এদেশে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ঘটতে পারে। এর ফলে প্রথম দিকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত মিশনারিদের উদ্যোগেই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটে।
জেসুইট মিশনারিদের উদ্যোগে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ –
জেসুইট মিশনারিদের উদ্যোগে 1835 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ‘সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ’ এবং 1842 খ্রিস্টাব্দে ‘লরেটো হাউস স্কুল’ প্রতিষ্ঠিত হয়।
চুঁইয়ে পড়া নীতি বা Filtration Theory বলতে কী বোঝায়?
চুঁইয়ে পড়া নীতি বা Filtration Theory –
পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সূচনায় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বাংলার উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটানো হলে ওই উচ্চশিক্ষিত লোকেরা সাধারণ জনগণের মধ্যেও তার বিস্তার ঘটাবে। ফিলটারের জল যেমন উপর থেকে পরিশ্রুত হয়ে চুঁইয়ে নীচে নামে, তেমনই সমাজের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে শিক্ষাবিস্তারের এই নীতিকেই চুঁইয়ে পড়া নীতি বা Filtration Theory বলা হয়ে থাকে।
1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের দুটি গুরুত্বের কথা উল্লেখ করো।
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হওয়া 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের দুটি গুরুত্ব –
- অর্থ বরাদ্দ – এই সনদ আইনে প্রথম ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক 1 লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।
- জনশিক্ষা – ভারতীয়দের শিক্ষার অর্থাৎ জনশিক্ষার দায়িত্ব কোম্পানি সরকারের – এ কথা স্বীকৃত হয়। দেরিতে হলেও কোম্পানি সরকারকে জনশিক্ষার দায়িত্ব নিতে হয়। বরাদ্দ টাকা পাওয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিষয়ক দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।
কে, কবে জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন প্রতিষ্ঠা করেন?
1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে কোম্পানি সরকার জনশিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করতে পারেনি। শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার এই কমিটি গঠন করে।
জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন প্রতিষ্ঠা –
- প্রতিষ্ঠাতা – বড়োলাট লর্ড হেস্টিংস এই কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন।
- প্রতিষ্ঠাকাল – 1823 খ্রিস্টাব্দে এই কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারিভাবে শিক্ষা প্রবর্তনের সূচনা না-হওয়া পর্যন্ত এই কমিটি এদেশে শিক্ষার দায়িত্বে ছিল।
1823 খ্রিস্টাব্দে জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা জনশিক্ষা কমিটি কেন গঠিত হয়?
অথবা, জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
1823 খ্রিস্টাব্দে জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা জনশিক্ষা কমিটি গঠিত হয়।
জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠনের উদ্দেশ্য
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-শাসিত তৎকালীন ভারতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা।
- শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নের জন্য কী কী করা উচিত সে বিষয়ে সুপারিশ করা।
প্রাচ্যবাদী (Orientalist) ও পাশ্চাত্যবাদী (Anglicist) কাদের বলা হয়?
1813 খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট বা সনদ আইনে বলা হয়, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বছরে 1 লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। এই অর্থ কোন্ শিক্ষাখাতে ব্যয় হবে তা নিয়ে জনশিক্ষা কমিটির সদস্যরা দু-ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল –
- প্রাচ্যবাদী ও
- পাশ্চাত্যবাদী।
- প্রাচ্যবাদী – এইচ টি প্রিন্সেপ, কোলব্রুক প্রমুখ যাঁরা প্রাচ্য বা প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষাখাতে সরকারি অর্থ ব্যয় করার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের প্রাচ্যবাদী বলা হয়।
- পাশ্চাত্যবাদী – আলেকজান্ডার ডাফ, স্যান্ডার্স প্রমুখ যাঁরা পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয় ও ইংরেজি শিক্ষাখাতে সরকারি অর্থ ব্যয় করার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের পাশ্চাত্যবাদী বলা হয়।
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব কী?
1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক 1 লক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষা –
এই সময় এদেশে দু-ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। যেমন –
- সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষা নিয়ে প্রাচ্য শিক্ষা এবং
- ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা।
প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব –
জেমস প্রিন্সেপ প্রমুখ প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষে এবং ট্রেভেলিয়ান প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। সরকার কর্তৃক বরাদ্দ 1 লক্ষ টাকা কোন্ খাতে ব্যয় করা হবে তা নিয়ে এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে (1813-1835 খ্রিস্টাব্দ), একে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব বলে। মেকলের মন্তব্যে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।
মেকলে মিনিট কী?
অথবা, মেকলে প্রস্তাব কী?
মেকলে মিনিট –
থমাস ব্যাবিংটন মেকলে ছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিষ্কের আইনসচিব ও জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা জনশিক্ষা কমিটির সভাপতি। মেকলে ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক। তিনি 1835 খ্রিস্টাব্দের 2 ফেব্রুয়ারি গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিষ্কের কাছে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের পক্ষে যে মিনিট বা প্রস্তাব পেশ করেন, তাকে মেকলে মিনিট বা মেকলে প্রস্তাব বলা হয় মেকলের প্রস্তাব দ্বারা ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব’ -এর অবসান ঘটে।
কে, কবে ইংরেজি ভাষাকে ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেন? এর গুরুত্ব কী?
লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক 1835 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষাকে ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেন।
ইংরেজি ভাষাকে ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণার গুরুত্ব –
- এর ফলে সরকারি প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির জয়যাত্রা শুরু হয় এবং ভারতবাসী পাশ্চাত্য সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়।
- ইংরেজি ভাষা পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ঘোষিত হওয়ার ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যবাদী বিতর্কের অবসান ঘটে।
বেন্টিঙ্ক ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর গড়ে ওঠা কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম লেখো।
লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের সমর্থক ছিলেন। অবশেষে 1835 খ্রিস্টাব্দে বড়োলাটের পরিষদ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের পক্ষে সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির জয়যাত্রা শুরু হয়।
লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ –
বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল – কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, বোম্বাই এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি।
কাউন্সিল অফ এডুকেশন কী?
ভারতে উনিশ শতকে কোম্পানির আমলে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের উদ্যোগ শুরু হয়। মূলত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে।
কাউন্সিল অফ এডুকেশন –
লর্ড হার্ডিঞ্জ শিক্ষাবিস্তারের জন্য 1842 খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সরকারি চাকরিতে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।
হার্ডিঞ্জের ঘোষণা কী কারণে বিখ্যাত?
1835 খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমলে ভারতে প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়।
হার্ডিঞ্জের ঘোষণা –
1842 খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ শিক্ষাবিস্তারের জন্য কাউন্সিল অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঘোষণা করেন যে, সরকারি চাকরিতে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই ঘোষণার ফলে ভারতীয়রা ইংরেজি ভাষা শিক্ষালাভ করতে অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম হয়।
পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে বেসরকারি উদ্যোগী কারা ছিলেন?
বেসরকারি উদ্যোগীরাই প্রথম এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে এগিয়ে আসে।
পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে বেসরকারি উদ্যোগীগণ –
- ইউরোপীয় – শেরবোর্ন, মার্টিন বাউল, ডেভিড ড্রুমন্ড প্রমুখ ইউরোপীয়রা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার করেন।
- মিশনারি – ব্যাপটিস্ট মিশন, স্কটিশ মিশন, লন্ডন মিশনারি, জেসুইট মিশন, ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রভৃতি সংস্থার মিশনারিরাও এক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন।
- মনীষী – ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, বেথুন সাহেব, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।
পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে বেসরকারি উদ্যোগীর অবদান –
এইসব বেসরকারি উদ্যোগীদের চেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে।
শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা ছিলেন?
হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও শিক্ষাবিস্তারের কাজ শুরু করে।
শ্রীরামপুর ত্রয়ী –
উইলিয়ম কেরি, ফ্রাঁসোয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড – এই তিনজন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এঁদের একত্রে বলা হয় শ্রীরামপুর ত্রয়ী।
শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান –
এঁরা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, দিগদর্শন ও সমাচার দর্পণ পত্রিকা প্রকাশ, 26টি আঞ্চলিক ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং একাধিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।
কবে, কারা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?
বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা –
- প্রতিষ্ঠাতা – হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্ট ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এই কাজে সহযোগিতা করেন ডেভিড হেয়ার এবং রাজা রাধাকান্ত দেব। শোনা যায়, রাজা রামমোহন রায়ও এ ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন।
- প্রতিষ্ঠাকাল – 1817 খ্রিস্টাব্দের 20 জানুয়ারি এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের নামের তালিকায় রাজা রামমোহন অনুপস্থিত কেন?
1817 খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার, স্যার হাইড ইস্টের উদ্যোগে যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে রাজা রামমোহন রায়েরও সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। কিন্তু কয়েকজন গোঁড়া হিন্দুনেতা যখন জানতে পারেন যে, রামমোহন এর সঙ্গে জড়িত, তখন তারা রামমোহনকে বিদ্যালয় কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। এই অবস্থায় রামমোহন নিজেই কমিটি থেকে সরে গিয়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেন। এ কারণে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের নামের তালিকায় রাজা রামমোহন অনুপস্থিত।
কে, কেন ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন?
অথবা, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?
1817 খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার কলকাতায় ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।
ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য –
- ভালো পাঠ্যবই প্রকাশ করা – ডেভিড হেয়ার ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় ভালো পাঠ্যবই রচনা করার জন্য এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।
- শিক্ষার প্রসার ঘটানো – তিনি অল্প দামে বই বিক্রি করে, আবার কখনও বিনামূল্যে বই বিতরণ করে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হন।
কারা, কেন ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন?
বেসরকারি উদ্যোগে যেসব স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলি ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। মফস্সল অঞ্চলে আরও স্কুল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে 1818 খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি সমিতি প্রতিষ্ঠা –
- প্রতিষ্ঠাতা – ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।
- কারণ – মফস্সলে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।
উড -এর ডেসপ্যাচ কী?
অথবা, উডের নির্দেশনামার দুটি সুপারিশ উল্লেখ করো।
বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড 1854 খ্রিস্টাব্দে ভারতের শিক্ষাবিষয়ক নির্দেশনামা বা ডেসপ্যাচ জারি করেন।
নির্দেশনামা বা ডেসপ্যাচ –
- ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে (কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই) তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে।
- শিক্ষক-শিক্ষণ, ছাত্রদের মেধা অনুযায়ী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হবে।
- প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে।
- নারীশিক্ষাকে প্রসারিত করতে হবে ইত্যাদি।
উডের নির্দেশনামার গুরুত্ব –
ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে এই নির্দেশনামা ছিল একটি মহাসনদ বা ম্যাগনাকার্টা।
কবে, কেন উড -এর নির্দেশনামা জারি হয়?
ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে চার্লস উড -এর নির্দেশনামা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
উড -এর নির্দেশনামা জারি –
- সময়কাল – 1854 খ্রিস্টাব্দে উড -এর নির্দেশনামা জারি হয়।
- কারণ – বিভিন্ন স্কুল, কলেজের পাঠ্যক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, ভারতে শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তোলা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে উড -এর নির্দেশনামা জারি করা হয়।
উডের নির্দেশনামার গুরুত্ব –
ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে এই নির্দেশনামাকে বলা হয় ম্যাগনাকার্টা বা মহাসনদ।
উডের ডেসপ্যাচকে মহাসনদ বলা হয় কেন?
অথবা, উডের ডেসপ্যাচ কী? একে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ম্যাগনাকার্টা বলা হয় কেন?
বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য 1854 খ্রিস্টাব্দের 19 শে জুলাই একটি নির্দেশনামা প্রকাশ করেন, যা চার্লস উডের প্রতিবেদন নামে খ্যাত।
উডের ডেসপ্যাচকে ‘মহাসনদ’ বলার কারণ –
- উডের রিপোর্টের আগে পর্যন্ত ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার গতি ছিল অত্যন্ত ধীর। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বহু স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাই ইংল্যান্ডের ম্যাগনাকার্টা বা মহাসনদের অনুকরণে উডের
ডেসপ্যাচকে ‘মহাসনদ’ বা ‘ম্যাগনাকার্টা’ বলা হয়।
উডের সুপারিশ অনুযায়ী কবে, কোথায় কোথায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়?
বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড 1854 খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাবিষয়ক এক নির্দেশনামা জারি করেন, যা উডের প্রতিবেদন নামে পরিচিত।
উডের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ –
উডের সুপারিশ অনুযায়ী 1857 খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষা অধিকর্তা পদও সৃষ্টি করা হয়।
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন – এ (1904 খ্রিস্টাব্দ) কী বলা হয়েছিল?
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (1904 খ্রিস্টাব্দ) –
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা ও সম্ভাবনা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়েছিল সেই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে 1904 খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন রচিত হয়। এতে বলা হয় –
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সিনেটে সরকারের মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
- কলেজগুলি পরিদর্শন করা হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশকিছু সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে।
কবে স্যাডলার কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল? এই কমিশন অপর কী নামে পরিচিত হয়?
স্যাডলার কমিশন –
1917 খ্রিস্টাব্দে ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও উচ্চশিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্রিটিশ সরকার স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশন স্যাডলার কমিশন নামে পরিচিত। স্যাডলার কমিশনের দুই জন ভারতীয় সদস্য হলেন – স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ। এই কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নামেও পরিচিত হয়।
স্যাডলার কমিশনের দুটি সুপারিশ লেখো।
উনিশ শতকে ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে যেসকল উন্নয়নমূলক সংস্কার প্রবর্তিত হয় তা বিশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ বিষয়ে স্যাডলার কমিশনের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
স্যাডলার কমিশনের দুটি সুপারিশ –
1917 খ্রিস্টাব্দে স্যাডলার কমিশন নিযুক্ত হয় এবং 1919 খ্রিস্টাব্দে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। এখানে বলা হয় –
- স্নাতক স্তরের শিক্ষার সময়সীমা হবে তিনবছর।
- স্যাডলার কমিশন বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার সময়সীমা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার সময়ের মাঝে দু-বছরের জন্য ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার সুপারিশ করে। এই কমিশনে স্বশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও বেশি উৎসাহদানের কথা বলা হয়।
বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নিয়েছিল এমন কয়েকটি সংগঠনের নাম লেখো।
উনিশ শতকে খ্রিস্টান মিশনারিদের সক্রিয় উদ্যোগে বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে গতি বৃদ্ধি হয়।
নারীশিক্ষা প্রসারে কতগুলি উল্লেখযোগ্য সংগঠন –
- ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি – ইংল্যান্ডের মিশনারিদের উদ্যোগে 1819 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি।
- কলকাতা স্কুল সোসাইটি – বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে অপর একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন হল কলকাতা স্কুল সোসাইটি।
ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি কী?
বাংলা প্রদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে খ্রিস্টান মিশনারিরা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।
ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি –
ইংল্যান্ডের মিশনারিরা 1819 খ্রিস্টাব্দে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় বালিকাদের শিক্ষাদান ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমিতির উদ্যোগে 6 বছরে প্রায় 6টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
কয়েকজন বিদেশিনীর নাম লেখো যারা বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে কাজ করেছেন?
উনিশ শতকের বাংলায় ইউরোপীয় উদ্যোগে নারীশিক্ষার সূচনা হয় এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় আলোড়ন ঘটে।
বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে যে বিদেশিনীরা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন – মেরি কার্পেন্টার, মিস কুক, মিস ব্রিটন প্রমুখ।
বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে রাজা রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে রাজা রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
নারীশিক্ষা প্রসারে প্রচেষ্টা –
নারীশিক্ষা প্রসারে রাধাকান্ত দেব আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন।
- তিনি 1812 খ্রিস্টাব্দে ‘স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে প্রমাণ করেন যে, নারীশিক্ষা হিন্দু আদর্শ ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়।
- 1817 খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে ভালো স্কুল পাঠ্য বই তৈরি করার জন্য ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে রাধাকান্ত দেব তার অবৈতনিক সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন।
- 1819 খ্রিস্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি।
ডেভিড হেয়ার স্মরণীয় কেন?
অথবা, পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে ডেভিড হেয়ারের অবদান লেখো।
ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে যেসব বিদেশিরা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে ডেভিড হেয়ারের অবদান –
স্কটল্যান্ডের ঘড়িনির্মাতা ডেভিড হেয়ার এদেশে এসে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হন। তিনি হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন 1817 খ্রিস্টাব্দে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতেও তিনি সাহায্য করেন। স্কুল পাঠ্যবই প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। মফস্সলে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটিও গড়ে তোলেন 1818 খ্রিস্টাব্দে।
কবে, কাদের উদ্যোগে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়? এর বর্তমান নাম কী?
উনিশ শতকের বাংলায় বেসরকারি ও সরকারি উদ্যোগে নারীশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়। সামাজিক কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বাধা কাটিয়ে নারীশিক্ষার প্রসারে গতি আসে।
হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রতিষ্ঠাতা –
1849 খ্রিস্টাব্দের 7 মে জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যৌথ প্রচেষ্টায় কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের বর্তমান নাম –
হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের বর্তমান নাম হল বেথুন স্কুল।
নারীশিক্ষা বিস্তারে বেথুন সাহেবের অবদান লেখো।
ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা বিস্তারে যেসব মনীষী উদ্যোগী হন, জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।
নারীশিক্ষা বিস্তারে বেথুন সাহেবের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা –
মিশনারিদের স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ে ভদ্র হিন্দু বালিকারা যেত না। বেথুন সাহেব এদের জন্য 1849 খ্রিস্টাব্দে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নারীশিক্ষার সপক্ষে সংস্কৃত শ্লোক – লেখা ঘোড়ার গাড়ি বা পালকি করে বালিকাদের আসা-যাওয়ার ব্যবস্থাও করেন।
নারীশিক্ষা বিস্তারে বেথুন সাহেবের অবদান –
21 জন বালিকা-সহ একটিমাত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেও বিদ্যালয়টি আদর্শ হয়ে ওঠে। হিন্দু বালিকাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার দিশারি হয়ে ওঠে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, যা বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত।
নারীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য কী ছিল?
নারীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য –
- নারীমুক্তি – বিদ্যাসাগর লক্ষ করেছিলেন বাংলার সমাজে নারীরা বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত হয়। অত্যাচারের হাত থেকে নারীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হয়েছিলেন।
- সমাজসংস্কার – বিদ্যাসাগর ছিলেন সমাজসংস্কারক। তিনি বুঝেছিলেন নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটলে তবেই সমাজসংস্কার সম্ভব হবে।
কে, কোথায় ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন?
নারীশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বুঝেছিলেন নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমেই একমাত্র নারীমুক্তি সম্ভব।
ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা –
বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ গ্রাম বীরসিংহে 1890 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মা ভগবতী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
রাজা রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্য কী ছিল?
রাজা রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্য –
- মানুষের জাগতিক বিকাশ ও সমাজকল্যাণ – রাজা রামমোহন রায় কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করা তাত্ত্বিক শিক্ষার্থী তৈরি করতে চাননি। তিনি শিক্ষাকে মানুষের জাগতিক বিকাশ ও সমাজকল্যাণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এজন্য প্রয়োজন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী শিক্ষা।
- ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক চেতনার সঞ্চার করা – রাজা রামমোহন রায় ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনের কেরানি তৈরি করার জন্য নয়, ভারতীয়দের মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার করার জন্য। যে চেতনা ভারতীয়দের প্রকৃত মুক্তির পথের সন্ধান দিতে পারবে।
রামমোহনের স্মারকলিপি কী?
রাজা রামমোহন রায় ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। সরকার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হলে রামমোহন একটি স্মারকলিপি দেন।
রামমোহনের স্মারকলিপি –
রামমোহন বড়োলাট লর্ড আমহার্স্টকে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠার কাজ বন্ধ করতে বলেন এবং পরিবর্তে ইংল্যান্ডের মতো গণিত, শারীরবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা ভারতে চালু করার দাবি জানান।
রামমোহনের স্মারকলিপির গুরুত্ব –
রামমোহনের জীবনীকার মিস কলেট -এর কথায় এই স্মারকলিপির ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়।
পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে রামমোহনের ভূমিকা লেখো।
রাজা রামমোহন রায় বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হন এবং অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তিদের সাহায্য করেন।
পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে রামমোহনের ভূমিকা –
- পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে রামমোহনের ব্যক্তিগত উদ্যোগ – তিনি পটলডাঙায় অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল (1822 খ্রিস্টাব্দ) এবং বেদান্ত কলেজ (1825 খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেন।
- পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে রামমোহনের সহায়তা – তিনি ডেভিড হেয়ারকে হেয়ার স্কুল, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতেও তিনি সহায়তা করেন।
রামমোহন রায় কবে, কী উদ্দেশ্যে বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?
উনিশ শতকে ভারতের ধর্ম ও সমাজকে কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে যেসকল মানবতাবাদী সমাজসংস্কারক ভারতবাসীকে আলোর পথ দেখান, রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।
রামমোহনের বেদান্ত কলেজ –
রামমোহন রায় 1825 খ্রিস্টাব্দে বেদান্ত শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত ‘বেদান্তবাদ’ -এর উপর ভিত্তি করেই রামমোহন রায় তাঁর ধর্মপ্রচার ও ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।
রাজা রামমোহন রায়ের দুটি ত্রুটি লেখো।
ভারতীয় সমাজের সংস্কার আন্দোলনে ‘ভারত-পথিক’ রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হলেও তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি।
রাজা রামমোহন রায়ের দুটি ত্রুটি –
- রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, সতীদাহপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তার পরিচয় দিতে পারেননি। আজীবন তিনি ব্রাহ্মণত্বের প্রতীক উপবীত (পৈতা) ধারণ করে গেছেন।
- রামমোহন ভারতীয় কৃষকদের উপর রাজস্বের বোঝা লাঘব করার জন্য সোচ্চার হলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষকদের সর্বনাশ দেখেও তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি।
কারা, কেন রাজা রামমোহন রায়কে আধা উদারপন্থী বলেছেন?
রাজা রামমোহন রায় বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবাসীকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন থেকে মুক্ত করতে পারে যুক্তিনির্ভর পাশ্চাত্য শিক্ষা। তিনি প্রাচ্যের মহান চিন্তাধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁকে সমন্বয়বাদীও বলা হয়ে থাকে।
নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী এই সমন্বয়বাদকে ভালো চোখে দেখেনি, তাই তাঁরা রামমোহন রায়কে ‘আধা উদারপন্থী’ বলে সমালোচনা করেছেন।
চিকিৎসাবিদ্যার বিকাশে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব লেখো।
ভারতে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ -এর প্রতিষ্ঠা ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা।
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা ও বিকাশ –
মেডিক্যাল কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষায় 100 জন ছাত্র অংশ নেয়। পরীক্ষার পর 49 জন ভরতি হয়। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত প্রথম ভারতীয় হিসেবে শবব্যবচ্ছেদ করেন। জনসেবার জন্য শল্যচিকিৎসক পদে অনেক ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হয়।
চিকিৎসাবিদ্যার বিকাশে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব –
এই মেডিক্যাল কলেজ থেকে ভারতীয় ছাত্ররা MRCS, FRCS, MD ইত্যাদি ডিগ্রি অর্জন করে। কলেজটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে।
MRCS -এর পুরো কথা কী? কবে, কোন্ দুজন বাঙালি ডাক্তার সর্বপ্রথম MRCS ডিগ্রি লাভ করেন?
উনিশ শতকে ভারতবর্ষে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা চর্চার এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করে বহু ছাত্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসকের কাজে যুক্ত হন।
- MRCS -এর পুরো কথা হল – Member of the Royal College of Surgeons.
- ভোলানাথ বসু ও গোপালচন্দ্র শীল নামে দুই বাঙালি ডাক্তার সর্বপ্রথম MRCS ডিগ্রি লাভ করেন।
মধুসূদন গুপ্ত কে ছিলেন?
অথবা, মধুসূদন গুপ্ত স্মরণীয় কেন?
ভারতের আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে মধুসূদন গুপ্ত একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।
মধুসূদন গুপ্তের জন্ম –
মধুসূদন গুপ্ত 1800 খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার বৈদ্যবাটীতে জন্মগ্রহণ করেন।
মধুসূদন গুপ্তের অবদান –
তৎকালীন পরিস্থিতিতে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তথা সমাজে পতিত হওয়ার ভয়ে কোনও ছাত্র শবব্যবচ্ছেদে এগিয়ে আসতেন না। কিন্তু 1836 খ্রিস্টাব্দের 28 অক্টোবর রাজকৃষ্ণ দে, উমাচরণ শেঠ-সহ আরও কয়েকজনের সহায়তায় মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন। এই উপলক্ষ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে তোপধ্বনির মাধ্যমে মধুসূদনকে অভিনন্দন জানানো হয়। মধুসূদন গুপ্তের কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ হল – বাংলায় লেখা ‘London Pharmacopoeia’ এবং সংস্কৃতে লেখা ‘Anatomist Vade Mecum’ প্রভৃতি।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য –
1857 খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বিবিধ।
- বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা – চার্লস উডের প্রতিবেদনে (1854 খ্রিস্টাব্দ) প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে উচ্চশিক্ষার জন্য একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। সেইমতো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কলকাতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- কলেজ অনুমোদন, পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি প্রদান – বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় কলেজ অনুমোদন, পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি প্রদান করা ইত্যাদির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন গোলদিঘির গোলামখানা বলা হত?
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হল ভারতের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং -এর আমলে 1857 খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলদিঘির গোলামখানা বলার কারণ –
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল গোলদিঘির কাছে। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করে ছাত্ররা মূলত সরকারি অফিস-আদালতে কেরানির কাজ করত। তাই অনেকেই ব্যঙ্গ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘গোলদিঘির গোলামখানা’ বলে ডাকত।
উচ্চশিক্ষার বিকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান লেখো।
উডের নির্দেশনামা অনুসারে 1857 খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বিকাশ –
প্রথমদিকে অধীনস্থ স্কুল, কলেজগুলির পরীক্ষাগ্রহণ ও ফলপ্রকাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল। পরে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পঠনপাঠন ও গবেষণার কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন বিভাগও খোলা হয় এবং নারীরা পড়াশোনার সুযোগ পায়।
উচ্চশিক্ষার বিকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান –
উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবিস্তারের কাজ করে।
কাদম্বিনী গাঙ্গুলি স্মরণীয় কেন?
উনিশ শতকের প্রথম দিকে নারীরা বেশিরভাগই ছিলেন নিরক্ষর। এরপর মিশনারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে নারীশিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে, ফলে নারীশিক্ষায় গতি আসে।
কাদম্বিনী গাঙ্গুলি স্মরণীয় হওয়ার কারণ –
1882 খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতক হন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। এ ছাড়া তিনি ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হওয়া প্রথম ভারতীয় ছাত্রী। এ কারণে তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়।
উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির প্রধান লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
উনিশ শতকের বাংলায় সমাজসংস্কার আন্দোলনে জোয়ার এসেছিল।
উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য –
- যুক্তিবাদের বিস্তার – উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণার অবসান ঘটিয়ে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিস্তার ঘটানো।
- নারীকল্যাণ – সমাজে নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণসাধনের জন্য আন্দোলন পরিচালনা।
উনিশ শতকের বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
উনিশ শতকের বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য –
উনিশ শতকের বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল –
- নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন – উনিশ শতকের বাংলার সমাজসংস্কারকরা সমাজে নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন করেছিলেন।
- সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন – তৎকালীন সমাজে সতীদাহপ্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। সমাজসংস্কারকরা এইসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন।
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
রাজা রামমোহন রায় 1828 খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হয়।
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য –
- এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা করা।
- বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
- হিন্দুধর্মের নামে যেসব কুসংস্কার ও অন্যায়-অবিচার প্রচলিত ছিল তা উচ্ছেদ করা।
ঊনবিংশ শতকে ব্রাহ্মদের উদ্যোগে সমাজসংস্কারের বিষয়ে লেখো।
রাজা রামমোহন রায় সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে 1830 খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
ঊনবিংশ শতকে ব্রাহ্মদের উদ্যোগে সমাজসংস্কার –
- সতীদাহপ্রথা রদ – হিন্দুসমাজের সতীদাহপ্রথা দূর করার জন্য রামমোহন আন্দোলন করেন। তাঁর আন্দোলনের ফলে বড়োলাট বেন্টিঙ্ক সপ্তদশ বিধি জারি করে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করেন।
- নারীশিক্ষা বিস্তার – ব্রাহ্মদের চেষ্টায় ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীশিক্ষায় উৎসাহদানের জন্য বামাবোধিনী, অবলাবান্ধব ইত্যাদি পত্রিকাও প্রকাশ করতেন ব্রাহ্মরা।
ব্রাহ্মসমাজের যে-কোনো দুটি সমাজসংস্কারমূলক কাজের উল্লেখ করো।
রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ সেযুগে সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল।
ব্রাহ্মসমাজের যে-কোনো দুটি সমাজসংস্কার কর্মসূচি –
- ব্রাহ্মসমাজ নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার দাবি জানায়; বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার দাবি তোলে এবং অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রচলনের কথা বলে।
- জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, শ্রমিক কল্যাণ ও শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা করেন ব্রাহ্মরা। তাঁদের চেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছিল।
সতীদাহপ্রথা কী?
সতীদাহপ্রথা –
পূর্বে হিন্দুসমাজে সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ বলতে বোঝায় মৃত স্বামীর শব দাহ করার সময় একই চিতায় তার বিধবা স্ত্রীকে দাহ করা। একে সহমরণ প্রথাও বলা হয়।
সতীদাহপ্রথা রদ –
রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় 1829 খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।
উনিশ শতকের বাংলাদেশে সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলনের পরিচয় দাও।
ভারতে হিন্দুসমাজের প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত একটি কুপ্রথা ছিল সতীদাহ।
উনিশ শতকের বাংলাদেশে সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলন –
- মিশনারিরা এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালায়।
- ইউরোপীয় বণিকেরা তাদের বাণিজ্য এলাকায় সতীদাহ নিষিদ্ধ করে।
- রাজা রামমোহন রায় পুস্তিকা প্রকাশ করে, সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায় প্রতিবেদন লিখে জনমত গঠন করেন। তারপর বড়োলাট উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক -এর কাছে সতীদাহপ্রথা বন্ধের আবেদন জানান।
উনিশ শতকের বাংলাদেশে সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলনের পরিণতি –
বাস্তব পরিস্থিতি, উদার ও মানবতাবাদী নব্য ধারা, রামমোহনের আবেদন ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বড়োেলাট উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক 1829 খ্রিস্টাব্দে সপ্তদশ বিধি জারি করে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করেন।
নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী কাদের বলা হত?
নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী –
পোর্তুগিজ বংশোদ্ভূত তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। ডিরোজিওর অনুগামীদের নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল বলা হত। তাঁদের আন্দোলন নব্যবঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত। নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর কয়েকজন সদস্য হলেন রামতনু লাহিড়ি, রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ।
নব্যবঙ্গ আন্দোলনের দুজন নেতার নাম উল্লেখ করো।
ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে হিন্দু কলেজে এক ছাত্রগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই ছাত্রগোষ্ঠী নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত ছিল।
নব্যবঙ্গ আন্দোলনের দুজন নেতা –
এই নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীতে অনেকে ছিলেন। এঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন – দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক।
নব্যবঙ্গ আন্দোলনের গুরুত্ব –
বাংলাদেশের জরাজীর্ণ রক্ষণশীল সমাজে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী প্রবল আঘাত করে। সামাজিক কুপ্রথার বিরোধিতা করে নতুন সমাজ গঠনের চেষ্টা করে এই গোষ্ঠী।
ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের কীভাবে যুক্তিবাদী করে তোলেন?
হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর অনুগামীরা নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী নামে পরিচিত।
ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের যুক্তিবাদী করে তোলার প্রয়াস –
- যুক্তিবাদের শিক্ষা – তিনি তাঁর ছাত্রদের বিনা বিচারে কোনো কিছু মেনে না নেওয়ার কথা বলেন।
- অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা – ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটাতে ডিরোজিও 1828 খ্রিস্টাব্দে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন।
অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও তৎকালীন হিন্দুসমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর তরুণ অনুগামীরা ইয়ং বেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী নামে পরিচিত।
অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা –
ডিরোজিও 1828 খ্রিস্টাব্দে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গঠন করে হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অনুগামী যারা তাদের উৎসাহিত করেন। এই সভায় তাঁর ছাত্ররা ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করত এবং ভাগ্য, সত্য, মূর্তিপূজা নিয়ে বিতর্ক হত।
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা কী?
ডিরোজিওর প্রভাবে তরুণ ছাত্রদল বা নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী উগ্র মানসিকতা নিয়ে ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা –
ডিরোজিওর অনুগামী নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর সদস্যরা 1838 খ্রিস্টাব্দে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা নামক একটি সংগঠন স্থাপন করে খ্রিস্টান পাদরিদের গোঁড়ামি, দাসপ্রথা, নারী নির্যাতন – প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনার প্রতিবাদ জানান।
ডিরোজিও কেন কর্মচ্যুত হন?
হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে হিন্দু কলেজে এক ছাত্রগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যারা নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত ছিল।
ডিরোজিও কর্মচ্যুত হওয়ার কারণ –
পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজ থেকে তিনি কর্মচ্যুত হন, এর পিছনে বেশ কিছু কারণ ছিল –
- ডিরোজিওর নেতৃত্বে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার জন্ম হয়।
- বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজ, কুপ্রথা প্রভৃতির সমালোচনা করে তিনি রক্ষণশীলদের বিরাগভাজন হন।
- ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় তাঁর অনুগামীরা হিন্দুসমাজের প্রথাগত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করতে থাকলে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠী ডিরোজিওর বিরোধিতা করে নালিশ জানালে তিনি কর্মচ্যুত হন।
নব্যবঙ্গ আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয়?
অথবা, নব্যবঙ্গ আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা লেখো।
হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে যে অনুগত ছাত্রগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, তারা নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী নামে পরিচিত।
নব্যবঙ্গ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ –
- আন্দোলনকারীদের কোনো গঠনমূলক কর্মসূচি ছিল না এবং আন্দোলনকারীদের চিন্তাধারা ছিল নেতিবাচক।
- তাঁদের আন্দোলনের পিছনে জনসমর্থন ছিল না। ও কৃষক-শ্রমিক ও মুসলিমদের নিয়ে তাঁরা ভাবেননি।
- ডিরোজিওর মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব ঘটে।
নব্যবঙ্গ আন্দোলনের অবদান লেখো।
অথবা, সমাজসংস্কারে নব্যবঙ্গদের ভূমিকা কী ছিল?
উনিশ শতকের বাংলার সমাজে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর আবির্ভাব ও কার্যকলাপ বিতর্কিত হলেও এঁদের অবদান অস্বীকার করা যায় না।
নব্যবঙ্গ আন্দোলনের অবদান –
- এই গোষ্ঠীর সদস্যদের আধুনিক মানসিকতা ও উচ্চ আদর্শ ছিল।
- হিন্দুসমাজের কুপ্রথাগুলির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং যুক্তির আলোয় সনাতন রীতিনীতিকে যাচাই করার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা।
- তাঁরা নারী-পুরুষের সমানাধিকার, নারীনির্যাতন, নারীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, দাসপ্রথা, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ বিধি, একচেটিয়া বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনাতেও মতপ্রকাশ করেন।
অনেকে তাঁদের কালাপাহাড়, উচ্ছৃঙ্খল ও সমাজবিচ্ছিন্ন উগ্রগোষ্ঠী; আবার কেউ কেউ তাঁদের কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া, আলোর ঝলক ও দেশের ভবিষ্যৎ বলে উল্লেখ করেছেন।
নব্যবঙ্গ আন্দোলনের গুরুত্ব কী?
হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর অনুগামীরা নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত।
নব্যবঙ্গ আন্দোলনের গুরুত্ব –
- সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে – সমাজের বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- নবজাগরণের ক্ষেত্রে – নব্যবঙ্গ দলের সত্যানুসন্ধানী মনোভাব, সংস্কারমূলক কার্যাবলি উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণকে সমৃদ্ধ করে।
রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল দলের সমাজসংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?
উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সংস্পর্শে প্রগতিশীল উদারপন্থীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন – রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ।
রামমোহন ও ইয়ংবেওগল দলের সমাজসংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্যের পার্থক্য –
রাজা রামমোহন রায় গঠনমূলক কর্মসূচির ভিত্তিতে সমাজসংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সমর্থক হয়েও হিন্দুধর্মকে তিনি উগ্রভাবে আক্রমণ করেননি।
অন্যদিকে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল প্রচলিত হিন্দুধর্ম। পরবর্তীকালে উগ্র কালাপাহাড়ি মনোভাবের জন্য তাঁরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।
কে, কবে বিধবাবিবাহ আইন পাস করেন?
বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে যে সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়, বিধবাবিবাহ আইন পাস ছিল তার অন্যতম ফল।
বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন –
- আইনপ্রণেতা – ভারতের বড়োলাট লর্ড ক্যানিং বিধবাবিবাহ আইন পাস করেন।
- সময়কাল – 1856 খ্রিস্টাব্দের 26 জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়।
বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা লেখো।
উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে কয়েকজন মনীষী সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু করেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।
বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা –
বিধবাবিবাহের সপক্ষে জনমত গঠনের জন্য বিদ্যাসাগর বিভিন্ন পত্রিকায় (সর্বশুভকরী, তত্ত্ববোধিনী) প্রবন্ধ লেখেন, পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তারপর 1000 জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পেশ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রায় 36,763 স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রতিবাদপত্র সরকারের কাছে পাঠায়। তবুও সরকার বিচারবিবেচনা করে 1856 খ্রিস্টাব্দের 26 জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস করে।
বিদ্যাসাগরকে কে, কেন ‘ট্রাডিশনাল মর্ডানাইজার’ বলেছেন?
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলার ইতিহাসে এক বিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।
বিদ্যাসাগরকে ‘ট্রাডিশনাল মর্ডানাইজার’ বলার কারণ –
প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ‘ট্রাডিশনাল মর্ডানাইজার’ (Traditional Moderniser) বলে অভিহিত করেছেন। কারণ –
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বিধবাবিবাহ প্রচলন। তিনি পুরাণ, পরাশর সংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বিধবাদের পুনরায় বিবাহের কথা প্রচার করেছিলেন।
- পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রামমোহন রায়ের দেখানো পথেই সামাজিক কুসংস্কার ও বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যান।
এসকল কারণে বিদ্যাসাগরকে ‘ট্রাডিশনাল মর্ডানাইজার’ বলা হয়।
কাকে বাংলার আধুনিক গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়?
উনিশ শতকে ভারতে শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ইতিহাসে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব।
বাংলার আধুনিক গদ্য সাহিত্যের জনক –
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ‘আধুনিক গদ্যসাহিত্যের জনক’ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ –
- বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা – বিদ্যাসাগর বেশ কিছু গদ্যসাহিত্য রচনা করে বাংলা ভাষায় জনশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নেন। বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, অনুবাদ গ্রন্থ শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি।
- বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অবদান – বাংলা ভাষাকে রক্ষণশীলতার বেড়াজাল থেকে বের করে এনে তিনি সরল ও সাবলীল করে তোলেন।
এসকল কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ‘আধুনিক গদ্য সাহিত্যের জনক’ বলা হয়।
হাজি মহম্মদ মহসিন বিখ্যাত কেন?
হাজি মহম্মদ মহসিন –
হাজি মহম্মদ মহসিন ছিলেন বাংলার একজন ধর্মপ্রাণ ও মহান জনহিতৈষী ব্যক্তি। মহম্মদ মহসিন তাঁর বিশাল সম্পত্তি বিভিন্ন সৎ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেন। তাঁর অর্থে অনেক স্কুল, মসজিদ, হাসপাতাল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর সরকার মহসিন ফান্ড তৈরি করে তাঁর সঞ্চিত অর্থ নানা জনহিতকর কার্যে ব্যয় করে চলেছে।
মহম্মদ মহসিনের দানের অর্থে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম লেখো।
হাজি মহম্মদ মহসিন ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ও জনহিতৈষী ব্যক্তি। মক্কা, মদিনা ইত্যাদি স্থানে হজ করার পর তাঁর নাম হয় মহম্মদ মহসিন।
মহম্মদ মহসিনের দানের অর্থে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ –
মহম্মদ মহসিনের মৃত্যুর পর সরকার ‘মহসিন ফান্ড’ তৈরি করে তাঁর সম্পদ সৎ কাজে খরচের ব্যবস্থা করেন। তাঁর দানের অর্থে ইমামবাড়া হাসপাতাল, হুগলি মহসিন কলেজ, হুগলি মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।
রাজা রামমোহন রায় ‘আত্মীয় সভা’ স্থাপন করেন কেন?
বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় কুসংস্কারে নিমজ্জিত সমাজ ও জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 1815 খ্রিস্টাব্দে তিনি আত্মীয় সভা স্থাপন করেন।
রাজা রামমোহন রায় আত্মীয় সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য –
- ধর্মভাবনার প্রচার – রাজা রামমোহন রায় তাঁর ধর্মভাব ও প্রচারের উদ্দেশ্যে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন।
- কুপ্রথার বিরুদ্ধাচারণ – প্রচলিত কুসংস্কার, মূর্তিপূজার অসারতা, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধাচারণ করাও ছিল আত্মীয় সভা স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।
ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম আন্দোলনে বিভাজন কেন ঘটে?
রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজসংস্কারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন 1830 খ্রিস্টাব্দে। পরে বিভিন্ন কারণে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম আন্দোলনে বিভাজন ঘটে।
ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম আন্দোলন বিভাজনের কারণ –
- উপবীত ধারণ, জাতিভেদ প্রথার প্রশ্নে ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে মতভেদ ও বিভাজন ঘটে (1866 খ্রিস্টাব্দ)।
- এরপর অসবর্ণ বিবাহ, বিবাহের ন্যূনতম বয়স (নারীর) নির্ধারণ, কীর্তনরীতি, খ্রিস্টপ্রীতির প্রশ্নে কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে মতভেদ ও বিভাজন ঘটে (1878 খ্রিস্টাব্দ)।
ব্রাহ্মসমাজে প্রথম বিভাজন কবে এবং কেন হয়?
ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বিভাজন –
1866 খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম বিভাজন দেখা দেয়।
ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বিভাজনের কারণ –
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিভেদ প্রথার বিরোধী হলেও অসবর্ণ বিবাহ ও উপবীত বর্জনের দাবি মানতে পারেননি। ফলে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ বাধে। ফলে 1866 খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্থাপিত হয় আদি ব্রাহ্মসমাজ।
তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বলতে কী বোঝায়?
তত্ত্ববোধিনী সভা –
রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সমাজসংস্কারের আদর্শ ও তত্ত্ব আলোচনার জন্য 1839 খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, রামতনু লাহিড়ি প্রমুখ এই সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন।
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা –
তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই পত্রিকায় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের ন্যায় সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়। বিধবাবিবাহ প্রচলন, নারীশিক্ষা প্রসারে এই পত্রিকা মধ্যবিত্তশ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হল কেন?
অথবা, ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বিভাজন কবে এবং কেন হয়?
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বিভাজন –
কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে কিছুদিন পর থেকেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের মতভেদ সৃষ্টি হয়।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বিভাজনের কারণ –
- কেশবচন্দ্র সেন যুক্তিবাদ থেকে সরে গিয়ে ব্রাহ্মসমাজে গুরুবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন, যা ছিল ব্রাহ্মধর্মের নীতিবিরুদ্ধ।
- ব্রাহ্মসমাজের বিধান উপেক্ষা করে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর 14 বছর বয়সি কন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে কোচবিহারের নাবালক রাজপুত্র নৃপেন্দ্র নারায়ণের বিবাহ দেন।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বিভাজন –
এর ফলশ্রুতিতে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা বিচ্ছিন্ন হয়ে 1878 খ্রিস্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র সেনের গোষ্ঠীর ব্রাহ্মদের নাম হয় নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।
কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করো।
1857 খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে ব্রাহ্ম আন্দোলন গতিশীল হয়। তাঁর আমলে পূর্ববাংলায়, এমনকি বাংলার বাইরে ভারতের অন্যত্র মোট 54টি স্থানে ব্রাহ্মসমাজের শাখা গড়ে ওঠে।
কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিষ্ঠানসমূহ –
রামমোহন রায়ের ধর্ম ও সমাজসংস্কারমূলক চিন্তাকে কার্যকরী করাই ছিল কেশবচন্দ্র সেনের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হল – 1862 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবন্ধু সভা। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজের কর্মসূচি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ ছাড়া কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল – বামাবোধিনী সভা (1863 খ্রিস্টাব্দ), ব্রাত্মিকা সমাজ (1865খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি।
কেশবচন্দ্র সেনের হাত ধরে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন কীভাবে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়?
কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার ফলে ব্রাহ্ম আন্দোলন নবজীবন লাভ করে। 1862 খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে অধিষ্ঠিত করে ‘ব্রহ্মানন্দ’ উপাধিতে ভূষিত করেন।
কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে ছড়িয়ে পড়ে। 1865 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় 50টি ও সারা ভারতে মোট 54টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়।
তিন আইন কী?
উনিশ শতকে বাংলায় সমাজসংস্কার আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ -এর আন্দোলন এসময় বিশেষ সাফল্যলাভ করেছিল। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়।
তিন আইন –
- কেশবচন্দ্র সেনের সক্রিয় আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার 1872 খ্রিস্টাব্দে একটি আইন পাস করে। এটি তিন আইন নামে পরিচিত।
- এই আইন পাসের ফলে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের কুসংস্কারগুলি বিলুপ্ত হতে থাকে এবং মহিলা ও সাধারণ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র সেনের অবদান কী ছিল?
ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র সেনের অবদান –
চারিত্রিক স্ববিরোধিতা এবং একনায়কতন্ত্রের প্রতি আসক্তি থাকলেও ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র সেনের অবদান অবিস্মরণীয়।
- প্রথমত – তিনিই প্রথম ব্রাহ্মধর্মকে বাংলার বাইরে প্রচার করে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে সাহায্য করেছিলেন।
- দ্বিতীয়ত – কেশবচন্দ্র সেন মানুষের সমস্ত আচার-আচরণকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত হতে শিখিয়েছিলেন, যা তরুণ প্রজন্মকে চিন্তায় ও কর্মে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে অনুপ্রেরণা দান করেছিল।
- তৃতীয়ত – কেশবচন্দ্র সেনের নারীমুক্তি ও স্বাধীনতার আদর্শ পরবর্তী প্রজন্মকে সচেতন করেছিল।
শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় -এর আদর্শ কীরকম ছিল?
বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী সর্বধর্মসমন্বয় -এর আদর্শ তুলে ধরে।
শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় -এর আদর্শ –
রামকৃষ্ণদেব সব ধর্ম ও সাধনপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি বলেন, “যত মত তত পথ”। অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে সত্য আছে। প্রত্যেক ধর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।
রামকৃষ্ণদেবের ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সহনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।
স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কারের অভিমুখ কীরূপ ছিল?
স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কারের অভিমুখ –
প্রচলিত মত থেকে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কারের অভিমুখ ছিল ভিন্ন। ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।” তিনি বলেছেন, পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করো, তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। ধর্ম মানে শুধু মতবাদ নয়, ধর্ম মানে সাধনা। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা – এই দুয়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম নিহিত। তিনি বলেছেন, “জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।”
কত খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দেন? এই সম্মেলনে তিনি কী বাণী প্রচার করেন?
1893 খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন।
স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসম্মেলনের বাণী –
- বেদান্তের প্রচার – স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম মহাসভায় বেদান্তের মহিমা ও মানবতার বাণী প্রচার করেন।
- সৌভ্রাতৃত্ববোধ – হিন্দুধর্মের মহত্ব প্রচারের পাশাপাশি তিনি সমগ্র আমেরিকাবাসীকে স্নেহের ভাই ও বোন সম্বোধন করে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছিলেন।
স্বামী বিবেকানন্দের নব্য বেদান্তবাদ কী?
স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নব্য বেদান্তবাদ।
স্বামী বিবেকানন্দের নব্য বেদান্ত –
রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, “যত মত তত পথ” এবং “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”। গুরুদেবের বাণীকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিবেকানন্দ বলেন, “বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে হবে।” এর অর্থ ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে পাশ্চাত্যের কর্মযোগকে যুক্ত করতে হবে। ফলে এক নতুন ভারত গড়ে উঠবে।
স্বামী বিবেকানন্দের লেখা দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।
স্বামীজি ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার একজন উগ্র সমর্থক ছিলেন। বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রভাবে পরবর্তীকালে বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।
স্বামী বিবেকানন্দের লেখা দুটি গ্রন্থসমূহ –
স্বামী বিবেকানন্দের লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হল পরিব্রাজক এবং বর্তমান ভারত।
স্বামী বিবেকানন্দের লেখা দুটি গ্রন্থের প্রভাব –
এই গ্রন্থগুলি ভারতীয় বিপ্লবীদের নিত্যসঙ্গী ছিল। স্বামীজির জাতির প্রতি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জাতীয় চেতনার উন্মেষে এক অমোঘ মন্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল।
ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের মিকেলেঞ্জোলো কাকে, কেন বলা হয়?
ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের মিকেলেঞ্জোলো আখ্যা দিয়েছেন।
ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতের আধ্যাত্মিক জগতের মিকেলেঞ্জোলো বলার কারণ –
ইতালীয় শিল্পী মিকেলেঞ্জোলো যেমন ধ্রুপদি শিল্পরীতি, নব্যপ্লেটোবাদী আদর্শ এবং রেনেসাঁর বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় ঘটান ও জীবনমুখী শিল্প রচনা করেন, সেই রকমই বিবেকানন্দ বিমূর্ত দার্শনিক চিন্তা ও ধর্মীয় তাত্ত্বিক বিচারের সঙ্গে দেশবাসীর বাস্তব সমস্যাকে মিলিয়ে তাঁর চিন্তাধারা গঠন করেছিলেন।
লালন ফকির কেন স্মরণীয়?
লালন ফকির –
লালন ফকির ছিলেন বাউল সাধনার একজন প্রধান গুরু। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বাউলগান রচয়িতা ও গায়ক। প্রায় 2 হাজার গান রচনা করেন তিনি। তাঁর মর্মস্পর্শী গানগুলি মানবজীবনের রহস্য, আদর্শ ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কে ছিলেন? বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নববৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ব্যক্তির নাম লেখো।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য। পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম সাধনায় মগ্ন হন। তিনি যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন তা নব্য বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নববৈষ্ণব আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ –
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নববৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন – বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্মরণীয় কেন?
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী –
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য। তিনি নব্য বৈষ্ণববাদের প্রচারকও ছিলেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রথমে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ প্রচার ও ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তিনি বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তিনি কুসংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল সমাজ গঠনে সচেষ্ট ছিলেন।
উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ বলতে কী বোঝায়?
বাংলার নবজাগরণ –
উনিশ শতকে অবিভক্ত ভারতের বাংলায় বহু মনীষীর আবির্ভাব হয় ও সংস্কারের জোয়ার আসে। একে বাংলার নবজাগরণ বলা হয়। মূলত রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে এই নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। এই নবজাগরণে বাংলার সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কার হয়েছিল এবং সাহিত্য, সাংবাদিকতা, দেশপ্রেম ও বিজ্ঞানচিন্তার অগ্রগতি ঘটেছিল।
ইটালির রেনেসাঁর সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের দুটি সাদৃশ্য লেখো।
মধ্যযুগের তন্দ্রাচ্ছন্নতা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে যেমন ইটালির রেনেসাঁ প্রথম মুক্তির পথ দেখায়, তেমনি ভারতের মধ্যযুগের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণ মুক্তির পথ দেখায়।
ইটালির রেনেসাঁর সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের দুটি সাদৃশ্য –
- ইটালির রেনেসাঁর ফলে ধ্রুপদি সাহিত্যের পুনরায় চর্চা শুরু হয়, বাংলাতেও প্রাচ্যবাদীরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ও মধ্যযুগীয় ফারসি সাহিত্যের চর্চা করেন।
- ইটালির রেনেসাঁর স্বাধীন, অনুসন্ধানী, যুক্তিবাদী মানসিকতা বাংলার ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর আন্দোলনে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।
ইটালির রেনেসাঁর সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের দুটি বৈসাদৃশ্য লেখো।
অনেক ঐতিহাসিকের মতে, বাংলার নবজাগরণকে কখনোই প্রকৃত রেনেসাঁ বলা যায় না। কারণ ইটালির রেনেসাঁর সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের অনেক বৈসাদৃশ্য রয়েছে।
ইটালির রেনেসাঁর সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের দুটি বৈসাদৃশ্য –
- ইটালির ফ্লোরেন্স শহর রেনেসাঁ-কে যেভাবে বরণ করেছিল বাংলার নবজাগরণের কেন্দ্র কলকাতা সেই ভূমিকা পালন করতে পারেনি।
- ফ্লোরেন্সে বুর্জোয়া শ্রেণি যেভাবে শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তার সঙ্গে বাংলার জমিদারদের তুলনা করা চলে না। তা ছাড়া বাংলার নবজাগরণের প্রচারকদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ছিলেন সরকারি কর্মচারী।
বাংলার নবজাগরণ নামকরণ কতটা যথার্থ?
বাংলার নবজাগরণ নামকরণ –
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বাংলায় সমাজজীবন মধ্যযুগীয় তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়। নারীশিক্ষার প্রচলন ও বিধবাবিবাহ চালু হয়, সতীদাহপ্রথা ও অন্যান্য কুপ্রথা দূর হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে।
আচার্য যদুনাথ সরকার, সুশোভন সরকার এই ঘটনাকে বাংলার নবজাগরণ বলেছেন। অন্যদিকে সুমিত সরকার, বরুণ দে, নরহরি কবিরাজ তা মানতে নারাজ। বিতর্ক সত্ত্বেও বলতে হয়, এই ঘটনায় কিছু পরিবর্তন এসেছিল, সমাজজীবন আলোড়িত হয়েছিল এবং মানসিক স্ফুরণ ঘটেছিল। এই নিরিখে সীমিত অর্থে হলেও এই ঘটনাকে নবজাগরণ বলা যায়।
বাংলার নবজাগরণকে কে, কেন এলিটিস্ট আন্দোলন বলেছেন?
উনিশ শতকে অবিভক্ত ভারতের বাংলায় বহু মনীষীর আবির্ভাব হয় ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জোয়ার আসে। একে বাংলার নবজাগরণ বলা হয়। ডঃ অনিল শীল-সহ অনেকেই বাংলার নবজাগরণকে এলিটিস্ট আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন।
এলিটিস্ট আন্দোলন বলার কারণ –
- ডঃ অনিল শীল -এর মতে, এই আন্দোলন মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরা নিজেদের স্বার্থের জন্য ইংরেজ সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকত।
- এরা নিজেদের স্বার্থ উপেক্ষা করে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গলচিন্তা করেনি।
বাংলার নবজাগরণকে কে, কেন তথাকথিত নবজাগরণ বলেছেন?
অশোক মিত্র 1951 খ্রিস্টাব্দে আদমশুমারি বা Census তৈরির সময় বাংলায় উনিশ শতকের জাগরণকে তথাকথিত নবজাগরণ বলে অভিহিত করেছেন।
বাংলার নবজাগরণকে ‘তথাকথিত নবজাগরণ’ বলার কারণ –
অশোক মিত্রের মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে নয়া জমিদার শ্রেণি সাধারণ রায়তদের শোষণ করে যে বিপুল অর্থ লাভ করেছিল তার একটা বিরাট অংশ তারা কলকাতার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করেছিল। এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও যোগ ছিল না। তাই সর্ব অর্থে নবজাগরণ বলতে যা বোঝায় বাংলায় তা ঘটেনি।
বাংলার নবজাগরণের উপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যেসব সাহিত্য প্রভাব ফেলেছিল তা উল্লেখ করো।
বাংলায় নবজাগরণে সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কারের সূচনা হয়েছিল এবং সাহিত্য, সাংবাদিকতা, দেশপ্রেম ও বিজ্ঞানচিন্তার অগ্রগতি ঘটেছিল।
নবজাগরণের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের প্রভাব –
সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে-সকল সাহিত্য বাংলার নবজাগরণকে প্রভাবিত করেছিল, সেগুলি হল – আনন্দমঠ, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, দেবী চৌধুরাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি। দেশবাসীর সামনে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শ প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।
বাংলার নবজাগরণের উপর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যেসব সাহিত্য প্রভাব ফেলেছিল তা উল্লেখ করো।
পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রচলনের পর বাংলাপ্রদেশে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। এই নবজাগরণের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল।
নবজাগরণের উপর শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের প্রভাব –
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত যেসব সাহিত্য বাংলার নবজাগরণের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল, সেগুলি হল – পথের দাবী, শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজ, গৃহদাহ প্রভৃতি।
উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অবদানগুলি কী ছিল?
উনিশ শতকে বাংলায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, তাকে বাংলার নবজাগরণ বলে অভিহিত করা হয়। এই নবজাগরণের উদ্ভব হয়েছিল কলকাতায়।
বাংলার নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ –
- নবজাগরণের ফলে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার পথ প্রশস্ত হয়।
- বাংলার সমাজজীবন মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়। সতীদাহপ্রথা ও অন্যান্য কুপ্রথা দূর হয়।
- নারীশিক্ষার প্রচলন ও বিধবাবিবাহ চালু হয়।
কীভাবে সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ও সাহিত্য থেকে উনিশ শতকের সমাজের প্রতিকলন পাওয়া যায়?
উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের একটি বিশেষ উপাদান হল সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ও সাহিত্য। এগুলিতে সমসাময়িক সমাজের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, কৃষি ও কৃষক, সমাজ ও জাতিবিন্যাসের কথা যেমন জানা যায় তেমনি সমাজের অগ্রগতি ও আধুনিকীকরণের কথাও জানা যায়। ‘বামাবোধিনী নামক সাময়িক পত্রিকা, হিন্দু প্যাট্রিয়ট’-এর মতো সংবাদপত্র, ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ ও ‘নীলদর্পণ’ নামক সাহিত্য থেকে একথা জানা যায়।
বামাবোধিনী পত্রিকা বিখ্যাত কেন?
ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক নারীশিক্ষার প্রসার ও নারী সমাজের উন্নয়ন। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ছিল বামাবোধিনী’ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ (1863 খ্রিস্টাব্দ)। এই পত্রিকায় নারী সমাজের অবস্থা, শিক্ষাগ্রহণ ও তার তাৎপর্য, চাকরিসহ বিভিন্ন পেশায় যোগদান ও তার অভিজ্ঞতা, গৃহচিকিৎসাসহ গৃহপরিচালনার খুঁটিনাটি সম্পর্কিত রচনা প্রকাশিত হত।
স্ত্রীধন কী?
বামাবোধিনী পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, ভারতীয় নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হল স্ত্রীধন এবং এগুলি সাধারণত অলংকার ও পোশাক। বিবাহকালে নারীর ‘পিতৃদত্ত বা পিতার দেওয়া, ‘ভ্রাতৃদত্ত’ বা ভাইয়ের দেওয়া অলংকার ও উপহার ছিল স্ত্রীধনের উৎসস্থল। এছাড়া নারীর মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি স্বামী অথবা পুত্রেরা পেত না, তা পেত তার কন্যা বা কন্যারা।
হিন্দু প্যাট্রিয়ট থেকে বাংলার জনজীবন সম্পর্কে কী জানা যায়?
হিন্দু প্যাট্রিয়ট -এ বাংলার জনগণের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রতিবেদন রচিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসনকালে অর্থকরী ফসল (যেমন – পাট, তুলা, তৈলবীজ, আখ) চাষ ও তা বিদেশে রফতানির কারণে কৃষিপণ্য ও খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধির কারণে জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাদের কর্মসংস্থানও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে
হিন্দু প্যাট্রিয়ট থেকে নীলচাষ সম্পর্কে কী জানা যায়?
হিন্দু প্যাট্রিয়ট নামক সংবাদপত্র হল নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্পর্কে জানার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কৃষকদের কাছে নীলচাষ অলাভজনক হলেও দাদন বা অগ্রিম অর্থ গ্রহণের কারণে নীলচাষিরা নীলচাষ করতে বাধ্য হত। নীলচাষে অনিচ্ছুক কৃষকরা নীলকর সাহেবদের দ্বারা অত্যাচারিত হত।
হুতোম প্যাঁচার নক্শা থেকে কীভাবে কলকাতার সমাজ বিন্যাসের কথা জানা যায়?
কালীপ্রসন্ন সিংহের রচিত ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ নামক ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থ থেকে ইংরেজ শাসনের পূর্বে বাংলার বড় বড় বংশের (কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ) পতন এবং নতুন বংশের (মল্লিক পরিবার, শীল পরিবার) উত্থানের কথা জানা যায়। এর পাশাপাশি নতুন নতুন জাতের উদ্ভব হয়। এর মূল কারণ ছিল ইংরেজ শাসন ও ব্যাবসা-বাণিজ্য।
হুতোম প্যাঁচার নক্শা থেকে উনিশ শতকের সংস্কৃতির কথা কীভাবে জানা যায়?
হুতোম প্যাঁচার নক্শা’ থেকে উনিশ শতকের বিভিন্নধর্মী সংস্কৃতির কথা জানা যায় — যেমন, নীলের ব্রত, গাজন সন্ন্যাসী (চড়কি)-দের শিবের কাছে মাথা ঘোরানো বা মাথা চালা, যাত্রাগান, বুলবুলের গান, অশ্লীল শব্দযুক্ত আখড়াই গান প্রভৃতি। এছাড়া চড়কপূজা, নীলষষ্ঠী, রামলীলা, রথ উৎসব, বারোয়ারি দুর্গাপূজাও ছিল সংস্কৃতির অঙ্গ।
নীলদর্পণ নাটকের গুরুত্ব কি?
নীলচাষিদের নীলচাষ ও অনিচ্ছুক নীলচাষিদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারই ছিল ‘নীলদর্পণ’ নাটকের মূল বিষয়। অনুমান করা হয় যে, নদিয়ার গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশাই এই নাটকের মাধ্যমে ফুটে উঠেছিল। নীল বিদ্রোহ ও ‘নীল কমিশন’ গঠনের পর এই নাটকটি প্রকাশিত হলে পাদ্রি জেমস্ লং এই নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা-র কয়েকটি দিক চিহ্নিত করো।
হরিনাথ মজুমদার বা কাঙাল হরিনাথ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ ছিল এক সাময়িক পত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন। এছাড়া এই পত্রিকায় সমসাময়িক বিভিন্ন খবরও প্রকাশিত হত।
ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের গুরুত্ব কী?
1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতি বছর অন্তত এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এভাবে সরকার ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আবার এই সুপারিশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদী শিক্ষার বিতর্ক।
ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক বলতে কী বোঝো?
ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ‘ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষাচর্চার মাধ্যম’ কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। এইচ. টি. প্রিন্সেপ, কোলব্রুক প্রমুখ পণ্ডিত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা অর্থাৎ প্রাচ্য ভাষাকে সমর্থন জানালেও স্যার জন শোর, চার্লস গ্রান্ট, লর্ড মেকলে প্রমুখ পণ্ডিত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাচর্চার পক্ষেই মত প্রকাশ করেন। আধুনিক ভারতের শিক্ষাচর্চার ইতিহাসে এই বির্তক ‘প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী বিতর্ক’ নামে পরিচিত।
কে, কবে ইংরেজি ভাষাকে ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করেন? এর গুরুত্ব কী?
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক 1835 সালে ইংরেজি ভাষাকে ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করেন। এর ফলে ভারতে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সরকারি নীতি গৃহীত হয় এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যবাদী বিতর্কের অবসান ঘটে।
উডের নির্দেশনামা কী?
ভারতের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার মধ্যে সামঞ্চসা প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করার জন্য উনিশ শতকে চার্লস উডের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের সুপারিশগুলিকে ‘উডের নির্দেশনামা বলা হয় (1854 খ্রিস্টাব্দ)।
ভারতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের ক্ষেত্রে চার্লস উডের দুইটি সুপারিশ উল্লেখ করো।
ভারতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের ক্ষেত্রে চার্লস উডের অনেকগুলি সুপারিশের (1854 খ্রিস্টাব্দ) মধ্যে দুইটি সুপারিশ ছিল –
- সরকারি শিক্ষানীতি রূপায়ণ ও পরিচালনার জন্য সরকারি শিক্ষা বিভাগ গঠন করা।
- ভারতের প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে (কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই) একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
হান্টার কমিশন কী?
ভারতের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য 1882 খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম হান্টার নামে এক শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে ভারত সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করে, যা ‘হান্টার কমিশন’ নামে পরিচিত।
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনে (1904 খ্রিস্টাব্দ) কী বলা হয়েছিল?
ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে (1904 খ্রিস্টাব্দ) বলা হয়েছিল যে —
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে সরকার মনোনীত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
ভারতে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের অবদান কী ছিল?
ঊনবিংশ শতকে বাংলা তথা ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয় পরিদর্শকের সরকারি পদে থাকার সুবাদে তিনি 35টি (মতান্তরে 40টি) বালিকা বিদ্যালয় এবং 100টি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল 1849 সালে বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় ‘হিন্দু ফিমেল স্কুল স্থাপন।
বেথুন কলেজ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন 1841 খ্রিস্টাব্দে হিন্দু ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। 1878 খ্রিস্টাব্দে এই স্কুলের সঙ্গে বালিগঞ্জের ‘বলামহিলা বিদ্যালয়’ বেথুন স্কুলের সঙ্গে সম্মিলিত বা একত্রিত হয়ে বেথুন কলেজে পরিণত হয়। 1888 খ্রিস্টাব্দে এটি প্রথম শ্রেণির কলেজে পরিণত হয়।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কেন?
1800 খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মরত উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, আইন ও রীতিনীতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
হিন্দু কলেজ কখন ও কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
1817 খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের যৌথ উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং বিচারপতি হাইড ইস্ট-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশের মতে, ডেভিড হেয়ার ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রস্তাবক ও এদেশীয় ক ধনবান ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতায় তিনি এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। আবার ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, হাইড ইস্ট-ই এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।
পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে রাধাকান্ত দেব গুরুত্বপূর্ণ কেন?
রাধাকান্ত দেব কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালনা এবং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর সহযোগিতায় ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা ‘ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন।
বেথুন বিখ্যাত কেন?
জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ভারতের বড়োলাটের কাউন্সিলের আইন সদস্যরূপে যোগদান করেন (1848 খ্রিস্টাব্দ)। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালির সহযোগিতায় 1849 খ্রিস্টাব্দে ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল পরবর্তীকালে ‘বেথুন স্কুল’ নামে পরিচিত হয়।
ডা. মধুসূদৰ গুপ্ত বিখ্যাত কেন?
ডা. মধুসূদন গুপ্ত ছিলেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। এই কলেজে তিনি হিন্দু ওষুধের পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন (1830 খ্রিস্টাব্দ)। আবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এখানে ডাক্তাররূপে যোগদান করেন। তিনি 1836 খ্রিস্টাব্দের 10 জানুয়ারি হিন্দু কুসংস্কার উপেক্ষা করে নিজহাতে শব ব্যবচ্ছেদ করেন।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থার কার্য পরিচালনা করত?
1857 খ্রিস্টাব্দের 24 জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন হত না। শুরুতে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন স্কুল ও কলেজকে অনুমোদন প্রদান করত এবং এন্ট্রান্স ও বি. এ পরীক্ষা পরিচালনা করত। পরীক্ষা শেষে ছাত্রদের সার্টিফিকেট ও ডিগ্রি প্রদান করত।
হাজী মহম্মদ মহসীন বিখ্যাত কেন?
হুগলিতে জন্মগ্রহণকারী হাজী মহম্মদ মহসীন (1730-1812 খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন বিত্তবান, মানবতাবাদী ও পরোপকারী ব্যক্তি। তিনি তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি ও সম্পদের উপর ভিত্তি করে দানমূলক একটি ট্রাস্টি সংস্থা গঠন করেন। সমাজসেবামূলক কাজ ও শিক্ষার প্রসারে তিনি এবং তাঁর এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির প্রধান লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল –
- প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা দ্বারা সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথার অবসান ঘটানো
- নারীকল্যাণ সাধন করা
- সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটানো।
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল?
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল –
- হিন্দুধর্মের প্রচলিত কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা দূর করে একেশ্বরবাদের প্রচার বা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা
- খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরণের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা।
কে, কবে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন?
রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগিতায় গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক 1829 খ্রিস্টাব্দের 4 ডিসেম্বর এক আইনের (‘সপ্তদশ বিধি) মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেন।
উনিশ শতকের একটি সমাজসংস্কার আন্দোলনের উল্লেখ করো। এই আন্দোলনের পুরোভাগে কে ছিলেন?
উনিশ শতকের একটি সমাজসংস্কার আন্দোলন ছিল। ‘নব্যবঙ্গ আন্দোলন।’ এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।
ডিরোজিওকে মনে রাখা হয় কেন?
ডিরোজিও ছিলেন একজন যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী ও হিন্দু কলেজের শিক্ষক। তিনি বিখ্যাত ছিলেন কারণ, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের একজন উল্লেখযোগ্য সমাজসংস্কারক। প্রগতিশীল চিন্তাধারার ভিত্তিতে তিনি হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের বিরোধিতা করেন। এছাড়া ‘নব্যবঙ্গ’ বা ‘ইয়ংবেঙ্গল’ আন্দোলনের নেতা হিসাবে ডিরোজিওকে মনে রাখা হয়।
কার উদ্যোগে নব্যবঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়েছিল? এই আন্দোলনের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার নাম লেখো।
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র উদ্যোগে নব্যবঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাদ মিত্র প্রমুখরা ছিলেন নব্যবঙ্গ আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা।
ইয়ংবেঙ্গল কাদের বলা হত? এই দলের উদ্দেশ্য কী ছিল?
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র অনুগামীরা ‘ইয়ং বেঙ্গল’ বা ‘নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়’ নামে পরিচিত।
ইয়ংবেঙ্গল দলের উদ্দেশ্য ছিল –
- জনসাধারণের মধ্যে প্রগতিশীল ধ্যানধারণা প্রচার করা ও যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা,
- হিন্দুসমাজে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করা,
- যুক্তিবাদী আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও শিক্ষার বিস্তার ঘটানো।
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’ কী?
1838 খ্রিস্টাব্দে ডিরোজিওর অনুগামী নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়ের সদস্যগণ ‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’ নামে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের সর্বাঙ্গীন অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যেই এই সভা স্থাপিত হয়।
লালন ফকির বিখ্যাত কেন?
লালন ফকির ছিলেন একজন বাউল সাধক ও মানবতাবাদী এবং জাতিবিদ্বেষের তীব্র বিরোধী। তিনি প্রথ মুরশিদাবাদের চেউরিয়াতে বাউল সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বাউল গান রচনা করেন। তাঁর এই গানগুলি দরিদ্র কৃষকসহ জনগণের কাছে খুব আকর্ষণের বিষয়।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বিখ্যাত কেন?
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (1841 – 1891 খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ব্রাত্মধর্মের একজন বিখ্যাত প্রচারক। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের আ সঙ্গে কলকাতার বাইরে পূর্ববঙ্গে ব্রাত্মধর্ম প্রচার করেন। এর পাশাপাশি তিনি এই অঞ্চলে ব্রাত্ম উপাসনা মন্দির, বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ কীভাবে ধর্মসমন্বয়বাদী আদর্শ বাস্তবায়িত করেন।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাত্মধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের প্রসারকে কেন্দ্র করে। একেশ্বরবাদ ও বহুদেবতাবাদ সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। রামকৃয়দের বিভিন্ন ধর্ম বর্ণিত ঈশ্বরলাভের পথ ধরে ঈশ্বর সাধনা করেন ও সফল হন। তাঁর উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি প্রচার করেন যে, সাকার ও নিরাকার (একই ঈশ্বরের বিচিত্র = রূপ)। একেশ্বরবাদ ও বহুদেবতাবাদ হল ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গ। এভাবে তিনি ধর্মসমন্বয়বাদী আদর্শের প্রচার করেন।
বিবেকানন্দ কীভাবে নবাবেদান্ত মতাদর্শের সূচনা করেন?
মানবতাবাদী ও সমাজপ্রেমী বিবেকানন্দ আত্মমুক্তি অপেক্ষা সমাজে উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ ‘বনের বেদান্ত’কে ঘিরে’ আনার কথা প্রচার করেন এবং বেদান্তকে মানবহিতের কাজে ব্যবহারের কথা বলেন। এভাবে বিবেকানন্দ বেদান্তের নতুন যে ব্যাখ্যা দেন তা নব্যবেদান্ত নামে পরিচিত।
বাংলার নবজাগরণ কী?
উনিশ শতকে বাংলায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শবাদের ভিত্তিতে সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটে, যা নবজাগরণ নামে পরিচিত। নবজাগরণের একটি দিক ছিল বাংলা তথা ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন করা। তবে বাংলার নবজাগরণ ক্রমশ সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও বিজ্ঞানচিন্তার ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।
বাংলায় নবজাগরণের প্রধান ভিত্তি কী ছিল?
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদী আদর্শ ছিল বাংলার নবজাগরণের প্রধানতম ভিত্তি। প্রাচ্য আদর্শের ভিত্তিগুলি হল এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা মাদ্রাসা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও কলকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা। প্রাচ্যবাদের চর্চা ভারতের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটায়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বাংলায় মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, প্রগতিবাদী আদর্শের সঞ্চার ঘটায়। এই দুই আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতেই সৃষ্টি হয় বাংলার নবজাগরণ।
আজকে এই আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়, “সংস্কার: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা” এর কিছু “সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বা আপনি যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন, তাহলে আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে, টেলিগ্রামে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি। এছাড়া, এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।


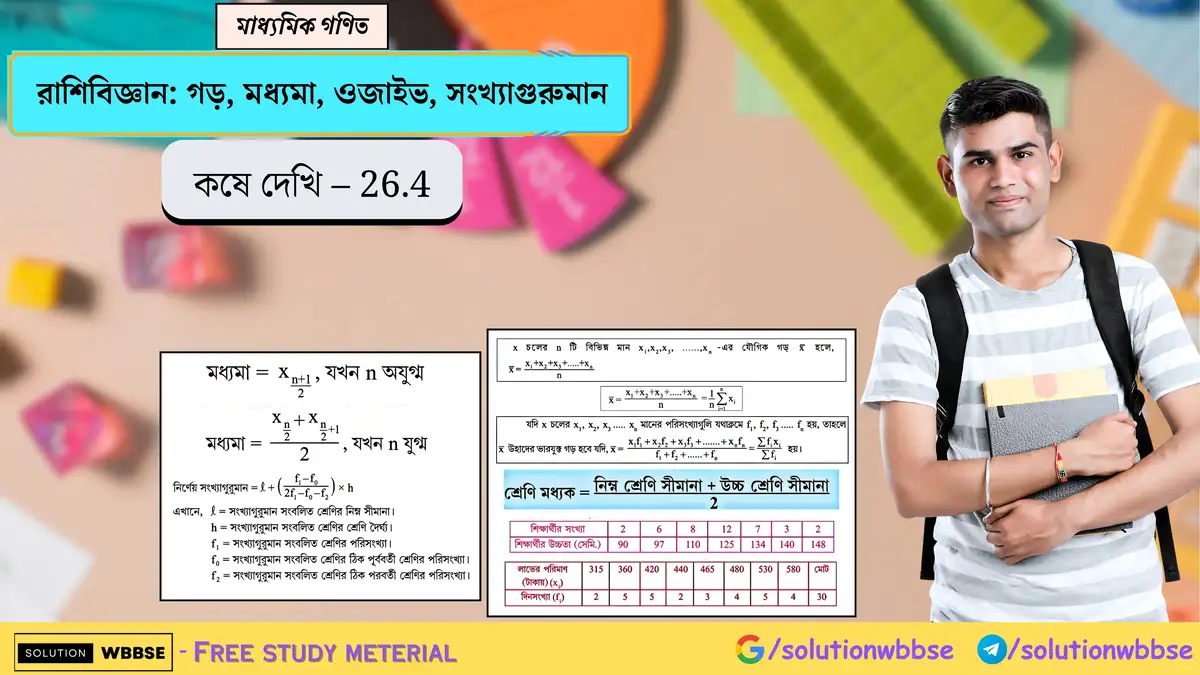
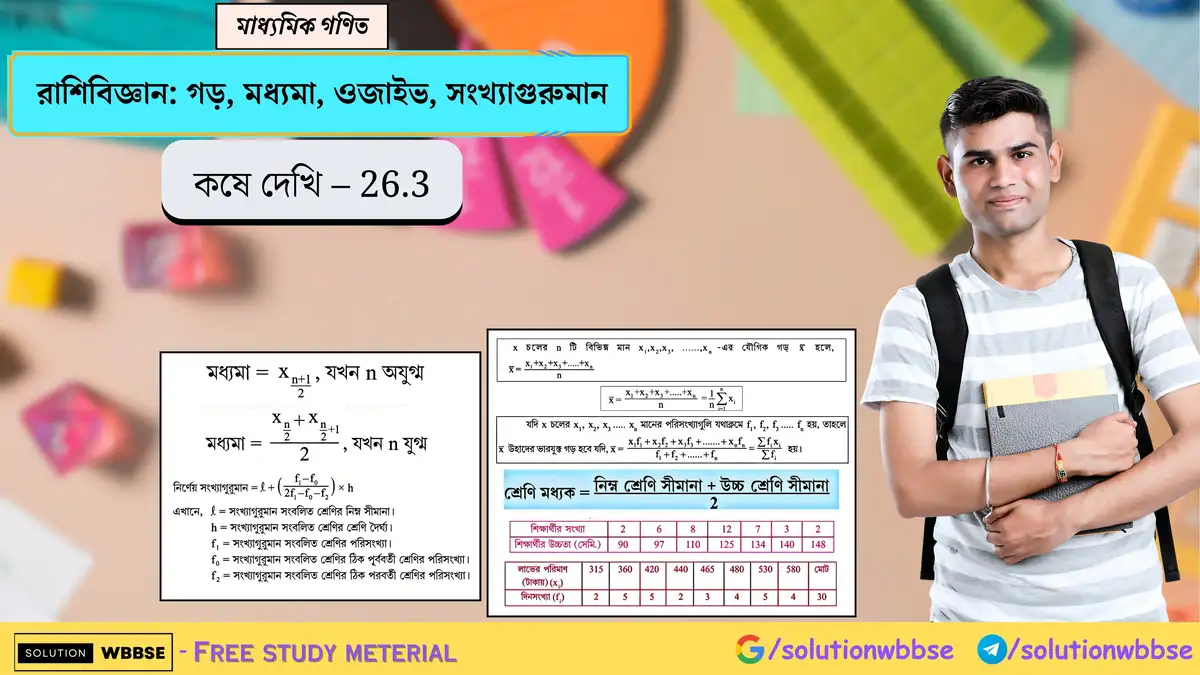
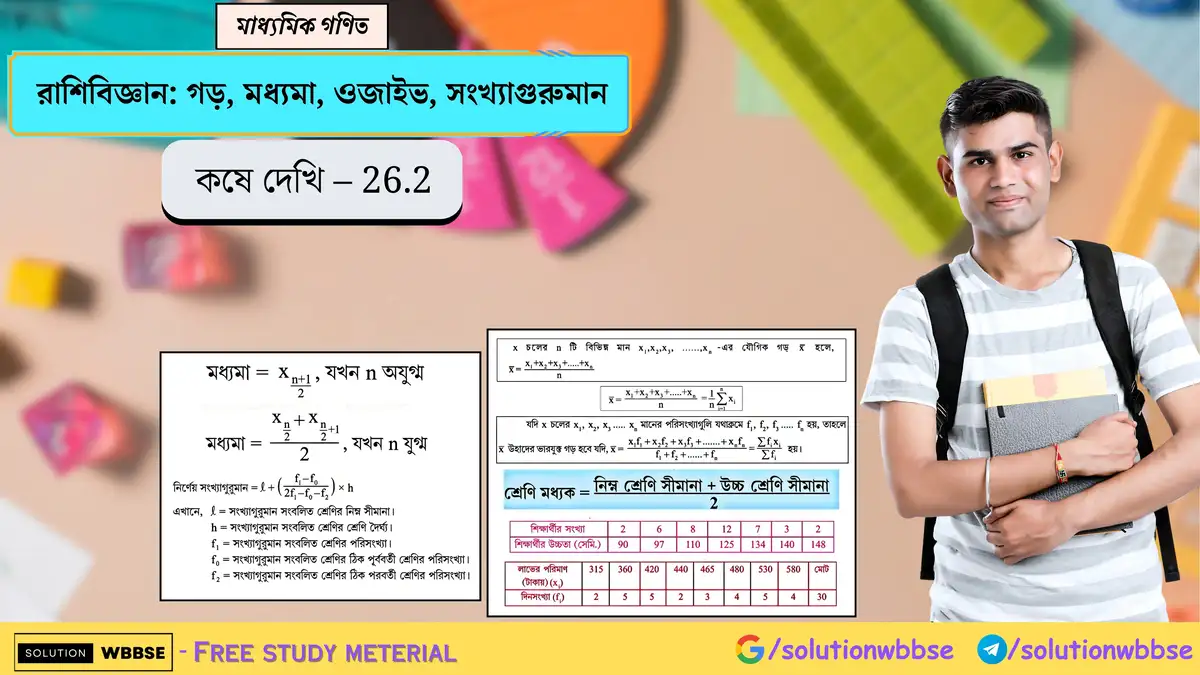

মন্তব্য করুন