আজকে আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায় “বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ” অধ্যায়ের ‘বংশগতি‘ বিভাগের বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বা আপনি যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন, তাহলে আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি যে এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।

বংশগতি ও প্রকরণ, বংশগতি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা
বিষয়সংক্ষেপ
- জননের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে জীবের বৈশিষ্ট্যের সঞ্চরণকে বলে বংশগতি। সর্বপ্রথম বংশগতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। এজন্য তাঁকে বংশগতিবিদ্যা বা জেনেটিক্স -এর জনক বলা হয়।
- ক্রোমোজোমের DNA -তে অসংখ্য জিন রৈখিক সজ্জাক্রমে অবস্থান করে। ক্রোমোজোমের বা DNA -এর অন্তর্গত জিনের স্থায়ী পরিবর্তনকে বলে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি।
- যৌন জনন ও পরিব্যক্তির কারণে জীবপ্রজাতির সদস্যদের আকার, আকৃতির ও স্বভাবের যে পার্থক্য দেখা যায় তাকে ভ্যারিয়েশন বা প্রকরণ বলে। যেমন – মানুষের মুক্ত কানের লতি ও যুক্ত কানের লতি, রোলার জিভ ও স্বাভাবিক বা নন্-রোলার জিভ।
- বংশগতির ব্যাখ্যায় মেন্ডেলের কাজ বুঝতে কতকগুলি শব্দ সম্পর্কে জানা জরুরি। যেমন — একটি জিনের দুটি রূপ থাকে যাদের অ্যালিল বলে। অ্যালিল ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে। সেই স্থানটিকে বলে লোকাস। একটি অ্যালিল একটি বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন – T অ্যালিলটি লম্বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। একই রকম অ্যালিল থাকলে (TT বা tt) জীবটিকে হোমোজাইগাস জীব বলে। আবার ভিন্ন অ্যালিল থাকলে (Tt) জীবটিকে হেটেরোজাইগাস বলে। জীবের অ্যালিলগত বৈশিষ্ট্যকে বলে তার জিনোটাইপ (যেমন – TT বা tt)। আবার, জীবের বাইরের বা প্রকাশিত চরিত্র অথবা বৈশিষ্ট্যকে বলে ফিনোটাইপ (যেমন — লম্বা বা বেঁটে)।
মটর গাছের ওপর মেন্ডেলের কাজ, মেন্ডেলের সাফল্যের কারণ, মেন্ডেলের নির্বাচিত মটর গাছের বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য, মেন্ডেলের পরীক্ষা, সূত্র এবং সূত্রের বিচ্যুতি
বিষয়সংক্ষেপ
- মেন্ডেল দুটি বিপরীত প্রলক্ষণবিশিষ্ট মটর গাছের মধ্যে (যেমন – লম্বা ও বেঁটে) ইতর পরাগযোগ ঘটান ও অপত্য মটর গাছের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ লক্ষ করেন।
- মেন্ডেল সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংকরায়ণের পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করেন। এগুলি হল – গাছের দৈর্ঘ্য (লম্বা-বেঁটে), কান্ডে ফুল-ফলের অবস্থান (কাক্ষিক-শীর্ষস্থ), ফলের আকৃতি (স্ফীত-খাঁজযুক্ত), ফলের রং (সবুজ-হলদে), ফুলের রং (বেগুনি-সাদা), বীজের আকৃতি (গোল-কুঞ্চিত), বীজত্বকের রং (হলদে-সবুজ)।
- মেন্ডেল বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি একইসঙ্গে কেবল এক বা দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি সংকরায়ণ পরীক্ষা করেন। এজন্য তাঁর সাফল্য লাভ সহজ হয়েছিল।
- একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেন্ডেল যে সংকরায়ণের পরীক্ষা করেন তাকে এক সংকরায়ণ বা মনোহাইব্রিড ক্রস বলে। এই পরীক্ষা থেকে তিনি পৃথকীভবন সূত্র প্রণয়ন করেন, যা মেন্ডেলের প্রথম সূত্র নামে পরিচিত। এই সূত্র অনুযায়ী কোনো জীবের একজোড়া ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তার পরবর্তী জনুতে মিশে না গিয়ে আলাদাভাবে অবস্থান করে এবং জনন কোশ গঠনকালে তারা আবার পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়।
- মেন্ডেলের লম্বা-বেঁটে মটর গাছের ক্ষেত্র ছাড়াও গিনিপিগের সাদা-কালো গাত্রবর্ণের জন্য একসংকর জনন পরীক্ষায় একই ফল লক্ষ করা যায়।
- মটর গাছের দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেন্ডেল যে সংকরায়ণ পরীক্ষানিরীক্ষা করেন তাকে দ্বিসংকরায়ণ বা ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে। হলদে-গোল বীজ ও সবুজ-কুঞ্চিত বীজযুক্ত মটর গাছের মধ্যে ক্রসের বিশ্লেষণ করে তিনি যে সূত্র প্রণয়ন করেন তা স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র বা মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র নামে খ্যাত।
- মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী, কোনো জীবের গ্যামেট উৎপাদনের সময় একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য অন্য জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য অ্যালিলের থেকে স্বাধীনভাবে বংশানুসৃত হয়।
- গিনিপিগের ক্ষেত্রে কালো-খর্ব লোম ও সাদা-দীর্ঘ লোমযুক্ত গিনিপিগ দুটির মধ্যে ক্রসটি একটি দ্বিসংকর জননের উদাহরণ। কালো-মসৃণ লোম × সাদা-কর্কশ লোমযুক্ত গিনিপিগের মধ্যে ক্রসটিও একইরকম আরেকটি ক্রস।
- মেন্ডেলের একসংকর জননের জিনোটাইপিক অনুপাত 1 : 2 : 1 ও ফিনোটাইপিক অনুপাত 3 : 1। পক্ষান্তরে মেন্ডেলের দ্বিসংকর জননের ক্ষেত্রে জিনোটাইপিক অনুপাত হল 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1 এবং ফিনোটাইপিক অনুপাত 9 : 3 : 3 : 1।
- মেন্ডেলের সূত্র সর্বজনীন নয়। অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে এই সূত্রের বিচ্যুতি দেখা যায়। সন্ধ্যামালতীর ক্ষেত্রে লাল ও সাদা ফুলের উদ্ভিদদের ক্রসে F1 জনুতে গোলাপি ফুল সৃষ্টি হয়। অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে জিনোটাইপিক ও ফিনোটাইপিক অনুপাত উভয়েই 1 : 2 : 1 হয়।
মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ
বিষয়সংক্ষেপ
- জননের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে জীবের বৈশিষ্ট্যের সঞ্চরণকে বলে বংশগতি। সর্বপ্রথম বংশগতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন গ্রেগর জোহান মেন্ডেল। এজন্য তাঁকে বংশগতিবিদ্যা বা জেনেটিক্স -এর জনক বলা হয়।
- ক্রোমোজোমের DNA -তে অসংখ্য জিন রৈখিক সজ্জাক্রমে অবস্থান করে। ক্রোমোজোমের বা DNA -এর অন্তর্গত জিনের স্থায়ী পরিবর্তনকে বলে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি।
- যৌন জনন ও পরিব্যক্তির কারণে জীবপ্রজাতির সদস্যদের আকার, আকৃতির ও স্বভাবের যে পার্থক্য দেখা যায় তাকে ভ্যারিয়েশন বা প্রকরণ বলে। যেমন – মানুষের মুক্ত কানের লতি ও যুক্ত কানের লতি, রোলার জিভ ও স্বাভাবিক বা নন্-রোলার জিভ।
- বংশগতির ব্যাখ্যায় মেন্ডেলের কাজ বুঝতে কতকগুলি শব্দ সম্পর্কে জানা জরুরি। যেমন — একটি জিনের দুটি রূপ থাকে যাদের অ্যালিল বলে। অ্যালিল ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে। সেই স্থানটিকে বলে লোকাস। একটি অ্যালিল একটি বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন – T অ্যালিলটি লম্বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। একই রকম অ্যালিল থাকলে (TT বা tt) জীবটিকে হোমোজাইগাস জীব বলে। আবার ভিন্ন অ্যালিল থাকলে (Tt) জীবটিকে হেটেরোজাইগাস বলে। জীবের অ্যালিলগত বৈশিষ্ট্যকে বলে তার জিনোটাইপ (যেমন – TT বা tt)। আবার, জীবের বাইরের বা প্রকাশিত চরিত্র অথবা বৈশিষ্ট্যকে বলে ফিনোটাইপ (যেমন — লম্বা বা বেঁটে)।
আজকে আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানের তৃতীয় অধ্যায় “বংশগতি এবং কয়েকটি সাধারণ জিনগত রোগ” অধ্যায়ের ‘বংশগতি‘ বিভাগের বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বা আপনি যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন তাহলে আপনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি যে এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া, আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জন যার এটি প্রয়োজন হবে তার সাথে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।


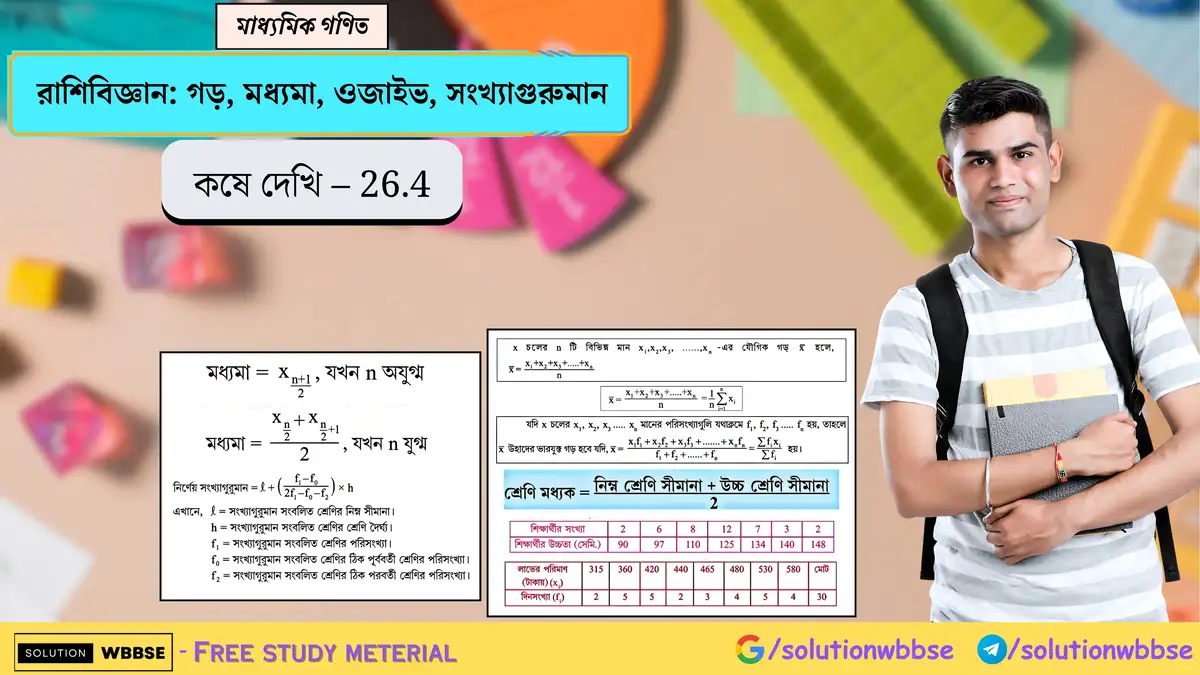
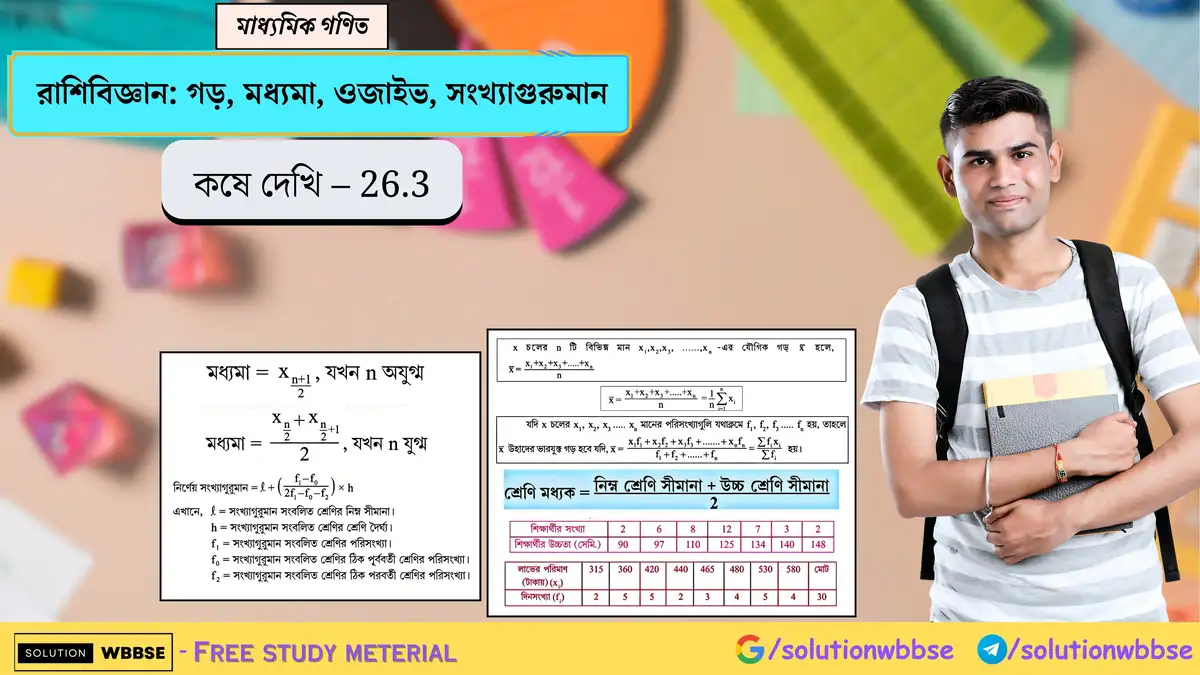
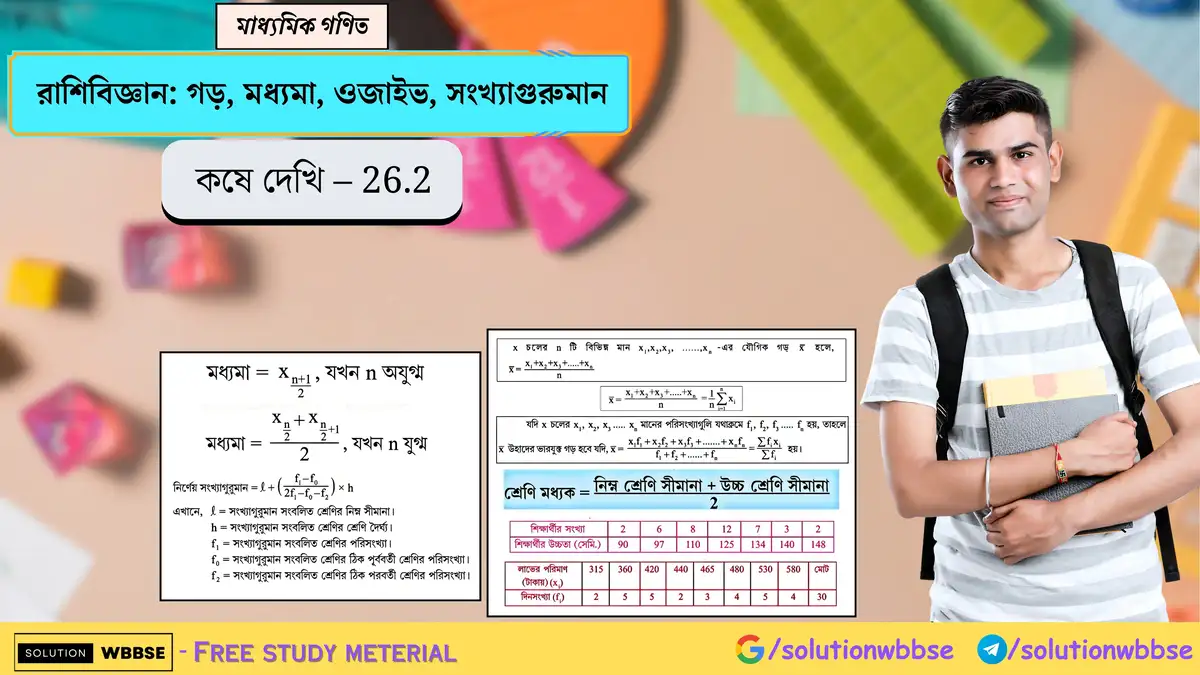

মন্তব্য করুন