এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “সভা-সমিতির যুগ বলতে কী বোঝায়? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলা হয় কেন?” নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাস পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই “সভা-সমিতির যুগ বলতে কী বোঝায়? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলা হয় কেন?“ প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায় “সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা“ -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়।
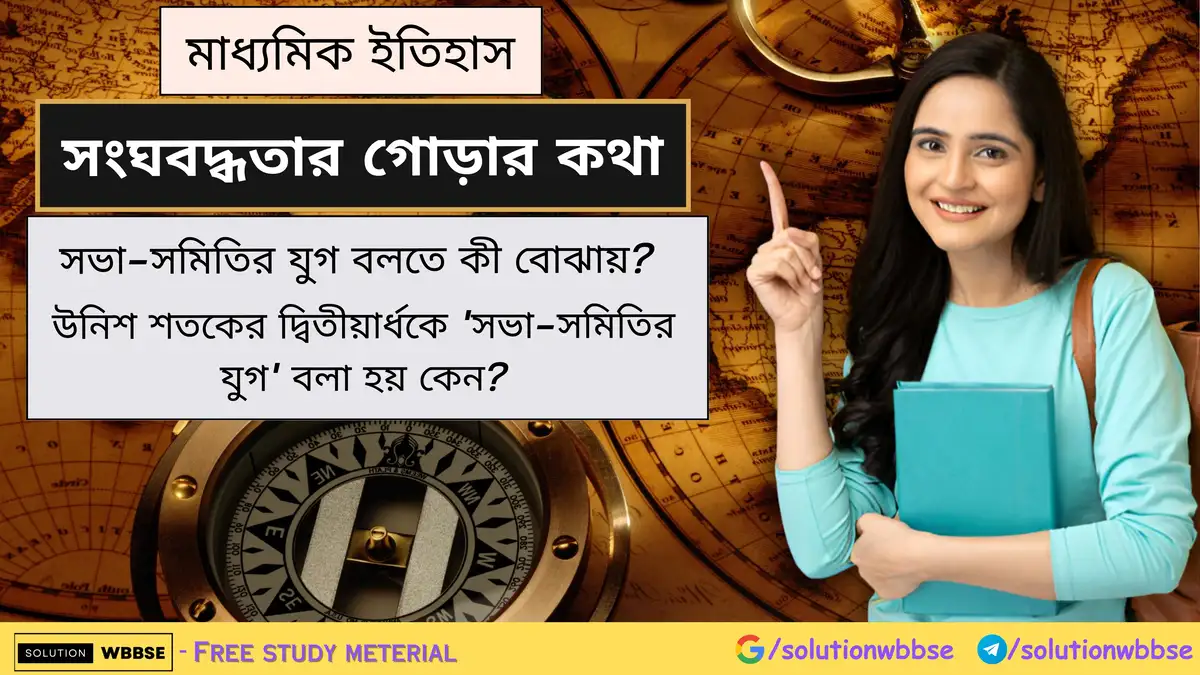
সভা-সমিতির যুগ বলতে কী বোঝায়?
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ প্রভৃতির ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এজন্য এই সময়কালকে ‘সভাসমিতির যুগ’ বলা হয়। ড. অনিল শীল ঊনবিংশ শতককে ‘সভাসমিতির যুগ‘ বলে অভিহিত করেছেন।
সভা-সমিতির যুগের বৈশিষ্ট্য –
উনিশ শতকে গড়ে ওঠা সভা-সমিতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হল –
- এইগুলি ছিল এক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
- সাধারণত সমাজের শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিতরা এই সমিতিগুলির সদস্য হতেন।
- এইগুলির সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না।
সভা-সমিতির যুগের গুরুত্ব –
উনিশ শতকে সংগঠিত সভা-সমিতিগুলির গুরুত্ব হল –
- এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যদিয়ে সরকারি শোষণ ও অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে সংঘবদ্ধ জনমত গড়ে ওঠে।
- ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনার প্রসার ঘটে।
- সর্বোপরি জাতীয় কংগ্রেস ছিল উনিশ শতকের সভাসমিতিগুলির চূড়ান্ত পরিণতি।
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলা হয় কেন?
জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়রা উপলব্ধি করে যে, দেশের স্বার্থরক্ষার্থে তথা সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকেই উনিশ শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য রাজনৈতিক সভা-সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। এইজন্য অধ্যাপক অনীল শীল উনিশ শতককে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর
কে প্রথম ‘সভা-সমিতির যুগ’ কথাটি ব্যবহার করেন?
ড. অনীল শীল উনিশ শতককে “সভা-সমিতির যুগ” বলে অভিহিত করেছেন।
সভা-সমিতির যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
সভা-সমিতির যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল –
1. এই সংগঠনগুলি ছিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
2. এগুলির সদস্য ছিলেন প্রধানত শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ।
3. এগুলির ধর্মীয় সম্পৃক্ততা ছিল না, অর্থাৎ এগুলি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল।
4. সরকারি শোষণ ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা হয়।
সভা-সমিতির যুগের গুরুত্ব কী?
সভা-সমিতির যুগের গুরুত্ব হল –
1. ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনার প্রসার ঘটায়।
2. সরকারের শোষণ ও নীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জনমত গঠিত হয়।
3. এই সংগঠনগুলির ধারাবাহিকতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ছিল এই যুগের চূড়ান্ত পরিণতি।
উনিশ শতককে কেন ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলা হয়?
এই সময়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে এবং ভারতীয়রা উপলব্ধি করে যে সামষ্টিক আন্দোলন ছাড়া ব্রিটিশ শাসনের অবসান সম্ভব নয়। তাই দেশজুড়ে অসংখ্য রাজনৈতিক সভা-সমিতি গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে।
সভা-সমিতির যুগের কিছু উল্লেখযোগ্য সংগঠনের নাম লেখো।
সভা-সমিতির যুগের কিছু উল্লেখযোগ্য সংগঠনের নাম হল –
1. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (1836),
2. জমিদার সভা (1838),
3. ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (1843),
4. ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (1876, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়),
5. মাদ্রাজ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন (1852),
6. বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন (1852)।
সভা-সমিতির যুগের সীমাবদ্ধতা কী ছিল?
সভা-সমিতির যুগের সীমাবদ্ধতা ছিল –
1. এগুলির সদস্য ছিলেন মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ কম ছিল।
2. বেশিরভাগ সংগঠন নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা থেকে দূরে ছিল।
3. প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলি কেবল আবেদন-নিবেদনের নীতিতে কাজ করত, প্রতিবাদমুখী আন্দোলন ততটা শক্তিশালী ছিল না।
এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “সভা-সমিতির যুগ বলতে কী বোঝায়? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলা হয় কেন?” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই “সভা-সমিতির যুগ বলতে কী বোঝায়? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে ‘সভা-সমিতির যুগ’ বলা হয় কেন?” প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায় “সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা” -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকলে, আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তাছাড়া, নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।


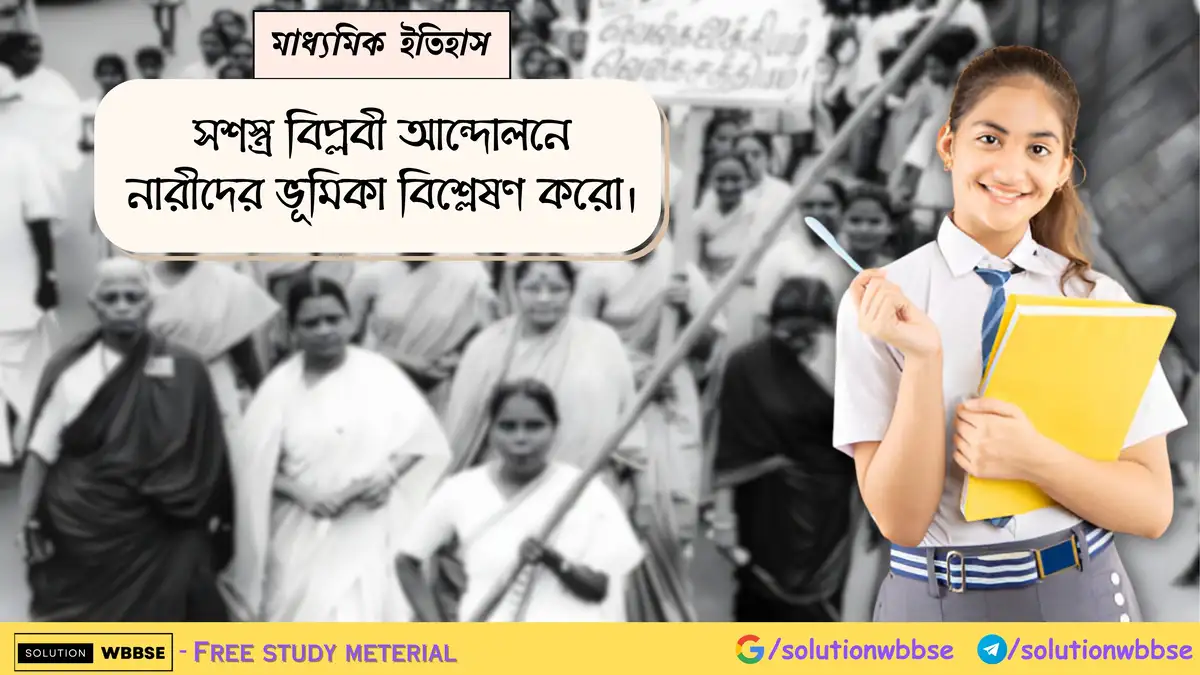
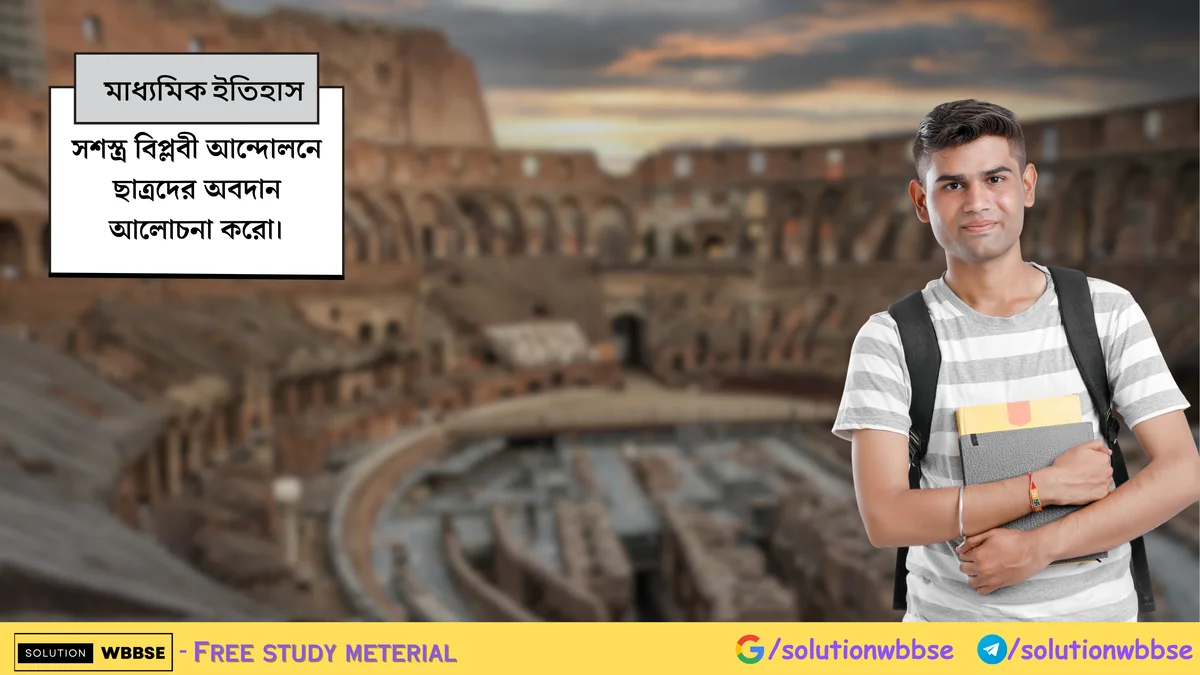
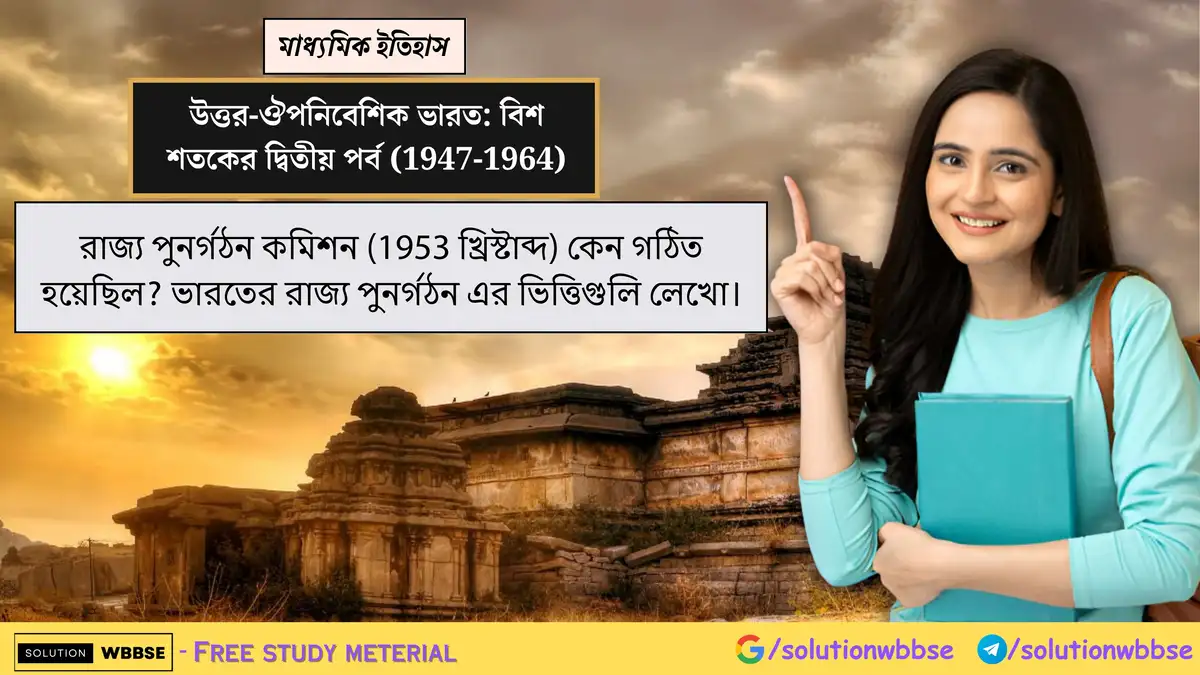

মন্তব্য করুন