আজকে আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক বাংলার পঞ্চম পাঠের তৃতীয় বিভাগ, ‘প্রলয়োল্লাস’ নিয়ে কিছু বিশ্লেষণধর্মী ও রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর এবং তাদের উত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।
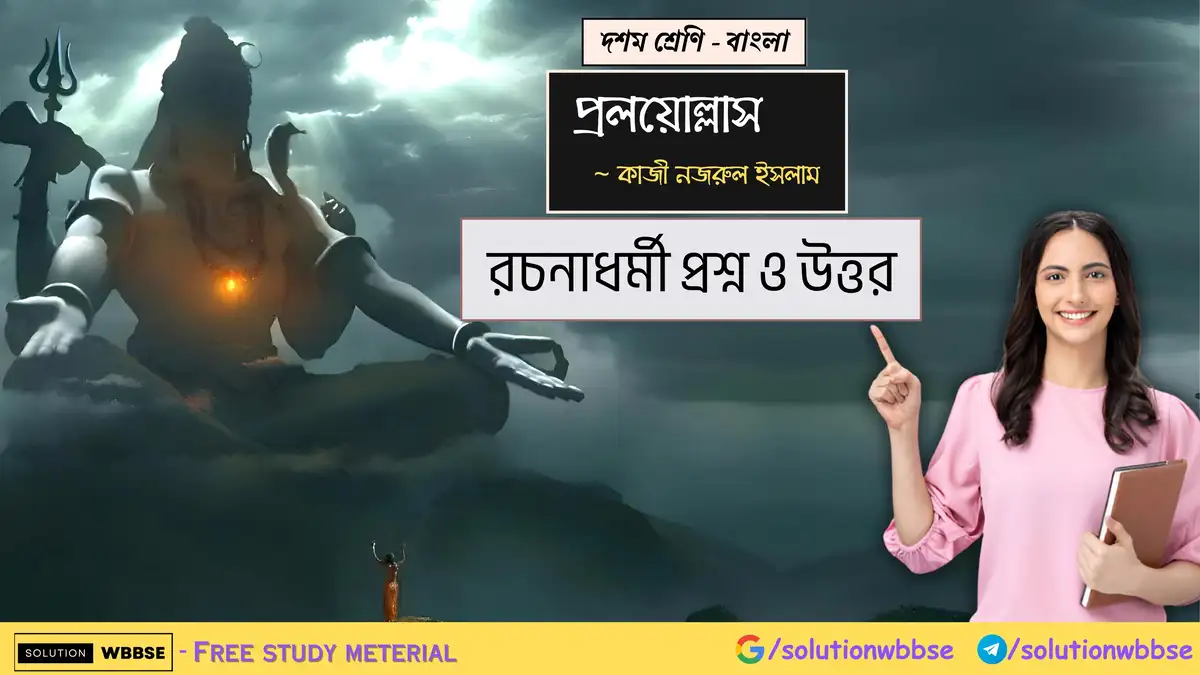
“ওই নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।” – ‘নূতনের কেতন’ কী? প্রলয়োল্লাস কবিতার বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্যটির তাৎপর্য আলোচনা করো।
‘নূতনের কেতন’ – ‘নূতনের কেতন’: ‘কেতন’ শব্দের অর্থ পতাকা। ‘নূতনের কেতন’ অর্থাৎ স্বাধীনতার ভিত্তিতে যে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তার প্রতীক পতাকার কথা বলা হয়েছে।
তাৎপর্য – ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অগ্নিগর্ভ সময়ে কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি রচিত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন মুক্তি আন্দোলন ঘটছিল এবং কবি এসব আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। এ থেকেই তাঁর মনে হয়েছিল যে নতুন দিনের আগমন অবশ্যম্ভাবী। সেই নতুন দিনের আগমন ‘কালবৈশাখীর ঝড়’-এর মতো আসবে — অর্থাৎ এক প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সর্বনাশের পথ ধরে এই পরিবর্তন আসবে — “বস্ত্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর।” সর্বনাশী ধূমকেতুর মতো তার আবির্ভাব হবে। সশস্ত্র বিপ্লবের এই আগমনে স্থিতাবস্থার আসন টলে যাবে। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপের মতো কিংবা মেঘের গর্জনের মতো বিপ্লবী শক্তির আগমন ঘটবে। মহাসমুদ্রও যেন সেই ভয়ংকরের আগমনে দুলে উঠবে। কিন্তু এই ভয়ংকরের আড়ালে সুন্দরের প্রতিশ্রুতি লুকিয়ে আছে। প্রলয়ের রূপ নিয়ে এ হল ‘চিরসুন্দর’ -এর আগমন। ভাঙনের মধ্য দিয়েই সৃষ্টিই তাঁর লক্ষ্য। তাই কবি ভয়ংকরকে ভয় না পেয়ে, তারই জয়ধ্বনি করতে বলেছেন। কারণ ‘কালবৈশাখীর ঝড়’-এর মধ্যে দিয়েই ‘নূতনের কেতন’ – “কাল-ভয়ংকরের বেশে এবার ওই আসে সুন্দর।”
“বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর!” – এখানে ‘ভয়ংকর’ বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের কীভাবে আগমন ঘটছে নিজের ভাষায় লেখো।
‘ভয়ংকর’ -এর পরিচয় – কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় ‘ভয়ংকর’ বলতে মহাকালের মতো চণ্ড মূর্তিতে যে তরুণ বিপ্লবীদের আগমন ঘটছে, তাদের কথা বলা হয়েছে।
ভয়ংকরের আগমন – যে তরুণ বিপ্লবীদের আগমন কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা। ইংরেজের দুর্গে আঘাত হানাই তাদের উদ্দেশ্য। কালবৈশাখীর ঝড়ের প্রচণ্ডতা নিয়ে তাদের আগমন ঘটে। তারা ‘নূতনের কেতন’ ওড়ায়। পুরোনো ব্যবস্থার বদল ঘটিয়ে তারা এক মানব-বাসযোগ্য সুন্দর সমাজ গড়তে চায়, যেখানে অত্যাচার ও অন্যায় অবসান ঘটবে। কিন্তু তার জন্য প্রথমে প্রয়োজন পুরোনো ব্যবস্থার বদল। তাই ধ্বংসের উন্মত্ততা নিয়ে তরুণ বিপ্লবীদের আগমন ঘটে। কবি তাদেরকে বলেছেন – “অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল।” শিব যেমন তাঁর রুদ্র মূর্তিতে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়েছিলেন, এই তরুণদলও চায় সত্য, ন্যায় এবং সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে। ‘সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে’ অর্থাৎ সমুদ্রপারে আন্দামানের সেলুলার জেলের দরজা ভাঙতে চায় তারা। কারণ এই কারাগার ইংরেজের অত্যাচার ও দমনের প্রতীক। এই মৃত্যুপুরীতে মহাকালের চণ্ড-মূর্তিতে এভাবেই ভয়ংকরের আগমন ঘটে।
“দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়।” – মন্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। কবিতায় এই প্রসঙ্গটি উল্লেখের কারণ কী?
মন্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ – ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল রূপকে তুলে ধরার জন্য প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটির উপস্থাপনা করেছেন। মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের দীপ্তি ভয়াল, তা অগ্নিজ্বালা সৃষ্টি করে। আবার আকাশে যখন মেঘ করে, মনে হয় যেন আগুনরঙা জটাজাল সৃষ্টি হয়েছে। সেই মেঘ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টি যেন দিগন্তেরই কান্না। বিন্দু বিন্দু করে পড়া চোখের জলের মতো সেই বৃষ্টি সপ্তমহাসমুদ্রকে আলোড়িত করে তোলে। কবি প্রলয়ের এই রূপকে শুধু প্রকৃতিতেই নয়, চারপাশের সমাজজীবনেও প্রত্যক্ষ করেছেন।
প্রসঙ্গটি উল্লেখের কারণ – প্রলয়ের ধ্বংসের মধ্যেই কবি বিশ্বমাতার সৃষ্টির অভিষেক দেখেছেন। নজরুল তাঁর যুগবাণী গ্রন্থের ‘নবযুগ’ রচনায় উল্লেখ করেছেন – “আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহা উদ্বোধন।” বিক্ষোভ ও আন্দোলনের তীব্রতায় ধ্বংসের যে উন্মাদনা কবির চোখে পড়ে, তার সঙ্গে কবি প্রকৃতির ভয়ংকর রূপের মিল খুঁজে পান। যদিও সেই রূপ দেখে মানুষ শঙ্কিত ও দিশাহারা হয়, কবি এর মধ্যেই নতুন দিনের এবং নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি খুঁজে পেয়েছেন। সংগ্রামের ভয়ংকর রূপকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে কবি এই মন্তব্যটি করেছেন।
“জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে/জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ওই বিনাশে!” – ‘জগৎ জুড়ে প্রলয়’ কথাটির অর্থ লেখো। এই প্রলয়ের সার্থকতা কী?
‘জগৎজুড়ে প্রলয়’ -এর অর্থ – কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত হলেও, পৃথিবীজুড়ে যে গণমুক্তির সংগ্রামগুলি কবি নানাভাবে সংঘটিত হতে দেখেছেন, সেগুলিও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতাগুলোও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। রাশিয়ার বিপ্লব, তুরস্কে কামাল পাশার উত্থান, আয়ারল্যান্ডের বিপ্লব ইত্যাদি ঘটনা নজরুলের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। সংগ্রাম এবং শোষণমুক্তির বিভিন্ন রূপ বিক্ষিপ্ত আকারে থাকলেও, বিপ্লবের সেই উন্মাদনা নজরুলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ‘জগৎজুড়ে প্রলয়’ বলতে এই বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম-আন্দোলনের কথাই বোঝানো হয়েছে।
প্রলয়ের সার্থকতা – প্রলয় যদিও ধ্বংসের বার্তাবাহক, তবুও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই প্রলয়কে কবি স্বাগত জানিয়েছেন। কারণ, তাঁর মতে, এই প্রলয় প্রচলিত ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নতুন দিনের সূচনা করবে, যা আসলে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। যুগবাণী-র ‘নবযুগ’ রচনায় নজরুল লিখেছিলেন – “নরে আর নারায়ণে আজ আচার-ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁর হাতে স্বাধীনতার বাঁশি।” প্রলয়ের মধ্যে এই নতুন ব্যবস্থাকেই কবি দেখতে পেয়েছেন। তাই ভয়ংকরকে ভয় না পেয়ে, তার জয়ধ্বনি করার কথা বলেছেন তিনি।
“ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!” – কোন্ ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে? প্রলয়কে ‘নূতন সৃজন-বেদন’ বলার তাৎপর্য কী?
ধ্বংসের পরিচয় – কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় রুদ্ররূপী শিবের সংহারমূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। সেই সংহারমূর্তিতে শিব অসুন্দরকে ধ্বংস করে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করবেন। এখানে মহাকাল শিবের ধ্বংসলীলার কথাই বলা হয়েছে।
‘নূতন সৃজন-বেদন’ বলার তাৎপর্য – জীর্ণ পাতা ঝরে গিয়েই গাছে গাছে নতুন পাতার জন্ম হয়। একইভাবে, সামাজিক জীর্ণতা ধ্বংস না হলে নতুন সৃষ্টি সম্ভব নয়।
- মূল্যবোধের অবক্ষয় – সমকালীন বাংলা দেশে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কালো ছায়া নেমে এসেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসন মানুষের প্রাণের মুক্তিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। অন্যদিকে, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। মনুষ্যত্বের অপমান, শোষণ, বঞ্চনা প্রভৃতি ছিল সাধারণ মানুষের ভাগ্যলিপি।
- ধর্মান্ধ সমাজের ধ্বংস – নজরুল আন্তরিকভাবে এই সমাজের ধ্বংস চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রলয়রূপী শিবের আবির্ভাব কামনা করেছিলেন।
- সংহারক ও রক্ষক – শিব হলেন একাধারে সংহারক ও রক্ষক। তিনি ধ্বংসের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি করেন। তাঁর আবির্ভাবে প্রলয় সংঘটিত হয়। প্রলয় নিয়ে আসে ধ্বংস, আর সেই ধ্বংসের সঙ্গে আসে বিনাশের জন্য বেদনা।
- সৃজন-বেদন – কিন্তু প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির আগমন সুনিশ্চিত হয়। আপাত ধ্বংসের পেছনে সৃষ্টির অবস্থান বলে কবি প্রলয়কে ‘সৃজন-বেদন’ বলেছেন।
“কাল-ভয়ংকরের বেশে এবার ওই আসে সুন্দর!” – ‘কাল-ভয়ংকরের’ পরিচয় দাও। কীভাবে তিনি সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করবেন বলে কবির ধারণা?
কাল-ভয়ংকরের পরিচয় – কাল-ভয়ংকর হলেন ‘প্রলয়নেশার নৃত্যপাগল’ শিব। তিনি আসেন কালবৈশাখীর রূপ ধরে। তাঁর হাতে বজ্রশিখার মশাল। সর্বনাশী জ্বালামুখী ধূমকেতুর মতো তাঁর আগমন ঘটে। রক্তমাখা কৃপাণ হাতে অট্টহাসি হেসে তিনি যাবতীয় অশুভ শক্তির অবসান ঘটান। জীবনহীন অসুন্দরকে তিনি ছেদন করেন বলে তাঁর আগমন ধ্বংসাত্মক। সমাজ-সভ্যতা যদি রথের প্রতীক হয়, তবে তিনি সেই রথের সারথি। রক্ত-তড়িৎ চাবুক হেনে তিনি দুরন্ত ঘোড়ার গতিকে আরও বাড়িয়ে দেন। সেই ঘোড়ার খুরের দাপটে আকাশে উল্কার ছোটাছুটি বা স্থান পরিবর্তন ঘটে। এভাবে মহাবিশ্বের সব কিছুর পরিবর্তন ঘটে।
সুন্দরের প্রতিষ্ঠা – সমাজের জীর্ণ-পুরাতনকে ধ্বংস করে মহাকাল শিব নতুনের বার্তা বয়ে আনেন। প্রলয়রূপী শিবের আগমনপ্রার্থনার মধ্য দিয়ে কবি নতুন সূর্যোদয় প্রার্থনা করেছেন। মানুষের অন্ধবিশ্বাস, বিপথগামিতা, দাসত্ব এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় দূর না করলে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শিব নিজেই সত্য ও সুন্দরের প্রতীক। তাঁর ধ্বংসমূর্তি যেমন প্রলয়কে আহ্বান করে, তেমনই তাঁর সৃষ্টিও সুন্দরেরই প্রতিষ্ঠা ঘটায়। তাই সমাজের জীর্ণ অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে তিনি সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করবেন। এই কারণেই কবি মহাকালরূপী শিবের আগমনে সকলকে জয়ধ্বনি দিতে বলেছেন।
“ওই ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর?” – ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় ভাঙা-গড়ার কোন্ রূপকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখো।
- নবযৌবনের বন্দনা – ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি নজরুল চিরবিদ্রোহী নবযৌবনের বন্দনা করেছেন। এই বিপ্লবী শক্তির আগমন ঘটে ভয়ংকরের বেশ ধরে। ‘মহাকালের চণ্ড-রূপে’, অর্থাৎ শিবের প্রলয়ঙ্কর মূর্তিতে যেন তাদের আগমন।
- মৃতপ্রায় সমাজের অবসান – ‘জয় প্রলয়ঙ্কর’ ধ্বনি তুলে জরাগ্রস্ত মৃতপ্রায় সমাজের তারা অবসান ঘটায়। চারপাশ দিশাহারা হয়ে যায় শক্তির সেই প্রচণ্ডতায়। রক্তাক্ততা, বিশৃঙ্খলা, এবং অস্থিরতার মধ্য দিয়ে তাদের এই আবির্ভাবে যে ধ্বংসের উন্মাদনা থাকে, তা মানুষকে শঙ্কিত করে তোলে।
- সৃষ্টির নবনির্মাণ – ধ্বংসের এই প্রচণ্ডতা আসলে সৃষ্টির নবনির্মাণের জন্য। প্রলয়ের দেবতা শিব ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকে নিশ্চিত করেন। সেভাবেই বিপ্লবী শক্তিও আপাত নৈরাজ্যের আড়ালে সুস্থ, সুন্দর এক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে। কবির চোখে এই প্রলয় তাই জড়ত্বের অবসান ঘটানোর জন্য।
- মানবতার প্রতিষ্ঠা – কালরাত্রির শেষেই রয়েছে ভোরের সূর্যোদয়। অন্ধকারাগারের হাড়িকাঠে যে দেবতা বাঁধা আছেন, তাকে মুক্ত করে মানবতার প্রতিষ্ঠা ঘটানোই এই তরুণদের লক্ষ্য। এই প্রলয় তাই ‘নূতন সৃজন-বেদন’।
- নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত – জীবনহারা অসুন্দরকে ছিন্ন করার জন্য যার আগমন ঘটেছে। তাই ভাঙনের পেছনে থাকে সৃষ্টির স্বপ্ন। স্বাধীনতা, সাম্য এবং সম্প্রীতির বীজমন্ত্রে থাকে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত।
“তোরা সব জয়ধ্বনি কর!” – কাদের উদ্দেশ্যে কবির এই আহ্বান? কবিতায় কেন এই আহ্বানটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে লেখো।
অথবা, “তোরা সব জয়ধ্বনি কর।” – তোরা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? তারা কেন জয়ধ্বনি করবে?
অথবা, “প্রলয়োল্লাস” কবিতায় একদিকে ধ্বংসের চিত্র আঁকা হয়েছে আবার অন্যদিকে নতুন আশার বাণী ধ্বনিত হয়েছে-কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো।
যাদের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান – ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানিয়েছেন।
আহ্বানের পুনরাবৃত্তির কারণ – প্রলয়োল্লাস কবিতায় মোট উনিশবার “তোরা সব জয়ধ্বনি কর” এই আহ্বানসূচক পঙক্তিটি উচ্চারিত হয়েছে, যা বুঝিয়ে দেয় এই পঙক্তিটিতেই কবি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে ‘প্রলয়োল্লাস’ হলো ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির বন্দনা। স্বাধীনতাপ্রিয় যে তরুণের দল তাদের দুর্জয় সাহস আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পরাধীনতা এবং সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে চায়, কবি তাদেরই জয়ধ্বনি করতে বলেছেন। কবির কথায় তারা হলো ‘অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল’, কিন্তু তারাই সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে আঘাত করে নতুন চেতনা, বিপ্লবের বার্তা বয়ে আনে। অসুন্দরকে দূর করতে তারা আপাতত ভয়ংকরের বেশ ধারণ করে। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নবপ্রাণের প্রতিষ্ঠা ঘটে, প্রাণহীনতার বিনাশ হয়। “… জগৎজুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে/জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ওই বিনাশে!” প্রলয়ংকর শিবের মতো রুদ্রমূর্তিতে যে বিপ্লবী শক্তির অভ্যুদয় ঘটে, তারাই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির কারিগর। তাই তাদের অভ্যর্থনা জানাতে হবে, সমাজকে সুন্দর করে তুলতে। এ কারণেই ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর’ পঙক্তিটি কবিতায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এটি বিপ্লবী যুবশক্তির প্রতি কবির মুগ্ধ অভিবাদন।
‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করো।
অথবা, ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় প্রলয়ের মধ্যে কবি উল্লাস অনুভব করেছেন কীভাবে বুঝিয়ে লেখো।
অথবা, ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় কবি প্রলয় ও আশাবাদের সুর কীভাবে ব্যক্ত করেছেন তা বর্ণনা করো।
- প্রাককথন – কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রলয়োল্লাস’ আসলে কবির জীবন-উল্লাসের কবিতা। শোষণ-বঞ্চনা, পরাধীনতার নাগপাশকে ছিন্ন করে জীবনের যে জাগরণ ঘটে, স্বাধীনতা আর সাম্যের ভোরে যার ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি প্রকাশ পায় ওই একই বছরে ধূমকেতু পত্রিকার এক সংখ্যায় নজরুল লেখেন – “পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খলা মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।”
- সুন্দরের আবির্ভাব – ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাতেও দেখা যায় – “সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল”। পঙক্তিটি দেখেই বোঝা যায় কবি স্পষ্ট বিদ্রোহের কথাই বলছেন। ভয়ংকরের বেশে এ হল সুন্দরের আবির্ভাব। প্রবল তেজ, বিপর্যয় নিয়ে যে বিপ্লবীশক্তির আগমন ঘটে তা প্রাথমিকভাবে শঙ্কিত করতে পারে, কিন্তু বিশ্বমায়ের আসন সে-ই পাতে।
- চিরসুন্দরের প্রতিষ্ঠা – কবি দেখেছেন “অন্ধ কারার বন্ধ কূপে/দেবতা বাঁধা, যজ্ঞ-যূপে” – এই ‘দেবতা’ স্বাধীনতার প্রতীক। এখান থেকে মুক্ত হয়ে তার আগমনের সময় হয়ে গিয়েছে। রথচক্রের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তাই আলোচ্য কবিতায় কবি বলেছেন যে ধ্বংস দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, প্রাণহীন অসুন্দরকে বিনাশ করতেই এই ধ্বংস। এরপরই চিরসুন্দরের প্রতিষ্ঠা ঘটবে। তাকেই স্বাগত জানানোর জন্য সকলকে আহ্বান করেছেন কবি।
‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটিতে কবির রচনারীতির যে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, তা লেখো।
- রচনাশৈলী – বাংলা সাহিত্যে ‘বিদ্রোহী’ কবি হিসেবে নজরুলের প্রতিষ্ঠা হলেও সেই বিদ্রোহের সুরকে কবিতায় সার্থক করে তুলেছেন নজরুল তাঁর অনবদ্য রচনাশৈলীর মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য তাঁর কবিতাকে বিশেষত্ব দিয়েছে।
- শব্দ প্রয়োগ – পবিত্র সরকার নজরুল সম্পর্কে বলেছেন, “বাংলার প্রায় সমস্ত কবির তুলনায় নজরুলের অভিধান বিস্তৃততর।” কিন্তু আরবি-ফারসি শব্দের যে বিপুল ব্যবহার নজরুলের কবিতায় সাধারণত দেখা যায়, তা ‘প্রলয়োল্লাস’-এ নেই। বরং তৎসম শব্দবাহুল্য থাকা সত্ত্বেও এই কবিতায় ধ্বনিময়তা ও গাম্ভীর্য এসেছে। যেমন – “দ্বাদশ রবির বহ্নিজ্বালা, ভয়াল তাহার নয়নকটায়/দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!”
- পঙক্তিটি বিন্যাস – কবিতার চালচলনে একইসঙ্গে উচ্ছ্বাস ও গাম্ভীর্য মিলে যাওয়া নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। কবিতার পঙ্ক্তিগুলি অসম হলেও, তার অন্ত্যমিল সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় ধ্রুবপদের মতো ফিরে এসেছে “তোরা সব জয়ধ্বনি কর!” পঙক্তিটি। এই জয়ধ্বনিই কবিতার মূলকথা—স্বাধীনতার ও নবযুগের।
- ভাষা ও ছন্দের মিশেল – বিপ্লবীশক্তির যে জীবনোল্লাস কবিতার প্রাণ, তা ভাষা ও ছন্দের মধ্যে অনায়াসে মিশিয়ে দিয়েছেন কবি। তীব্র বেদনা, ক্রোধ, এবং সেখান থেকে নতুন জাগরণের স্বপ্ন — কবিতার নির্মাণে এগুলো ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে।
‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতা অবলম্বনে কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামী চেতনার পরিচয় দাও।
- কথামুখ – কবি নজরুল কলমকে তরবারিতে রূপান্তরিত করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অংশীদার হয়েছিলেন। ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি কবির সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার অনবদ্য প্রকাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়েই নজরুলের কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটে।
- সামাজিক অবক্ষয় – তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন সমকালীন সমাজের সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের রূপ। এই পচনশীল সমাজ ধ্বংস করে নতুন সমাজ গড়ার অদম্য ইচ্ছা বুকে নিয়ে কবি মহাকালরূপী শিবের আগমন কামনা করেছেন।
- নটরাজ শিবের আগমন – নজরুল জানেন, সর্বব্যাপী দুর্দশা আর অবক্ষয় থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচাতে রক্ষক ও সংহারক নটরাজ শিবকেই প্রয়োজন। এই অলৌকিক শক্তিই সামাজিক পাঁকে ফোটাবে মানবিকতার পদ্ম।
- সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা – মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হলেই সমাজে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হবে। তার জন্য জীর্ণতার অবসান চাই। ধ্বংসরূপী শিব তাঁর বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে রুদ্রমূর্তিতে আবির্ভূত হবেন। তিনি ভেঙে দেবেন জড়তাগ্রস্ত, বিপথগামী সমাজকে।
- শিবের সংহারক মূর্তি – সমগ্র কবিতায় প্রলয়রূপী শিবের সংহারক মূর্তিকেই কবি তুলে ধরেছেন। নজরুলের সংগ্রামী চেতনার পথেই নটরাজ শিবের আবাহন সূচিত হয়েছে। এই শিবই দিনবদলের সূচনা করবেন।
- দেশপ্রেমের স্বরূপ – শিবের প্রতীকে নজরুল তারুণ্যের শক্তিকে মর্যাদা দিয়েছেন। সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য কবির এই চেষ্টা তাঁর দেশপ্রেমের স্বরূপকেই স্পষ্ট করে তোলে।
‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় নজরুল সমাজ পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার বর্ণনা দাও।
অথবা, ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতার পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে নজরুলের কবিমানসের পরিচয় দাও।
- কথামুখ – ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে ইংরেজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে কঠোর দমননীতির আশ্রয় নিয়েছিল। নজরুল এ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, বিপ্লবীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।
- মূল্যবোধের অবক্ষয় – পাশাপাশি, ধর্মের নামে ভণ্ডামি চলছে চারদিকে। মেকি দেশনেতারা স্বার্থের খেলায় মেতে উঠেছে। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়কে আরও ত্বরান্বিত করেছে।
- সমাজ পরিবর্তন – নজরুল অনুভব করেছিলেন যে, সমাজকে পালটাতে হলে আগে মানুষকে জাগ্রত করতে হবে। জড়তাগ্রস্ত, মৃতপ্রায় মানুষদের জীবনের আলোয় ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন প্রলয়রূপী শিবের মতো কোনো অলৌকিক শক্তির।
- সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা – সত্য ও সুন্দর প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে জাতিকে গ্রাস করবে অসুন্দর। নজরুল কামনা করেছেন নটরাজ শিবের আবির্ভাব। এই নটরাজ শিবই হলেন নববিধানের বাণীবাহক। তিনি পুরোনো ও জীর্ণ সমাজকে ধ্বংস করে সত্য ও সুন্দর প্রতিষ্ঠা করবেন। নজরুল আশাবাদী এই ভেবে – “এবার মহানিশার শেষে/আসবে ঊষা অরুণ হেসে।”
- জয়ধ্বনি – নতুন সৃষ্টির জন্য তিনি প্রলয়ংকরের জয়ধ্বনি করেছেন। ধ্বংস দেখে ভয় নয়, বরং সৃষ্টির আনন্দে ভরে উঠেছে কবির মন। সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় ভয়ংকরের ভীষণ রূপ তখন আর ভীতিজনক মনে হয়নি। বরং তাঁকে বরণ করার প্রত্যাশায় নজরুল দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন।
কাজী নজরুল ইসলামের প্রলয়োল্লাস কবিতার নামকরণ কতদূর সার্থক হয়েছে বিচার করো।
নামকরণ হলো যে কোনো সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে প্রবেশের মূল চাবিকাঠি। নামকরণের মাধ্যমে লেখক তার রচনাটি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন। আলোচ্য “প্রলয়োল্লাস” কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামের শুভচেতনার বাণী প্রতিফলিত হয়েছে। সত্য, শিব এবং সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি এই কবিতায় ধ্বংসের দেবতা শিবকে আহ্বান করেছেন। “প্রলয়োল্লাস” নামকরণের মাধ্যমে শিবের ভাঙাগড়ার গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।
শিব হলেন প্রলয়ের দেবতা। একদিকে তিনি যেমন সৃষ্টির দেবতা, অন্যদিকে তেমনই ধ্বংসের দেবতা। আলোচ্য কবিতায় প্রলয়দেবের ধ্বংসাত্মক রূপই মুখ্য। তিনি আসছেন কালবৈশাখী ঝড়ের রূপ ধারণ করে, সামাজিক অসংগতি, ধর্মান্ধতা, পরাধীনতা এবং সর্বব্যাপী অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাতে। নটরাজ শিবের আগমনে কবি আকাশে নতুনের পতাকা উড়তে দেখেছেন। প্রলয়নৃত্যে মত্ত শিব বন্দি ভারতবাসীকে মুক্তি দেবেন। মহাভয়ংকর রূপে বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে তিনি আসছেন। জগৎজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে কবি বলতে চেয়েছেন, সেই আতঙ্ক সাময়িক। কারণ মহাকাল শিব নিত্য ভাঙাগড়ার খেলায় মগ্ন। তিনি সামাজিক অন্ধকার দূর করে শুভচেতনার উদয় ঘটাবেন। নতুন সৃষ্টির জন্য ভাঙনই তাঁর নেশা। তাই প্রলয়ের সময়ও তাঁর উল্লাস ধরা পড়ে। কবিও সেই কথাই বলেছেন – “প্রলয় বয়েও আসছে হেসে/মধুর হেসে।” কবির অভিপ্রেত বক্তব্যকে সামনে রেখে বলা যায় যে, কবিতাটির নামকরণ একেবারে সার্থক।
আজকের আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক বাংলার পঞ্চম পাঠের তৃতীয় বিভাগ, ‘প্রলয়োল্লাস’ থেকে কিছু বিশ্লেষণধর্মী ও রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকে, তাহলে আমাকে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করুন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এছাড়াও, নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।


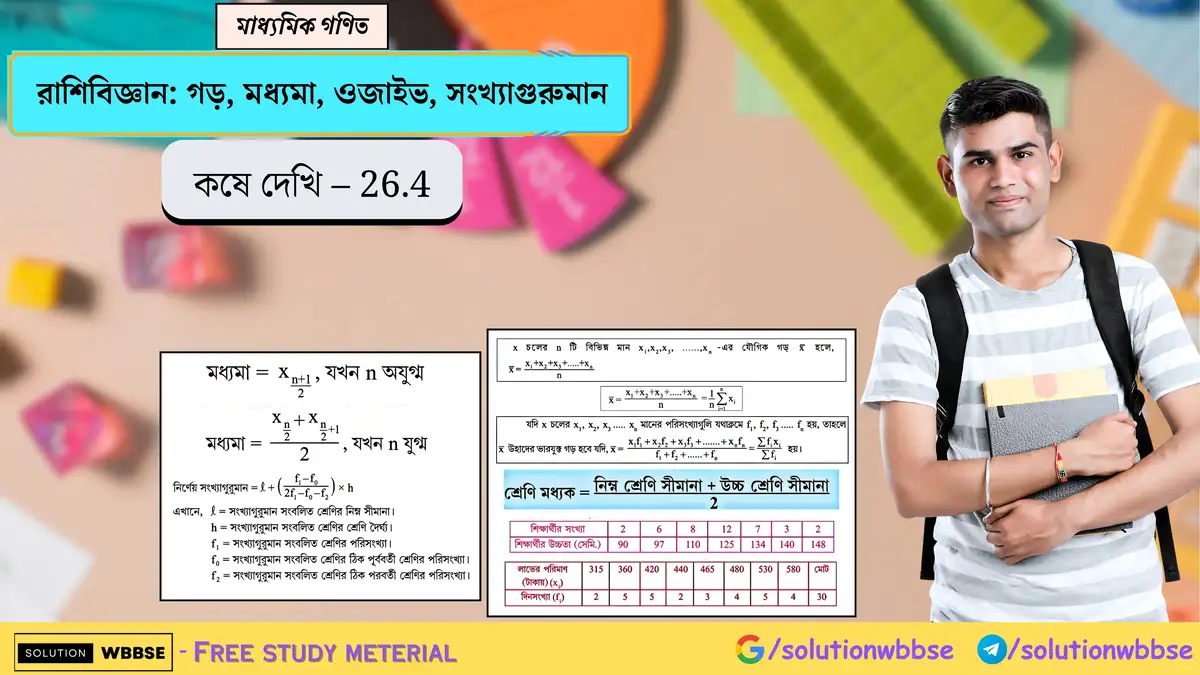
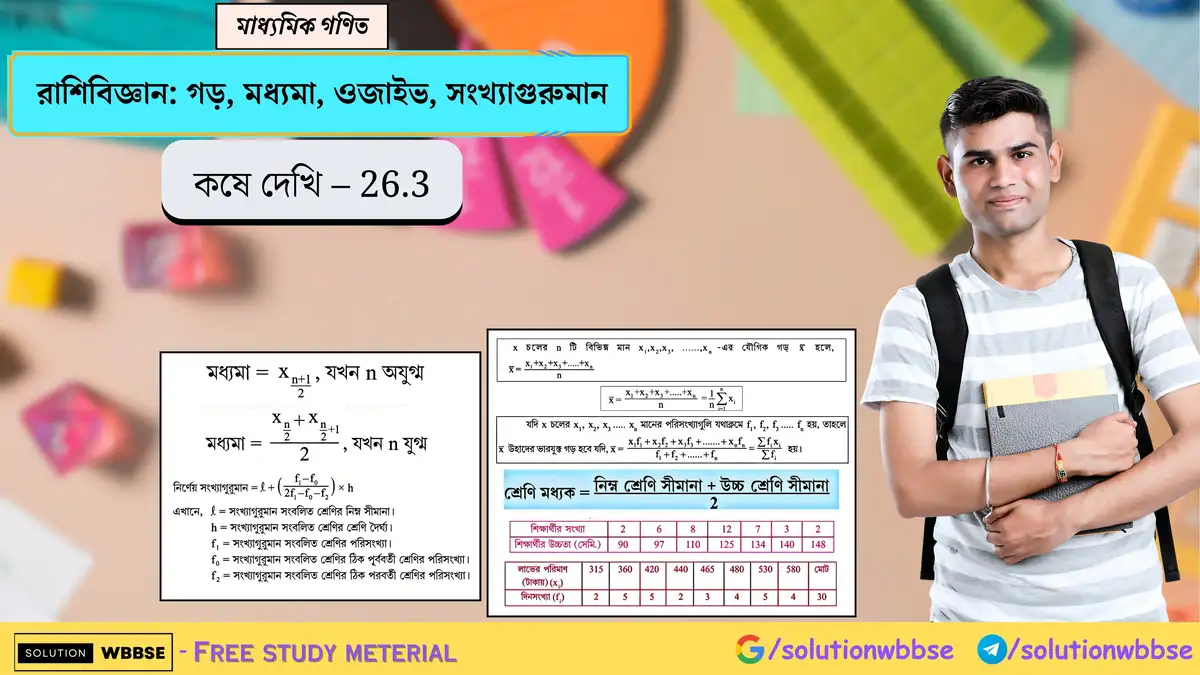
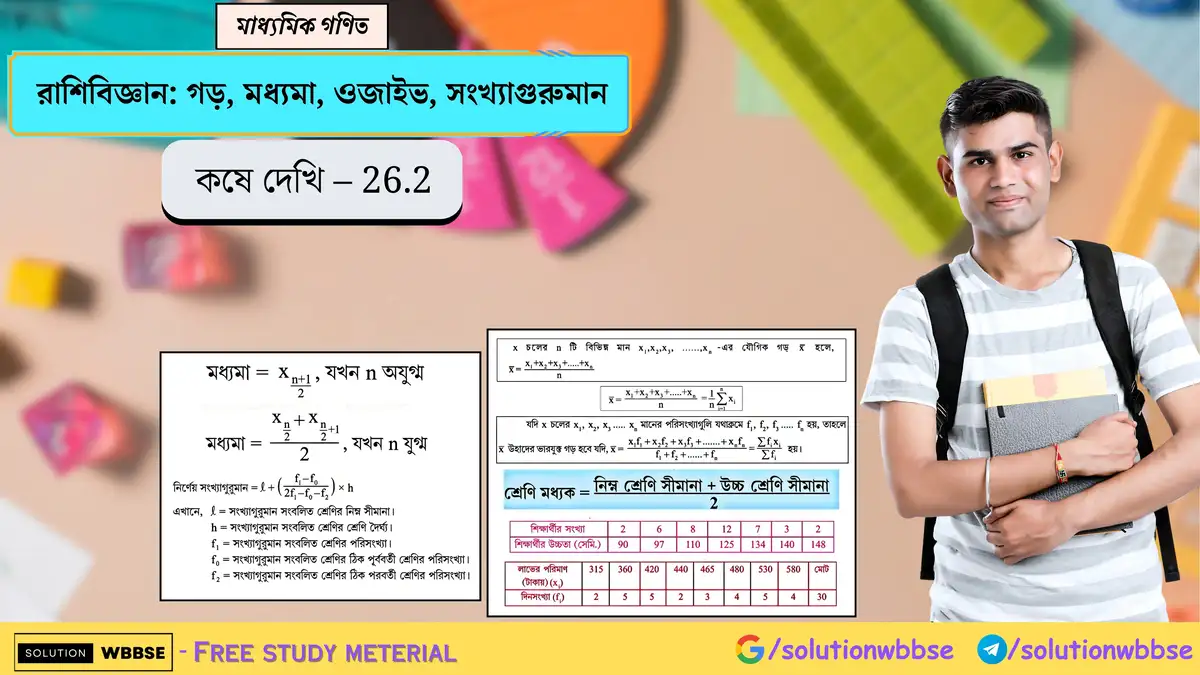

মন্তব্য করুন