আজকের এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের চতুর্থ পাঠের প্রথম অধ্যায়, ‘খেয়া’ -এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নোত্তরগুলো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নবম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত আসে।
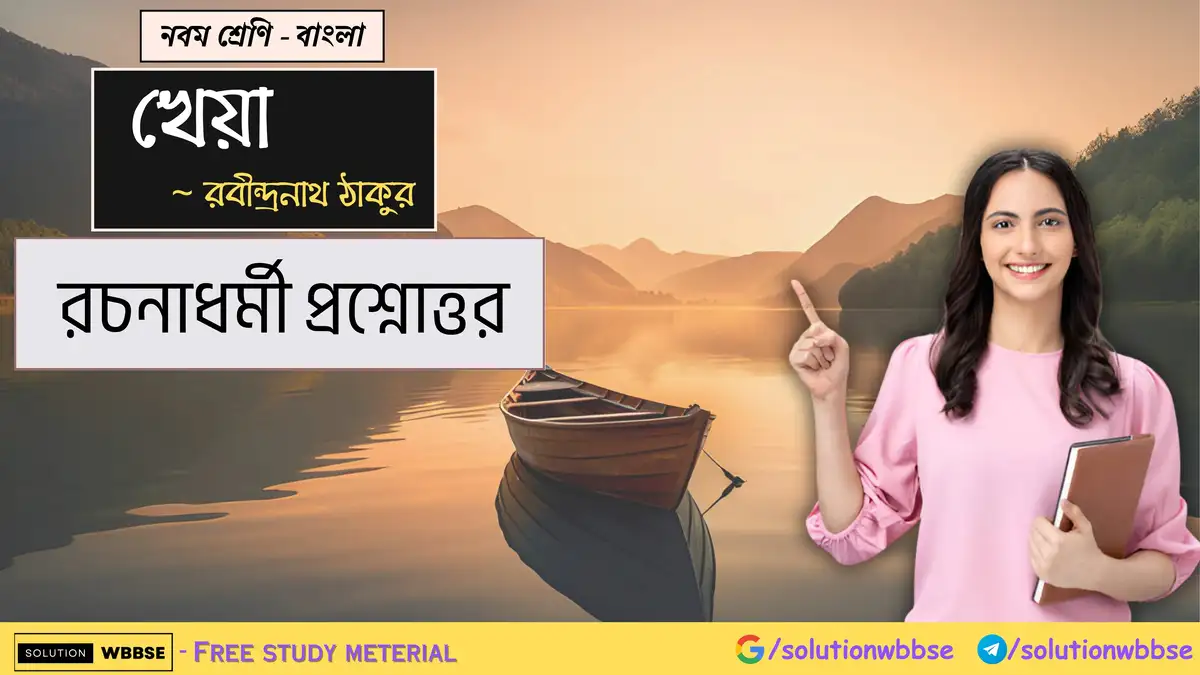
‘খেয়া’ কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
ভূমিকা – সাহিত্যের আঙ্গিনায় শিরোনাম পাঠক আর লেখকের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে। নামকরণের মাধ্যমে পাঠক মূল বিষয়ের একটা আভাস পেয়ে যায় আবার লেখক তাঁর সৃষ্টিকে পাঠকমহলে প্রথম পরিচয়ও করান এই শিরোনামের সহায়তায়—ফলত নামকরণের গুরুত্ব ও অনিবার্যতা আজ প্রশ্নাতীত। মূল বিষয়ের নির্যাস এখানে আভাসিত হয়, সাহিত্যিক সচেতনভাবে সযত্নে এই শিরোনাম প্রয়োগ করেন। ‘খেয়া’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার বিষয়ের গভীর ব্যঞ্জনাকে আরও গভীরতা দান করলেন নামকরণের মাধ্যমে।
নামকরণের সার্থকতা – মানবজীবন প্রবাহের অনিবার্য ও চিরন্তন গতিময়তাকে কুর্নিশ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কবিতার শিরোনাম রেখেছেন ‘খেয়া’। দেশি এই প্রচলিত শব্দের অনুষঙ্গে এসেছে নদীস্রোত, ঘাট, পারাপার, যাত্রী, তাদের নিত্যকর্ম। শত ব্যস্ততা, প্রতিকূলতার মধ্যে এপার-ওপারকে মিলিয়ে দেয় এই খেয়া। নদীতটের নির্জনতায় বসে উদাসী কবি দেখেছেন মানুষের হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ-রক্তরঞ্জিত ইতিহাসের বহু অধ্যায়। কিন্তু তা জীবনের সহজ অনাড়ম্বর চলনকে রোধ করতে পারেনি কখনও। ঋষিসম উদাসীনতা থেকে নদী বয়ে চলেছে, নবীন আর প্রবীণের ভিড়ে ভরিয়ে দিয়েছে তরিকে।
উপসংহার – জীবনরসে সিক্ত কবি অনন্ত প্রসারিত দৃষ্টিতে জীবনকেই সর্বদা বিজয়ী হতে দেখেছেন। বক্ষে ভাসমান জীবননদীর খেয়াতরি সদা ভরে থেকেছে নবীন আর প্রবীণ যাত্রীদলের ভিড়ে। তার গতি অপ্রতিরোধ্য, তার গন্তব্য অসীমের দিকে। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘খেয়া’ কবিতায় শিরোনামটি গভীর ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ এবং সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।
‘খেয়া’ কবিতায় কীভাবে গভীর জীবনভাবনা সংহতরূপে প্রকাশিত হয়েছে?
ভূমিকা – অমরত্বের প্রত্যাশী কিংবা বৈরাগ্যসাধনে মুক্তিলোভী নন, বরং মর্ত্যপ্রেমে প্রাণিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবের নিরন্তর প্রবাহধারার স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন যুগান্তরের ঋষিসুলভ নিমগ্ন সাধনায়। সেই গভীর বিস্তৃত কবিভাবনা ‘খেয়া’ কবিতার ছোটো পরিসরে মুক্তি পেয়েছে অনন্য কাব্যশৈলীর মধ্য দিয়ে।
কাব্যশৈলী – ‘খেয়া’ কবিতা নির্মাণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কাব্যধারার মেলবন্ধন করেছেন কবি। সনেটের আঁটোসাঁটো পরিধিতে কবি তাঁর সুগভীর জীবনদর্শনকে মুক্তি দিয়ে, খেয়া নৌকা-যাত্রীদল-নদীস্রোতের প্রসঙ্গে এনেছেন মানবের দর্পিত অস্তিত্বের কাহিনিকে। নদীপারের গ্রাম দুটি তাই মানবসভ্যতার আঁতুড়ঘর হয়ে থেকেছে চিরকালের জন্য।
কবির জীবন ভাবনা – কালান্তক হিংসার আগুনে পুড়েছে সাধের মানবজীবন, খোদিত হয়েছে রক্তাক্ত ইতিহাস। আবার সেই ইতিহাসে বিজয়ীর গৌরব যাবতীয় অর্থ হারিয়েছে। পক্ষান্তরে সন্ধ্যাতারার মতো দূর নদীপারে জেগে রয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার অসীম প্রেরণা – সেই পবিত্র শক্তিধারাই মানুষের শাশ্বত চলনকে গতিশীলতা দান করেছে –
“এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে-
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।।”
ভাববাদী কিংবা মায়াবাদী হতে পারেননি কবি; বরং মর্ত্যপ্রেমে আপ্লুত হয়ে গরলে-অমৃতে সিক্ত জীবনের পবিত্র প্রবাহের অন্বেষণকে পূর্ণ করেছেন।
‘খেয়া’ কবিতায় কবির বাস্তববোধের পরিচয় দাও।
অথবা, কবিমনের কোন্ বৈশিষ্ট্য ‘খেয়া’ কবিতায় প্রকটরূপে প্রতিভাত হয়েছে?
ভূমিকা – রবীন্দ্রকাব্য ধারার দ্বিতীয় পর্বে লিখিত ‘চৈতালি’ কাব্য থেকে পাঠ্য ‘খেয়া’ কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। নানা উত্থানপতনে ভরা মানব-সভ্যতার চিরন্তন প্রবাহধারার স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন কবি আলোচ্য কবিতায়; আর সেই সূত্রেই কবির গহন মনের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে।
অনন্ত জীবনপ্রবাহ – অখণ্ড নিসর্গানুভূতিকে পূর্ণতা দিয়েছে মানুষ প্রকৃতি-প্রেম-সৌন্দর্য; সেই তৃপ্ত অনুভব নিয়ে কবি দৈনন্দিন জীবনের মাঝেই অনন্ত জীবনপ্রবাহকে অবলোকন করেছেন। প্রতিদিনের জীবনযাপনের স্থবিরতা-দৈন্যতায় পীড়িত কবিমন শেষপর্যন্ত মর্ত্যপ্রেমেই ফিরে এসেছেন। বৈরাগ্যবিমুখ জীবনপ্রীতিই তাঁর আরাধ্য; আর সে সাধনার শেষে একাকী নৈঃশব্দ্যের মাঝে, সমাহিত প্রকৃতির শান্ত কোলে জীবনকে দেখেছেন নদীস্রোতের রূপে।
বাস্তবতা বোধ – জীবন বাস্তবতাকে কবি আবেগশূন্য দৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন নিসর্গসৌন্দর্যের মাঝে দাঁড়িয়ে। অতীতচারী হয়ে অখণ্ড মানবসভ্যতার প্রবাহধারাকে মূর্ত করেছেন তিনি। আধ্যাত্মিক জীবন উপলব্ধির মাধ্যমে রবীন্দ্র-ভাবনায় উৎসারিত হয়েছে বাস্তব জীবনচিত্রের মধ্যেই বিমূর্ত এক ভাবনা। এখানে রোমান্টিক ভাবব্যাকুলতা প্রাবল্য পায়নি; বরং বহুকালের সাধনায় নিমগ্ন এক ঋষির বাণীরূপ হয়ে উঠেছে এই খেয়া। সেই শুচিশুভ্র অনুভবে কবি বলেছেন –
“এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে-
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।।”
উপসংহার – ভাববাদী কিংবা মায়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেননি কবি, বরং জীবনের অখণ্ড প্রবাহধারাকে অবলোকন করেছেন নিসর্গসৌন্দর্য বৈভব আর মর্ত্যপ্রীতির মাধ্যমে। তাই ইতিহাসকে কবির মনে হয়েছে বিজয়ী আর বিজিতের হিংসা-হননের রক্তাক্ত অধ্যায়। সেই ধ্বংসের, সর্বনাশের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ থেকে বহু যোজন দূরের এই গ্রাম দুটিতেই তিনি প্রকৃত মানবতার প্রবাহকে খুঁজে পেয়েছেন। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে আহৃত বলে ‘খেয়া’ কবিতায় চিত্রিত সৌন্দর্যপট সুগভীর আত্মোপলব্ধিতে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে।
‘খেয়া’ কবিতায় সভ্যতার ইতিহাসের বাস্তবচিত্র কীভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কবির এই ভাবনাটিকে তুমি কী সঠিক বলে মনে করো?
অথবা, ইতিহাসের যে ইঙ্গিত ‘খেয়া’ কবিতায় আভাসিত তা স্পষ্ট করো।
ভূমিকা – ইতিহাস সচেতন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা ‘খেয়া’ কবিতায় মানবসভ্যতার সমস্ত প্রবাহধারার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তথাকথিত ইতিহাসের কঠোর সমালোচনা করেছেন। নির্জন নদীতটে উদাসী কবির একাকী অনুভবে উঠে এসেছে ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা, দ্বন্দ্ব-বিক্ষুদ্ধে ভরা খণ্ড ইতিহাস।
ইতিহাসের বাস্তবচিত্র – সভ্যতার বিবর্তনের নানা পর্যায়ে উত্থানপতনের বন্ধুর পথ ধরে এগিয়ে চলা মানবের ইতিহাসে কবি দেখেছেন –
“পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস-“
একদিকে অতীত ঘটনারাজির উন্মাদনা-উন্মত্ততা, অন্যদিকে নিস্পৃহ, নির্মোহ জীবনের স্বাভাবিক চলন – এই দ্বিতীয় পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে প্রকৃত মানবসভ্যতা। হিংসা-দ্বেষ-রাগ-রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস যে মানবতার পথে বারবার ‘সর্বনাশ’ ডেকে এনেছে তা কবিহৃদয়কে নিদারুণভাবে পীড়িত করেছে। ইতিহাসের রাজশক্তির দম্ভকে হাস্যকর, অর্থহীন বলে মনে হয়েছে কবির।
কবির ভাবনা – ভাবনাটি যথাযথ, কেন-না অতীতচারী কবি ইতিহাসের তথ্য, তত্ত্ব, ঘটনাধারায় শুধু মানবসভ্যতার উত্থানপতনের তরঙ্গমালাকে অবলোকন করেছেন। সেখানে দেখেছেন কালে কালে যে জীবন উপেক্ষিত সেই সাধারণ নিস্তরঙ্গ জীবনের হাত ধরেই মানবসভ্যতার গতি বহমান। দূর খেয়াঘাটের নির্জনতায় একাকী কবি মনশ্চক্ষে তা লক্ষ করেছেন এবং বলেছেন –
“সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা-
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!”
কিন্তু সাধারণের জীবনযাপনে, তাদের কর্ম-উদ্দীপনায়, জীবনের অনন্ত প্রেরণায় মানবসভ্যতার যে ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছে; তা শাশ্বত, চিরন্তন। তাই নদীতটের গ্রাম দুখানি ইতিহাস উদাসীন থেকে নিভৃতে জীবনের পূজায় যাবতীয় উপাচার সাজিয়ে রেখেছে – নদীতট, খেয়াতরি, যাত্রীদল, নদীস্রোত আসলে সভ্যতার তিলোত্তমা প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেছে। সুতরাং সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কিত কবির ভাবনাটি সঠিক।
‘খেয়া’ কবিতাটিতে কবির সমাজজীবন চিত্রের মূল ভাবনাটি পরিস্ফুট করো।
ভূমিকা – পার্থিব জগতের অনিবার্য বাস্তবতার মাঝে দাঁড়িয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রোমান্টিক অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের বিস্তৃত কালে খুঁজতে চেয়েছেন তিনি মানবসভ্যতার বিরামহীন ধারার স্বরূপটিকে – সেই অনন্য অন্বেষণের কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে ‘খেয়া’ নামক সনেটটির ছোটো পরিসরে।
গ্রামীণ সমাজচিত্র – চিরন্তন গ্রামীণ সমাজচিত্রের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে খেয়াঘাটের এপার-ওপারে। দুই তীরে দুখানি গ্রাম রেখে নদীটি প্রবাহিত হয়ে গেছে। সুস্থ জীবনের অনিবার্য সম্পর্ক রক্ষার তাগিদে, জীবনধারণে পরস্পরের নির্ভরশীলতার জন্য গ্রামের মানুষগুলো এপার-ওপার করে খেয়া নৌকার মাধ্যমে। জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তার জন্য এপার ছুটে যায় ওপারে, ওপার আসে এপারে।
মানবসভ্যতার রূপক – কিন্তু গ্রাম দুটির রূপকে আসলে রবীন্দ্রনাথ মানবসভ্যতায় মানুষের নিরন্তর আসা-যাওয়াকেই ইঙ্গিত করেছেন। জীবনরূপ নদীতে জীবনেরই তরি বেয়ে মানুষ জন্ম থেকে যাত্রা করে। আর সে যাত্রা মৃত্যুতে মিলিয়ে যায়। তাই দুখানি গ্রাম দুজনের প্রতি চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে, তাদের মধ্যে জানাশোনা যুগ-যুগান্তরের, তাই তাদের সম্পর্ক নিবিড়। সেই শাশ্বত পরিচয়ের ডোরে তারা উভয়কেই বেঁধে রেখেছে। তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল, একের বিহনে অন্যজন অসম্পূর্ণ। কবি নদীঘাটে একাকী বসে উদাস নয়নে বিষণ্ণ সেই সত্যকেই উদ্ঘাটন করলেন ইঙ্গিতপূর্ণ এই নির্মল নিসর্গ-মাঝে চিত্রিত সমাজ-অবয়বের মাধ্যমে।
‘খেয়া’ কবিতায় কবিতাশৈলীর দিক থেকে কোন্ বিশেষত্ব ধরা পড়ে?
ভূমিকা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘খেয়া’ একটি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। এখানে কবি মানবসভ্যতার চিরন্তন স্বরূপের অন্বেষণ করেছেন সনেটের সীমিত পরিসরের মধ্যে।
সনেট – নবজাগরণের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কবি তাঁর জীবনদর্শন ও সাহিত্য-প্রকরণে নতুনত্ব নিয়ে আসেন। সেই নব ভাবধারার ফলিত রূপ তাঁর এই সনেট নির্মাণ। ইটালির কবি পেত্রার্কের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট লেখেন কবি মধুসূদন; সে ধারার আরও সমৃদ্ধি ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে। সনেট নির্মাণের অবশ্যম্ভাবী শর্ত হিসেবে কবি ‘খেয়া’ কবিতায় চোদ্দোটি পঙক্তি ব্যবহার করেছেন, তাদের বিভাজিত করেছেন ‘অষ্টক’ আর ‘ষটক’-এ।
ভাষার সংহত ব্যবহার – সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে আহৃত বলে এ কবিতার ভাবনার সঙ্গে সংগতি রেখে ভাষা হয়ে উঠেছে সংহত-অনাবশ্যক বর্ণনা দোষে কাতর নয়। সনেটের সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে খেয়া নৌকা, যাত্রীদল, নদীস্রোত ইত্যাদির রূপকে জীবনপ্রবাহের প্রসারিত ও শাশ্বত স্বরূপের উদ্ঘাটন করেছেন কবি। তাই সুগভীর ভাবনা, সংহত ভাষা, সীমাবদ্ধ পরিসর ও সনেটের মান্য শর্তাবলির প্রতিফলনে ‘খেয়া’ কবিতা সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষ সৃষ্টিরূপে ভাস্বর হয়ে রয়েছে।
‘কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে’। – পঙক্তিটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে? এরূপ ব্যবহারের কারণ কী, সে বিষয়ে তোমার যুক্তি দাও।
পঙক্তির ব্যবহার – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘খেয়া’ কবিতায় মানবজীবন প্রবাহের চিরন্তনত্ব বোঝাতে প্রশ্নোধৃত পঙক্তিটি দু’বার ব্যবহৃত হয়েছে।
নদীবক্ষে খেয়াতরি দুই তীরের দুইখানি গ্রামকে সম্পর্কের গভীরতায় বেঁধে রেখেছে, যাত্রীদের পারাপারে সদাব্যস্ত থেকেছে। এদের সম্ভাব্য গন্তব্য প্রসঙ্গে কবি মন্তব্য করেছেন –
‘কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।।’
পঙক্তি ব্যবহারের কারণ – জীবননদীর দুই কূলে গ্রাম দুই খানি দাঁড়িয়ে আছে জীবন-মরণের প্রতীক হয়ে। যাত্রীদল এপার থেকে ওপারে বা ওপার থেকে এপারে নিরন্তর যাতায়াত করে। দুই পারের যাত্রীদল কেউ কেউ নিজ ঘর থেকে গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করে, আবার অন্যদল বাইরে থেকে ফেরে আপন গৃহে। নির্জন নদীতটে দাঁড়িয়ে একাকী কবি উদাস হয়ে সেই নিরন্তর যাত্রাপথের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছেন। মানসচক্ষে কবি দেখেছেন এই খেয়া নৌকার যাত্রীদলই মানবের চিরন্তন বহমানতাকে নিশ্চিত করে চিরন্তনত্ব লাভ করেছে। মানুষের জীবনপ্রবাহ নদীর স্রোতের মতো, যাত্রী সকলের পারাপারের সদৃশ খেয়া নৌকায় জীবনযাত্রীবৃন্দও ভেসে চলেছে জন্ম থেকে মৃত্যুর পানে। অর্থাৎ এহেন পঙক্তি প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী ছিল কবিভাবনার প্রকাশে-তাই তা যুক্তিযুক্ত।
‘সকাল হইতে সন্ধ্যা’ কবি কেন বলেছেন? ‘দুই গ্রাম’ কীসের ব্যঞ্জনা বয়ে এনেছে?
সকাল হইতে সন্ধ্যার ব্যঞ্জনা – ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘খেয়া’ কবিতার প্রায় প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকাল ও সন্ধ্যার উল্লেখ করেছেন। খেয়া নৌকা নদীপারের গ্রাম দুটিতে একইসঙ্গে আনাগোনা করে; দিনের প্রারম্ভ আর পরিসমাপ্তির ঘোষণাবার্তা নিয়ে আসে। এখানে ‘সকাল’ হল মানবজীবনের শুরু আর ‘সন্ধ্যা’ সেই জীবনের অন্তিম লগ্নকে স্পষ্ট করে-তাই শব্দ দুটি গভীর ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত।
‘দুই গ্রাম’ -এর ব্যঞ্জনা – রোমান্টিক কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পানে প্রসারিত করে মানবের জীবনপ্রবাহকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। উদাসী কবির সম্মুখে প্রসারিত নদীস্রোত, এপার-ওপারে দুখানি সাধারণ গ্রাম – তারই মাঝে যাত্রীদল নিয়ে খেয়াতরি চলমান। দুটি গ্রাম পরস্পরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, যেন তারা বহু যুগের চেনাজানা। যাত্রীরা কেউ ঘরে ফিরেছে, কেউ বা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। তাদের আসা-যাওয়া চলেছে নিরন্তর। তথাকথিত সভ্যতা থেকে দূরবর্তী এই গ্রামদুটি পৃথিবীর হিংস্র উন্মত্ততায় বিচলিত নয়। তারা মিলনের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে নিজেদের অস্থিত্ব বজায় রেখেছে বহমান কাল ধরে। দুটি গ্রাম তাই কবির দৃষ্টিতে প্রবহমান মানবতার প্রতীক। নদীতটে একাকী উদাসী কবি তাই মানবের অনন্ত আসা-যাওয়ার অর্থ শেষত খুঁজে পেয়েছেন –
“এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে-
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।।”
‘পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ’ – ‘দ্বন্দ্ব’ ও ‘সর্বনাশ’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? এই দ্বন্দ্ব ও সর্বনাশ পৃথিবীতে কীসের ভূমিকা পালন করেছে? তার সঙ্গে খেয়া নৌকার যোগ কোথায়?
দ্বন্দ্ব ও সর্বনাশের স্বরূপ – সভ্যতার বিবর্তনের বিস্তৃত ইতিহাস লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুগ-যুগান্তরের মানুষের বিচিত্র কর্মকাণ্ড দেখেছেন; দেখেছেন হিংসায় মত্ত মানুষেরা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে বারবার ডেকে এনেছে সর্বনাশ।
পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব ও সর্বনাশের ভূমিকা – ইতিহাসের ধূসর অতীতে ধাবিত কবিমন খুঁজে পেয়েছে বিস্তৃত অতীত জুড়ে হিংসায় উন্মত্ত সৃষ্টিতলকে; জনপদের পর জনপদ শূন্য, সর্বহারা। সর্বনাশের সে আগুনের লেলিহান শিখা ভস্মীভূত করতে চেয়েছে মানবসভ্যতাকে। আত্মঘাতী মারণযজ্ঞে প্রমত্ত মানুষ বারবার ইতিহাসের অধ্যায়কে রক্তাক্ত করেছে। বিষণ্ণ কবি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তারই মাঝে দেখেছেন মানবসভ্যতার অপরাজেয় দুর্মর সত্তাকে। জীবনের প্রসাদে আহ্লাদিত কবি সেই অমরত্বের বাসনাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।
দুই কূলে দুইখানি গ্রাম নিয়ে নদী বয়ে চলেছে যুগ-যুগান্তর ধরে। খেয়াতরিতে পারাপার করে যাত্রীদল গ্রাম দুটির মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করেছে – তাদের সম্বন্ধ নিবিড়, অচ্ছেদ্য – সেই খেয়াঘাটের কূলে নেই কোনো দ্বন্দ্ব, নেই ঈর্ষা-কোন্দল।
খেয়া নৌকার যোগ – বহির্জগতের রক্তক্ষয়ী সর্বনাশা ধ্বংসের ঢেউ আছড়ে পড়েনি দূর নদীতটের এই শাশ্বত জীবনের প্রান্তে। ইতিহাসের প্রমত্ত অধ্যায় দোলা দেয় না সে সভ্যতাকে। ইতিহাস উদাসীন থেকে গ্রাম দুটির মাঝে এই খেয়া পারাপার চলে নীরবে। নিস্তরঙ্গ, নির্দিষ্ট সেই জীবনধারাই আসলে সভ্যতার অনিবার্য বহমানতাকে বয়ে নিয়ে চলে। তাই খেয়া নৌকার চলন উপেক্ষা করে যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সর্বনাশের ঘটনারাজিকে। দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ জীবন থেকে দূর চরাচরের এই শান্ত, নিরীহ, নিস্তরঙ্গ জীবনকে আগলে রাখে খেয়াতরি, মানবসভ্যতার যাত্রাপথকে সুনিশ্চিত করে, জুড়ে দেয় এপারের সঙ্গে ওপারকে।
‘নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস’ – পঙক্তিটির গূঢ়ার্থ বিশ্লেষণ করো।
ভূমিকা – ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘খেয়া’ কবিতা থেকে আলোচ্য কবিতাংশটি নেওয়া হয়েছে, যেখানে মানবসভ্যতার বিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে রোমান্টিক কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে অস্পষ্ট অতীতের শেষতম ক্ষণ পর্যন্ত প্রসারিত করে মানবসভ্যতার শাশ্বত ধারাটির স্বরূপ খুঁজতে চেয়েছেন। সভ্যতা পর্যবেক্ষণের সেই সামগ্রিক চিত্রে উঠে এসেছে মানবসভ্যতার দীর্ঘ বিবর্তনরেখাটি। কবি দেখেছেন যুগে যুগে মানুষ বহু বিচিত্র ইতিহাস নির্মাণ করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের সভ্যতাটিকে।
গূঢ়ার্থ – নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে খেয়াঘাটের তটে বসে একাকী কবি উদাস হয়ে দেখেছেন, এপারের গ্রামখানি থেকে মানুষ খেয়া নৌকায় পার হয়েছে সম্মুখের নদীবক্ষ, আবার কেউ ওপারের গ্রাম থেকে এসেছে এপারে। খেয়া পারাপারের এই দৃশ্য অবলোকন করতে করতে কবির মন হয়েছে অতীতচারী। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে ভেসে উঠেছে অখণ্ড মানব ইতিহাসের বিস্তৃত ক্যানভাস। সেখানে ইতিহাসের ঘনঘটাপূর্ণ অধ্যায়গুলি এসেছে একের পর এক, আর তাদের কর্ম উদ্দীপনায় বিস্মিত হয়েছেন কবি।
কবির বক্তব্য – পরিবর্তিত পরিস্থিতির দাবিতে সহজাত সৃজনের নেশায় মানুষ যুগে যুগে কালে কালে নব নব প্রেরণায় মেতে উঠেছে, নির্মাণ করেছে সভ্যতার বহু বিচিত্র উপকরণ। কিন্তু সভ্যতার বিদেহী মূর্তিকে এই বহু বিচিত্র উপাচারে আরাধনা যেমন করেছে, আবার সেই মানুষই পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে। আত্মঘাতী মারণযজ্ঞে রক্তস্নাত সে ইতিহাস কবিকে ব্যথিতও করেছে। যদিও লোভাতুর, স্বার্থান্ধ মানুষের সেই সর্বনাশা শক্তি মহাকালের প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব হারিয়েছে; থেকে গেছে তাদের কলঙ্কের রেখা, ইতিহাসের পাতাকে তা কেবলই বেদনায় আর্দ্র করেছে। কিন্তু নব প্রেরণায় প্রাণিত সাধারণ মানুষ নিভৃতে নিজের প্রাণের ও মনের তাগিদে সভ্যতার যে প্রাসাদ রচনা করেছে, তাই মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই নির্মাণের-সৃজনের-সম্ভাবনার ইতিহাসকেই রবীন্দ্রনাথ নতুন সৃষ্ট ইতিহাস বলে মনে করেছেন আলোচ্য সনেটটিতে।
‘রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া ওঠে’ – সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।
প্রসঙ্গ – ‘খেয়া’ কবিতায় প্রায় মধ্যাংশে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তির বীভৎসতাকে প্রকাশ করতে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নে প্রদত্ত পঙক্তিটি ব্যবহার করেছেন। ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত আলোচ্য কবিতায় কবি দেখেছেন রাজশক্তির রণহুংকারে, তাদের জান্তব শক্তিদর্পে কেঁপে উঠেছে পৃথ্বীতল-সর্বনাশের খেলায় তারা মেতে উঠেছে বারবার।
ব্যাখ্যা – অতীতচারী কবি ইতিহাসের ঘটনাক্রমে দৃষ্টিপাত করে দেখেছেন মানবসভ্যতার প্রবাহ যতবার অবরুদ্ধ হয়েছে স্বার্থান্ধ ক্রোধান্মত্ত মানুষের হিংস্র ছোবলে-ধরণিতল ততবারই রক্তে ভেসে গেছে। মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করে এইসব শক্তি সভ্যতার বুকে অশনিসংকেত নিয়ে হাজির হয়েছে। বিজয়ী আর বিজিতের তরবারিতে রক্তাক্ত হয়েছে সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু তাদের দম্ভ, দর্প চিরস্থায়ী হয়নি। কবি বলেছেন –
‘সোনার মুকুট কত ফুটে, আর টুটে!’
অমরত্বের প্রত্যাশায় অবিসংবাদী হওয়ার স্বার্থান্ধ মানুষের দল মসির সাধনা করে না, আপন করে অসিকেই। সেই নিষ্ঠুর পাষাণ হৃদয় সৃষ্টির তাড়না অনুভব করে না, ধ্বংসের উল্লাসে মেতে ওঠে বারবার। তথাপি বৃহৎ জগৎ তাদের মনে রাখে না, তারাও মানবসভ্যতায় রেখে যায় না কোনো অবদান; বরং তারা এ সভ্যতার গতিকে রুদ্ধ করতে চায় বলে তারা সভ্যতার কীটে পরিণত হয়। ফলত সোনার মুকুটের ঔজ্জ্বল্য ও গাম্ভীর্য অর্থহীন হয়ে পড়ে।
উপসংহার – হাস্যকর অর্থহীন ধ্বংসাত্মক সে রক্তের খেলার মাঝে কবি জীবনের ইতিবাচকতাকে খুঁজে পাননি; বরং বৃহৎ সভ্যতার ক্ষেত্রে সেই ধূসর রক্তাক্ত ইতিহাস গুরুত্বহীন ঘটনারাজি হয়ে কলঙ্কিত করেছে মানবতাকেই।
‘সোনার মুকুট কত ফুটে, আর টুটে!’ – ‘সোনার মুকুট’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ‘কত’ শব্দের মধ্য দিয়ে কী ব্যক্ত হয়েছে?
‘সোনার মুকুট’-এর তাৎপর্য – মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ বিবর্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখেছেন, যুগে যুগে সভ্যতার বাহ্যিকরূপের বদল ঘটলেও তার শাশ্বত প্রবাহটি অক্ষয় থেকেছে-সভ্যতার সেই চিরন্তন রূপের অন্বেষণ ব্যক্ত হয়েছে ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘খেয়া’ কবিতার মাধ্যমে। কবি লক্ষ করেছেন, স্বার্থান্ধ-ক্রোধান্ধ মানুষের বিষাক্ত হিংস্র ছোবলে মানবজীবনের প্রবাহধারা অবরুদ্ধ হয়েছে, ধরণীতল রক্তে পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করে এইসব শক্তি সভ্যতার পুণ্যভূমিতে সর্বনাশের খেলায় মেতে উঠেছে। বিজয়ী আর বিজিতের তরবারিতে ঝলসে উঠেছে দিগবিদিক – সেই বিজয়ী শক্তির গৌরবকেই ‘সোনার মুকুট’ বলেছেন কবি।
‘কত’ শব্দের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা – কবি সচেতনভাবে ‘কত’ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সমগ্র মানবসভ্যতার প্রেক্ষিতে সেইসব বিজয়গাথা কত তুচ্ছ, কত গুরুত্বহীন। খেয়াঘাটের নির্জন তটে একাকী বসে কবি দূরে খেয়া পারাপারের দৃশ্য মগ্নচিত্তে অবলোকন করেছেন। উদাস কবিমন উধাও হয়েছে অস্পষ্ট অতীতে। মনশ্চক্ষে কবি সেখানে দেখেছেন ইতিহাসের বিজয়গাথা যে রাজশক্তি রচনা করে গেছে, তাদের জয়টিকা মুছে দিয়েছে মহাকালের ঢেউ। তাদের সেই সময়ের দন্ত-দর্প চিরস্থায়ী হয়নি, তারাও পায়নি অমরত্ব। শক্তিদর্পে প্রমত্ত সেই মানুষের অবদান সভ্যতার সামগ্রিক ইতিহাসকে কেবল কলঙ্কিতই করেছে। ‘ফুটে’ আর ‘টুটে’ এই শব্দজোড় ব্যবহার করে কবি সেই জয়পরাজয়কে গুরুত্বহীন-অর্থহীন বলে মনে করলেন। আবার বৃহৎ সভ্যতা যে তাদের ওপর নির্ভরশীল নয়, সে কথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করলেন ‘খেয়া’ কবিতার বিশেষ তাৎপর্যবাহী এই পঙক্তির মাধ্যমে।
‘উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা’ – ‘হলাহল’ ও ‘সুধা’ শব্দদ্বয়ের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করো। সভ্যতার ইতিহাসে ‘শব্দদ্বয়’ কোন্ ভূমিকা পালন করেছে?
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘খেয়া’ কবিতা থেকে প্রশ্নোদ্ভূত অংশটি সংগৃহীত।
শব্দদ্বয়ের প্রাসঙ্গিকতা – পুরাণগাথা অনুযায়ী সমুদ্রমন্থনে উত্থিত কালকূট বিষই কবি কথিত ‘হলাহল’ এবং সমুদ্রমন্থন শেষে প্রাপ্ত অমৃত অর্থাৎ ‘সুধা’ – যা পান করে দেবতারা পেয়েছিলেন অমরত্বের সন্ধান। আলোচ্য এই শব্দদ্বয় মানসভ্যতার উত্থানপতনের ইতিকথার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। কবি বলতে চেয়েছেন। মানুষের কল্যাণপূত কর্মে যেমন সভ্যতার সুধাভাণ্ডটি ভরে ওঠে। তেমনই তার পাশবিক আচরণ, ধ্বংসাত্মক রূপটি পৃথিবীবক্ষে অবিহিত সত্য-শিব-সুন্দরকে পীড়া দেয়।
শব্দ দুটির ভূমিকা – বিবর্তনের দীর্ঘ রূপরেখায় মানবসভ্যতার যে ক্রমোন্নতির ইতিহাস – সেই ইতিহাস পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মানুষের ক্রম-বর্ধমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা তাকে উন্মত্ত করেছে। লিপ্ত করেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ক্ষমতার উত্থানপতনের চিরকালীন। এক সাম্রাজ্যের পতনেই সুপ্ত থেকেছে আর-এক সাম্রাজ্যের উত্থানের সম্ভাবনা।
মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য কবিতায় পৃথিবীর রক্তাক্ত ইতিহাসের বিপরীতে এক নিসর্গ-পল্লির সহজ-সরল চিত্ররূপ উপস্থাপনে হিত-অহিতের সেই বৈপরীত্যকেই প্রকট করেছেন। সভ্যতার অমৃত-গরলকেই প্রতীকায়িত করেছেন পৌরাণিক কাহিনির গভীর ব্যঞ্জনায়।
‘দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।’ – এরূপ উক্তির কারণ কী?
অথবা, মুখোমুখি চেয়ে থাকা গ্রাম দুটি কীসের ইঙ্গিত বহন করে?
ভূমিকা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘খেয়া’ কবিতায় প্রাপ্ত গ্রাম দুটি অবস্থান করছে নীরবে বয়ে যাওয়া নদী স্রোতের দুই তীরে। তারা আশ্রয় দিয়েছে সভ্যতার মহান সন্তানদের, যাদের মাধ্যমে যুগ যুগে ধরে বয়ে চলেছে মানবসভ্যতার চিরন্তন প্রবাহধারাটি।
বহুযুগের পরিচিত গ্রাম দুটি এক সুগভীর সম্পর্কের ডোরে আবদ্ধ –
“দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।”
নিশ্চল প্রশান্তি – একই সূর্যরশ্মির কিরণসম্পাতে আলোকিত গ্রাম দুটির মানুষ নদীতটের খেয়াতরিকে ব্যস্ত রাখে। গ্রাম দুটি বহির্বিশ্বের কাছে অচেনা অজানা কারণ জগতের যাবতীয় উন্মাদনা-উন্মত্ততার তরঙ্গমালা তাদের উঠোনে এসে নিশ্চল প্রশান্তিতে আশ্রয় নেয়।
উক্তির কারণ – নবীনের আবাহন আর প্রবীণের বিসর্জন স্থানু হয়ে অবলোকন করেছে গ্রাম দুখানি। তারা যেন পান্থনীড়; ক-দিনের জন্যে এখানে মানুষ আসে, আবার কাজ ফুরোলেই তাকে চলে যেতে হয়। বিষণ্ণ কবিমন সেই নিরন্তর যাতায়াতকে খেয়া পারাপারের রূপে ব্যক্ত করেছেন। গ্রাম দুটি তাই অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। জীবন যেমন মরণের দিকে চেয়ে থাকে, মরণও জীবনের দিকে – সেই শাশ্বত সম্বন্ধ নিয়ে তারা নদীবক্ষের দুই তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে –
“শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।”
অনন্ত জীবনপ্রবাহ ধারা – নদীবক্ষে ভাসমান খেয়াতরি গ্রাম দুইখানিকে সুগভীর সম্পর্কের ডোরে বেঁধে রেখেছে। বিপুলা এ জগৎসংসার তাদের না চিনলেও তারা নির্বিকার থেকে নিজেদের সম্বন্ধকে দৃঢ়তর করেছে। জীবন ও মরণের দ্যোতনা নিয়ে গন্তব্যের শুরু ও সমাপ্তির অনিবার্য ঠিকানা হয়ে গ্রাম দুইখানি মানবের অনন্ত জীবনের প্রবাহধারাকে স্থায়িত্ব দান করেছে।
‘এই খেয়া চিরদিন চলে নদী স্রোতে’ – প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে তাৎপর্য লেখো।
প্রসঙ্গ – রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘খেয়া’ কবিতার আলোচ্য অংশে জীবনকে বৃহতের প্রেক্ষাপটে দেখবার আকুতি প্রকাশিত হয়েছে। ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত পাঠ্য এ কবিতায় কবি চিরন্তন জীবনধারার স্বরূপটিকে খুঁজতে চেয়েছেন। উত্থানপতনে, ধ্বংস-সৃষ্টিতে সমাকীর্ণ মানবসভ্যতার বিবর্তনকে স্পষ্ট করতে কবি খেয়াতরি, নদীস্রোত, যাত্রীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন প্রসারিত নিসর্গসৌন্দর্যের প্রেক্ষাপটে। মানবের সেই নিরন্তর চলন প্রসঙ্গে কবির প্রশ্নে প্রদত্ত উক্তিটির অবতারণা।
তাৎপর্য – রোমান্টিক কবি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে মনশ্চক্ষে দেখেছেন মানবের অনিবার্য ও নিশ্চিত প্রবাহকে। নদীতটে একাকী বসে তিনি দুই তীরের গ্রাম দুখানি দেখেছেন, দেখেছেন যাত্রীদের খেয়াতরি নিয়ে নিরন্তর পারাপার। বিষাদঘন হৃদয়ে উদাসী কবি মানুষের খেয়া পারাপার লক্ষ করে বলেছেন –
‘কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।।’
জীবন-মৃত্যুর দ্যোতক এপার-ওপার তথা গ্রাম দুখানি থেকে মানুষ আপন ঘরে ফেরে, কেউ বা অজানা গন্তব্যে পাড়ি দেয়। কিন্তু তাদের যাতায়াতে কোনো ছেদ পড়ে না – নিরন্তর এই চলাকে কবি আলোচ্য কাব্যাংশে স্পষ্ট করেছেন।
সভ্যতার সারসত্য – জগৎসংসার সম্বন্ধে নির্মোহ থেকে কবি মানবসভ্যতার অনন্ত প্রবাহধারার স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন খেয়া চলাচলের চিরন্তনতার মাধ্যমে। সম্মুখে খেয়াঘাট, কবি একাকী বসে উদাস নয়নে অপলকে চেয়ে আছেন সেই দিকে। যাত্রীদল পারাপার করছে এপার থেকে ওপারে, এ গ্রাম থেকে পরপারের গ্রামখানিতে। মানবজীবনরূপ নদীবক্ষে জীবনতরিতে ভেসে চলেছে মানুষও – সে চলা শুরু হয়েছে জন্ম থেকে, চলবে আমৃত্যু। নবীনের আগমনে, পুরাতনের বিদায়ে এই চলন যেন অনন্ত। সংঘাত-সংক্ষুব্ধ ইতিহাসের প্রতি উদাসীন থেকে প্রকৃতির কোলে শান্ত সমাহিত নিরীহ গ্রাম দুখানির যাত্রীদল খেয়া নৌকার চলনকে গতিদান করে চলেছে যুগ-যুগান্তর ধরে-বিষণ্ণ কবি সভ্যতার সেই শাশ্বত রূপটি অবলোকন করেছেন হৃদয়লোকে। ‘খেয়া’ কবিতার আলোচ্য অংশে সভ্যতার সেই সার সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
আজকের এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের চতুর্থ পাঠের প্রথম অধ্যায়, ‘খেয়া’ -এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নোত্তরগুলো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নবম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত আসে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে, তবে টেলিগ্রামে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত। ধন্যবাদ।






মন্তব্য করুন