এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল কেন?” নিয়ে আলোচনা করব। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাস পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই “ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল কেন?“ প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাসের পঞ্চম অধ্যায় “বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা“ -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়।
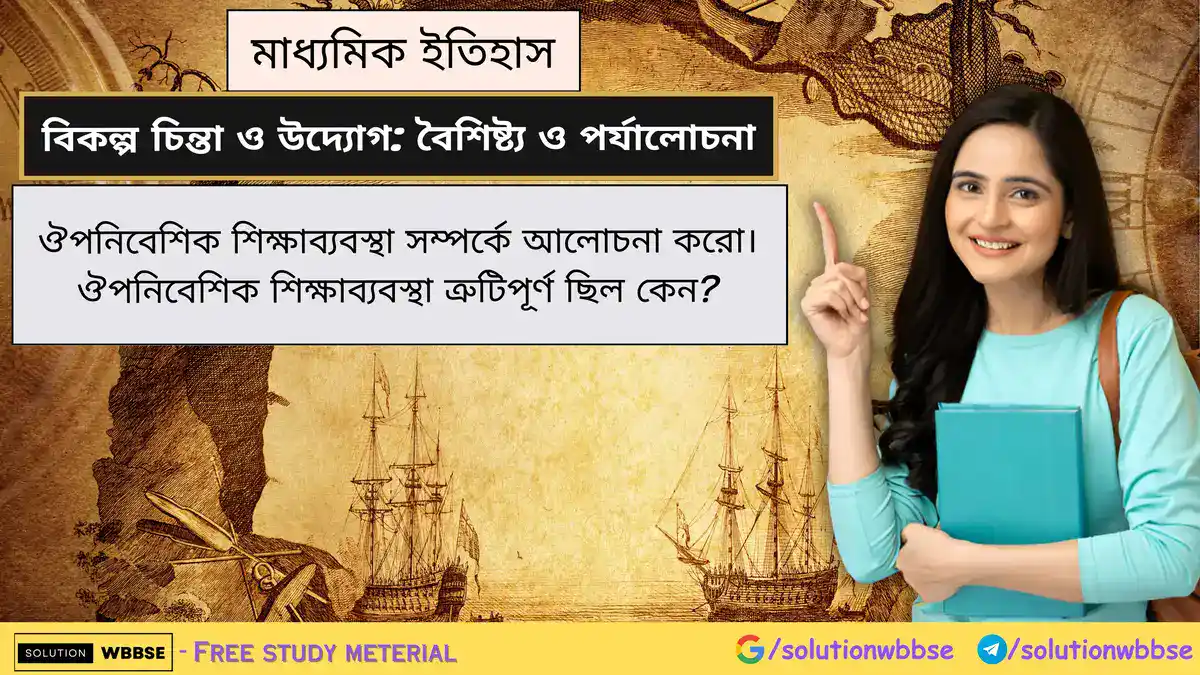
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।
ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ছিল নৈরাজ্যবাদী, নেতিবাচক, হৃদয়হীন, মনুষত্ব নাশক ও জাতীয়তা বিরোধী। এ শিক্ষাধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবন ও পারিপার্শ্বিকতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সমকালীন শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এভাবেই ভারতে প্রচলিত ব্রিটিশ শিক্ষা নীতির সমালোচনা করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই শিক্ষানীতির নির্মম সমালোচক ছিলেন।
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণহীন ও যান্ত্রিক শিক্ষা –
- রবীন্দ্রনাথ এর মতে তৎকালীন ভারতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীর কোনো প্রানের যোগ ছিল না। তিনি লিখেছেন যে, “ছেলেদের ভালোলাগা মন্দ লাগা বলিয়া খুব একটা মস্ত জিনিস আছে। বিদ্যালয় হইতে সে চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত।” শিক্ষার্থীর ভালোলাগা মন্দ লাগা নয়, কোনোক্রমে তাদের পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়াই ছিল শিক্ষার লক্ষ।
- বাল্যজীবনে স্কুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এর অভিজ্ঞতা খুব একটা মধুর ছিল না। তাই পরবর্তীকালে তিনি লেখেন যে, ছেলেদের মানুষ করে তোলার জন্য যে যন্ত্র তৈরি হয়েছে, তার নাম ইস্কুল এবং সেটার মধ্য দিয়ে মানবশিক্ষার সম্পূর্ণতা হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক শিক্ষা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন।
- রবীন্দ্রনাথ এর মতে ভারতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের নাড়ির কোনো যোগ নেই। এই শিক্ষা দিয়ে দেশের কোনো উপকার হয় না। এ জন্য তাঁর বক্তব্য দেশবাসীকেই দেশের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে হবে। তিনি লিখেছেন যে, “আমাদের সমাজ যদি বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠকিতেই হইবে। বিদেশি গভর্মেন্ট এদেশে অনুকূল শিক্ষা কখনও দিতে পারেন না।”
- দেশের অধিকাংশ লোককে নিরক্ষর করে রেখে দেশের সামান্য অংশের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা তিনি মানতে পারেননি। তাঁর মতে এটা ছিল ‘একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে ঢালা’ ব্যাপার। দেশের সব শিক্ষা রীতিকে এক ছাঁচে শক্ত করে জমিয়ে দেওয়া হবে। এটাই সরকারের একমাত্র চেষ্টা।
- দেশবাসীর বুদ্ধিবৃত্তির ওপর সম্পূর্ণ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করাই সরকারের লক্ষ। সুতরাং এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ‘কেরানিগিরির কল’ হয়ে উঠেছে। এর মধ্য প্রানের কোনো সাড়া নেই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এখানে হয় না।
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন –
তাঁর মতে, এই শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়তাবিরোধী। তাঁর মতে, এখানে যা সেখানো হয়, তার মাধ্যমে “পড়াপাখি, বুলিপড়া পাখির গতানুগতিক দল সৃষ্টি করে। তারা হয় বিদেশের বুলি মুখস্থ করা খাঁচার পাখি।” রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি শিক্ষাদর্শনের পরিকল্পনা করেছেন।
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল কেন?
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ ছিল সুলভে অনুগত কেরানি তৈরি। এই শিক্ষা ছিল একান্তভাবেই যান্ত্রিক, পুঁথিসর্বস্ব এবং স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিপন্থি। ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি ছিল কায়েমী স্বার্থরক্ষাকারী ও প্রভুত্ববাদী। তা ছাড়া দেশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অবহেলা এই শিক্ষাব্যবস্থার অপর একটি ত্রুটিপূর্ণ দিক।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা কী?
ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে চালু করা শিক্ষাব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা বলা হয়। এটি মূলত ব্রিটিশদের প্রশাসনিক চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল ইংরেজি ভাষায় দক্ষ কেরানি ও আমলা তৈরি করা।
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী ছিল?
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল –
1. ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য – স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির অবহেলা।
2. যান্ত্রিক ও পুঁথিগত শিক্ষা – সৃজনশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতার অভাব।
3. কেরানি তৈরি করার লক্ষ্য – প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়, চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ।
4. জাতীয়তাবাদবিরোধী – ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে উপেক্ষা করা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার কী সমালোচনা করেছিলেন?
রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাকে “প্রাণহীন, যান্ত্রিক ও মনুষত্ববিধ্বংসী” বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে –
1. এটি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেয়।
2. বিদ্যালয়গুলি “খাঁচার পাখির মতো” মুখস্থবিদ্যায় নির্ভরশীল করে তোলে।
4. এটি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন।
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা কেন জাতীয়তাবিরোধী ছিল?
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়তাবিরোধী ছিল কারণ এটি —
1. ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করত।
2. শিক্ষার্থীদের ব্রিটিশ আদর্শে গড়ে তুলে স্বদেশপ্রেম কমিয়ে দিত।
3. ভারতীয়দের মধ্যে “নিম্নমানসিকতা” তৈরি করত, যাতে তারা নিজেদেরকে ব্রিটিশদের চেয়ে নিচু মনে করে।
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি কী ছিল?
এর সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল “সৃজনশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতার অভাব”। এটি শিক্ষার্থীদের যান্ত্রিকভাবে পরীক্ষায় পাস করানোর জন্য তৈরি করেছিল, প্রকৃত জ্ঞান দেয়নি।
রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃত শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত ছিল?
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন –
1. প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষা (যেমন – শান্তিনিকেতনে)।
2. সৃজনশীলতা ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ।
3. ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সমন্বয়।
4. শিক্ষার মাধ্যমে সামগ্রিক মানবিক বিকাশ।
ঔপনিবেশিক শিক্ষা ভারতের জন্য কী ক্ষতি করেছিল?
1. ভারতীয়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব তৈরি করেছিল।
2. নিজের সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা গড়ে তুলেছিল।
3. সত্যিকারের বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পচর্চাকে পিছিয়ে দিয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা কীভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিপরীত ছিল?
রবীন্দ্রনাথ “মানুষের সম্পূর্ণ বিকাশ” -এর উপর জোর দিয়েছিলেন, যেখানে –
1. শিক্ষা হবে আনন্দময় (নয়তো যন্ত্রণাদায়ক)।
2. শিক্ষার্থী প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।
3. ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবাচক দিক কী ছিল?
যদিও এটি সমালোচনার যোগ্য, তবুও কিছু ইতিবাচক দিক ছিল –
1. আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রচলন।
2. ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংযোগ।
3. একটি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা (যদিও তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল)।
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক প্রভাব কি এখনও রয়েছে?
হ্যাঁ, কিছু ক্ষেত্রে এখনও এর প্রভাব দেখা যায়, যেমন—
1. পরীক্ষানির্ভরতা ও মুখস্থবিদ্যার প্রাধান্য।
2. ইংরেজি মাধ্যমের অত্যধিক গুরুত্ব।
3. স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির তুলনামূলক অবহেলা।
এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন “ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল কেন?” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই “ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল কেন?” প্রশ্নটি মাধ্যমিক ইতিহাসের পঞ্চম অধ্যায় “বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা” -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবং চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকলে, আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তাছাড়া, নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।


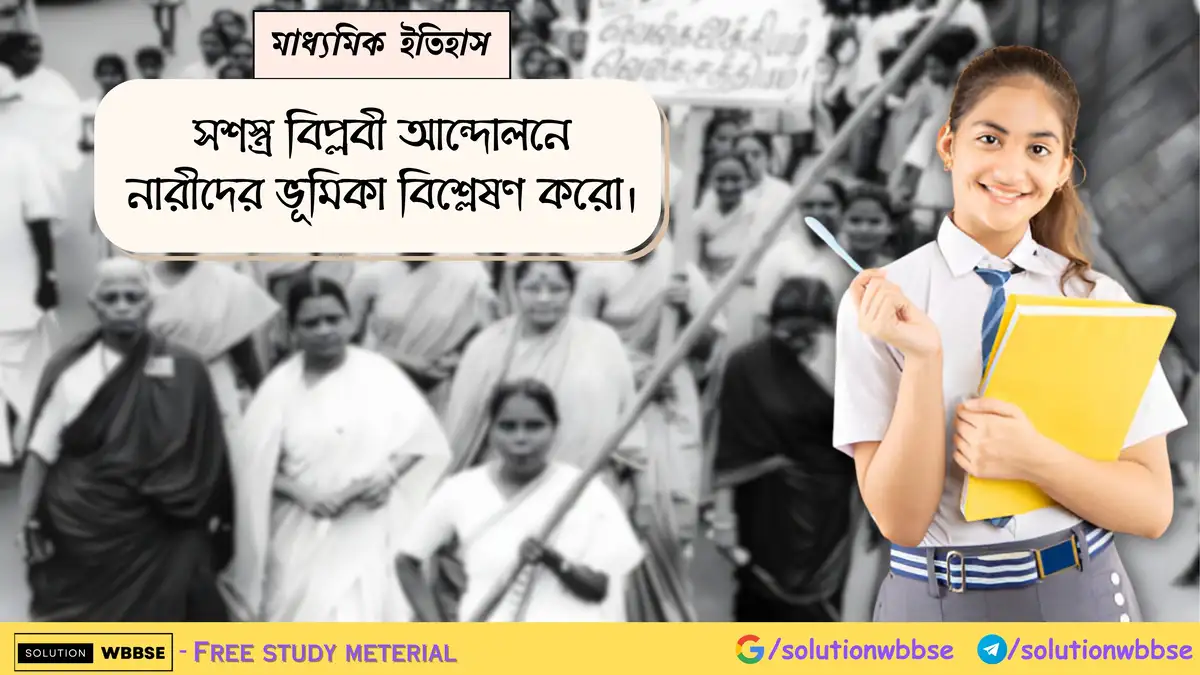
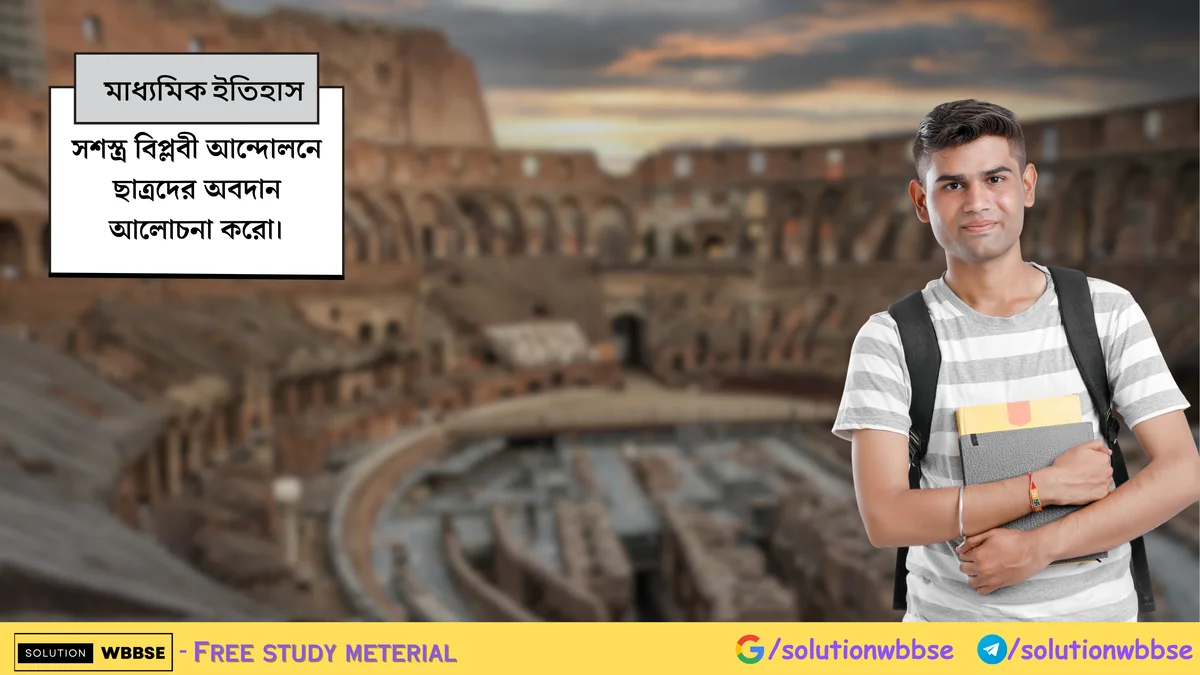
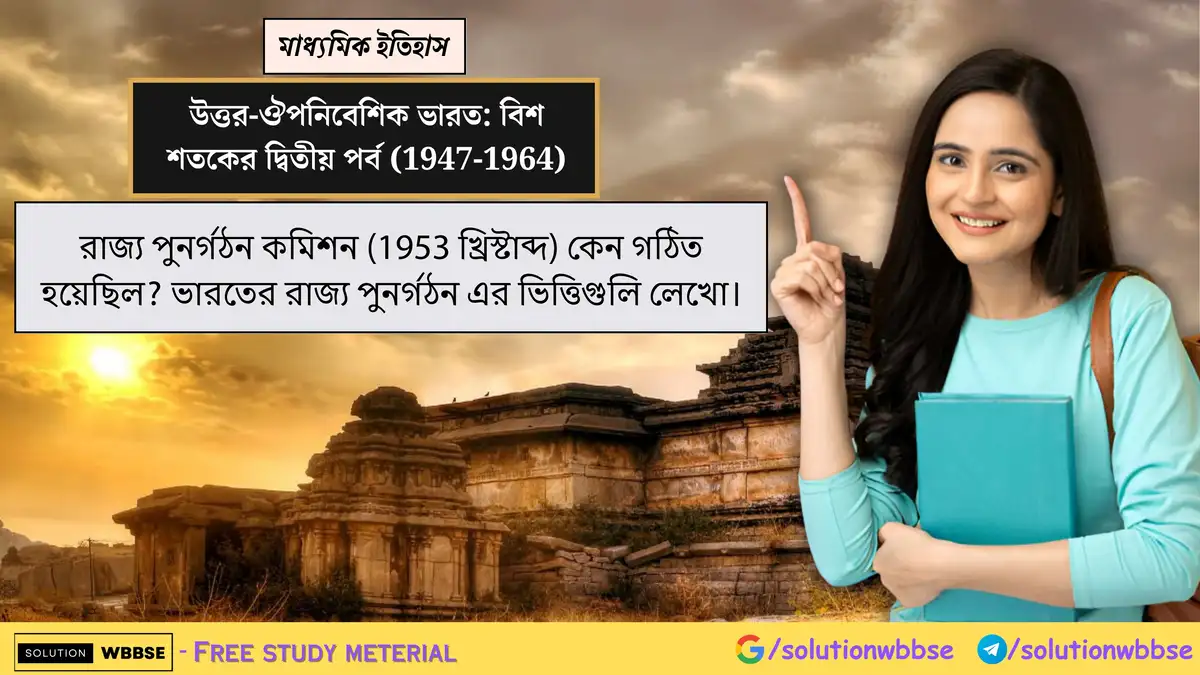

মন্তব্য করুন