আজকের এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের দ্বিতীয় পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘নব নব সৃষ্টি’ -এর কিছু ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নোত্তরগুলো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নবম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত আসে।
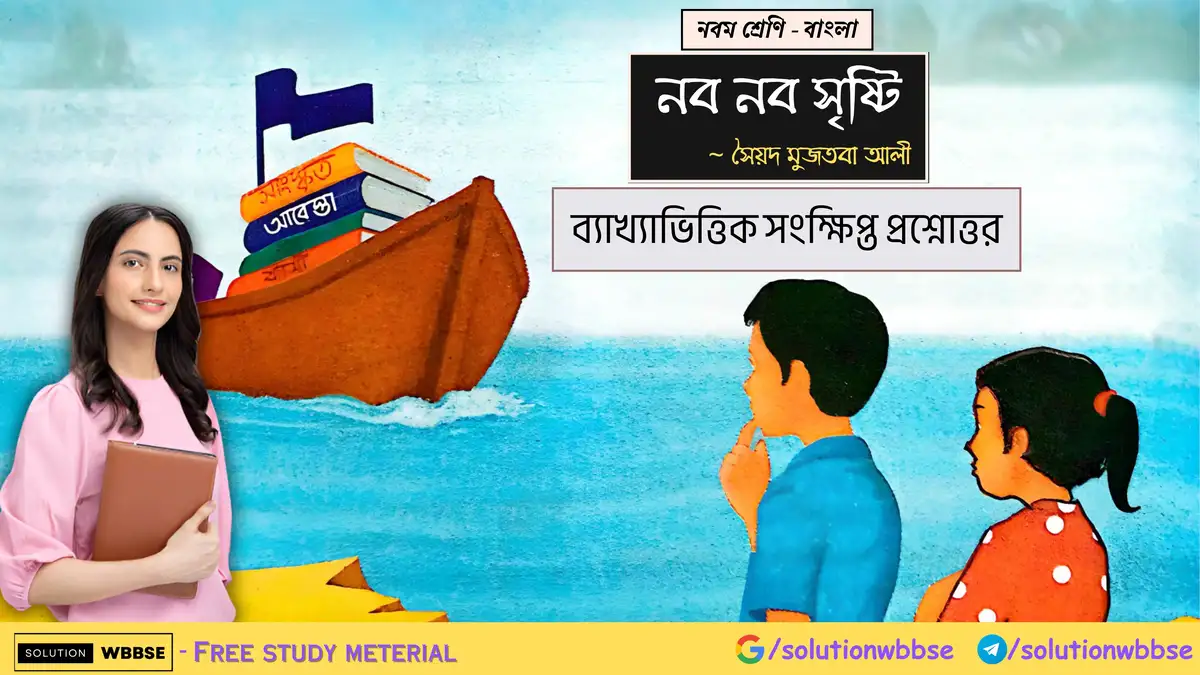
“সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল” – ব্যাখ্যা করো।
ব্যাখ্যা – সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে ভাষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রশ্নে দেওয়া মন্তব্যটি করেছেন। সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর একটি। এ ভাষা নিজস্বতায় সমৃদ্ধ। সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে এক উন্নত, বিপুল শব্দভাণ্ডার। কোনো নতুন চিন্তা, অনুভূতি কিংবা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ভাষা তাই অন্য ভাষার কাছে হাত না পেতে নিজের ভাণ্ডারেই খোঁজে। ধাতু বা শব্দের সামান্য অদলবদল করে প্রয়োজনীয় শব্দটিকে গড়ে নেবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা নিজের প্রয়োজন নিজেই মেটায়। এমনকি বিদেশি শব্দগ্রহণের পরিমাণও মুষ্টিমেয় হওয়ায় তা মূলভাষাকে প্রভাবিত করে না। এজন্যই সংস্কৃতভাষা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল ভাষা।
বাংলা ভাষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলা যায় না কেন-তা আলোচনা করো।
কারণ – ভাষা যখন নিজের যাবতীয় প্রয়োজন নিজের শব্দভাণ্ডারের সাহায্যে মিটিয়ে নিতে পারে, তখন সে হয়ে ওঠে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বা আত্মনির্ভরশীল ভাষা, সে আপনাতেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার অভিলাষী। তার প্রয়োজনে সে নিজের ভাষা ভাণ্ডারেই অনুসন্ধান করে এবং নিজেকেই ভেঙেচুরে নেয়। বিদেশি ভাষার ছোঁয়া থাকলেও বিদেশি প্রভাব তার মৌলিকতাকে কখনোই বিনষ্ট করে না। বাংলা বিদেশি প্রভাবান্বিত, সে আত্মখননের দ্বারা নতুন শব্দনির্মাণে পটু নয়, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বিদেশি ভাষা ও শব্দগ্রহণের পক্ষপাতী। তাই লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী আলোচ্য প্রবন্ধে বলেছেন বাংলা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা নয়।
বাংলা ভাষায় কোন্ কোন্ ভাষার প্রভাব বেশি এবং তা কেন লেখো।
বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, আরবি-ফারসি এবং ইংরেজি ভাষার প্রভাব বেশি।
কারণ – একটি ভাষা আত্মনির্ভর না হলে অন্য ভাষার দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হয়। ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ভাষা প্রভাবিত হওয়ার নানা কারণ লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে প্রধান হল জন্মগত প্রভাব।
ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের স্তরে জন্ম নেওয়া বাংলা ভাষার উপর সে ভাষার অগ্রজ ভাষা সংস্কৃত ভাষার গভীর প্রভাব জন্মসূত্রে প্রাপ্ত।
দ্বিতীয়ত অন্য জনগোষ্ঠীর প্রভাব এবং তাদের সঙ্গে আদানপ্রদান, ভাববিনিময়, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি কারণে ভাষা প্রভাবিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের শাসনকালে বাংলা আরবি-ফারসি প্রভাবিত ভাষা হয়ে ওঠে সহজেই। আবার ইংরেজ শাসনে ইংরেজি ভাষার প্রভাবপুষ্ট হয়। এপ্রভাব কালক্রমে এতোই বৃদ্ধি পায় যে ইংরেজির মারফত অন্য ভাষা থেকে নেওয়ার কাজ আজও চলছে।
“সে সম্বন্ধেও কারও কোনো সন্দেহ নেই” – কী সম্পর্কে সন্দেহ নেই?
যা সম্পর্কে সন্দেহ নেই – প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষার ভিনদেশীয় শব্দের প্রবেশ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছেন। বাংলা ভাষা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। জন্মসূত্রে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাবংশের অগ্রজ ভাষা সংস্কৃতর থেকে সে প্রচুর শব্দ নিয়েছে। পরবর্তীযুগে পাশ্চাত্যের ইংরেজি ভাষা থেকে এবং ইংরেজি ভাষা মারফত অন্যন্য ইউরোপীয় ভাষা থেকে বাংলায় শব্দগ্রহণ চলছে। পরাধীন ভারতে ইংরেজি ছিল শিক্ষার মাধ্যম। পরবর্তীকালে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজিকে বর্জন করলেও ইউরোপীয় শব্দ বাংলাভাষায় আসতেই থাকবে এ নিয়ে কারও কোনো সন্দেহ নেই। আত্মনির্ভর না হলে পরমুখাপেক্ষী হতেই হয়। বাংলা ভাষার স্বনির্ভর না হওয়াই এই সন্দেহহীনতার কারণ।
“এই দুই বিদেশি বস্তুর ন্যায় …” – কোন্ দুই বিদেশি বস্তুর কথা বলা হয়েছে? তার ন্যায় কী হবে?
বিদেশী দ্রব্য – প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনায় দুই বিদেশি বস্তু বলতে আলু-কপি এবং বিলিতি ওষুধকে বুঝিয়েছেন।
এর ন্যায় যা হবে – আত্মনির্ভর না হওয়ার কোনো নতুন চিন্তা, অনুভূতি কিংবা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজন হলে বাংলা ভাষাকে ভাষাঋণ করতে হয়। সংস্কৃত-আরবি-ফারসি-ইংরেজি এসব ভাষার থেকে তার ঋণ প্রচুর। প্রাত্যহিক জীবনে বিদেশি সূত্রে ভারতে আগত আলু-কপি (পোর্তুগাল থেকে আসা) খাদ্য হিসেবে যেমন বর্তমানে অপরিহার্য, বিলিতি ওষুধ যেমন প্রায় সকলেই খান তেমনই বাংলা ভাষাতেও বিদেশি শব্দ অপরিহার্য, অবশ্যম্ভাবী। বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ থাকবেই, নতুন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না।
“নূতন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না” – লেখকের এই প্রতীতির কারণ কী?
কারণ – ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন আদানপ্রদান, ব্যাবহারিক ও রাষ্ট্রীয়-সামাজিক কারণবশত বাংলা ভাষার মধ্যে শতাধিক বছর আগে থেকে আরবি-ফারসি, পোতুর্গিজ ও ইংরেজি ভাষার বহু শব্দ প্রবেশ করেছে। কালক্রমে আজ বহু ইউরোপীয় শব্দ বাংলার সঙ্গে এমন জড়িয়ে পড়েছে যে, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি বর্জন করে বাংলাভাষার প্রচলন ঘটালেও এ নির্ভরতা বন্ধ করা যাবে না। আত্মনির্ভর না হওয়ায় এই চাহিদাও মিটবে না, বরং যতই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জীবনের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে ততই ক্রমবর্ধমান হবে এ চাহিদা। এই প্রয়োজন মেটাতে নিত্যনতুন ইউরোপীয় শব্দের আমদানি বন্ধ হবে না বলেই লেখকের প্রতীতি।
“হিন্দি উপস্থিত সেই চেষ্টাটা করছেন” – হিন্দির চেষ্টাটা কী? কেন তা করা হয়েছে?
“হিন্দির চেষ্টা” – ‘নব নব সৃষ্টি‘ প্রবন্ধে লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, হিন্দি ভাষা থেকে আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি শব্দ বর্জন করে হিন্দি ভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি এখানে হিন্দির ‘চেষ্টা‘ বলে উল্লিখিত।
কারণ – বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষাগুলোর মতো হিন্দি ভাষা ও আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। বিবিধ ভাষার প্রভাব ও ঋণ হিন্দির ভাষার নিজস্বতাকে বিনষ্ট করছে। এই প্রভাব ও বিনষ্টিকরণ থেকে হিন্দিভাষাকে মুক্ত করতে হিন্দিভাষার তাত্ত্বিক ও বহু সাহিত্যিক বর্তমানকালে সচেতন হয়েছেন। মাতৃভাষাকে বিপন্নতা থেকে রক্ষা করে নতুন করে গড়া তোলা তাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। এ প্রচেষ্টা সময় সাপেক্ষ হলেও ভবিষ্যতে যে সার্থকতা পাবে, এ নিয়ে লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী আশাবাদী।
“চেষ্টাটার ফল হয়তো আমি দেখে যেতে পারব না।” – কোন্ চেষ্টা কেন দেখে যেতে পারবেন না লেখক?
আলোচ্য অংশে সৈয়দ মুজতবা আলী “চেষ্টা” বলতে মাতৃভাষাকে বিদেশি ভাষার প্রভাব মুক্ত করার প্রচেষ্টাকে বুঝিয়েছেন।
কারণ – ভাষার জন্ম থেকে স্বাভাবিক প্রবাহে মিশ্রণ ঘটতে ঘটতে ভাষা নবরূপ নেয়। তার পুনর্গঠন খুবই জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। নিজের সমকালে সৈয়দ মুজতবা আলী হিন্দি ভাষায় এই কাজ ও প্রচেষ্টা শুরু হতে দেখলেও তাঁর জীবন পরিসীমায় এ কাজ সম্পূর্ণ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় থেকেই তাঁর এমন মন্তব্য।
রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল কীভাবে বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তা উদাহরণ-সহ আলোচনা করো।
“Literature is an art-forms by the medium in which it works – Language.” – Charles Hockett -এর এই অমোঘ কথাটি সাহিত্যের চরম সত্য। সাহিত্যের কাজ বিমূর্তকে মূর্ত করা, ভাষা তার বাহন। আত্মনির্ভরশীল না হওয়ায় বাংলাভাষার রচনাকারেরা তাই বাধ্য হয়েছেন বিভাষাগুলোর সাহায্যে বিমূর্তকে মূর্ত করতে।
উদাহরণ-সহ আলোচনা – বাংলা সাহিত্যে বিদেশি শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বিদেশি শব্দগ্রহণ ও ব্যবহারে উদারমনা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীনভাবে সাহিত্যের প্রয়োজনে “আব্রু”, “ইজজৎ”, “ইমান” ব্যবহার করেছেন। নজরুল ও “ইনকিলাব”, “শহিদ”, “খুন”, “বাগিচা” ইত্যাদি অজস্র আরবি-ফারসি শব্দকে বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়েছেন।
বিদ্যাসাগরের রচনার কী বৈশিষ্ট্যর কথা লেখক আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন?
বৈশিষ্ট্য – বাংলা গদ্যকে জড়তা ও দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত থেকে সাহিত্যের আটপৌরে ব্যবহারের উপযোগী করেন বিদ্যাসাগর। সরল সহজ বাংলা গদ্যে তিনি আনলেন লালিত্য। আর একাজে সহায়ক হয়েছিল তাঁর শব্দ ব্যবহার। সংস্কৃত ঘেঁষা সাধুভাষায় লেখা রচনাগুলোতে তৎসম, তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করলেও বিদেশি শব্দ তিনি কখনও ব্যবহার করতেন না। অথচ ছদ্মনামে লেখা রচনাগুলোতে তিনি সাধুভাষার বাঁধন ভেঙে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করে নতুন রীতির গদ্য লিখতেন।
প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী বিদ্যাসাগরের রচনার এই বৈশিষ্ট্যই উল্লেখ করেছেন।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরিচয় দাও।
পরিচয় – হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (6/12/1853 – 17/12/1931) নৈহাটির রামকমল তর্করত্নের পুত্র। সংস্কৃত কলেজ থেকে 1877 খ্রিস্টাব্দে এমএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে একমাত্র ছাত্র হিসেবে উত্তীর্ণ হয়ে “শাস্ত্রী” উপাধি এবং পরবর্তীকালে গবেষণা-আবিষ্কারাদির জন্য “মহামহোপাধ্যায়” উপাধি লাভ করেন। হেয়ার স্কুল, লখনউ ক্যানিং কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” পুথি আবিষ্কার করে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণ, পুথি গবেষণা, লেখ পাঠোদ্ধার ইত্যাদি বহু কর্মে আজীবন প্রবৃত্ত ছিলেন তিনি। তাঁর মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য – “কাঞ্চনমালা”, “বেনের মেয়ে “মেঘদূত ব্যাখ্যা”, “বৌদ্ধধর্ম”, ভারতবর্ষের ইতিহাস ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় বহু পুথি এবং সর্বোপরি “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা”। বিষয় গৌরব ও রচনাগুণে হরপ্রসাদের প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য ছিল। তাঁর রচনাভঙ্গি সরল, লঘু, দ্রুতগুতি। বাংলা সাহিত্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন চিরোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।
“আলাল” ও “হুতোম” কী? আলালের পরিচয় দাও।
লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে “আলাল” বলতে “আলালের ঘরের দুলাল” এবং “হুতোম” বলতে “হুতোম প্যাঁচার নকশা” গ্রন্থ দুটোকে বুঝিয়েছেন।
পরিচয় – “আলাল” অর্থাৎ “আলালের ঘরে দুলাল” গ্রন্থটির রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা চলিত গদ্যের আদলে অভিনব লঘু গদ্যভঙ্গির প্রবর্তন করেন। “আলালের ঘরে দুলাল” (1264 বঙ্গাব্দ) তাঁর টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে লেখা অভিনব গদ্যরচনা। এটি বাংলায় রচিত বিলেতি নভেল ধারার সূত্রপাত ঘটায়। হাস্যরসাত্মক এই রচনায় মিশ্র সাধুভাষা ব্যবহৃত। ভাষার প্রধান গুণ সর্বসাধারণের বোধগম্য সরস ভাষা। বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যের ইঙ্গিত প্রথম এ রচনাতেই পাওয়া যায়।
হুতোম কী? বাংলা সাহিত্যে এর গুরত্ব কোনখানে?
কালীপ্রসন্ন সিংহ 1861-1862 খ্রিস্টাব্দে রচনা করেছিলেন। “হুতোম প্যাঁচার নক্শা”। এটি বাংলা চলিত ভাষায় রচিত “নক্শা জাতীয়” গদ্য। রচনাকার “হুতোম পেঁচা” ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন এবং রচনাটি “হুতোম” বলে পরিচিত ছিল।
গুরুত্ব – ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার হঠাৎ-বাবুদের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শনই ছিল আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়। সহজ, সরল অকপট ও সরস ভঙ্গিতে রচিত এই গ্রন্থটির ভাষা ছিল আদ্যন্ত চলিত বাংলা। তৎকালীন কলকাতার ব্যবহৃত কথ্যভাষাকে লেখক অবিকৃত ও অবিমিশ্রভাবে গদ্যে ব্যবহার করেছেন। বাংলা চলিত গদ্যের সূচনা লগ্নে কালীপ্রসন্ন সিংহের “হুতোম প্যাঁচার নক্শা” বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
প্রেমচন্দ্র কে? তাঁকে “হিন্দি ভাষার বঙ্কিমচন্দ্র” বলা হয় কেন?
বেনারসের কাছে লামহি গ্রামে 31 জুলাই 1880 খ্রিস্টাব্দে মুনসী প্রেমচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। প্রেমচন্দ্র হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।
কারণ – গদ্য সাহিত্যে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি ভারতীয় সাহিত্যে চিরখ্যাত। উপন্যাস ও ছোটোগল্পে দক্ষ প্রেমচন্দ্র “হিন্দি সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র” বলে খ্যাত। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা “গোদান”। প্রেমচন্দ্রের প্রকৃত নাম ধনপত রায় শ্রীবাস্তব। প্রথম ছোটোগল্পের বই “পেজ-এ-ওয়ন”। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিভিন্নরকম অসাধুতা, সামাজিক বিকৃতির বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন। “রঙ্গভূমি”, “নির্মাল্য”, “প্রতিজ্ঞা” ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ্য রচনা। 1936 খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।
শংকরের পরিচয় দাও। তাঁর আলোচনার ভাষা শব্দবহুল হবেই কেন?
পরিচয় – শংকর তর্কবাগীশ তাঁর পিতার সঙ্গে মুরশিদাবাদ অঞ্চল থেকে নবদ্বীপে আসেন। পিতার কাছেই ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করা এই ব্রাহ্মণ ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত কর্কশ তর্কশাস্ত্রের মুখ্য অবতার নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক পদে দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। দেশিবিদেশি ছাত্ররা তাঁর কাছে পাঠ নিত।
কারণ – “শংকরদর্শন” শব্দটি প্রাথমিকভাবে শংকরাচার্যকে মনে করায়। তাঁর রচনা সংস্কৃত ভাষাতেই ছিল। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রসূত্র রচনায় শংকর তর্কবাগীশ তৎসম শব্দবহুল ভাষা ব্যবহার করেন। কারণ তখনও বাংলা ভাষা প্রবলভাবে সংস্কৃত প্রভাবিত এবং সংস্কৃত রীতিনীতিরই একান্ত অনুগামী ছিল।
“অত্যধিক দুশ্চিন্তার কারণ নেই” – প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
তাৎপর্য – স্বনামখ্যাত রচয়িতা সৈয়দ মুজতবা আলী ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনায় বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছেন। বাংলা ভাষা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। ফলে জন্মসূত্রে সে যেমন সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত, তেমনই অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নানান আদানপ্রদানের সূত্রে আরবি-ফারসি-ইংরেজি ভাষার প্রভাবপুষ্ট। স্পষ্ট করে বললে বর্তমান বাংলা ভাষায় এই ভাষাগুলোর প্রভাব এতই গভীর যে বাংলা শব্দভাণ্ডারের অনেকটাই এদের অধিকৃত। নানান আদানপ্রদান এবং ব্যাবসাবাণিজ্য ইত্যাদির সূত্রে পোর্তুগিজ, ফরাসি ও স্প্যানিশ শব্দও বাংলাভাষায় এসেছে। কিন্তু তাদের পরিমাণ নগণ্য। ফলত তারা বাংলাভাষার মৌলিকতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। এজন্য লেখক বলেছেন এদের অনুপ্রবেশ নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তার কারণ নেই।
“… সে ভাষার শব্দ বাংলাতে ঢুকবেই” – অন্য ভাষার শব্দ বাংলাতে ঢোকে কেন?
কারণ – আধুনিক পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার মতোই বাংলাভাষাও আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। ফলে জন্মসূত্র ছাড়াও ব্যাবসাবাণিজ্য, সামাজিক সাংস্কৃতিক মেলামেশা, বিজাতীয় শাসন ইত্যাদি নানা সূত্রে বিদেশি শব্দ বাংলাভাষা প্রবেশ করেছে এবং আজও করে চলছে। বাংলা ভাষা উৎপত্তিগত কারণে সংস্কৃত ভাষার সংলগ্ন। সংস্কৃত ভাষার প্রবল চর্চার ফলে এককালে সংস্কৃত শব্দ বাংলায় এসেছে। একইভাবে আরবি-ফারসি এবং ইংরেজি শব্দ, ক্ষীণভাবে পোর্তুগিজ, ফরাসি, স্প্যানিশ শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। বাংলা ভাষায় ভিন্ন নানা ভাষার শব্দ প্রবিষ্ট হওয়ার আরও একটি কারণ নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালির মিশ্রজাতি হয়ে ওঠা।
“… অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব” – প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করো।
‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্য করেছেন।
তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা – সৈয়দ মুজতবা আলী পাঠ্য রচনার প্রথমেই জানিয়েছেন বাংলা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। তাই নিজের চাহিদাপূরণে সে পরভাষা মুখাপেক্ষী। জন্মসূত্রে বাংলা ইন্দোইউরোপীয় শাখার অগ্রজ ভাষা সংস্কৃতের উপর নির্ভরশীল। সংস্কৃত ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকায় বিস্তর সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ঢুকেছে। বর্তমানে এই সংস্কৃত ভাষার চর্চা আছে বলে আজও বাংলার অনুপ্রবেশ ঘটছে। গঠনগতভাবে বাংলা ভাষা অনেকটাই সংস্কৃতনির্ভর। সংস্কৃত বাংলা ভাষার অন্যতম ভিত্তি তাই রচনাটির সময় এবং আজও বাংলায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন রয়েছে। তাই স্কুল কলেজ থেকে সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিলে বাংলা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হবে।
“… ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি” – এ কথা কেন বলেছেন লেখক?
কারণ – সৈয়দ মুজতবা আলী ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে মাতৃভাষা বাংলায় ভিনভাষার প্রভাব নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। বাংলা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। ফলত নিজের চাহিদাপূরণের জন্য সে পরভাষার মুখাপেক্ষী। জন্মসূত্রে সংস্কৃত ভাষার মতোই রাজনৈতিক, সামাজিক কারণে, ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য বাংলা ইংরেজি ভাষার প্রভাবপুষ্ট। সংস্কৃতর পাশাপাশি আধুনিককালে ইংরেজিও বাংলার প্রধান এক খাদ্য।
আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সংযোগে, ইউরোপীয় দেশগুলোর রীতিনীতি, ইতিহাস-সংস্কৃতিকে জানতে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগে, বিশেষ করে দর্শন, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান ও ততোধিক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের শব্দের জন্য ইংরেজিই প্রধান ভরসা। টেকনিক্যাল শব্দের প্রয়োজন মেটাতেও ইংরেজি অদ্বিতীয়।
তাই লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, বাংলা ভাষাতে ইংরেজি ভাষা চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি।
“একমাত্র আরবি-ফার্সি শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে” – কী বলা যেতে পারে এবং কেন তা বলা যেতে পারে?
যা বলা যেতে পারে – সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনায় বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রবেশ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশ্নে প্রদত্ত মন্তব্য করেছেন। বাংলা ভাষায় অন্য ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ নিয়ে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন আরবি-ফারসি শব্দই একমাত্র বাংলা ভাষায় আর ব্যাপকভাবে প্রবেশ করবে না।
কারণ – পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে আরবি-ফারসি ভাষার চর্চা বিলুপ্তির পথে। এই দুই অঞ্চলের তরুণ সম্প্রদায়ও ভাষাচর্চায় আগ্রহী নয়। আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে হঠাৎ অভূতপূর্ব জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়ে বাংলায় প্রভাব বিস্তার করবে এমন সম্ভাবনাও নেই। তাই প্রশ্নে প্রদত্ত মন্তব্যটি যথাযথ।
“… জীবস্মৃত এসব শব্দের …” – কোন্ শব্দগুলো, কেন জীবন্মৃত?
শব্দ – বাংলা ভাষায় আগত আরবি-ফারসি শব্দগুলোকে প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনায় “জীবন্মৃত” শব্দ বলেছেন।
কারণ – আত্মনির্ভরশীল না হওয়ায় জন্মগত ও অন্যান্য সূত্রে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিদেশি শব্দ প্রবেশ করেছে। রাষ্ট্রীয় শাসন ও সামাজিক পটবদলের কারণে আরবি ফারসি শব্দ একসময়ে বাংলার শব্দভাণ্ডারে স্থান পেলেও বর্তমানে চর্চার অভাবে এদের ব্যবহার কম এবং নতুন শব্দের আগমনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। তাই বর্তমানে এই ভাষাগুলির কম শব্দ ব্যবহারের নিরিখে লেখক এদের “জীবন্মৃত” বলেছেন।
“… কবি ইকবালই এ তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন …” – কবি ইকবাল কে? কোন্ তত্ত্বের কথা এখানে বলা হয়েছে?
পরিচয় – কবি মহম্মদ ইকবাল বর্তমান পাকিস্তানের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। কবি ইকবাল দার্শনিক ও রাজনীতিবিদরূপে খ্যাত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা “সারে জাঁহা সে আচ্ছা” আজও প্রচলিত ও জনপ্রিয়। দ্বিজাতি তত্ত্ব ও পাকিস্তান প্রস্তাব তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। তাঁর বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ হল – “আসরার-ই-খুদাহ”, রুমাজ-ই-বেখুদী”, “জাভিদ নাসা” ইত্যাদি।
তত্ত্বের স্বরূপ – ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে আরবি ভাষার সংঘর্ষে নবীন সিন্ধি, উর্দু, কাশ্মীরি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনো কারণে ভারতবাসীরা এ তিন ভাষা ফারসির মতো ঐশ্বর্যশালী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে নি। এ তত্ত্বই কবি ইকবাল উপলব্ধি করেন এবং উর্দুকে ফারসি অনুকরণ থেকে নিষ্কৃতি দানের প্রচেষ্টা করেন।
“… কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন’ – প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য লেখো।
প্রসঙ্গ – বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত এক মনোজ্ঞ আলোচনা পাওয়া যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধটিতে। আরবি-ফারসি ভাষার বাংলা ভাষা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক প্রশ্নে প্রদত্ত মন্তব্যটি করেছেন।
তাৎপর্য – ইরানে আর্য ইরানি ভাষা ও সেমিতি আরবি ভাষার সংঘর্ষে সৃষ্ট ফারসি ভাষা এবং ভারতে সিন্ধি, উর্দু ও কাশ্মীরি সাহিত্য, সৃষ্টি হয়। ফারসি জনপ্রিয় হলেও ভারতের তিনটি ভাষা ঐশ্বর্যশালী সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। উর্দুভাষী কবি ইকবাল এ তত্ত্ব অনুধাবন করেন এবং উর্দু ভাষাকে ফারসির অনুকরণমুক্ত ও প্রভাবমুক্ত করে সাবলীল করার চেষ্টা করেন। ইকবালের এই প্রচেষ্টা আংশিক সার্থক হওয়ায় লেখক আলোচ্য মন্তব্যটি করেছেন।
পদাবলি সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের অভিমত কী?
অভিমত – ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হল পদাবলি সাহিত্য। এই সাহিত্যের সূচনা মধ্যযুগের বাংলা ভাষাতে হলেও এর প্রাণ ও দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালি। বাঙালির পূর্ণ নিদর্শন হল এই পদাবলি সাহিত্য এবং সাহিত্য মাহাত্ম্য ও ভক্তিরসাশ্রিত কীর্তনগানগুলো। এখানে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ কানুরূপ ধারণ করেছেন, শ্রীমতী রাধা হয়েছেন খাঁটি বাঙালি কন্যা। এমনকি ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুরশিদিয়ার আশিকের সঙ্গে পদাবলির রাধা সেখানে হয়ে গেছেন একাকার।
“এ সাহিত্যের প্রাণ ও দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালি।” – কোন্ সাহিত্য কীর্তির কথা বলা হয়েছে? ‘প্রাণ’ ও ‘দেহ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
সুবিখ্যাত রচয়িতা সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে ‘এ সাহিত্য’ বলতে ‘বৈষ্ণব পদাবলি’কে বুঝিয়েছেন।
‘প্রাণ’ ও ‘দেহ’ অর্থ – অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে কাব্যের আত্মা হচ্ছে রস। আলোচ্য পাঠে “প্রাণ” বলতে কাব্যের রসকেই বোঝানো হয়েছে। এবং কাব্যের “দেহ” হল ধ্বনি, অলঙ্কার, শব্দ ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কাব্যভাষা, যা পাঠ্যাংশে বাংলা ভাষাকে চিহ্নিত করেছে।
‘গতানুগতিক পন্থা’ বলতে কী বোঝায়? বাঙালি বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করে কেন?
যা হয়ে আসছে, চলে আসছে, ঘটে আসছে সেই পথ বা পদ্ধতিই “গতানুগতিক পন্থা”। অনেক ক্ষেত্রেই এ পন্থা সময়োপযোগী ও সংস্কারমুক্ত নয়। ফলত তা প্রগতির পরিপন্থী।
কারণ – ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন – বাঙালির চরিত্রেই নিহিত আছে বিদ্রোহ। সত্য-শিব-সুন্দরকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তার বিদ্রোহ। কিন্তু বিদ্রোহ কখনোও-কখনোও লক্ষ্য-আদর্শ ভুলে উচ্ছৃঙ্খলতায় বদলে গেলে বাঙালি সেই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করে পুনরায় সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য।
“বিদেশি শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর” – কেন লেখক এ কথা বলেছেন আলোচনা করো।
লেখকের যুক্তি – বাংলা ভাষা কখনোই আত্মনির্ভরশীল নয়। পাঠান ও মোগল যুগে আইন-আদালত ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে ইংরেজি ভাষা থেকেও ঐ শব্দ নেওয়া হয়েছে। তার পরিমাণ এতটাই বেশি যে, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থহীন। লেখকের মতে, শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজিকে বর্জন করে বাংলা গ্রহণ করার পরে এই প্রবণতা আরও বাড়বে। ফলে বিদেশি শব্দের আমদানি কখনো বন্ধ করা যাবে না; সেক্ষেত্রে তার ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবা নিতান্তই অর্থহীন।
বাংলা সাহিত্যে বিদেশি শব্দ ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত লেখক দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।
লেখকের উল্লিখিত দৃষ্টান্ত – সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা ভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে বিদেশি শব্দগ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আব্রু, ইজ্জত, ঈমান ইত্যাদি শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। নজরুল ইসলামও তাঁর সাহিত্যে ইনকিলাব, শহীদ–এর মতো প্রচুর বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর বেনামে লেখা রচনায় প্রচুর আরবি-ফারসির ব্যবহার ঘটিয়েছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরবি-ফারসির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করাকে আহাম্মকি বলে মনে করতেন।
“আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।” — কোন্ প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে আলোচনা করো। অথবা, স্কুল থেকে সংস্কৃতচর্চা উঠিয়ে না দেওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বক্তা কী বলেছেন?
প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা – বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে লেখক সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিষয়ে উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। সংস্কৃত ভাষার চর্চা এদেশে ছিল এবং তাই প্রচুর সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ঢুকেছে, যার ধারা এখনও বজায় রয়েছে। স্কুল-কলেজ থেকে সংস্কৃতচর্চা যদি সম্পূর্ণ উঠে যায়, তবে বাংলায় এখনও অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলা ভাষার খাদ্যের অন্যতম প্রধান উৎসই হল সংস্কৃত।
স্কুল থেকে সংস্কৃতচর্চা না-ছেড়ে যাওয়ার কারণ – বাংলার শব্দভাণ্ডারের অন্যতম প্রধান উৎস সংস্কৃত হওয়ায়, এর চর্চা বন্ধ করলে বাংলা শব্দসম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে।
“সুতরাং ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি।” — কেন লেখক এ কথা বলেছেন আলোচনা করো।
লেখকের যুক্তি – লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর নব নব সৃষ্টি রচনাংশে এ উক্তিটি পাওয়া যায়। তাঁর মতে, ইংরেজি শব্দ এড়িয়ে সাহিত্য রচনা বাংলা ভাষার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বিশেষত দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাংলা শব্দের অভাব রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ লেখক বলেছেন যে রেলের ইঞ্জিন কীভাবে চালাতে হয়, সে সম্পর্কে বাংলায় কোনো বই নেই। পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনে তাই ইংরেজিরই শরণ নিতে হবে।
“উদুর্বাক কবি ইকবালই এ তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।” — কীসের কথা বলা হয়েছে? ইকবাল এ কারণে কী করেছিলেন?
তত্ত্বের স্বরূপ – ভারতীয় মক্তব ও মাদ্রাসাগুলিতে ব্যাপক আরবি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হলেও, ভারতীয় আর্যরা ফারসি ভাষার সৌন্দর্যে বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই উর্দু সাহিত্যের মূলসুর ফারসির সঙ্গে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। ইরানে যেমন আর্য-ইরানি ভাষা ও সেমিটিক-আরবি ভাষার সংঘর্ষে নবগঠিত ফারসি ভাষার জন্ম হয়েছিল, ভারতেও অনুরূপভাবে সিন্ধি, উর্দু ও কাশ্মীরি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়; কিন্তু কোনো-না-কোনো কারণে এসব ভাষা ফারসির মতো নবনব সৃষ্টির মাধ্যমে সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে তুলতে পারেনি। এই তত্ত্বই ইকবাল গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।
ইকবালের পদক্ষেপ – তিনি এসব বুঝে মৌলিক সৃষ্টির মাধ্যমে উর্দুকে ফারসির অনুসরণ থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন।
“বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলি কীর্তনে।” এই পদাবলি কীর্তনের কোন্ বৈশিষ্ট্যের দিকে লেখক ইঙ্গিত করেছেন?
পদাবলির বৈশিষ্ট্য – সৈয়দ মুজতবা আলীর মতে, পদাবলির আত্মা ও দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালি। এতে শুধু মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাংলার “কানু” হয়েই উঠেছেন তাই নয়, রাধাও পরিণত হয়েছেন খাঁটি বাঙালি নারীর রূপে। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুরশিদির আশেক আর পদাবলির রাধা—সবাই একই চরিত্রের বিভিন্ন প্রকাশ।
“বাঙালি চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান।” — প্রসঙ্গ নির্দেশ করে লেখক যা বোঝাতে চেয়েছেন লেখো।
প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা – সৈয়দ মুজতবা আলীর মতে, রাজনীতি, ধর্ম ও সাহিত্যে—যখনি বাঙালি সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে, তখনি তা আত্মস্থ করতে চেয়েছে। আর অন্ধ গতানুগতিকতা বা প্রাচীন ঐতিহ্যের অজুহাতে কেউ যদি তাতে বাধা দিতে চায়, তবে বাঙালি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আবার সেই বিদ্রোহ যখন উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়, সুন্দরের উপাসক বাঙালি তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে। এতে বাঙালি মুসলমানরাও সহযোদ্ধা হয়েছে। কারণ ধর্ম পরিবর্তন করলেও জাতির মৌলিক সত্তা অপরিবর্তিত থাকে।
“এ বিদ্রোহ বাঙালি হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়।” – মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।
উৎস – সৈয়দ মুজতবা আলীর নব নব সৃষ্টি রচনা।
ব্যাখ্যা – লেখকের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য—যে-কোনো ক্ষেত্রে সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ পেলে বাঙালি তা লাভ করতে চায়। ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে কেউ তাতে বাধা দিলে বাঙালি বিদ্রোহ করে। এবং এই বিদ্রোহ কেবল বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সীমিত নয়; বাঙালি মুসলমানও একই চেতনায় অনুপ্রাণিত। কারণ লেখকের মতে—ধর্মান্তর হলেও জাতির প্রকৃত চরিত্র অপরিবর্তিত থাকে।
সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনায় বাংলা ভাষার বিবর্তন: তিনি নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধে বাংলা ভাষার বিবর্তন ও পরিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতামত: বাংলা ভাষা একটি সজীব ভাষা, যা নিরন্তর রূপান্তরিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই পরিবর্তনের পেছনে নানাবিধ কারণ দায়ী—তার মধ্যে সংস্কৃত ও ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে শব্দ ঋণগ্রহণ অন্যতম প্রধান।
আজকের এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের দ্বিতীয় পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘নব নব সৃষ্টি’ -এর কিছু ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নোত্তরগুলো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নবম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত আসে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে, তবে টেলিগ্রামে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত। ধন্যবাদ।






মন্তব্য করুন