আজকের এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক বাংলার দ্বিতীয় পাঠের দ্বিতীয় বিভাগ, “আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি” থেকে কিছু বিশ্লেষণধর্মী ও রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।
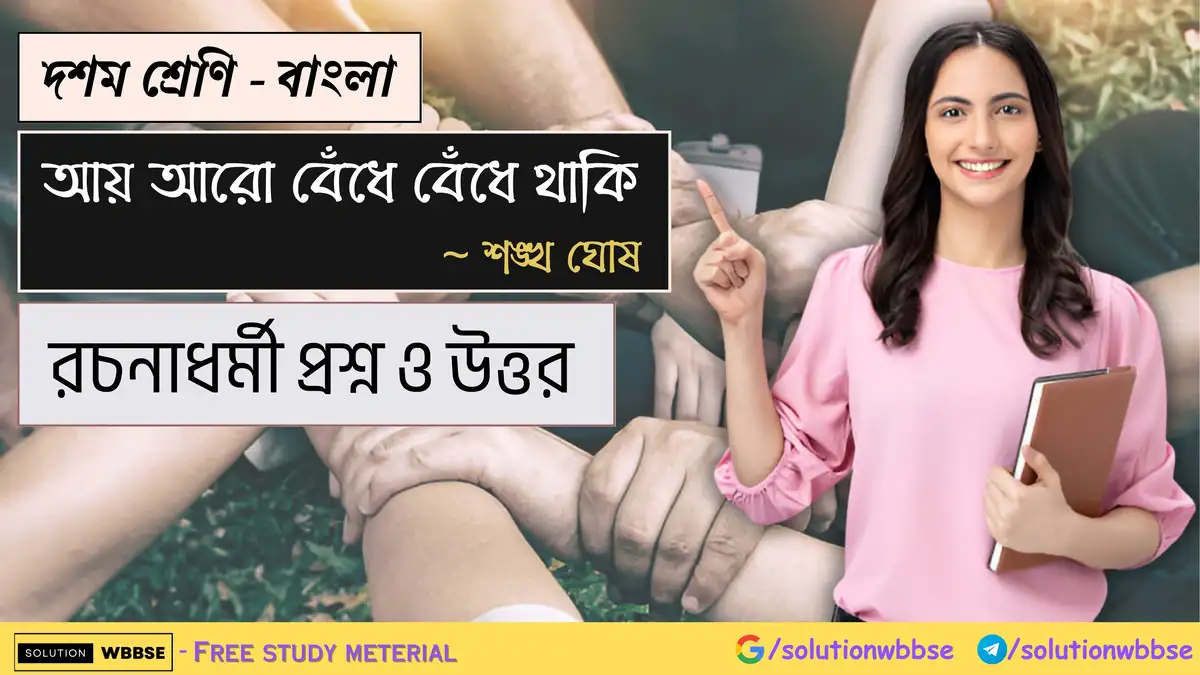
“আমাদের ডান পাশে ধ্বস/আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ” — সমগ্র কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্যের তাৎপর্য লেখো।
উৎস – শঙ্খ ঘোষের ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতাটি অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষের বিপন্ন অবস্থাকে ছোঁয়ার চেষ্টা।
প্রসঙ্গ – বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অনেকগুলি সংকট। একুশ শতকের শুরু থেকেই পৃথিবীজুড়ে এই সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গেই কবি আলোচ্য উদ্ধৃতিটির উল্লেখ করেছেন।
তাৎপর্য – সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা নির্বিচারে আক্রান্ত হয়েছে একের পর এক দেশ। মানুষের বর্বরতা, ধর্মান্ধতা ‘হিমানীর বাঁধ’ -এর মতো চলার পথকে বন্ধ করে দিচ্ছে। ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে মৃত্যু আর রক্তাক্ততায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। সাধারণ মানুষ আশঙ্কায় ভুগছে – “আমরাও তবে এইভাবে/এ-মুহূর্তে মরে যাব না কি?” এই অবস্থায় প্রয়োজন ছিল আদর্শবোধের প্রতিষ্ঠা, যা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারত আমাদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানেও কোনো সম্ভাবনা কবি দেখতে পাচ্ছেন না। ‘ডান পাশ’ এবং বাঁ-দিক অর্থাৎ সর্বত্রই ধ্বংস এবং মৃত্যুর হাতছানি। ‘সম্পর্কের উৎসব’ নামক গদ্যরচনায় কবি লিখেছিলেন – “নতুন শতাব্দীর মানুষকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে তার আয়োজন। … যেখানে এক সম্প্রদায়ের মানুষ আর অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ শুধু মানুষ পরিচয়েই মেলাতে পারেন হাত …।” কিন্তু দিশাহীন চারপাশে কবি সেই আদর্শের আলো খুঁজে পাচ্ছেন না, যা পথ দেখাতে পারে।
“আমাদের পথ নেই আর” — ‘আমরা’ কারা? পথ নেই কেন? পথহীন মানুষগুলোর কর্তব্য কী?
‘আমরা’-র পরিচয় – ‘আমরা’ বলতে সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে।
পথ না থাকার কারণ – বর্তমানে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে সাধারণ মানুষ ক্রমশ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। রাজনৈতিক বা সামাজিক অস্থিরতা তাকে কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। আদর্শবোধের ভাঙন ক্রমশই এত তীব্রতর হচ্ছে যে মানুষের চেতনা কোন্ পথে যাবে তা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ডান দিকে ধ্বংসের তাণ্ডব, বাম দিকেও মৃত্যুফাঁদ। এরই পাশাপাশি মাথার ওপরে বোমারু বিমানের হানা আর চলতে গেলে পায়ে পায়ে প্রতিবন্ধকতা। এভাবেই মানুষের কাছে চলার পথ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। সার্বিক অন্ধকার এবং আদর্শহীনতা গ্রাস করছে আমাদেরকে।
পথহীন মানুষের কর্তব্য – পথহীন মানুষদের সামনে বেঁচে থাকার তীব্র সংকট। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর তীব্র আশঙ্কা। এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে হবে। এর জন্য পরস্পরের হাতে হাত রেখে চলতে হবে। প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য এই একতাই হল একমাত্র শক্তি।
“আমাদের শিশুদের শব-/ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে।” ー কোন্ পরিস্থিতিতে কবি ‘শিশুদের শব’ দেখেছেন? এই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ কেন?
পরিস্থিতি – শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায় সময় এবং সমাজের নানারকম অস্থিরতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। চারপাশে শুধু ধ্বংসের আয়োজন। ‘ডানপাশে ধ্বস’ আর ‘বাঁয়ে গিরিখাদ’ যেন বিপদের প্রতীক। মাথায় বোমারু বিমানের আনাগোনা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে। আর যুদ্ধ মানেই ধ্বংস আর মৃত্যু। যার পরিণতিতে মানুষের চলার পথ ধ্বংস হয়, মানুষ নিরাশ্রয় হয়। আর এই ধ্বংস উন্মত্ততাই শিশুদের মৃত্যু ঘটায়। ‘কাছে দূরে’ অর্থাৎ বিস্তীর্ণ প্রান্তরজুড়ে পড়ে থাকে শিশুদের মৃতদেহ।
ঘটনাটির তাৎপর্য – শিশুদের মৃত্যু সভ্যতার জন্য সর্বনাশের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। যুদ্ধ কত নিষ্ঠুরতা নিয়ে আসে এই ঘটনা তার প্রতীক। শিশুদের মৃত্যু সাধারণ মৃত্যুর থেকে আলাদা। কারণ, শিশুরা ভবিষ্যতের সমাজ গঠনের কারিগর। তাদের মৃত্যু ঘটার অর্থই হল সভ্যতার ভবিষ্যতে শূন্যতা সৃষ্টি হওয়া। দ্বিতীয়ত, শিশুদের মৃত্যু সমাজের বাকি অংশের মানুষদেরও মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত করে তোলে। “-আমরাও তবে এইভাবে/এ মুহূর্তে মরে যাব না কি?” ‘কাছে দূরে’ ‘শিশুদের শব’ সাধারণ মানুষকে নিজেদের বিষয়ে ভীত করে তোলে। তারা বিপন্নবোধ করে, আর তার মূলে থাকে শিশুদের মৃত্যু।
“আমরাও তবে এইভাবে/এ-মুহূর্তে মরে যাব না কি” — এমনটা মনে হচ্ছে কেন?
শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায় সমাজ-সভ্যতার অস্থির স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। যুদ্ধ, ভেদবুদ্ধি, আদর্শহীনতা ইত্যাদি সভ্যতার গতিপথকে রুদ্ধ করে তুলেছে। ‘ডান পাশে ধ্বস’ আর ‘বাঁয়ে গিরিখাদ’ চলার পথকে করেছে বিপৎসংকুল। মাথার উপরে যুদ্ধবিমান ধ্বংস ও মৃত্যুর ছায়াকে দীর্ঘতর করে তুলেছে। বরফ যেমন চলার পথকে দুর্গম করে তোলে সেভাবেই যুদ্ধ, আদর্শের অভাব, স্বার্থপরতা ইত্যাদি এগিয়ে চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধের তাণ্ডবে মানুষ নিরাশ্রয় হয়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটে – “আমাদের ঘর গেছে উড়ে/আমাদের শিশুদের শব-/ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে।” ধ্বংসের এই প্রচণ্ডতা শিহরিত করে সাধারণ মানুষদেরকেও। সর্বনাশের আশঙ্কা সংক্রমিত হয়। জীবনের অগ্রগতিই শুধু অবরুদ্ধ হয় না। তার অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। মৃত্যুভয় ছুঁয়ে যায় সকলকেই। আশঙ্কিত মানুষদের তখনই মনে হয় – “আমরাও তবে এইভাবে/এই মুহূর্তে মরে যাব না কি?”
“আমাদের ইতিহাস নেই” — এই ইতিহাস না থাকার কথা বলে কবি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন সমগ্র কবিতা অবলম্বনে লেখো।
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি কবিতায় সাধারণত মানুষের ইতিহাসহীনতার দুটি পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে।
শিকড়-বিচ্ছিন্নতা – ইতিহাস হল প্রকৃতপক্ষে কোনো জাতির এবং সভ্যতার আত্মবিকাশের কাহিনি। তাই অতীতের ওপরে দাঁড়িয়ে যখন বর্তমানকে তৈরি করা যায় তখনই তা যথাযথ হয়। একেই বলা যায় ঐতিহ্যের বিস্তার, যা ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করে তোলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের প্রকৃত ইতিহাস থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি। শঙ্খ ঘোষ যখন তাঁর ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায় আমাদের ইতিহাস না থাকার কথা বলেন, তখন তা আসলে দেশ এবং জাতির এই শিকড় থেকে বিচ্ছিন্নতার দিকেই ইঙ্গিত করে।
ইতিহাসের বিকৃতি – শুধু ইতিহাস না থাকা নয়, বিকৃত ইতিহাসের কারণে পথ হারানো মানুষের কথাও কবি বলেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যারাই যখন ক্ষমতায় থেকেছে ইতিহাসকে তারা তখন নিজেদের মতো করে, নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করেছে। যথার্থ মানুষের ইতিহাস কোনো দাম পায়নি। সে ইতিহাসে তাই “আমাদের চোখমুখ ঢাকা/আমরা ভিখারি বারোমাস।” প্রথাগত ইতিহাস মানুষকে অন্ধ করে তোলে, চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাসকে নিজেদের ইতিহাস বলে মেনে নিতে হয়।
উপসংহার – ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে বর্তমানের সংকটে তাই বাঁচার পথ খুঁজে পাওয়া ক্রমশই অসম্ভব হয়ে ওঠে।
“আমরা ভিখারি বারোমাস।” — ‘আমরা’ কারা? তারা নিজেদের ভিখারি বলেছে কেন কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো।
‘আমরা’ যারা – শঙ্খ ঘোষের ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতার উল্লিখিত অংশে ‘আমরা’ বলতে সাধারণ মানুষদের বোঝানো হয়েছে।
ভিখারি বলার কারণ – আমাদের সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিত্তবান ও ক্ষমতাবান মানুষদের দ্বারা। সমাজের অধিকাংশ যে সাধারণ মানুষ তারা সব দিক দিয়েই উপেক্ষিত থাকে। ইতিহাসে তাদের কোনো স্বীকৃতি ঘটে না। যে ইতিহাস তাদের দেওয়া হয় তা বিকৃত ইতিহাস। সাধারণ মানুষ এখানে সমস্তরকম অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দিন কাটায়। আমাদের চোখমুখ ঢাকা অর্থাৎ মানুষ নিজের মতো করে সব কিছু দেখতে পায় না কিংবা নিজেদের কথা বলতে পারে না। ক্ষমতাশালীদের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করে তাদের জীবন কাটাতে হয়। এই মানুষদের কথা কেউ জানে না, তারা খ্যাতিহীন, প্রচারের আলো তাদের থেকে অনেক দূরে থাকে। কিন্তু এরাই সভ্যতার ধারক। তাই এদের দুরবস্থায় পৃথিবীর অস্তিত্বও বিপন্ন হয়। বারোমাস ‘ভিখারি’ হয়ে থাকা বলতে এই অন্যের দয়ার ওপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকাকেই বোঝানো হয়েছে।
উপসংহার – “আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।” – যুদ্ধ কিংবা রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের পাশাপাশি এই মানবিক লাঞ্ছনা যেন মানবসভ্যতার এক অসহায় অবস্থাকেই স্পষ্ট করে দেয়।
“তবু তো কজন আছি বাকি” — এই ‘কজন’ কারা? তাদের থাকার গুরুত্ব সমগ্র কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো।
‘কজন’ -এর পরিচয় – শঙ্খ ঘোষের ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায় ‘কজন’ বলতে সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের বোঝানো হয়েছে।
গুরুত্ব বিশ্লেষণ – আমাদের চারপাশের এক অস্থির সময়কে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানে মানুষের চলার পথে অজস্র বাধা। সাম্রাজ্যবাদীদের লোভ যুদ্ধকে ডেকে আনছে। মানুষ নিরাশ্রয় হচ্ছে। মৃত্যু ও মৃত্যুর আতঙ্ক তাড়া করছে সকলকে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জীবন আরও বেশি করে বিপন্ন হয়ে পড়ছে ক্ষমতাবানদের অত্যাচারে। তাদের ইতিহাসকে স্বীকার করা হয় না। ক্ষমতাবানদের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয় এই সব মানুষদের। সব মিলিয়ে সভ্যতা এবং পৃথিবীর বিপন্নতাকে কবি লক্ষ করেছেন তার অভিজ্ঞতায়। কিন্তু আশাবাদী কবি মনে করেছেন এই ধ্বংস-যুদ্ধ-লাঞ্ছনা কখনও সভ্যতার শেষকথা হতে পারে না। সমাজে এখনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছে। স্বার্থপরতা, আদর্শহীনতা যুদ্ধ উন্মত্ততা কিংবা লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে এই মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ হলে সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব। তাদের উদ্দেশ্য করেই তাই কবির আন্তরিক আহ্বান “আয় আরো হাতে হাত রেখে-আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।” অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সম্প্রীতিই সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে।
“আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।” — কবি কাদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছেন? এভাবে থাকার প্রয়োজন কেন?
উদ্দিষ্ট ব্যক্তি – শঙ্খ ঘোষের ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায় কবি সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের উদ্দেশ্য করে কথাটি বলেছেন।
এভাবে থাকার প্রয়োজনীয়তা – অস্থির সময়ে পৃথিবী জুড়ে অনিশ্চয়তা, ধ্বংস আর মৃত্যুর ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন কবি। সেখানে নানা বাধার কারণে চলার গতি রুদ্ধ, পথ দুর্গম। মাথার উপরে বোমারু বিমানের আনাগোনা। ধ্বংস ও মৃত্যুর নিশ্চিত আগমন। যুদ্ধের কারণে মানুষ আশ্রয়হীন হচ্ছে, চারপাশে পড়ে আছে মৃত শিশুদের দেহ। এদিকে যারা ক্ষমতাবান তাদের ইচ্ছায় সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের অবদানের ইতিহাসকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের অধিকারকেও স্বীকার করা হচ্ছে না। এককথায় সাধারণ মানুষেরা, সমাজে যারা সংখ্যায় বেশি, তারাই দয়া ভিক্ষা করে বেঁচে আছে। এভাবে মনুষ্যত্বের এই বিপর্যয়ের পরেও পৃথিবী টিকে আছে – এমন কথা বলা যায় কি না, তা নিয়ে কবির মনে সংশয় তৈরি হয়েছে। কিন্তু আশাবাদী কবি শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করেন যে এই যুদ্ধ-হত্যা-বঞ্চনা কখনও চূড়ান্ত সত্য হতে পারে না। সমাজে এখনও অনেক শুভবোধসম্পন্ন মানুষ আছে। তারা যদি একত্রিত হয় তাহলে অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারবে। তার জন্যই দরকার একসঙ্গে থাকা, সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করা, হাতে হাত রাখা।
“আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।” — কবির এই আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা কবিতা অবলম্বনে লেখো।
অস্থির সংকটকালের ছবি – শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায় অস্থির সময়ে মানুষের সংকটের ছবিকে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক আদর্শহীনতা যেমন মানুষকে ঠিক পথ দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে তেমনই সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মান্ধতার মতো অসুখ সমাজকে রক্তাক্ত করছে। অস্তিত্বের সংকটে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে মানুষ। “আমাদের পথ নেই কোনো/আমাদের ঘর গেছে উড়ে/আমাদের শিশুদের শব/ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে।”
প্রকৃত ইতিহাসহীনতা – এই সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রেরণা সংগ্রহ করার মতো কোনো ইতিহাসও আমাদের নেই। কারণ ক্ষমতাবান শাসকেরা যে ইতিহাস আমাদের উপহার দিয়েছে তা বিকৃত এবং তাদের মতো করে গড়ে তোলা। এখানে ‘ভিখারি’ হয়ে বেঁচে থাকাটাই মানুষের নিয়তি।
মুক্তির পথ সন্ধান – এই হতাশার মধ্যেই মুক্তির পথ খুঁজেছেন কবি। তাঁর মনে হয়েছে, কোথাও কিছু না থাকলেও এমন কিছু মানুষ এখনও সমাজে রয়েছে যারা তৈরি করবে সম্প্রীতির এবং সৌভ্রাতৃত্বের পথ। সেকারণেই দরকার পরস্পরের হাত ধরা। কোনো পথ দেখতে না পাওয়ার সময়ে হাতে হাত রেখে বেঁধে থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।
শঙ্খ ঘোষের আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি কবিতার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করো।
অথবা, ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায় কবির সমাজভাবনার যে প্রকাশ ঘটেছে তা নিজের ভাষায় লেখো।
আর্দশহীনতা – কবিকে ব্যথিত করেছে রাজনৈতিক আদর্শহীনতা। ডান দিকে ধস আর বাম দিকে গিরিখাত জীবনের চলার পথকেই দুর্গম করে তোলে। মাথার ওপরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাণ্ডব, চারপাশে ধর্মান্ধতা, মধ্যযুগীয় বর্বরতা ইত্যাদি যেন ক্রমশই পথকে ধূসর করে দেয়। মৃত্যুর আতঙ্ক তাড়া করে সব মানুষকেই।
প্রকৃত ইতিহাসের অভাব – যে জাতীয়তার ধারণা মানুষের সঙ্গে মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধতে পারত তা-ও বিরল। কারণ, ‘আমাদের ইতিহাস নেই“। তাই ইতিহাসের সত্যকে মানুষ পায় না, যা তাদের পথ দেখাতে পারে। ক্ষমতাবান শাসকেরা নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের মতো করে ইতিহাস তৈরি করে নেয়। সাধারণ মানুষ সেখানে উপেক্ষিত হয়। – “আমাদের কথা কে-বা জানে/ আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।”
মানব মৈত্রীর সেতুবন্ধন – তবুও কিছু মানুষ থেকে যায়, মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সেতুবন্ধ তৈরি করাই যাদের কাজ। শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘এ আমরা কী করছি’ গদ্যরচনায় লিখেছিলেন – “আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা এমন এক মুঢ় অহমিকা প্রকট করে তুলতে চাইছেন দেশবাসীর মনে, ফ্যাসিবাদ যার সুনিশ্চিত পরিণাম। অথচ আজও মানুষের মনে এক স্বাভাবিক মিলনক্ষুধা আছে, এক দেশের মানুষকে আর-এক দেশের মানুষ অন্তরঙ্গ ভালোবাসাতেই জড়িয়ে নিতে চায় আজও …”। এই ভালোবাসা আর মানবমৈত্রীর কথাই কবি উচ্চারণ করেছেন ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতায়।
“আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি” – কবিতায় কবিচেতনার কোন্ অভিনবত্ব লক্ষ করা যায় আলোচনা করো।
মনুষ্যত্বের বার্তা প্রকাশ – চারপাশের অশান্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতাটি রচিত। রাষ্ট্রীয় ভণ্ডামি, সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার, ধর্মীয় উগ্রতা এবং ক্রমশ চেপে বসা আদর্শহীনতা-ইত্যাদির বিস্তার কোনো পথের সন্ধান দেয় না, বরং এক আশ্রয়হীনতার দিকে নিয়ে যায়। মানুষ ক্রমশই যেন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে। যে ইতিহাস প্রেরণা হতে পারত, তা-ও ক্ষমতাবানদের দ্বারা বিকৃত।
একতার বার্তা – এই পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে টিকে থাকাটাই সন্দেহের। তবুও পারস্পরিক মিলনের পথ ধরেই মানুষকে চলতে হবে। একতাই পারে এই সংকট থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। সেই একতার কথাই কবি এখানে বলেছেন।
অনবদ্য প্রকাশশৈলী – মনুষ্যত্বের এই বার্তাকে প্রকাশ করা যদি কবিতার বিষয় হয়, তাহলে তাকে রূপ দিতে গিয়ে এক অনায়াস শব্দশৈলী ও প্রকাশরীতি কবি অনুসরণ করেছেন। লক্ষ করার মতো বিষয় হল, কবিতায় অন্ত্যমিল থাকলেও তা হয়েছে দ্বিতীয়-র সঙ্গে চতুর্থ, ষষ্ঠ-র সঙ্গে অষ্টম – এই ধারা মেনে। উত্তমপুরুষের জবানিতে কথা বলায় কবি যেন সব মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন।
উপসংহার – শব্দ ব্যবহারে জটিলতা এড়িয়ে তিনি কবিতাকে আন্তরিক করে তুলেছেন। সময়ের বিপন্নতা, আর তা থেকে মুক্তির চেষ্টা-দুটোই তাই আবেগময় হয়ে উঠেছে।
“আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি” – এই পঙ্ক্তিটির পুনরাবৃত্ত হওয়ার কারণ কবিতাটি অবলম্বনে আলোচনা করো।
তাৎপর্য – ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ কবিতার নামটিই পঙ্ক্তি হিসেবে কবিতায় দুবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কবিতার দুটি স্তবক এবং স্তবকের শেষ পঙক্তি হিসেবেই “আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি” শব্দবন্ধটি এসেছে। সমগ্র বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এই পঙক্তি দুটি আলাদা তাৎপর্য বহন করে।
একতার প্রয়োজনীয়তা – কবিতার প্রথম স্তবকে ডান পাশে ধ্বংস আর বাঁ-দিকে গিরিখাদ -এর উল্লেখে কবি বোঝাতে চেয়েছেন পথের দুর্গমতা। এই পথ আসলে সভ্যতার পথ। সেখানে মাথার উপরে বোমারু বিমান। এই পথ চলার মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে আসে নিরাশ্রয়তা। শিশুমৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। সেই মৃত্যুভয় সমস্ত মানুষকেই তাড়া করে। আর তখনই কবি উপলব্ধি করেন যে, আমাদের অন্য কোনো বিকল্প নেই। বেঁচে থাকার একটাই উপায় আছে। আর তা হল ঐক্যের এবং সম্প্রীতির। সেজন্যই আমাদের বেঁধে বেঁধে থাকতে হবে।
সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা – দ্বিতীয় স্তবকে কবি এনেছেন সভ্যতার অন্তঃশূন্যতার কথা। সাধারণ মানুষের সেখানে স্বীকৃতি নেই। ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতাবানরা। ফলে তৈরি হয় সাধারণ মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস। তাদের কৃপাপ্রার্থী হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। যুদ্ধ-ধ্বংস-প্রবঞ্চনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর অস্তিত্বই সেখানে সংশয়ের সামনে পড়ে। মানুষের সভ্যতাকে রক্ষার জন্য তাই দরকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া।
উপসংহার – এভাবে মৃত্যু আর বিনষ্টিকে অতিক্রম করে কবি আসলে শোনাতে চেয়েছেন একতার ও সম্প্রীতির প্রয়োজনের কথা। ধ্বংসোম্মুখ সভ্যতার বিশল্যকরণী তা। এই তাৎপর্যেই “আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।“ পঙক্তি পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন কবি। এটিই হয়ে উঠেছে কবিতার মূল সুর।
আজকের এই আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক বাংলার দ্বিতীয় পাঠের দ্বিতীয় বিভাগ, “আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি” থেকে বিশ্লেষণধর্মী ও রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের উপকারী হয়েছে। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো অসুবিধা হয়, তবে আমার সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন; আমি যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। এছাড়াও, পোস্টটি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না, যাদের এই তথ্য কাজে লাগতে পারে। ধন্যবাদ।


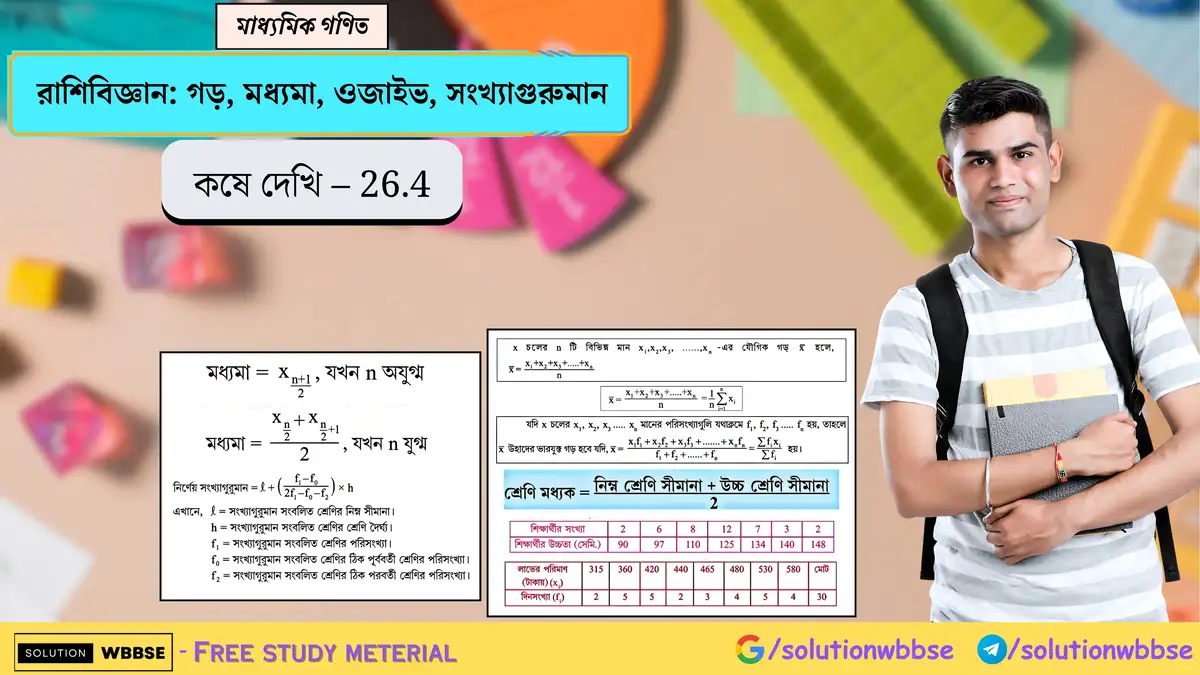
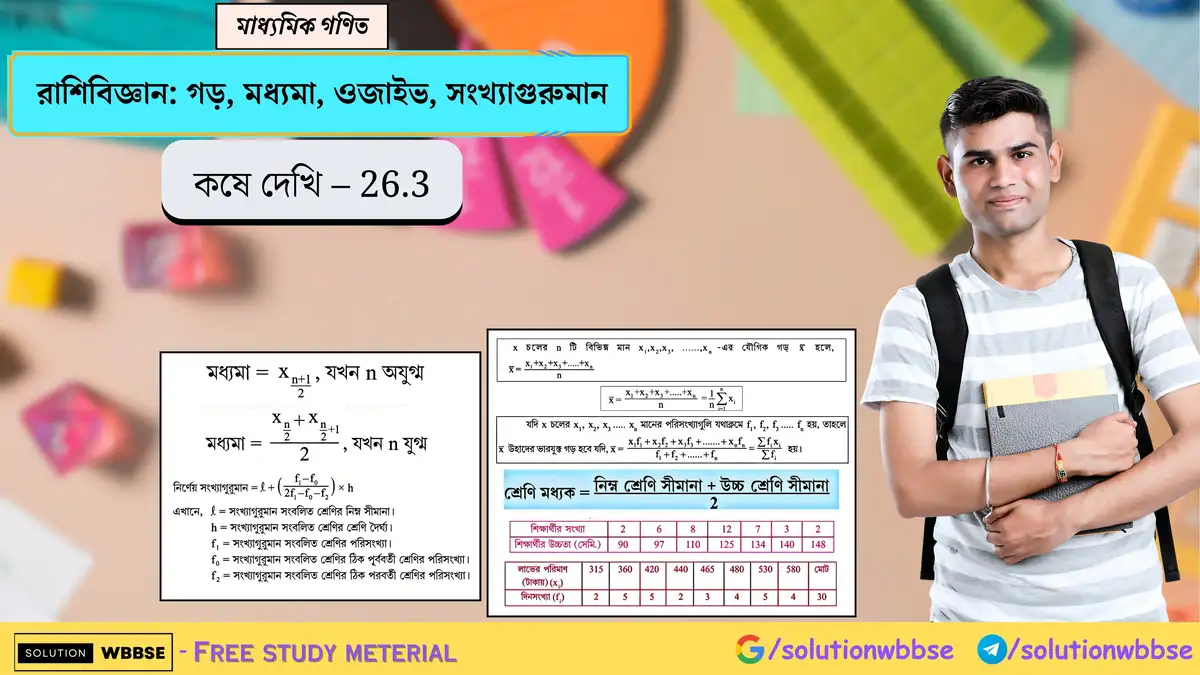
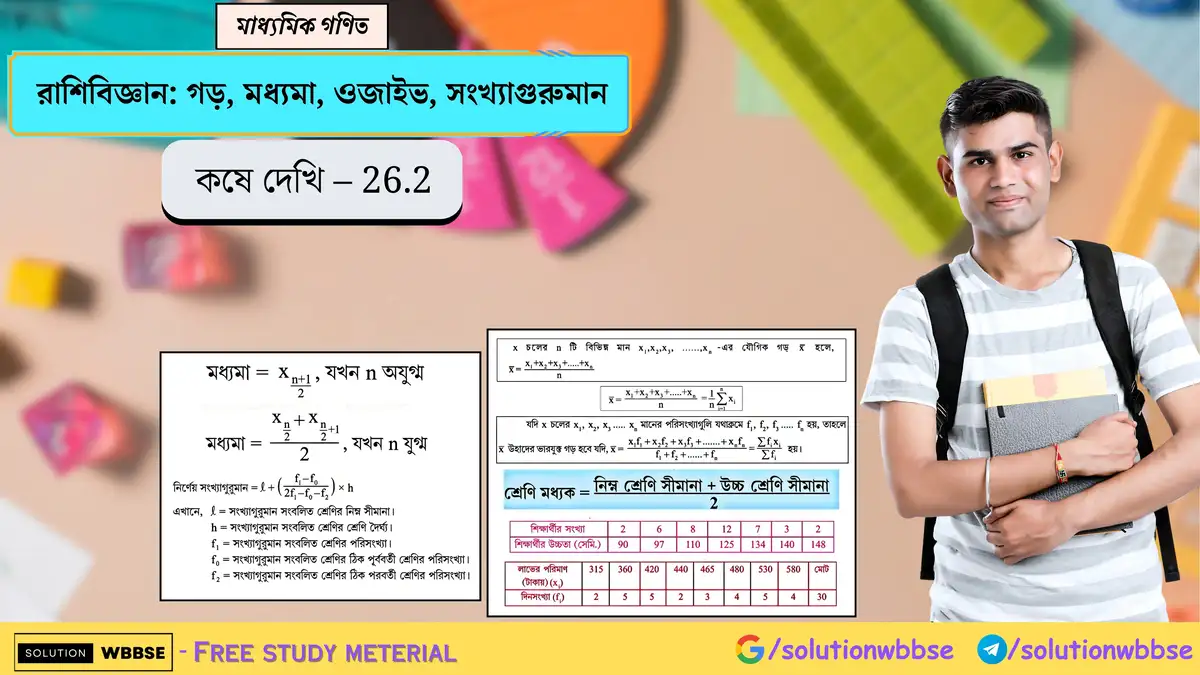

মন্তব্য করুন