আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোলের প্রথম অধ্যায় “বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ” -এর “বহির্জাত প্রক্রিয়া ও নদীর কাজ দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ” বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ “সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
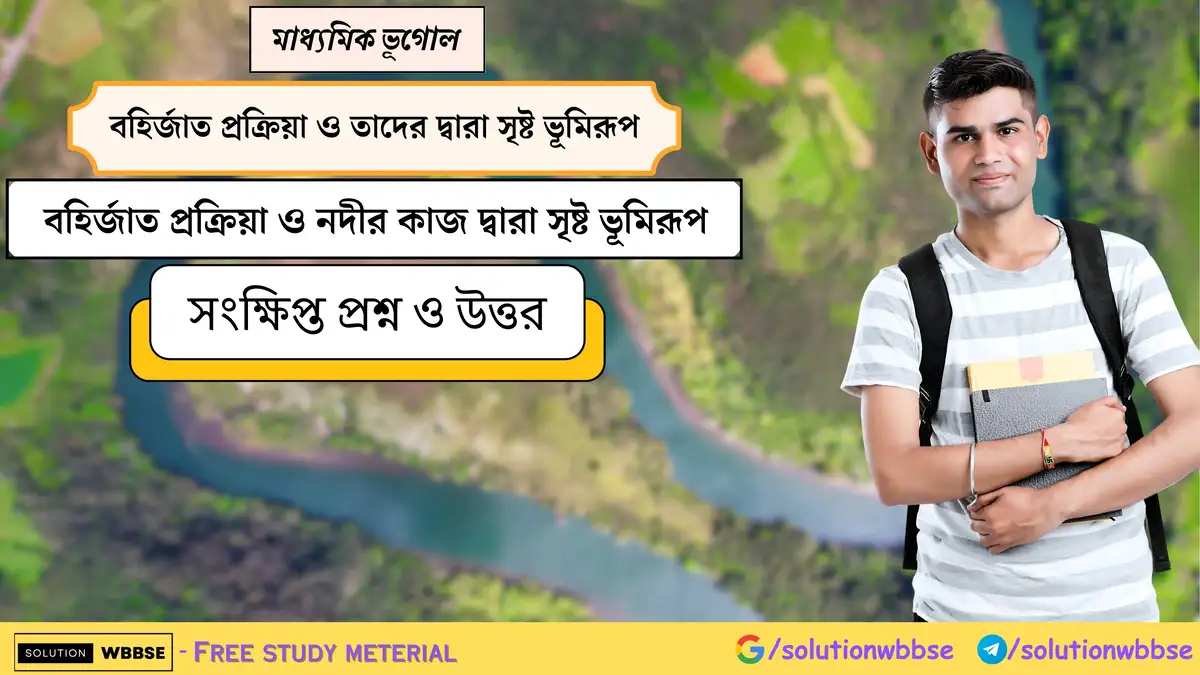
নদী বলতে কী বোঝ?
কোনো পাহাড়, পর্বত, মালভূমি বা উচ্চভূমির হিমবাহ নির্গত জলধারা বা বৃষ্টির জলধারা যখন ভূমির ঢাল অনুসরণ করে নির্দিষ্ট খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র, হ্রদ বা জলাভূমিতে এসে মেশে, তখন তাকে নদী বলে। উদাহরণ — গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা প্রভৃতি নদী।
উপনদী ও শাখানদী কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উপনদী – প্রধান নদীর গতিপথের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অনেক ছোটো ছোটো নদী এসে প্রধান নদীতে মিলিত হয়, এগুলিকে বলা হয় উপনদী। উদাহরণ — গঙ্গার উপনদী যমুনা।
শাখানদী – মূলনদী থেকে যেসব নদী শাখা আকারে বের হয়, সেগুলিকে বলা হয় শাখানদী। উদাহরণ — গঙ্গার শাখানদী ভাগীরথী-হুগলি।
আদর্শ নদী কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
যে নদীর গতিপথে ক্ষয়কার্য-প্রধান পার্বত্য প্রবাহ বা উচ্চগতি, বহনকার্য-প্রধান সমভূমি প্রবাহ বা মধ্যগতি এবং সঞ্চয়কার্য প্রধান বদ্বীপ প্রবাহ বা নিম্নগতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়, সেই নদীকে আদর্শ নদী বলা হয়। উদাহরণ — ভারতের প্রধান নদী গঙ্গার গতিপথে এই তিনটি অবস্থাই বিদ্যমান বলে গঙ্গা একটি আদর্শ নদী।
কার্য অনুসারে নদীর প্রবাহকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায়?
উৎস থেকে মোহানা পর্যন্ত নদী তার গতিপথে তিনটি কাজ করে – ক্ষয়সাধন, বহন এবং অবক্ষেপণ বা সঞ্চয়। আর, এই তিন প্রকার কাজের ভিত্তিতে নদীর প্রবাহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় —
- ক্ষয়কার্য – প্রধান উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহ,
- বহনকার্য – প্রধান মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ এবং
- সঞ্চয়কার্য – প্রধান নিম্নগতি বা বদ্বীপ প্রবাহ।
নদীর কাজ কী কী?
নদীর কাজ তিনটি — ক্ষয়সাধন, বহন এবং অবক্ষেপণ।
- পার্বত্য প্রবাহ বা উচ্চগতিতে নদী প্রধানত ক্ষয়কার্য করে। তা ছাড়া, ওই অংশে নদী ক্ষয়জাত দ্রব্যসমূহ বহনও করে।
- সমভূমি প্রবাহ বা মধ্যগতিতে নদীর প্রধান কাজ বহন। তবে এই অংশে নদী কিছু ক্ষয় (পার্শ্বক্ষয়) এবং অবক্ষেপণও করে।
- আর বদ্বীপ প্রবাহ বা নিম্নগতিতে নদীর প্রধান কাজ হয় সঞ্চয়। তবে এই অংশে নদী অল্প পরিমাণে বহনও করে।
নদীর ষষ্ঠঘাতের সূত্র কী?
নদীবাহিত ক্ষয়জাত পদার্থের পরিমাণ নদীর গতিবেগের ষষ্ঠঘাতের সমানুপাতিক। এই সূত্রটিকে নদীর ষষ্ঠঘাতের সূত্র বলে। কোনো একটি নদীর গতিবেগ, জলের পরিমাণ অথবা ভূমির ঢালের বৃদ্ধির কারণে নদীর বহনক্ষমতাও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। যেমন, ঘণ্টায় 2 কিমি বেগে প্রবাহিত নদী যে পরিমাণ বোঝা বহন করতে পারে, সেই নদী দ্বিগুণ বেগে অর্থাৎ ঘণ্টায় 4 কিমি বেগে প্রবাহিত হলে 26 = 64 গুণ বেশি পরিমাণ বোঝা বহন করতে সক্ষম হবে।
নদী অববাহিকা ও জলবিভাজিকা বলতে কী বোঝ?
নদী অববাহিকা – একটি নদী এবং তার বিভিন্ন উপনদী ও শাখানদীগুলি যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই অঞ্চলকে বলা হয় সেই নদীটির অববাহিকা।
জলবিভাজিকা – কাছাকাছি অবস্থিত দুই নদী অববাহিকাকে যে উচ্চভূমি পৃথক করে, সেই উচ্চভূমিকে বলা হয় জলবিভাজিকা। সাধারণত পাহাড় বা পর্বত জলবিভাজিকার কাজ করে।
নদী অববাহিকা ও জলবিভাজিকা
ধারণ অববাহিকা কাকে বলে?
নদীর উৎস অঞ্চলে হিমবাহের বরফগলা জল, ঝরনার জল অথবা বৃষ্টির জল অসংখ্য ছোটো ছোটো জলধারার আকারে প্রবাহিত হয়ে বড়ো নদী তৈরি করে। এই জলধারা-সহ মূল বা বড়ো নদীটি উৎস অঞ্চলের যে অংশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়, সেই অঞ্চলটাকে ধারণ অববাহিকা বলে।
নদী উপত্যকা কাকে বলে?
দুই উচ্চভূমির মধ্যবর্তী দীর্ঘ ও সংকীর্ণ নিম্নভূমিকে বলা হয় উপত্যকা। আর সেই সংকীর্ণ নিম্নভূমির মধ্যে দিয়ে যখন নদী প্রবাহিত হয়, তখন তাকে বলা হয় নদী উপত্যকা। অর্থাৎ নদী যে অংশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে নদী উপত্যকা বলে।
গিরিখাত কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
বৃষ্টিবহুল পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির ঢাল বেশি থাকে বলে নদীর গতিবেগ খুব বেশি হয়। এই অংশে নদী পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় বেশি করে। এর ফলে নদীখাত যথেষ্ট গভীর হয়। নদীখাত খুব গভীর ও সংকীর্ণ হতে হতে যখন ইংরেজি অক্ষর ‘V’-আকৃতির হয়, তখন তাকে বলা হয় গিরিখাত। উদাহরণ — দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর এল ক্যানন দ্য কলকা বিশ্বের একটি গভীরতম (3270 মিটার) গিরিখাত।
কিউসেক ও কিউমেক কী?
কিউসেক – নদীর একটি নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত ঘনফুট জল প্রবাহিত হয়, তাকেই কিউসেক (cubic feet per second) বলা হয়।
কিউমেক – নদীর একটি নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত ঘনমিটার জল প্রবাহিত হয়, তাকে কিউমেক (cubic meter per second) বলা হয়।
নদীবাঁক বা মিয়ান্ডার কাকে বলে?
সমভূমিতে ভূমির ঢাল খুব কম থাকে বলে নদীর গতিবেগও কমে যায়। এই সময় নদীর জলস্রোত খাতের বাইরের দিকে ক্ষয় করে উপত্যকাকে চওড়া করে। অন্যদিকে, জলস্রোতের গতিবেগ কম থাকায় খাতের ভেতরের অংশে নদী সঞ্চয় করে। এইভাবে ক্রমাগত নদীর খাতের বাইরের অংশে ক্ষয় হলে ও ক্ষয়জাত পদার্থ নদীর খাতের ভেতরের দিকে সঞ্চয় হতে থাকলে নদী সাপের মতো এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়। এই বাঁকগুলিকেই নদীবাঁক বলে। নদীবাঁকের একটি পাড় উত্তল ও বিপরীত পাড়টি অবতল হয়।
অন্তর্বদ্ধ শৈলশিরা কী?
পার্বত্য অঞ্চলে শৈলশিরাসমূহ নদীর গতিপথে এমনভাবে বাধার সৃষ্টি করে যে, সেই বাধা এড়াতে নদীকে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হতে হয়। এর ফলে শৈলশিরাগুলিকে দূর থেকে পরস্পর আবদ্ধ দেখায় এবং নদী ওই শৈলশিরাগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে মনে হয়। একে অন্তর্বদ্ধ শৈলশিরা বলা হয়।
কাসকেড কী?
যখন কোনো জলপ্রপাতের জল অজস্র ধারায় বা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নীচের দিকে নামে, তখন সেই জলপ্রপাতকে কাসকেড বলে। যেমন – ঝাড়খণ্ডের জোনা জলপ্রপাত।
ক্যানিয়ন কাকে বলে?
তুষারগলা জলে উৎপন্ন কোনো নদী যখন বৃষ্টিহীন শুষ্ক অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তার দুই পাড়ের ক্ষয় (পার্শ্বক্ষয়) খুব কম থাকে। এই অবস্থায় নদীর গতিপথে যদি কোমল শিলাস্তর থাকে তাহলে নদীজলের স্বল্পতার জন্য নদীর উপত্যকায় নিম্নক্ষয় বেশি হয়। এর ফলে ইংরেজি অক্ষর ‘I’-আকৃতির অত্যন্ত গভীর ও সংকীর্ণ যে গিরিখাতের সৃষ্টি হয়, তাকে ক্যানিয়ন বলা হয়। যেমন – গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন।
নদীগ্রাস কাকে বলে?
কোনো জলবিভাজিকা থেকে নির্গত পাশাপাশি প্রবাহিত দুটি নদীর মধ্যে যে নদীটি বেশি শক্তিশালী, সেই নদীটি অন্য, নদীটির মস্তকদেশের অংশবিশেষ গ্রাস করে। এই ঘটনাকে বলা হয় নদীগ্রাস (river capture)।
নদীর ক্ষয়সীমা বলতে কী বোঝ?
নদী ভূপৃষ্ঠে যে উচ্চতা পর্যন্ত ক্ষয় করতে সক্ষম, সেই উচ্চতাকে নদীর ক্ষয়সীমা বলে। সাধারণভাবে নদীর ক্ষয়সীমা হল সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা অর্থাৎ নদী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা পর্যন্ত ক্ষয়কার্য করে। তবে নদীর গতিপথে কোনো কঠিন শিলা অবস্থান করলে নদী এই কঠিন শিলাস্তরকে বিশেষ ক্ষয় করে না। তখন ওই কঠিন শিলাস্তর স্থানীয় ক্ষয়সীমারূপে কাজ করে। মরু অঞ্চলে নদীর ক্ষয়সীমা হল প্লায়া হ্রদ।
অন্তর্জাত শক্তি কী?
পৃথিবীর অভ্যন্তরে সৃষ্ট সংকোচন, প্রসারণ, উত্থান, অবনমন, বিচ্ছেদ, বিকৃতি, নির্গমন প্রভৃতি যেসব প্রক্রিয়ার জন্য ভূপৃষ্ঠের ভূমিরূপ প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হয়, সেগুলিকে ভূ-অভ্যন্তরীণ বা অন্তর্জাত শক্তি বলে। অগ্ন্যুদগিরণ, ভূমিকম্প ইত্যাদি অন্তর্জাত শক্তি। অন্তর্জাত শক্তির প্রভাবে মহাদেশ, মালভূমি, চ্যুতি, ফাটল, গ্রস্ত উপত্যকা, উত্থিত বা নিমজ্জিত উপকূল ইত্যাদি তৈরি হয়। এগুলি ধীর প্রক্রিয়া। অন্যদিকে আগ্নেয়গিরি, লাভা মালভূমি এগুলি আকস্মিক আলোড়নের ফলে তৈরি হয়। অন্তর্জাত আন্দোলন উল্লম্ব আলোড়ন এবং অনুভূমিক আলোড়নের মধ্যে দিয়ে হয়।
বহির্জাত শক্তি কী?
যেসব প্রাকৃতিক শক্তি প্রতিনিয়ত ভূপৃষ্ঠে এবং ভূপৃষ্ঠের সামান্য নীচে অর্থাৎ উপপৃষ্ঠীয় অংশে ক্রিয়াশীল থাকে তাদের বহির্জাত শক্তি বলে। যেমন – নদী, হিমবাহ, বায়ু, সমুদ্রতরঙ্গ প্রভৃতি বহির্জাত শক্তি।
ক্রমায়ন শক্তি কাকে বলে?
ক্রমায়ন শক্তি বলতে তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে বহির্জাত শক্তির কার্যপ্রক্রিয়াকে বোঝায়। প্রথম পর্যায়ে পদার্থের বিয়োজন ও ক্ষয়কাজ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিয়োজিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থসমূহ অপসৃত বা পরিবাহিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে অপসৃত বা পরিবাহিত দ্রব্যগুলি ভূপৃষ্ঠের নিচু অংশে সঞ্চিত হয়।
অবরোহণ প্ৰক্ৰিয়া কী?
বহির্জাত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী শক্তিগুলি যেভাবে ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন করে সেই প্রক্রিয়াকে অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে। আবহবিকার বা বিচূর্ণীভবন, পুঞ্জক্ষয় এবং অন্যান্য ক্ষয় প্রক্রিয়াগুলি অবরোহণ ক্রিয়ার ফল। কোন্ অঞ্চলে কী ধরনের অবরোহণ হবে, তা নির্ভর করে সেখানকার জলবায়ু, শিলার প্রকৃতি, ক্ষয়কারী শক্তির কার্যক্ষমতা ইত্যাদির ওপর।
আরোহণ প্রক্রিয়া কাকে বলে?
আরোহণ প্রক্রিয়া বলতে ভূপৃষ্ঠের ওপর সঞ্চয়, অবক্ষেপণ এবং অধঃক্ষেপণের মাধ্যমে ভূমিরূপের নির্মাণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে নিম্নভূমির উচ্চতা বেড়ে যায়। পর্বতের পাদদেশে সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ তৈরি হয়। নদী অববাহিকায় পলল ব্যজনী ও প্লাবনভূমির মতো ভূমিরূপ তৈরি হয়।
মানুষ এবং অন্যান্য জীব কীভাবে বহির্জাত শক্তির প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে?
মানুষ-সহ সমগ্র জীবজগত ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় এবং সঞ্চয়কার্যে অংশগ্রহণ ক’রে বহির্জাত শক্তির প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। মানুষ রাস্তাঘাট, বাঁধ-জলাধার ইত্যাদি নির্মাণের কাজে এবং রিভার প্রেইরি কুকুর ইত্যাদি প্রাণী জীবনধারণের প্রয়োজনে শিলাকে ক্ষয় ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। এইভাবেই ক্ষয়কার্য ঘটে। অন্যদিকে জলাভূমি, লেগুনে যেসব শ্যাওলা, গাছপালা জন্মায়, তাদের ফুল, পাতা, ফল ইত্যাদি পচে গিয়ে জৈব পদার্থ তৈরি করে। সেসব দিয়েই জলাভূমি ভরাট হয়। মানুষ নিজেও জলাভূমি ভরাট করে, নদী-সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং ভূমিভাগের সঞ্চয় প্রক্রিয়াকে জারি রাখে।
সমপ্ৰায় ভূমি কাকে বলে?
নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে এই ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হয়। আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে নদীর জলপ্রবাহ ভূমিভাগকে ক্ষয় করে এবং কঠিন শিলা কম ক্ষয় পায়। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চভূমি ক্ষয় পেতে পেতে যে নীচু প্রায়সমতল ভূমিভাগের সৃষ্টি করে, তাকে সমপ্রায়ভূমি বলে। এই সমপ্রায়ভূমির মধ্যে কঠিন শিলাগুলি ক্ষয় না পেয়ে মোনাডনক রূপে অবস্থান করে। ছোটোনাগপুরের সমভূমি হল একটি সমপ্রায়ভূমির উদাহরণ। এর মধ্যে পরেশনাথ ও পাঞ্চেত পাহাড় দুটি মোনাডনক।
নদীর মধ্যগতি বলতে কী বোঝ?
নদী যখন পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে সমভূমিতে এসে পড়ে, সেই সমভূমি অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদীর প্রবাহকে মধ্যগতি বলে। মধ্যগতিতে নদীর প্রধান কাজ বহন এবং সঞ্চয় করা। গঙ্গানদীর হরিদ্বার থেকে মুরশিদাবাদের ধুলিয়ান পর্যন্ত প্রবাহপথটি মধ্যগতির মধ্যে পড়ে।
মধ্যগতিতে নদীর প্রধান কাজ কী?
নদীর তিনটি গতিতে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করলেও মধ্যগতিতে নদী প্রধানত বহন কাজ করে। তবে স্থানভেদে এই প্রবাহে ক্ষয় এবং সঞ্চয় কাজও করে থাকে। যদিও এই দুই প্রকার কাজের পরিমাণ কম। অর্থাৎ মধ্যগতিতে নদী বেশি বহন করে এবং অল্প ক্ষয় এবং বেশ কিছুটা সঞ্চয় করে।
নদীর নিম্নগতি বা বদ্বীপ প্রবাহ কাকে বলে?
নদী যে স্থান থেকে একেবারে সমতলভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহকে নিম্নগতি বলে। সাধারণত নদী সমুদ্রের কাছাকাছি এসে পৌঁছোলেই নদীর নিম্নগতি শুরু হয়। মোহানা পর্যন্ত এই গতি বজায় থাকে। গঙ্গানদীর ক্ষেত্রে মুরশিদাবাদের ধুলিয়ানের পর থেকে গঙ্গাসাগরের মোহানা পর্যন্ত অংশ বদ্বীপ প্রবাহের অংশ।
প্ৰপাতকূপ কী?
পার্বত্য অংশে নদীর ঢাল বেশি থাকে বলে জল প্রবল বেগে নীচে নামে এবং ভূমির ঢালের তারতম্যহেতু জলতলের পার্থক্য সৃষ্টি হলে সেখানে জলপ্রপাত গঠিত হয়। এই জলপ্রপাতের জল নীচে যেখানে এসে আঘাত করে সেখানে প্রায় গোলাকার গর্ত সৃষ্টি হয়। এটি প্রপাতকূপ নামে পরিচিত। প্রপাতকূপ সৃষ্টিতে নদীবাহিত বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
মিয়েন্ডার ভূমিরূপ নামকরণ কেন হয়েছে?
সমভূমি প্রবাহে নদীর যে-কোনো বাঁককেই মিয়েন্ডার বলা হয়। তুরস্কের মেনডারেস (Menderes) নদীতে অসংখ্য নদীবাঁক দেখা যায়। ওই নদীবাঁকের কথা মনে রেখেই পৃথিবীর যাবতীয় নদীবাঁককে মিয়েন্ডার বলা হয়।
লোহাচড়া দ্বীপটি ডুবে যাচ্ছে কেন?
হুগলি নদীর মোহানায় লোহাচড়া দ্বীপটি বর্তমানে ডুবে গেছে। এর কারণ হিসেবে গবেষকরা কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন –
- সমুদ্রজলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি,
- উপকূলের ক্ষয়,
- প্রবল ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি। এ ছাড়া
- ম্যানগ্রোভের ধ্বংস এই দ্বীপের খুব ক্ষতি করছে।
ফারাক্কা ব্যারেজের সাথে লোহাচড়া দ্বীপের সম্পর্ক কী?
আপাতদৃষ্টিতে ফারাক্কা ব্যারেজের সঙ্গে লোহাচড়া দ্বীপের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ ফারাক্কা ব্যারেজ হল মুরশিদাবাদের একটি বাঁধ আর লোহাচড়া দ্বীপটি হল বঙ্গোপসাগরের মধ্যে সম্প্রতি ডুবে যাওয়া একটি দ্বীপ। বিশেষজ্ঞদের মতে, 1974 সালে ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরি হওয়ার পর থেকে শুষ্ক ঋতুতে হুগলি নদী দিয়ে আরও বেশি পরিমাণ জল প্রবাহিত হচ্ছে। বছরের প্রায় ছয় মাস সুন্দরবনের দ্বীপগুলি জলমগ্ন থাকে। এর সঙ্গে সমুদ্র জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় ক্ষয় ও ঘূর্ণবাতের তীব্রতা বাড়ার কারণেও লোহাচড়া দ্বীপের মতো আরও দ্বীপের অদৃশ্য হওয়ার ঘটনা ঘটছে।
দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ সম্পর্কে কী জান?
হাড়িয়াভাঙা নদীর মোহানা থেকে 2 কিমি দূরে এই দ্বীপের অবস্থান ছিল। ভৌগোলিক অবস্থা অনুযায়ী এটির অবস্থান ছিল 21°37′00″ উত্তর এবং 89°08′30″ পূর্ব। 1970 সালে ভোলা ঘূর্ণবাতের অব্যবহিত পরেই এই দ্বীপ সমুদ্র থেকে জেগে ওঠে। 1974 সালে এর আয়তন ছিল 2500 বর্গমিটার (উপগ্রহ চিত্র থেকে)। বর্তমানে এটি একটি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত দ্বীপ।
ঘোড়ামারা দ্বীপের বর্তমান অবস্থা কেমন?
কলকাতা থেকে মাত্র 92 কিমি দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে সুন্দরবনের এই সাধারণ দ্বীপটি অবস্থিত। পরীক্ষায় দেখা গেছে, 1951 সালে ঘোড়ামারা দ্বীপটির আয়তন ছিল 38.23 বর্গকিমি, 2011 সালে এর আয়তন দাঁড়ায় 4.37 বর্গকিমি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই দ্বীপটিও সম্পূর্ণ ডুবে যাবে।
নদীর পুনর্যৌবন লাভ বলতে কী বোঝ?
ভূমিঢালের পরিবর্তন হলে অনেকসময় নদীর নিম্নক্ষয় করার ক্ষমতা আবার ফিরে আসে। একেই নদীর পুনর্যৌবন লাভ বলে। ভূ-আন্দোলনের জন্য নদীখাতের উচ্চতা বৃদ্ধি, নদীর ক্ষয়সীমার উচ্চতার পরিবর্তন, নদীগ্রাস প্রভৃতি কারণে নদীতে জলের পরিমাণ বেড়ে গেলে অথবা কোনো কারণে নদীর বোঝার পরিমাণ কমে গেলে নদী পুনর্যৌবন লাভ করে।
নিক পয়েন্ট কী?
ভূমির পুনযৌবন লাভের ফলে নদী উপত্যকার নতুন ঢাল ও পুরোনো ঢালের সংযোগস্থলে যে খাঁজ তৈরি হয়, তাকে নিক পয়েন্ট বলে। এই নিক পয়েন্টে জলতলের পার্থক্য সৃষ্টি হয় বলে সেখানে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়।
অবঘর্ষ প্রক্রিয়া কী? অথবা, অবঘর্ষ কাকে বলে?
‘অবঘর্ষ’ কথাটির অর্থ ‘ঘর্ষণজনিত ক্ষয়’। সাধারণভাবে বলা যায়, নদী, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রতরঙ্গ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পরিবাহিত শিলাখণ্ড পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে বা ঘর্ষণে লিপ্ত হলে ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ঘটনাকে বলা হয় অবঘর্ষ। অবঘর্ষ ক্ষয়ের ফলে শিলার ক্ষয় দ্রুততর হয় এবং শিলা মসৃণ হয়।
মন্থকূপ কাকে বলে?
উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহে নদীর প্রবল স্রোতের সঙ্গে বাহিত প্রস্তরখণ্ড, নুড়ি, বালি প্রভৃতি ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে অগ্রসর হয়। এর ফলে পরিবাহিত নুড়ি ও প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ের কারণে নদীখাতে ছোটো ছোটো প্রায় গোলাকার গর্তের সৃষ্টি হয়। এগুলিকে বলা হয় মন্ত্রকূপ।
খরস্রোত কী?
নদীর গতিপথে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর একটির পর একটি লম্বালম্বিভাবে থাকলে কঠিন শিলাস্তরের তুলনায় কোমল শিলাস্তর তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। এর ফলে কয়েকটি ধাপ বা সিঁড়ির সৃষ্টি হয়। নদী তখন একটির পর একটি ধাপ পেরিয়ে দ্রুত নীচে নেমে আসে ও খরস্রোতের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ-আফ্রিকার বিখ্যাত নীলনদের গতিপথে খার্তুম থেকে আসোয়ান পর্যন্ত 6টি স্থানে এরকম খরস্রোতের সৃষ্টি হয়েছে।
পাখির পায়ের মতো বদ্বীপ কীভাবে গঠিত হয়?
মূল নদী অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়লে পাখির পায়ের মতো বদ্বীপ গঠিত হয়। নদীবাহিত সঞ্চয়জাত পদার্থ বহুদূরে সমুদ্রে সঞ্চিত হলে নদীর শাখাগুলি পাখির পায়ের মতো বা আঙুলের মতো আকৃতির বদ্বীপ তৈরি করে।
প্লাঞ্জ পুল কী?
জলপ্রপাতের পাদদেশে জলের সঙ্গে বাহিত নুড়ি, প্রস্তরখণ্ড ইত্যাদি সবেগে পতিত হয়। এর ফলে জলপ্রপাতের পাদদেশে যে প্রায় গোলাকার গর্তের সৃষ্টি হয়, তাকে প্লাঞ্জ পুল বলে। এই প্রকার গর্তের আয়তন ও গভীরতা জলের পরিমাণ ও জলধারা বাহিত বোঝার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে।
আরও পড়ুন – মাধ্যমিক ভূগোল – বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ – অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর
আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোলের প্রথম অধ্যায় “বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ” -এর “বহির্জাত প্রক্রিয়া ও নদীর কাজ দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ” বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ “সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর” নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক (দশম শ্রেণী) পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।


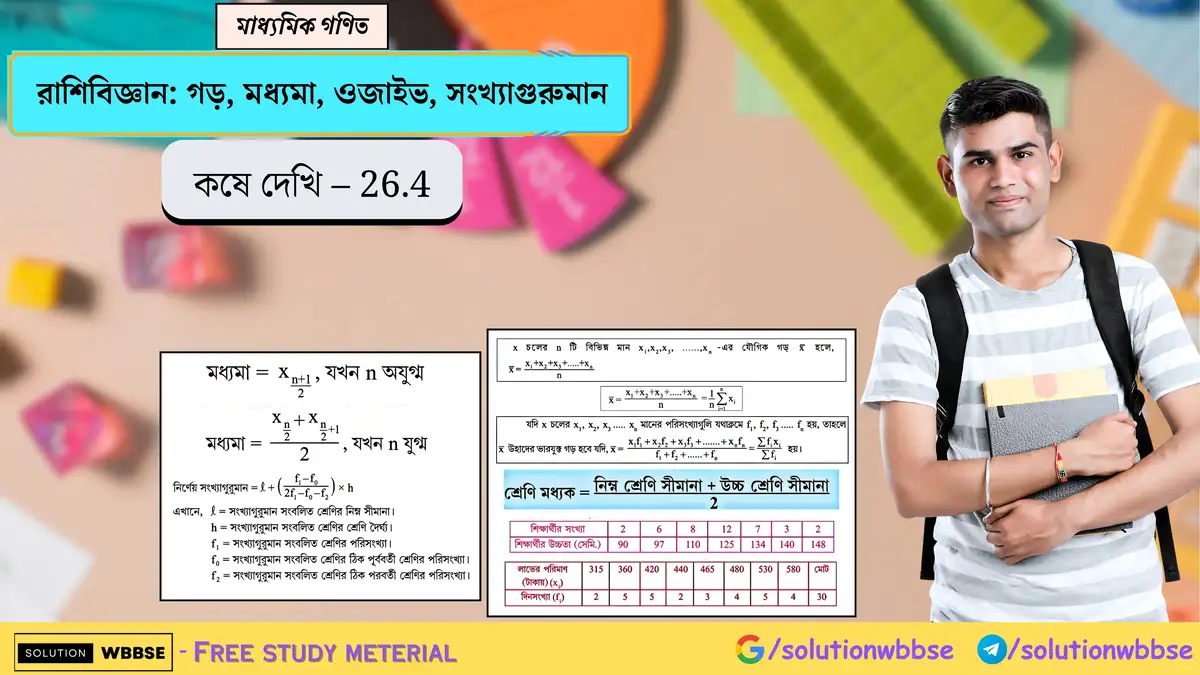
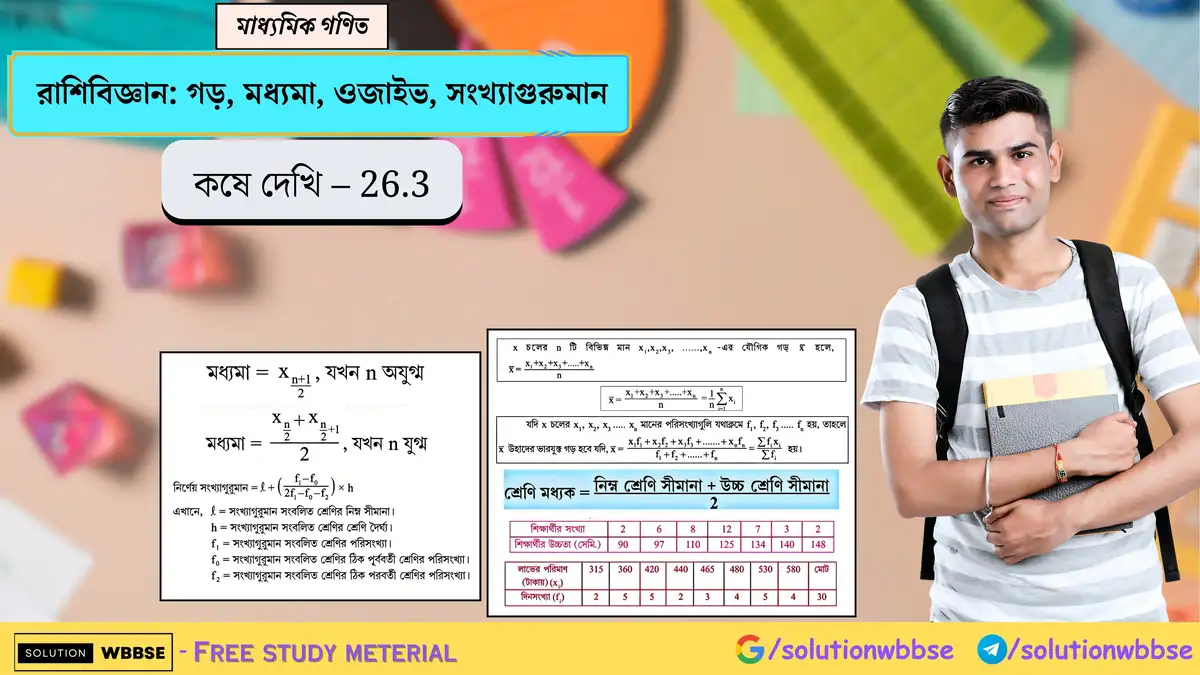
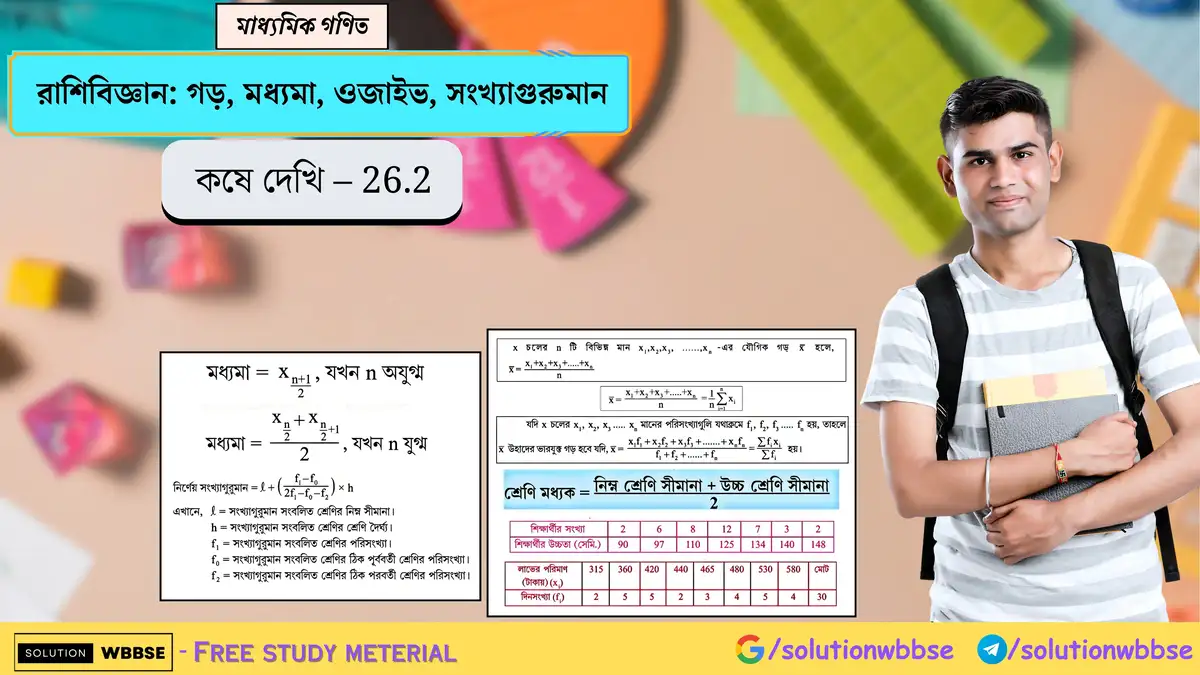

মন্তব্য করুন