নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা ভাষার বিবর্তন ও পরিবর্তনের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, ভাষা একটি জীবন্ত সত্তা, তাই তা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ আজ আর ব্যবহার হয় না। এর পরিবর্তে নতুন নতুন শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই নতুন শব্দগুলির মধ্যে কিছু সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা থেকে এসেছে।
মুজতবা আলী মনে করেন, বাংলা ভাষার বিবর্তনে এই নতুন শব্দগুলির বিশেষ অবদান রয়েছে। এই শব্দগুলি বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং এর সীমানা প্রসারিত করেছে। তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষাকে জীবিত রাখতে হলে এই নতুন শব্দগুলির ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।
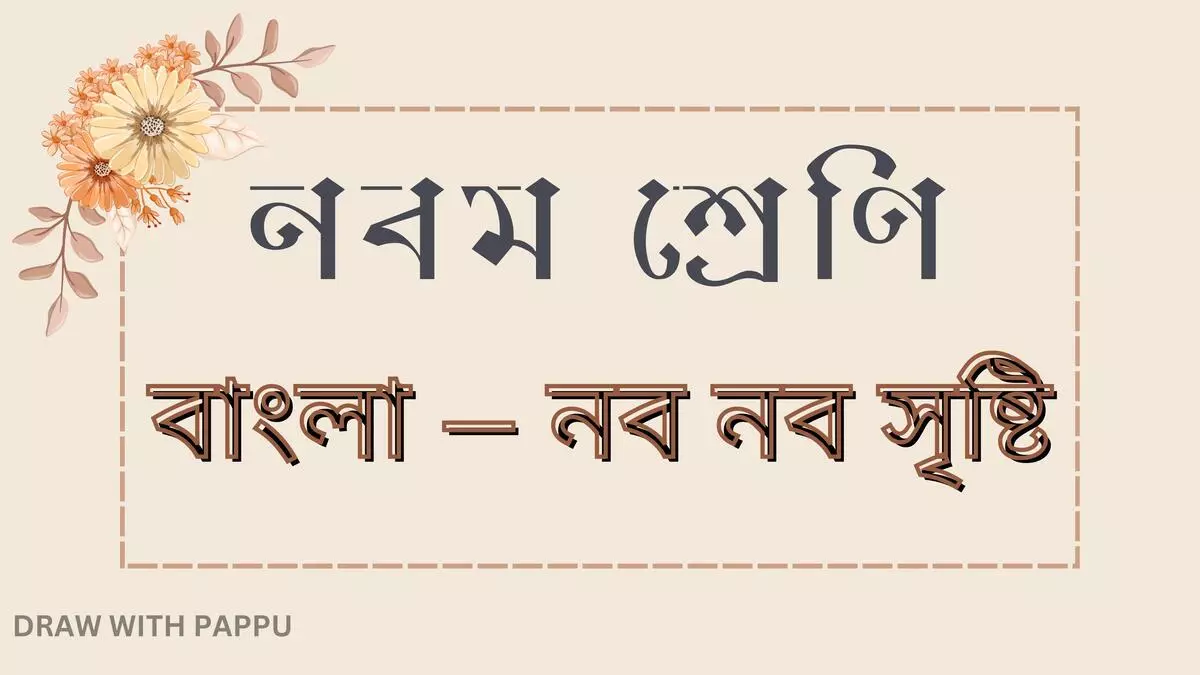
প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই। – কোন্ কোন্ ভাষার উল্লেখ করে লেখক কেন এরূপ বলেছেন? এ প্রসঙ্গে বর্তমান যুগের কোন্ দুটি ভাষা সম্পর্কে তিনি কী বলেছেন?
ভাষার উল্লেখ – সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধের আলোচ্য অংশে লেখক সংস্কৃত এবং তার সঙ্গে হিব্রু, গ্রিক, আবেস্তা এবং কিছুটা আধুনিক আরবি ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন যুগের অধিকাংশ ভাষাই নতুন চিন্তা-ভাবনা, নতুন বস্তু বোঝাতে নতুন শব্দের প্রয়োজন হলে তা নিজ শব্দভাণ্ডারের ধাতু বা শব্দ দ্বারাই তৈরি করার চেষ্টা করেছে। অন্য ভাষা থেকে ঋণ নেওয়ার কথা ভাবে না। বিদেশি শব্দ ব্যবহার করলেও তা অতিসামান্য। তাই লেখক প্রাচীন ভাষাগুলিকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেছেন।
দুটি ভাষা প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত – ভাষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা – ভাষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা – প্রসঙ্গেই লেখক বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা ভাষার উল্লেখ করেছেন। অতিরিক্ত শব্দগ্রহণ – আধুনিক কালের ভাষা ইংরেজি এবং বাংলা অন্যান্য ভাষা থেকে অতিরিক্ত শব্দ গ্রহণ করে নিজের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার ও প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে। আরবি-ফারসি শব্দের স্থানলাভ – পাঠান-মোগল যুগে এভাবেই বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ স্থানলাভ করেছে। বাংলা পরবর্তীকালে ইংরেজি থেকে এবং ইংরেজির মাধ্যমে অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করেছে। এই কারণে ইংরেজি ও বাংলা, লেখকের মতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা নয়।
বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা আত্মনির্ভরশীল নয় আত্মনির্ভরশীল ভাষা কাকে বলে? লেখকের এরকম মনে হওয়ার কারণ কী?
আত্মনির্ভরশীল ভাষা – লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর নব নব সৃষ্টি রচনায় বলেছেন যে, ভাষার আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ ভাষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা। সংস্কৃতকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে এই ভাষায় কোনো নতুন চিন্তা, অনুভূতি, কিংবা বস্তুকে বোঝানোর জন্য শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত তা নিজের ভাণ্ডারেই সন্ধান করে। প্রয়োজনে এমন কোনো ধাতু বা শব্দকে খুঁজে নিতে চায় যা সামান্য অদল-বদল করে বা পুরোনো ধাতুর সাহায্যেই একটি নতুন শব্দ নির্মাণ করে নেওয়া যায়। তাই সংস্কৃত একটি আত্মনির্ভরশীল ভাষা হয়ে উঠতে পেরেছে।
লেখকের এরকম মনে হওয়ার কারণ – ভাষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা – প্রসঙ্গেই লেখক বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা ভাষার উল্লেখ করেছেন। অতিরিক্ত শব্দগ্রহণ – আধুনিক কালের ভাষা ইংরেজি এবং বাংলা অন্যান্য ভাষা থেকে অতিরিক্ত শব্দ গ্রহণ করে নিজের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার ও প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে। আরবি-ফারসি শব্দের স্থানলাভ – পাঠান-মোগল যুগে এভাবেই বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ স্থানলাভ করেছে। বাংলা পরবর্তীকালে ইংরেজি থেকে এবং ইংরেজির মাধ্যমে অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করেছে। এই কারণে ইংরেজি ও বাংলা, লেখকের মতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা নয়।
বিদেশি শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর। মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
উৎস – আলোচ্য উদ্ধৃতাংশটি সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত নব নব সৃষ্টি রচনাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে।
তাৎপর্য – ভাষা তার নিজ শব্দভাণ্ডারের ধাতু বা শব্দ দ্বারা নতুন শব্দ তৈরি করতে পারলেই ভাষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিদেশি শব্দ গ্রহণ করলেও ভাষা অনেকসময় মধুর এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যদি সেই ভাষা বিষয়কেন্দ্রিক হয়। লেখক নিজেই বলেছেন, রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতি শব্দ অনায়াসে মিশেছে। ইংরেজি ভাষার বদলে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার ফল হাতেনাতে পাওয়া গেছে। কারণ তারপরই বাংলায় প্রচুর পরিমাণে ইউরোপীয় শব্দ ঢুকেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা বহু বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করে থাকি।
একইরকমভাবে বিদেশি শব্দও প্রবেশ করবে ভাষায়। হিন্দি ভাষাকে আরবি-ফারসি শব্দ মুক্ত করার জন্য চেষ্টা শুরু করেছেন হিন্দি ভাষার সাহিত্যিকরা। তার ফলাফল ভালো না খারাপ হবে লেখক তা ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে দিলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আনায়াসেই আরবি-ফারসি ভাষা মিশিয়ে লিখেছেন, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে। আবার নজরুল ইসলামও ইনকিলাব, শহিদ প্রভৃতি বিদেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহার করেছেন। বিষয়ের গাম্ভীর্য, আভিজাত্য এবং চটুলতার ওপর ভাষার ব্যবহার নির্ভর করে। ফলে বিদেশি শব্দের ব্যবহারও ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে যদি তা বিষয়বস্তুর যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারে।
ফল যদি ভালো হয় তখন তাঁরা না হয় চেষ্টা করে দেখবেন। — কোন্ প্রসঙ্গে লেখক এরূপ বলেছেন? বাংলা সাহিত্যিকদের নিয়ে এই প্রসঙ্গে লেখক কী বলেছেন?
প্রসঙ্গ – সৈয়দ মুজতবা আলী নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধে ভাষায় বিদেশি শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হিন্দি ভাষার সাহিত্যিকদের একটি প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেছেন। হিন্দি ভাষাকে আরবি, ফারসি, ইংরেজি শব্দ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন বেশ কিছু হিন্দি সাহিত্যিক। তাঁদের এই চেষ্টার ফল ভালো না খারাপ হবে, তা বিচার করার চেয়েও বড়ো কথা হল এই যে তাঁরা এই জাতীয় একটি চেষ্টা শুরু করেছেন।
বাংলা সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখকের অভিমত – বাংলা সাহিত্যিকরা অনায়াসেই বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে ভাষা বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক হবে এটাই মূল কথা। তাই রবীন্দ্রনাথ খুব স্বচ্ছন্দেই আরবি-ফারসি ভাষার সংমিশ্রণে লিখেছেন, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে। নজরুল ইসলামও ইনকিলাব বা শহিদ এই শব্দগুলি সহজেই তাঁর লেখায় বাংলা ভাষার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরও তাঁর চলিত ভাষায় লেখা রচনার মধ্যে আরবি- ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরবি-ফারসি শব্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাকে মূর্খামি বলে মনে করতেন।
রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
তাৎপর্য – কথামুখ – উদ্ধৃতাংশটি সৈয়দ মুজতবা আলীর নব নব সৃষ্টি পাঠ্য প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। রচনার গাম্ভীর্য, আভিজাত্য, চটুলতার সঙ্গে ভাষার ব্যবহার গভীরভাবে জড়িত।
বিদেশি ভাষার প্রয়োজনীয়তা – নতুন শব্দ তৈরি বা বিষয়ের মধ্য দিয়ে নতুন চিন্তা ও অনুভূতি ফুটিয়ে তুলতে গেলে বিদেশি ভাষার প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা বাতিল করার ফলে বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ আরও বেশি করেই প্রবেশ করেছে। তবে বিদেশি শব্দ কোনোভাবেই লেখার মাধুর্যকে নষ্ট করতে পারে না যদি তা বিষয়কেন্দ্রিক হয়। বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার – রবীন্দ্রনাথ আরবি-ফারসিকে স্বাগত জানিয়ে খুব স্বচ্ছন্দেই লিখেছেন, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে। নজরুল ইসলামও ইনকিলাব, শহিদ, প্রভৃতি শব্দ বাংলায় অনায়াসেই ব্যবহার করেছেন। শংকরদর্শন-এর আলোচনায় যে গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য রয়েছে, তা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারেই সঠিক রূপ লাভ করে।
বসুমতী পত্রিকার সম্পাদকীয় ভাষাও একইরকম গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু বাঁকা চোখে পত্রিকার ভাষায় চটুলতা তার বিষয় উপযোগী। আবার রেলের ইঞ্জিন কীভাবে চালাতে হয় বা বিজ্ঞানচর্চা ও দর্শনের বিষয় জানতে ইংরেজি ভাষার বিকল্প নেই। ইতিকথা – সুতরাং সঠিক ভাষা প্রয়োগ বিষয়বস্তুর মূলভাবকে তুলে ধরতে পারে।
বাংলায় যেসব বিদেশি ভাষার শব্দ ঢুকেছে তার মধ্যে কোন্ কোন্ ভাষাকে লেখক প্রধান বলেছেন? এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজি নিয়ে লেখক কী বলেছেন?
অথবা, বাংলা ভাষায় আগন্তুক শব্দ কোন্গুলি? প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা নিয়ে লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট করো।
লেখকের মতে বাংলায় আগত প্রধান বিদেশি ভাষাসমূহ – সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর নব নব সৃষ্টি রচনাংশে জানিয়েছেন যে বাংলায় যেসব বিদেশি শব্দ প্রবেশ করেছে সেগুলির মধ্যে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষার শব্দই প্রধান
সংস্কৃত ও ইংরেজি সম্বন্ধে লেখকের অভিমত – একসময়ে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চর্চা ছিল। কারণ সংস্কৃতই ছিল আদি ও মূল ভাষা। এখনও স্কুল-কলেজে সংস্কৃতচর্চা হয়। সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সংস্কৃত শব্দ এখনও সামান্য হলেও বাংলা ভাষায় প্রবেশ করছে। সংস্কৃত ভাষাকে বাংলার মাতৃসম ভাষাই বলা হয়, তাই সংস্কৃতচর্চা বন্ধ করে দিলে বাংলা ভাষা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। তাই লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হবো।
আধুনিক শিক্ষার ধারায় দর্শনশাস্ত্র, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার বিকল্প নেই। উদাহরণ হিসেবে লেখক বলেছেন যে রেলের ইঞ্জিন কী করে চালাতে হয়, সে বিষয়ে বাংলায় কোনো বই নেই। ফলে এই বিষয়টা বুঝতে হলে বাঙালিকে ইংরেজি ভাষারই আশ্রয় নিতে হয়। সুতরাং ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি। — এ কথা বলাই যায়।
ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি। — বক্তা কে? এরূপ উক্তির কারণ কী?
বক্তা – প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটির বক্তা নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধের লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী।
এরূপ উক্তির কারণ – নির্ভরশীল বাংলা ভাষা – বাংলা ভাষা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। আরবি-ফারসির মতোই ইংরেজির থেকেও আমরা প্রচুর শব্দ নিয়েছি। ভাষাকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য অন্য ভাষাকে ত্যাগ করার চেষ্টা একেবারে বিরল ঘটনা নয়। হিন্দিতে এ চেষ্টা হয়েছে। আবার বিখ্যাত লেখকদেরও দেখা গিয়েছে যে, তাঁরা অন্য পথে হেঁটেছেন। বাংলা ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর উদাহরণ। লেখক দেখিয়েছেন যে বাংলা ভাষায় যে শব্দসমূহ এসেছে তার মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি প্রধান। এক্ষেত্রে ইংরেজির ভূমিকা কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়। প্রয়োজনীয় বাংলা শব্দের অভাব – দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থ কিংবা রাসায়নবিদ্যা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ বাংলায় যথেষ্ট নেই। রেল ইঞ্জিন চালানোর প্রযুক্তি বিষয়ে বাংলায় কোনো বই নেই। এখানে ইংরেজির উপরে নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এইসব কারণেই লেখকের মনে হয়েছে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য ইংরেজির চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি।
লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী একবার বলেছেন আরবি- ফারসি ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নূতন শব্দ বাংলাতে ঢুকবে না, আবার একবার বলেছেন অচলিত অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ নূতন মেয়াদ পাবে। — এই দুই উক্তির কারণ বুঝিয়ে দাও৷
অথবা, বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করো।
প্রথম উক্তির কারণ – ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রবেশ এবং তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনায় লেখক বলেছেন যে বাংলা ভাষায় যেসব বিদেশি শব্দ প্রবেশ করেছে সেগুলির মধ্যে প্রধান হল আরবি এবং ফারসি। তবে আরবি এবং ফারসি—এই দুটি ভাষার প্রতি তরুণ বাঙালি সম্প্রদায় বর্তমানে ক্রমশ আগ্রহ হারাচ্ছে। এর ফলে এই দুই ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নতুন শব্দ বাংলাতে ঢুকবে না। তা ছাড়া, আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ফলে এই ভাষা দুটির বাংলাকে প্রভাবিত করতে পারার সম্ভাবনাও খুব ক্ষীণ ।
দ্বিতীয় উক্তির কারণ – বাংলা ভাষা প্রাচীন কাল থেকেই আরবি-ফারসি শব্দ ব্যাপক পরিমাণে গ্রহণ করেছে। আর এইসব শব্দ যে বহুদিন বাংলায় প্রচলিত থাকবে সে-বিষয়ে লেখক নিঃসন্দেহ। তা ছাড়া, মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল থেকে শুরু করে হুতোম প্যাঁচার নক্শা পর্যন্ত যেসব আরবি- ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে নতুন লেখক সম্প্রদায় সেগুলিকে নতুন করে খুঁজে আবার সাহিত্যে প্রয়োগের চেষ্টা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে প্রাচীন বাংলা পড়ার কারণেই অচলিত অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ নতুন মেয়াদ পাবে।
ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না। – নব নব সৃষ্টি রচনা অবলম্বনে এই উক্তির সত্যতা বিচার করো।
সত্যতা বিচার – কথামুখ – প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি বাঙালির চিরকালীন পক্ষপাতের কথা বলেছেন। রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য—বাঙালি যেখানে যখনই সত্য-শিব-সুন্দরের খোঁজ পেয়েছে তখনই তা সাদরে গ্রহণ করতে চেয়েছে।
বাঙালির চিরন্তন ধারণা – কেউ গতানুগতিকতা বা প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে তাতে বাধা দিতে গেলে বাঙালি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আবার সেই বিদ্রোহই যদি উচ্ছৃঙ্খলতা বা নৈরাজ্যের দিকে যায় তখন বাঙালি তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছে। অর্থাৎ সত্য-শিব- সুন্দরের ধারণাকে বাঙালি চিরন্তন বলে গ্রহণ করেছে। বাঙালি জাতিসত্তা – লেখক লক্ষ করেছেন যে এই রুচি বা জীবনাদর্শকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে হিন্দু বা মুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর এই বিদ্রোহে বাঙালি মুসলমানরাও যোগ দিয়েছে। তার কারণ ধর্ম গেলেও জাতিস বদলে গেলেও জাতিসত্তা একই থেকে যায়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি সমগ্র বাঙালি জাতিরই, কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নয়। লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, ধর্ম বদলালে জাতির চরিত্র বদলায় না। বাঙালি মুসলমানরাও বাঙালি জাতিসত্তারই অংশ। তার ধর্ম আলাদা হলেও এদেশের জল হাওয়াতেই তার চেতনা ও জীবনাদর্শের বিকাশ।
শেষের কথা; তাই ধর্ম বদলে যেতে গেলেও মনোভাবের কোনো বদল বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ঘটেনি।
বাংলা ভাষা একটি সমৃদ্ধ ভাষা। এর বিবর্তন ও পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা উচিত নয়। বরং, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও বিকশিত করা সম্ভব।

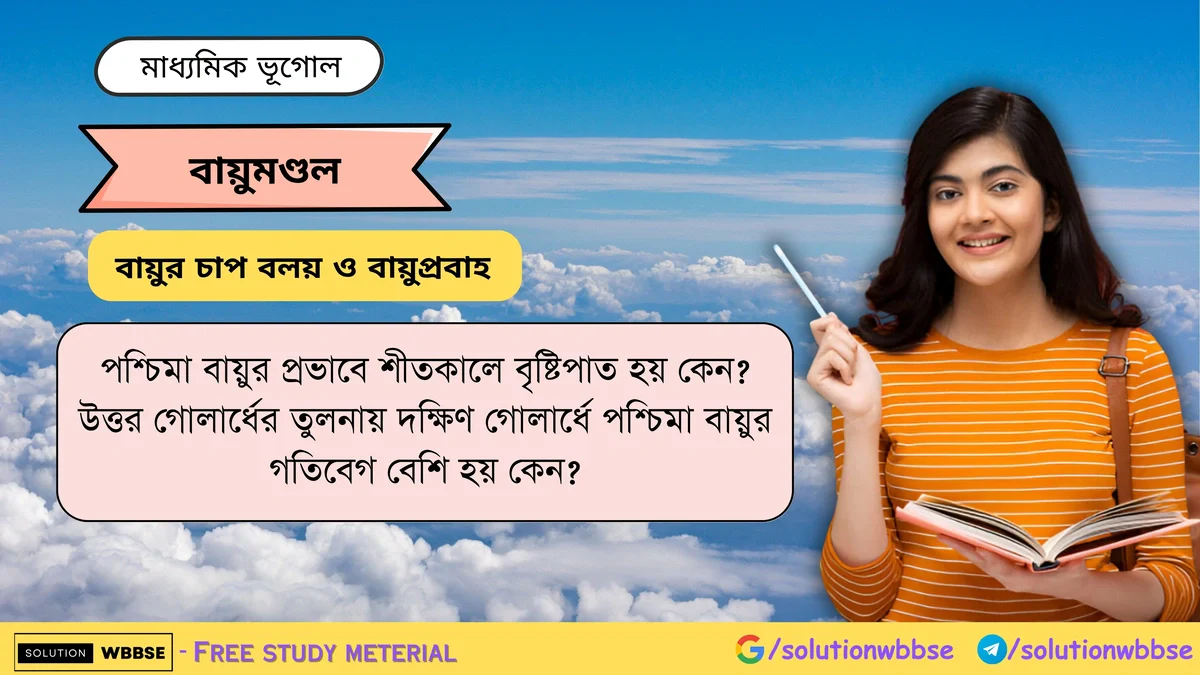
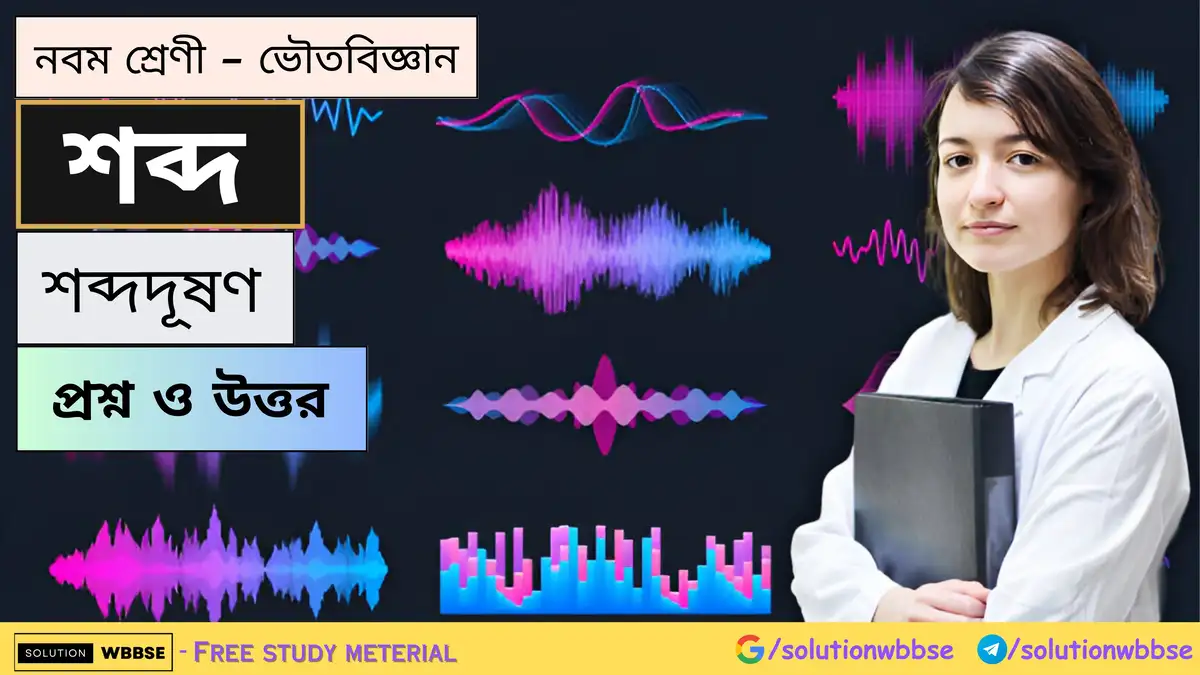
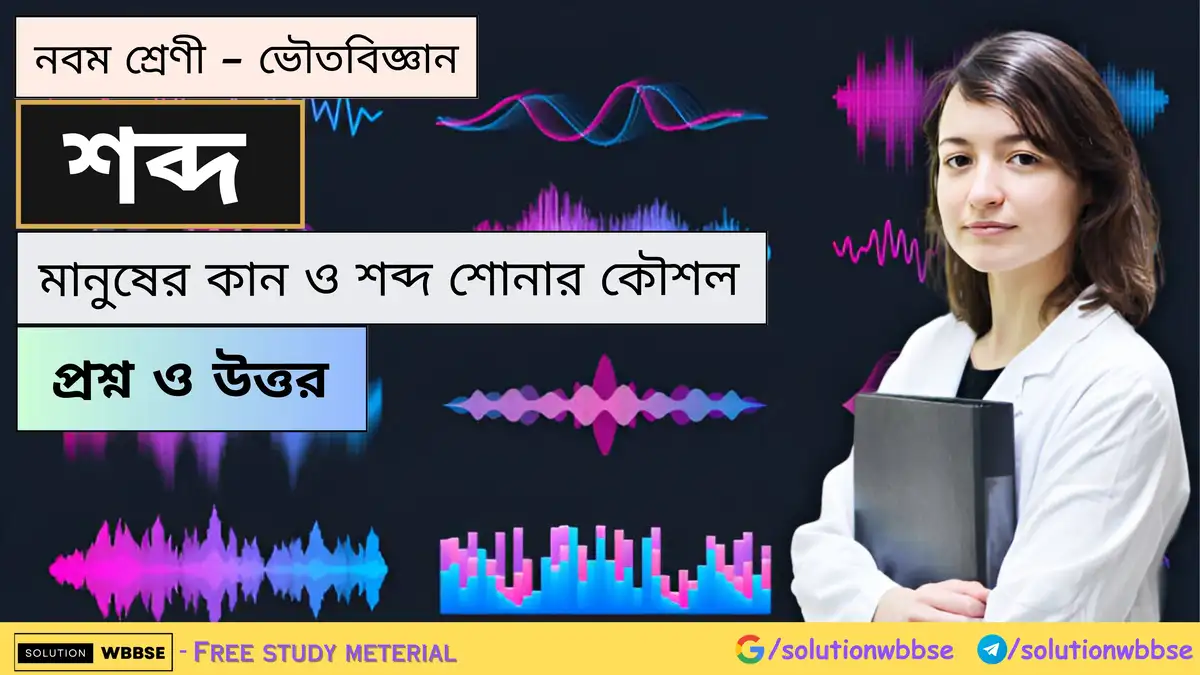
মন্তব্য করুন