আজকের এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের দ্বিতীয় পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘নব নব সৃষ্টি’ -এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নোত্তরগুলো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নবম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত আসে।
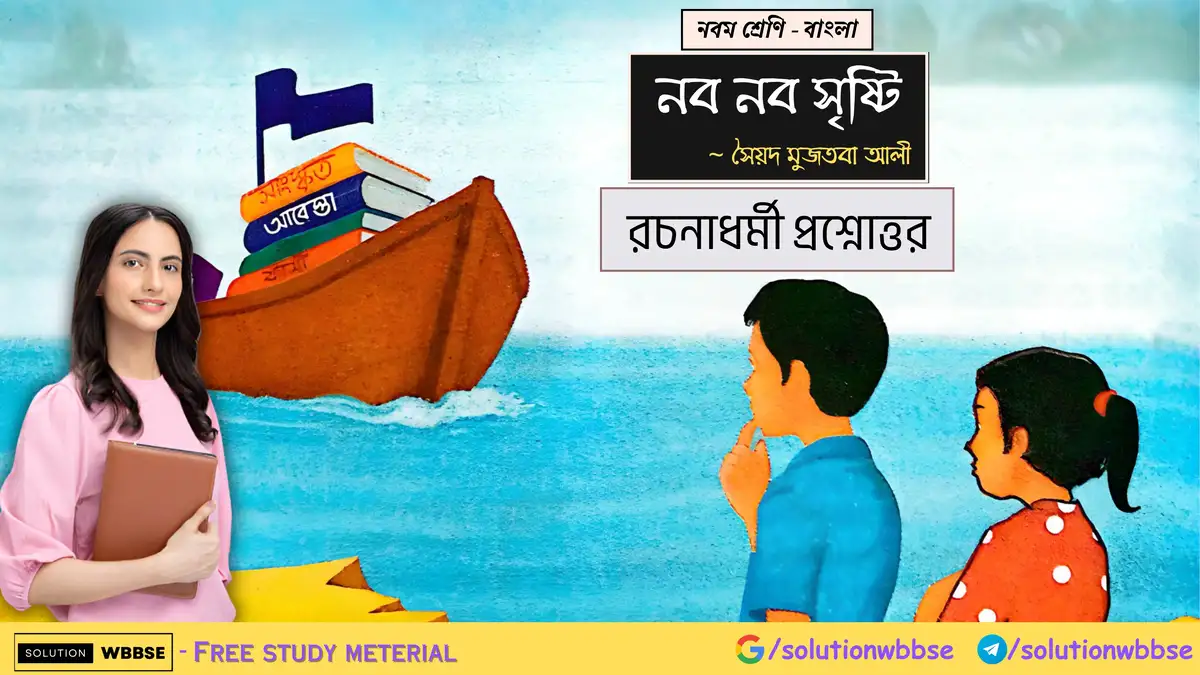
‘নব নব সৃষ্টি’ রচনাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।
ভূমিকা – সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনায় বিশিষ্ট ভাষাবিদ লেখক বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার এবং অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার তুলনা উপস্থিত করেছেন। বাঙালি জাতি ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন তিনি এই প্রবন্ধে।
বাংলা ভাষা পরনির্ভরশীল – ‘সৃষ্টি’ (সৃজ্ + তি) শব্দটির অর্থ নির্মাণ, রচনাপ্রণয়ন, উৎপাদন ইত্যাদি। নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য চাই মৌলিকতা, উন্মেষশালিনী শক্তি। পাঠ্য রচনায় বাংলা ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন বাংলা ভাষা সৃজনক্ষম মধুর ভাষা। কিন্তু তার একটি দুর্বলতা বিদ্যমান। দুর্বলতা এই যে, সে আত্মনির্ভরশীল বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা নয়। ফলে আত্মপ্রয়োজনে তাকে বিদেশি শব্দ ঋণ করতে হয়। পৃথিবীর যে-কোনো ভাষাই নব নব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ আত্মপ্রকাশের জন্য চাই নতুন শব্দ। সে শব্দ প্রয়োজনে ধার করতেও দ্বিধা নেই। কারণ আত্মপ্রকাশ ও সৃষ্টি ছাড়া ভাষা অবলুপ্ত হয়ে যায়।
বাংলায় গৃহীত নতুন শব্দাবলি – ভাষার সজীবতার জন্য চাই নব নব সৃষ্টি আর সৃষ্টির জন্য চাই নিত্যনতুন শব্দাবলি। বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা ও অন্যান্য ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তাই নানা ভাষার নানা শব্দ গৃহীত হয়। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সৃজনে সেইসব শব্দের ঝংকার শ্রুত হয়।
উপসংহার – সৃষ্টি কেবল সজীবতা বা সৌন্দর্যই প্রমাণ করে না, সৃষ্টির অর্থ প্রাণবান, বেগবান থাকাও। নব নব সৃষ্টি একটা ভাষার প্রবাহকে লাবণ্য দেয়, সমৃদ্ধ করে, নবীন ও জীবন্ত করে তোলে। সেই নব নব সৃষ্টির নবীনতায় ভাষার প্রবাহ লাবণ্যময় ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠায় ব্যঞ্জনধর্মী নামকরণ হিসেবে আলোচ্য রচনাংশের নামকরণটি সার্থক ও শিল্পশ্রীমণ্ডিত হয়েছে।
‘নব নব সৃষ্টি’ রচনাটি কী ধরনের রচনা তা যুক্তিসহ লেখো।
ভূমিকা – ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনাটি একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। এ রচনায় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী ভাষা, শব্দ, জাতি, সংস্কৃতির আলোচনা; প্রাসঙ্গিক তথ্যদান এবং তুলনা করে নিজের বক্তব্য বিস্তৃত করেছেন।
প্রবন্ধ কী? – প্রবন্ধ শব্দের অর্থ হল প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধ যে সাহিত্য প্রকরণে একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সংহত রূপে আলোচনা করা হয়, তাকে প্রবন্ধ বলে।
মূল বিষয় – প্রথমেই তিনি ভাষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ভাষায় শব্দের প্রয়োজনীয়তা এবং বিদেশি শব্দগ্রহণের কারণ, বাধ্যতা ইত্যাদির কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষাগুলির সঙ্গে আত্মনির্ভর নয় এমন ভাষাগুলির প্রভেদ। বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের ঋণ, ঋণগ্রহণের কারণ, ঋণগ্রহণের বাধ্যতা নিয়েও তিনি সুললিত আলোচনা করেছেন এই প্রবন্ধে। আরবি-ফারসি শব্দ এবং বাংলাও ভারতীয়অন্যান্য ভাষার সম্পর্ক, ভাষায় শব্দের ঋণমুক্তির প্রচেষ্টাও তার আলোচনার বিষয়।
উপসংহার – সার্বিক বিচারে তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ এ রচনাটি একটি সার্থক বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে। আবার বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালির স্বভাবধর্মের প্রকাশে এ প্রবন্ধ বস্তুনিষ্ঠাকে ছাপিয়ে ব্যাখ্যানধর্মী হয়ে উঠেছে কখনো-কখনো। তবে তুল্যমূল্য বিচারে সামগ্রিক দিক থেকে এ প্রবন্ধকে একটি সার্থক বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলাই শ্রেয়।
বাংলা ভাষার সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে? একে আত্মনির্ভরশীল ভাষা বলা চলে কি?
অথবা, “বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা আত্মনির্ভরশীল নয়।” – ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কীভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন?
বাংলা ভাষার সৃষ্টি – ভারতীয় আর্যভাষার স্তর বিবর্তনে বাংলা ভাষার সৃষ্টি। বাংলা ভাষার বর্তমান বয়স হাজার বছরেও বেশি। আনুমানিক 900-1000 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ট ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। নব্য ভারতীয় আর্যভাষার অঙ্গ এবং ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা হল বাংলা। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন ‘চর্যাচযবিনিশ্চয়’ বা ‘চর্যাপদ’।
বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার – ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্যান্য ভাষা, অনার্য ভাষাগোষ্ঠী, বিদেশি বিভিন্ন ভাষার শব্দ নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার। বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-সুনীতি কুমার-হরপ্রসাদ প্রমুখের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা বাংলা ভাষা আজ ইউনেসকোর মতে বিশ্বের মধুরতম ভাষা।
বাংলা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয় – প্রাবন্ধিক, ভাষাবিদ, সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষা সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত, মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি সঠিক বিশ্লেষণে বাংলাভাষাকে পরনির্ভরশীল ভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। পৃথিবীর যেকোনো ভাষাই সজীব ও প্রাণবন্ত। ভাষাও নদীর মতো প্রবহমান। নব নব সৃষ্টিতেই লুকিয়ে থাকে ভাষার প্রাণ শব্দ। ভাষা যখন কোনো নতুন চিন্তা-অনুভূতি বা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজনে নিজের শব্দভাণ্ডারে রসদ পায় কিংবা নিজের শব্দভাণ্ডারে থাকা ধাতু বা শব্দকে অদলবদল করে প্রয়োজনীয় শব্দটিকে গড়ে নেয় তখন সে ভাষা আত্মনির্ভরশীল ভাষার আখ্যা পায়। সংস্কৃত ভাষা তা করতে সক্ষম, তাই সে আত্মনির্ভরশীল। বাংলাভাষার চাহিদা মেটাতে বাংলা শব্দভাণ্ডার সক্ষম নয়। ফলে তাকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বিদেশি ভাষা থেকে শব্দঋণ করতে হয়। নিজের প্রয়োজন নিজে মেটাতে পারে না বলেই বাংলাভাষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল ভাষা বলা যায় না।
লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী সংস্কৃত ভাষাকে ‘আত্মনির্ভরশীল’ বলেছেন কেন? বর্তমান যুগে ইংরেজি ও বাংলা ভাষা আত্মনির্ভরশীল নয় কেন?
বাংলা ভাষার সৃষ্টি – ভারতীয় আর্যভাষার স্তর বিবর্তনে বাংলা ভাষার সৃষ্টি। বাংলা ভাষার বর্তমান বয়স হাজার বছরেও বেশি। আনুমানিক 900-1000 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ট ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। নব্য ভারতীয় আর্যভাষার অঙ্গ এবং ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা হল বাংলা। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন ‘চর্যাচযবিনিশ্চয়’ বা ‘চর্যাপদ’।
বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার – ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্যান্য ভাষা, অনার্য ভাষাগোষ্ঠী, বিদেশি বিভিন্ন ভাষার শব্দ নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার। বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-সুনীতি কুমার-হরপ্রসাদ প্রমুখের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা বাংলা ভাষা আজ ইউনেসকোর মতে বিশ্বের মধুরতম ভাষা।
বাংলা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয় – প্রাবন্ধিক, ভাষাবিদ, সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষা সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত, মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তিনি সঠিক বিশ্লেষণে বাংলাভাষাকে পরনির্ভরশীল ভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। পৃথিবীর যেকোনো ভাষাই সজীব ও প্রাণবন্ত। ভাষাও নদীর মতো প্রবহমান। নব নব সৃষ্টিতেই লুকিয়ে থাকে ভাষার প্রাণ শব্দ। ভাষা যখন কোনো নতুন চিন্তা-অনুভূতি বা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজনে নিজের শব্দভাণ্ডারে রসদ পায় কিংবা নিজের শব্দভাণ্ডারে থাকা ধাতু বা শব্দকে অদলবদল করে প্রয়োজনীয় শব্দটিকে গড়ে নেয় তখন সে ভাষা আত্মনির্ভরশীল ভাষার আখ্যা পায়। সংস্কৃত ভাষা তা করতে সক্ষম, তাই সে আত্মনির্ভরশীল। বাংলাভাষার চাহিদা মেটাতে বাংলা শব্দভাণ্ডার সক্ষম নয়। ফলে তাকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বিদেশি ভাষা থেকে শব্দঋণ করতে হয়। নিজের প্রয়োজন নিজে মেটাতে পারে না বলেই বাংলাভাষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল ভাষা বলা যায় না।
বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখো।
আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব – বাংলা ভাষা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। তাই নিজের চিন্তাচেতনা, অনুভূতি কিংবা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজনে আপন ভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় শব্দ সে সবসময় পায় না। এজন্য বাংলা ভাষা অন্য ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দের সাহায্যে আত্মপ্রয়োজন মেটায়। মোগল-পাঠান যুগে শাসনকার্য পরিচালনা ও রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় ‘আইন-আদালত’, ‘খাজনা-খারিজ’ ইত্যাদি প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ প্রবেশ করে। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন রচনায় চলে আসে এসব শব্দের ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘আব্রু দিয়ে’, ‘ইজজৎ দিয়ে’, ‘ইমান দিয়ে’, ‘বুকের রক্ত দিয়ে’। ‘ইনকিলাব’, ‘শহিদ’ -এর মতো অজস্র শব্দ ব্যবহার করলেন নজরুল। বিদ্যাসাগরের ছদ্মনামের রচনায় এবং অন্যান্য বাংলা গদ্য ও পদ্যে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হত। আজও তা হয়ে চলেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন আরবি-ফারসি শব্দের প্রবেশ বাংলায় কম পরিমাণে হলেও প্রাচীন থেকে গৃহীত শব্দগুলি এখনও সমমর্যাদায় ব্যবহৃত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরবি ও ফারসি শব্দের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ‘আহাম্মুখী’ বলে মনে করতেন।
লেখকের অভিমত – বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের এই প্রচলন এবং প্রয়োগ বহুকাল চালু থাকবে বলে লেখকের অভিমত। আজ নতুন লেখকরা এ শব্দ ব্যবহার-বর্জন করলেও প্রাচীন সাহিত্যে তা থেকে যাবে। প্রাচীন সাহিত্যগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়ায় নবযুগেও তাদের পরিচিতি ঘটবে। এভাবেই আরবি-ফারসি শব্দের মেয়াদ বাংলা ভাষায় বৃদ্ধি পাবে। এই পরিস্থিতির সামনে জীবন্মৃত আরবি-ফারসি শব্দগুলির নতুন খতিয়ান নেওয়া দরকার বলে লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী সংগতভাবেই তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনায় মন্তব্য করেছেন।
বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ও ইংরেজি শব্দের প্রভাব কতখানি?
অথবা, বাংলায় সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার চর্চা এখনও প্রয়োজন বলে লেখক মনে করেন কেন?
অথবা, “বাংলাতে এখনও আমাদের বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন … ইংরেজির বেলাতেও তাই” – এখনও প্রয়োজন বলে কেন লেখক মনে করেন?
ভূমিকা – ভাষাবিদ, প্রাবন্ধিক, সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা উপস্থিত করেছেন। বাংলা ভাষা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। ফলত বাংলার ভাষাপ্রবাহকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ভিনদেশি ভাষার সাহায্য বাংলাকে নিতে হয়েছে। বাঙালিরা বাংলা ছাড়া যে ভাষার চর্চা করেছে সেই ভাষার শব্দ বাংলার শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে।
সংস্কৃত প্রভাব – সংস্কৃত ভাষার চর্চা দীর্ঘকাল এদেশে ছিল বলে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ঢুকেছে। এবিষয়ে লেখক বলেছেন – এখনও ঢুকছে, যতদিন থাকবে ততদিনই – “আরও ঢুকবে বলে আশা করতে পারি।” বাংলা শব্দভাণ্ডারে তাই তৎসম, অর্ধতৎসম শব্দের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বস্তুত বাংলা ভাষার গড়ে ওঠা প্রতিমাটির কাঠামো আজও সংস্কৃত। তাই স্কুল কলেজ থেকে আজও সংস্কৃত চর্চা ওঠানো যায় না। প্রাবন্ধিক যথার্থ বলেছেন – “সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিলে আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।”
ইংরেজি প্রভাব – একই কথা আধুনিক ভারতে ইংরেজি ভাষার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বাংলা ভাষা গঠনে ইংরেজির প্রভাব নেই। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সংযোগে ইংরেজিই প্রধান মাধ্যম। তাই দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা চর্চায়, জ্ঞানার্জনে এবং প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের শব্দ পেতে ইংরেজিই ভরসা। টেকনিক্যাল শব্দের সুস্পষ্ট ধারণা, বাংলাভাষায় না থাকায় ইংরেজি চর্চা বন্ধের সময় বাংলাভাষায় আজও আসেনি।
বাংলা ভাষায় প্রধান আগন্তুক শব্দ কোনগুলি? অপ্রধান আগন্তুক শব্দই বা কোনগুলি? বাংলাভাষার আগন্তুক শব্দগুলি সম্পর্কে লেখকের ভাবনাচিন্তার পরিচয় দাও।
প্রধান আগন্তুক শব্দ – সৈয়দ মুজতবা আলী ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে বাংলাভাষায় আগন্তুক শব্দ বলতে বিদেশি শব্দগুলোকে বুঝিয়েছেন। তদনুযায়ী বাংলা ভাষায় প্রধান আগন্তুক শব্দ আরবি, ফারসি ও ইংরেজি।
বাংলা ভাষায় অপ্রধান আগন্তুক শব্দ পোর্তুগিজ, ফরাসি, স্প্যানিশ। বর্তমান বাংলা ভাষায় অপ্রধান আগন্তুক শব্দগুলোর প্রবেশ ও প্রভাব এতই কম যে সেগুলো নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সংস্কৃতর মতো ইংরেজিও আজ বাংলাভাষা অন্যতম প্রধান খাদ্য।
আগন্তুক শব্দ সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা – বাংলা ভাষা গড়ন-গঠনে ইংরেজির প্রভাব নেই। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সংযোগে ইংরেজিই প্রধান মাধ্যম। তাই দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা চর্চায়, জ্ঞানার্জনে এবং প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের শব্দ পেতে ইংরেজিই ভরসা। টেকনিক্যাল শব্দের সুস্পষ্ট ধারণা বাংলা ভাষায় না থাকায় ইংরেজি চর্চা বন্ধের সময় বাংলা ভাষায় আজও আসেনি।
বর্তমান বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দগুলোর প্রভাব অনেক কম। এককালে সম্পর্ক ও শাসনসূত্রে এদের চর্চা প্রবল ছিল। বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইত্যাদি সবাই এদের বহুল প্রয়োগ করেছেন দ্বিধাহীনভাবে। আজ দুই বাংলায় আরবি-ফারসির চর্চা ক্ষীণ। আগামীতে প্রবল হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্য রচনাসূত্রে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকমহলে এসব শব্দের সামান্য চর্চা আছে। তাই জীবন্মৃত এসব শব্দের নতুন করে আলোচনা করা প্রয়োজন।
‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধের অনুসরণ করে বাঙালির শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করো।
বহুভাষাজ্ঞ, বিশিষ্ট রচনাকার সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে বলেছেন –
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য – “বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলি কীর্তনে।” পদাবলি পদসমুচ্চয় বা পদের সংকলন। পদাবলি কীর্তন হল বৈষ্ণবপদাবলী। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ধারা পদাবলি কীর্তন। বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণ এবং বৈকুণ্ঠের দেবী লক্ষ্মীর মানবীরূপ শ্রীরাধিকার মানসসম্পর্কের আধানে এই পদাবলি ধারার সৃজন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবির সৃজিত অসামান্য সমস্ত পদ ও সাহিত্যের রত্নসম্ভার। প্রাবন্ধিক যথার্থই বলেছেন –
এ সাহিত্যের প্রাণ ও দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালি। পদাবলি কীর্তন বাঙালির নিত্যকার জীবনের ভাবে ভাষায় সমৃদ্ধ। বাঙালির অন্তরসৌন্দর্যে রূপবান। মহাভারতের কৃষ্ণ এ কাব্যে কানুরূপ ধারণ করেছেন। শ্রীমতী রাধিকা বাঙালির ঘরের কন্যা। বাঙালির ভক্তিরসাশ্রিত, ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুরশিদিয়ার আশিক পদাবলির রাধা একই চরিত্র, একইরূপে প্রকাশ পেয়েছে।
বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখো।
বাংলা ভাষা – ভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিবর্তনে বাংলা ভাষার সৃষ্টি। বাংলাভাষার বর্তমান বয়স হাজার বছরেরও বেশি। আনুমানিক 900-1000 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ট ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। বাংলা ভাষা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার অঙ্গ এবং ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান বিশ্বের মধুরতম ভাষা বলে স্বীকৃত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’।
বাঙালি জাতি সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলী ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে সামান্যই তথ্য দিয়েছেন। বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে ডঃ অতুল সুর জানিয়েছিলেন –
“বাংলার জাতিসমূহ যে মাত্র নানাজাতির রক্তের মিশ্রণের ফল তা নয়, পুনর্মিশ্রণের ফল।” (বিচিত্রবিদ্যা গ্রন্থমালা)
বাঙালি জাতি – প্রোটো অস্ট্রেলিয় বা আদি-অস্ত্রাল গোষ্ঠীর লোকেরাই বাংলার আদিম অধিবাসী। অস্ট্রিক ভাষা প্রচুর ব্যবহার করত তারা। যা আজ ‘দেশি’ শব্দ নামে খ্যাত। ক্রমে দ্রাবিড়, আলপীয় ইত্যাদির মিশ্রণে বাঙালি এক সংকর জাতিতে পরিণত হয়েছে। বাঙালির ভাষা বাংলাও আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়।
বাঙালির সহনশীল মন, উদার দৃষ্টি। তাই অন্যভাষা এবং সংস্কৃতির ভালোটুকু সে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে। লেখক বলেছেন বিদেশি খাদ্য, বিদেশি ঔষধ বাঙালির নিত্যসঙ্গী। আগামীতেও তা জীবনযাপনের অঙ্গ থাকবে। বাঙালি চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যামান। রাজনীতি-ধর্ম-সাহিত্য-সবেতেই বাঙালি সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানী। সে সন্ধানের গতানুগতিকতা বা প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে বাঁধা দিতে গেলে বাঙালি বিদ্রোহ করে। সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় রূপান্তরিত হলে তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করে। বাঙালি হিন্দু বা বাঙালি মুসলমান সকলেই এই চারিত্র্যধর্ম বজায় রাখে। বাঙালি আবেগপ্রবণ। ভক্তিরসাশ্রিত মানসে ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুরশিদিয়ার আশিক এবং পদাবলির রাধাকে সে একাকার করে নিয়েছে।
বাঙালি জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কীভাবে বাংলা সাহিত্য উপকৃত হয়েছে তা সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধটি অবলম্বনে আলোচনা করো।
অথবা, “বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি তার পদাবলি কীর্তনে” – প্রাবন্ধিকের এমন মন্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত বাঙালি জাতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
বাঙালি জাতি ও বাংলা সাহিত্য – সাহিত্য সমাজের দর্পণ। বাঙালি জাতির কিছু সুনির্দিষ্ট চরিত্রধর্মের আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে পাঠ্য সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনায়। বাঙালির অন্যতম গুণ পরকে আপন করা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরভাষার শব্দ গ্রহণ করে আপন ভাষাকে মাধুর্যময় করে তুলেছে। বাঙালির উদার মানসিকতা, উন্মুক্ত মন। তাই বাঙালি সাহিত্যিকরাও আব্রু, ইজজৎ, ইমান, ইনকিলাব, শহিদ ইত্যাদি বিদেশি শব্দ দিয়ে মাতৃভাষার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আবার মানসিক ঔদার্য দিয়ে তারা মহাভারতের কৃষ্ণকে কানু করে নিয়েছেন। শ্রীমতী রাধাও হয়ে উঠেছেন একেবারে বাঙালি মেয়ে ‘দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।’ এ চিন্তা বাঙালির একান্ত মনোবাসনার প্রকাশ। তাই তো আরাধ্যা রাধাও কখনও ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুরশিদিয়ার আশিক হয়ে ওঠে। আবার বাঙালি স্বভাবত বিদ্রোহী। তার এই মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে তার সাহিত্যেও। বাঙালির সাহিত্যও সত্য-শিব-সুন্দরকে সন্ধান করে চলেছে। উপনিষদ থেকে শুরু করে আজও সেই শাশ্বতর প্রতিই বাঙালির জীবন ও সাহিত্যের লক্ষ্য ও প্রকাশ। আধুনিক বাঙালি আরবি-ফারসি ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত। তেমনই আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এই দুই ভাষার শব্দ ব্যবহার কম। এভাবেই বাঙালি জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যকে উপকৃত করেছে আদর্শে-প্রকাশে-নিজস্বতায়।
“বিদেশি শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর।” – মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
অথবা, ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনাংশে লেখকের বিদেশি শব্দ ব্যবহারের ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করো।
আলোচ্য উদ্ধৃতিটি প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধের অন্তর্গত।
তাৎপর্য – ভাষা সজীব এবং প্রাণবন্ত। অস্তিত্বরক্ষার জন্য তার প্রয়োজন হয় নিত্যনতুন শব্দ। চিন্তাভাবনা অনুভূতি বা ভাবপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন শব্দ নিজের শব্দভাণ্ডারের সাহায্যে গঠন করে নিতে পারা ভাষা আত্মনির্ভরশীল বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা। স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলে আত্মপ্রয়োজন মেটাতে ভাষাকে বিদেশি শব্দ অনুসন্ধান করতে হয়। বিদেশি শব্দ গ্রহণ করা কেবলমাত্র ভাষার প্রয়োজন মেটানোর জন্যই নয়। লেখক বলেছেন রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে। বিষয় প্রকাশের তাগিদেও বিদেশি শব্দ গৃহীত হয় ভাষায়। আবার জীবনযাত্রার প্রাত্যহিকতায় বিদেশি সংস্পর্শ খাদ্য থেকে ভাষা সবেতেই বিদেশি শব্দের প্রবেশ ঘটায়। ভাষার মুখ্য কাজ মনের ভাব প্রকাশ। ভাষা মানুষের আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের মাধ্যম। এদিক থেকে বিচারে শব্দ ব্যবহার গৌণ ভাষা প্রকাশই, সাহিত্য রচনাই মুখ্য। তাই তো রবীন্দ্র-নজরুল বিদ্যাসাগর সকলেই বিদেশি শব্দ ব্যবহারে দ্বিধাহীন ছিলেন। এ কথা বোঝাতেই লেখক উক্ত মন্তব্যটি করেছেন।
“ফল যদি ভালো হয় তখন তাঁরা না হয় চেষ্টা করে দেখবেন।” – কোন্ প্রসঙ্গে লেখক এ কথা বলেছেন? এই প্রসঙ্গে লেখক বাংলা সাহিত্যিকদের নিয়ে কী বলেছেন?
প্রসঙ্গ – নদীর মতো প্রবহমানতাই সজীব প্রাণবন্ত ভাষার ধর্ম। প্রবাহিত ভাষা নিজেকে নানা রকমভাবে পরিমার্জনা করে সজীব থাকে। নব্যভারতীয় আর্যভাষা স্তরে উদ্ভূত হিন্দিভাষা আত্মনির্ভরশীল নয়। ফলত প্রয়োজন মেটাতে নানা বিদেশি শব্দ সে ঋণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে হিন্দিভাষার সাহিত্যিকরা – “হিন্দি থেকে আরবি, ফার্সি এবং ইংরেজি শব্দ তাড়িয়ে দেবার জন্য” এক অভিনব প্রচেষ্টা করেছেন। এই অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টার ফল আপাতত বোঝা না গেলেও লেখক বলেছেন সুদূর প্রসারী একাজের ফললাভের সময় তিনি জীবিত থাকবেন না। তাই এর পরিণাম যদি উত্তম হয় তখন তরুণ পাঠকরা বাংলা ভাষাতেও এ প্রচেষ্টা করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে লেখক উক্ত মন্তব্যটি করেছেন।
বাংলা সাহিত্যিক – এই কথার সূত্রে লেখক জানিয়েছেন বাংলা ভাষার সাহিত্যিকরা বিদেশি শব্দ ব্যবহারে সাবলীল ছিলেন। রচনার বিষয়বস্তুর উপর ভাষা নির্ভরশীল। তাই বিদ্যাসাগর ‘সাধু’ রচনায় বিদেশি শব্দ ব্যবহার করতেন না কিন্তু ‘অসাধু’ রচনায় চুটিয়ে বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে লিখেছেন ‘আব্রু’ ‘ইজজৎ’ ‘ইমান’ নজরুল ‘ইনকিলাব’ এবং ‘শহিদের’ মতো অজস্র শব্দ বাংলায় এনেছেন। অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরবি-ফারসির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ‘আহাম্মকী’ ভাবতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বিশেষ উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের গদ্যভাষা।
“আরবি-ফারসির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ‘আহাম্মুখী’ মনে করতেন” – কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছিল? কে, কেন একথা মনে করতেন?
প্রসঙ্গ – সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে বাংলাভাষার চরিত্রধর্ম ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আত্মনির্ভরশীল না হওয়ায় প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বাংলাভাষা ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ ধার করেছে। পাঠান-মোগল যুগে নানা আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছিল। যা কালক্রমে বাংলা ভাষার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল, যে বর্তমানে বেশকিছু আরবি-ফারসি শব্দ বাংলার অপরিহার্য অঙ্গ। লেখক বলেছেন, সাহিত্যিক নজরুল, রবীন্দ্রনাথও বিদেশি শব্দ ব্যবহারে দ্বিধাহীন ছিলেন। লেখক বলেছেন – বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমন মন্তব্য করেছিলেন।
যে, যে কারণে এমন মনে করতেন – অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলাভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা, সম্পাদক। তিনি বাংলা ভাষা চর্চার অন্যতম পুরোধা। ভাষা ব্যবহারে উদারমনস্ক হরপ্রসাদ জানতেন “সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিষ লইয়া ফেলিয়াছে। সেসব জিনিস বাঙলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না।” (বাঙ্গলা ভাষা)
তিনি মনে করতেন বাংলাভাষার গঠনেই নয় অতিসাধারণের মুখের ভাষাতেও আজ মুসলমানী অর্থাৎ আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার প্রচলিত যেমন কলম, দোয়াত, আদাল ইত্যাদি। অতএব আরবি-ফারসির বিরুদ্ধে জিহাদ অবশ্যই আহাম্মুখী।
“রচনার ভাষা রচনার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।” – মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
প্রসঙ্গ – বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে এ মন্তব্য করেছেন। ভাষার কাজ মনোভাব প্রকাশে সাহায্য করা। অন্যদিকে সাহিত্য মানবমনের বিমূর্ত কল্পনা, চিন্তা, অনুভূতিকে মূর্ত করে তোলে। সাহিত্যের ভাবপ্রকাশের বাহন তার ভাষা। ভাষা আত্মনির্ভর হলে নিজের প্রয়োজনীয় শব্দ নিজেরই শব্দভাণ্ডার থেকে তৈরি করে নেয়। আত্মনির্ভর বা স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলে তাকে অন্য ভাষার শব্দ ঋণ করতে হয়। অন্যভাষা থেকে শব্দ ঋণ ভালো না মন্দ, কতখানি সংগত তা আলোচনায় তিনি আরবি-ফারসি শব্দের প্রচলন বিষয়টিতে পৌঁছান। এবং সে প্রসঙ্গে নানা কথার সূত্রে তিনি প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছেন।
তাৎপর্য – লেখক দেখেছেন বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে লিখেছেন ‘আব্রু দিয়ে, ইজজৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।’ আবার একই কারণে নজরুল ‘ইনকিলাব’, ‘শহিদ’ – ইত্যাদি শব্দ ঋণ নিয়েছেন। বিদ্যাসাগর ‘সাধু’ রচনায় বিদেশি শব্দ ব্যবহার না করলেও বেনামিতে লেখা ‘অসাধু’ রচনায় অবাধে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রেমচাঁদ, টেকচাঁদ, হুতোম রচনায় বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ভাষায় শব্দ ব্যবহারের ছুৎমার্গকে ‘আহাম্মুখী’ বলেছেন। প্যারীচাঁদের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ কিংবা কালীপ্রসন্নের ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-তেও বিষয় অনুযায়ী কলকাতার কথ্যভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রাবন্ধিক বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনগুলি ছাড়াও বাংলা ভাষার বিভিন্ন ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের কতকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন শংকরদর্শনের আলোচনার ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল বা তৎসম শব্দবহুল। পক্ষান্তরে মোগলাই রেস্তোরার ভাষা হয় হুতোমধর্মী অর্থাৎ অতৎসম, বিদেশি, প্রাদেশিক শব্দসমৃদ্ধ কথোপকথনের ঢঙে চলিত গদ্যে। ‘বসুমতী’র সম্পাদকীয় ভাষায় যে, গাম্ভীর্য দেখা যায়, ‘বাঁকাচোখে’র ব্যঙ্গরচনার ভাষা ততটাই চটুল। তিনি দেখিয়েছেন এভাবেই বিষয় রচনার ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে।
“একমাত্র আরবি-ফার্সি’ শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে।” কী বলা যেতে পারে? সে কথা কেন বলা যেতে পারে বলে লেখকের ধারণা?
যা বলা যায় – সৈয়দ মুজতবা আলী ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে বলেছেন, আরবি এবং ফারসি ভাষা থেকে নতুন শব্দ আর বাংলা ভাষায় ঢুকবে না।
কারণ – বাংলা ভাষার উদ্ভব নব্যভারতীয় আর্যভাষা স্তরে। আনুমানিক 900 থেকে 1000 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ট ভাষা থেকে বাংলার জন্ম। এসময়কালীন অন্যান্য ভাষাগুলোর মতো বাংলাও স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। তাই প্রবহমানতার ধারায় সচল ও প্রাণবন্ত থাকতে তাকে শব্দ ঋণ করতে হয় ভিন্ন ভাষা থেকে। সংস্কৃত ভাষা ও ইংরেজি ভাষার উপর বাংলা ভাষার নির্ভরতা গভীর। ফলস্বরূপ এভাষা থেকে শব্দগ্রহণ না করলে বাংলভাষা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হবে।
বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে আরবি-ফারসি চর্চা অনেক কমেছে এবং পূর্ববাংলায় এই দুই ভাষার প্রতি তরুণ সম্প্রদায়ের কৌতূহল অতিশয় ক্ষীণ। ফলত এদের আয়ু দীর্ঘ হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে যে হঠাৎ কোনো অভূতপূর্ব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়ে বাংলাকে প্রভাবিত করবে এমন সম্ভাবনাও নেই। সেই কারণে প্রাবন্ধিক এমন মন্তব্য করেছেন।
“ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।” – ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনা অবলম্বনে এ উক্তির সত্যতা বিচার করো।
অথবা, “ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না” – কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? কথাটির তাৎপর্য কী?
প্রসঙ্গ – মানবজাতির একটিই ধর্ম মানবতা। কিন্তু কালের নিয়মে ‘ধৃ’ ধাতু থেকে উৎপন্ন ‘ধর্ম’ অর্থাৎ, ধূ + ম = ধর্ম শব্দটি ধারণকারী হয়ে থাকেনি। বরং দেশজাতি বিশেষের পরকাল বিশ্বাস, অলৌকিকতায় আস্থা এবং উপাসনা পদ্ধতি মেনে সে হয়ে উঠেছিল হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদির ধর্ম। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে বাঙালির চরিত্র মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনে ধর্মপ্রসঙ্গে এসেছেন। ‘ধর্ম’ বলতে তিনি হিন্দু ও ইসলাম এই দুই ধর্মকে বুঝিয়েছেন।
‘বিদ্রোহী’ চরিত্র – বাঙালি উদারস্বভাব। পরকে আপন করা তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। আবার বাঙালি চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য যেখানেই বাঙালি সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তা গ্রহণ করেছে। গতানুগতিকতা বা প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুকরণ সে কখনও মেনে নেয়নি। এদের দোহাই দিয়ে আবদ্ধতা সৃষ্টি করতে চাইলে বাঙালি বিদ্রোহী হয়েছে। আবার সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হলে তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী হয়েছে।
সত্যতা বিচার – বিদ্রোহী স্বভাব বাঙালির প্রাণের ধর্ম। হিন্দু বাঙালি, মুসলমান বাঙালি পরিচয় সেখানে গৌণ। ধর্মের পরিচয় সেখানে মানবিকতায় উজ্জ্বল। তাই ধর্ম বদল মিশ্র বাঙালি জাতির চরিত্র বদল ঘটাতে কখনও সক্ষম হবে না। এ কথা বোঝাতেই প্রাবন্ধিকের মূল্যায়ন –
“এ বিদ্রোহ বাঙালি হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালি মুসলমানও এ কর্মে তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।”
“প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই।” – কোন্ কোন্ ভাষার উল্লেখ করে লেখক কেন এরূপ বলেছেন? এ প্রসঙ্গে বর্তমান যুগের কোন্ দুটি ভাষা সম্পর্কে তিনি কী বলেছেন?
ভাষার উল্লেখ – সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধের আলোচ্য অংশে লেখক সংস্কৃত এবং তার সঙ্গে হিব্রু, গ্রিক, আবেস্তা এবং কিছুটা আধুনিক আরবি ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন যুগের অধিকাংশ ভাষাই নতুন চিন্তা-ভাবনা, নতুন বস্তু বোঝাতে নতুন শব্দের প্রয়োজনে হলে তা নিজ শব্দভাণ্ডারের ধাতু বা শব্দ দ্বারাই তৈরি করার চেষ্টা করেছে। অন্য ভাষা থেকে ঋণ নেওয়ার কথা ভাবে না। বিদেশি শব্দ ব্যবহার করলেও তা অতিসামান্য। তাই লেখক প্রাচীন ভাষাগুলোকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেছেন।
দুটি ভাষা প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত – ভাষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে লেখক বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা ভাষার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, আধুনিক কালের এই দুটি ভাষাই অন্যান্য ভাষা থেকে অতিরিক্ত শব্দ গ্রহণ করে নিজের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার এবং প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাঠান-মোগল যুগে বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ স্থানলাভ করেছে। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ইংরেজি থেকে এবং ইংরেজির মাধ্যমে অন্যান্য ভাষা থেকেও বহু শব্দ গ্রহণ করেছে। একইভাবে ইংরেজি ভাষাও নানা উৎস থেকে শব্দ ধার করেছে। এই কারণেই লেখকের মতে, ইংরেজি ও বাংলা – কোনওটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা নয়।
বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় আত্মনির্ভরশীল ভাষা কাকে বলে? লেখকের এরকম মনে হওয়ার কারণ কী?
আত্মনির্ভরশীল ভাষা – লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর নব নব সৃষ্টি রচনায় বলেছেন যে, ভাষার আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ ভাষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা। সংস্কৃতকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে এই ভাষায় কোনো নতুন চিন্তা, অনুভূতি, কিংবা বস্তুকে বোঝানোর জন্য শব্দের প্রয়োজনে হলে সংস্কৃত তা নিজের ভাণ্ডারেই সন্ধান করে। প্রয়োজনে এমন কোনো ধাতু বা শব্দকে খুঁজে নিতে চায় যা সামান্য অদল-বদল করে বা পুরোনো ধাতুর সাহায্যেই একটি নতুন শব্দ নির্মাণ করে নেওয়া যায়। তাই সংস্কৃত একটি আত্মনির্ভরশীল ভাষা হয়ে উঠতে পেরেছে।
লেখকের এরকম মনে হওয়ার কারণ – ভাষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গেই লেখক বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা ভাষার উল্লেখ করেছেন। আধুনিক কালে এই ভাষাগুলি অন্যান্য ভাষা থেকে অতিরিক্ত শব্দ গ্রহণ করে নিজেদের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার ও প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে। যেমন পাঠান-মোগল যুগে বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ প্রবেশ করেছে। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ইংরেজি থেকে এবং ইংরেজির মাধ্যমে অন্যান্য ভাষা থেকেও শব্দ গ্রহণ করেছে। এই কারণেই লেখকের মতে ইংরেজি ও বাংলা – কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা নয়।
বিদেশি শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর।” মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
উৎস – আলোচ্য উদ্ধৃতাংশটি সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত নব নব সৃষ্টি রচনাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে।
তাৎপর্য – ভাষা তার নিজ শব্দভাণ্ডারের ধাতু বা শব্দ দ্বারা নতুন শব্দ তৈরি করতে পারলেই ভাষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিদেশি শব্দ গ্রহণ করলেও ভাষা অনেকসময় মধুর এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যদি সেই ভাষা বিষয়কেন্দ্রিক হয়। লেখক নিজেই বলেছেন, রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতি শব্দ অনায়াসে মিশেছে। ইংরেজি ভাষার বদলে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার ফল হাতেনাতে পাওয়া গেছে। কারণ তারপরই বাংলায় প্রচুর পরিমাণে ইউরোপীয় শব্দ ঢুকেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা বহু বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করে থাকি।
একইরকমভাবে বিদেশি শব্দও প্রবেশ করবে ভাষায়। হিন্দি ভাষাকে আরবি-ফারসি শব্দ মুক্ত করার জন্য চেষ্টা শুরু করেছেন হিন্দি ভাষার সাহিত্যিকরা। তার ফলাফল ভালো না খারাপ হবে লেখক তা ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে দিলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আনায়াসেই আরবি-ফারসি ভাষা মিশিয়ে লিখেছেন, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে। আবার নজরুল ইসলামও ইনকিলাব, শহিদ প্রভৃতি বিদেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহার করেছেন। বিষয়ের গাম্ভীর্য, আভিজাত্য এবং চটুলতার উপর ভাষার ব্যবহার নির্ভর করে। ফলে বিদেশি শব্দের ব্যবহারও ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে যদি তা বিষয়বস্তুর যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারে।
“ফল যদি ভালো হয় তখন তাঁরা না হয় চেষ্টা করে দেখবেন।” — কোন্ প্রসঙ্গে লেখক এরূপ বলেছেন? বাংলা সাহিত্যিকদের নিয়ে এই প্রসঙ্গে লেখক কী বলেছেন?
প্রসঙ্গ – সৈয়দ মুজতবা আলী নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধে ভাষায় বিদেশি শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হিন্দি ভাষার সাহিত্যিকদের একটি প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেছেন। হিন্দি ভাষাকে আরবি, ফারসি, ইংরেজি শব্দ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন বেশ কিছু হিন্দি সাহিত্যিক। তাঁদের এই চেষ্টার ফল ভালো না খারাপ হবে, তা বিচার করার চেয়েও বড়ো কথা হল এই যে তাঁরা এই জাতীয় একটি চেষ্টা শুরু করেছেন।
বাংলা সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখকের অভিমত – বাংলা সাহিত্যিকরা অনায়াসেই বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে ভাষা বিষয়কেন্দ্রিক হবে এটাই মূল কথা। তাই রবীন্দ্রনাথ খুব স্বচ্ছন্দেই আরবি-ফারসি ভাষার সংমিশ্রণে লিখেছেন, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে। নজরুল ইসলামও ইনকিলাব বা শহিদ এই শব্দগুলি সহজেই তাঁর লেখায় বাংলা ভাষার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরও তাঁর চলিত ভাষায় লেখা রচনার মধ্যে আরবি- ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরবি-ফারসি শব্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাকে মূর্খামি বলে মনে করতেন।
“রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।” মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
তাৎপর্য – উদ্ধৃতাংশটি সৈয়দ মুজতবা আলীর নব নব সৃষ্টি পাঠ্য প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। রচনার গাম্ভীর্য, আভিজাত্য, চটুলতার সঙ্গে ভাষার ব্যবহার গভীরভাবে জড়িত।
বিদেশি ভাষার প্রয়োজনীয়তা – নতুন শব্দ তৈরি বা বিষয়ের মধ্য দিয়ে নতুন চিন্তা ও অনুভূতি ফুটিয়ে তুলতে গেলে বিদেশি ভাষার প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা বাতিল করার ফলে বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ আরও বেশি করেই প্রবেশ করেছে। তবে বিদেশি শব্দ কোনোভাবেই লেখার মাধুর্যকে নষ্ট করতে পারে না যদি তা বিষয়কেন্দ্রিক হয়। বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার – রবীন্দ্রনাথ আরবি-ফারসিকে স্বাগত জানিয়ে খুব স্বচ্ছন্দেই লিখেছেন, আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে। নজরুল ইসলামও ইনকিলাব, শহিদ, প্রভৃতি শব্দ বাংলায় অনায়াসেই ব্যবহার করেছেন। শংকরদর্শন-এর আলোচনায় যে গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য রয়েছে, তা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারেই সঠিক রূপ লাভ করে।
বসুমতী পত্রিকার সম্পাদকীয় ভাষাও একইরকম গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু বাঁকা চোখে পত্রিকার ভাষায় চটুলতা তার বিষয় উপযোগী। আবার রেলের ইঞ্জিন কীভাবে চালাতে হয় বা বিজ্ঞানচর্চা ও দর্শনের বিষয় জানতে ইংরেজি ভাষার বিকল্প নেই। সুতরাং, সঠিক ভাষা প্রয়োগ বিষয়বস্তুর মূলভাবকে তুলে ধরতে পারে।
বাংলায় যেসব বিদেশি ভাষার শব্দ ঢুকেছে তার মধ্যে কোন্ কোন্ ভাষাকে লেখক প্রধান বলেছেন? এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজি নিয়ে লেখক কী বলেছেন?
লেখকের মতে বাংলায় আগত প্রধান বিদেশি ভাষাসমূহ – সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর নব নব সৃষ্টি রচনাংশে জানিয়েছেন যে বাংলায় যেসব বিদেশি শব্দ প্রবেশ করেছে সেগুলির মধ্যে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষার শব্দই প্রধান।
সংস্কৃত ও ইংরেজি সম্বন্ধে লেখকের অভিমত – একসময়ে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চর্চা ছিল। কারণ সংস্কৃতই ছিল আদি ও মূল ভাষা। এখনও স্কুল-কলেজে সংস্কৃতচর্চা হয়। সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সংস্কৃত শব্দ এখনও সামান্য হলেও বাংলা ভাষায় প্রবেশ করছে। সংস্কৃত ভাষাকে বাংলার মাতৃসম ভাষাই বলা হয়, তাই সংস্কৃতচর্চা বন্ধ করে দিলে বাংলা ভাষা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। তাই লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন, আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হবো।
আধুনিক শিক্ষার ধারায় দর্শনশাস্ত্র, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার বিকল্প নেই। উদাহরণ হিসেবে লেখক বলেছেন যে রেলের ইঞ্জিন কী করে চালাতে হয়, সে বিষয়ে বাংলায় কোনো বই নেই। ফলে এই বিষয়টা বুঝতে হলে বাঙালিকে ইংরেজি ভাষারই আশ্রয় নিতে হয়। সুতরাং ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি। — এ কথা বলাই যায়।
ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি। — বক্তা কে? এরূপ উক্তির কারণ কী?
বক্তা – প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটির বক্তা নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধের লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী।
এরূপ উক্তির কারণ –
- নির্ভরশীল বাংলা ভাষা – বাংলা ভাষা আত্মনির্ভরশীল ভাষা নয়। আরবি-ফারসির মতোই ইংরেজির থেকেও আমরা প্রচুর শব্দ নিয়েছি। ভাষাকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য অন্য ভাষাকে ত্যাগ করার চেষ্টা একেবারে বিরল ঘটনা নয়। হিন্দিতে এ চেষ্টা হয়েছে। আবার বিখ্যাত লেখকদেরও দেখা গিয়েছে যে, তাঁরা অন্য পথে হেঁটেছেন। বাংলা ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর উদাহরণ। লেখক দেখিয়েছেন যে বাংলা ভাষায় যে শব্দসমূহ এসেছে তার মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি প্রধান। এক্ষেত্রে ইংরেজির ভূমিকা কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়।
- প্রয়োজনীয় বাংলা শব্দের অভাব – দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থ কিংবা রাসায়নবিদ্যা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ বাংলায় যথেষ্ট নেই। রেল ইঞ্জিন চালানোর প্রযুক্তি বিষয়ে বাংলায় কোনো বই নেই। এখানে ইংরেজির উপরে নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এইসব কারণেই লেখকের মনে হয়েছে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য ইংরেজির চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি।
লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী একবার বলেছেন “আরবি – ফারসি ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নতুন শব্দ বাংলাতে ঢুকবে না।”, আবার একবার বলেছেন “অচলিত অনেক আরবি-ফারসি শব্দ নতুন মেয়াদ পাবে।” — এই দুই উক্তির কারণ বুঝিয়ে দাও৷
প্রথম উক্তির কারণ – ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রবেশ এবং তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনায় লেখক বলেছেন যে বাংলা ভাষায় যেসব বিদেশি শব্দ প্রবেশ করেছে সেগুলির মধ্যে প্রধান হল আরবি এবং ফারসি। তবে আরবি এবং ফারসি—এই দুটি ভাষার প্রতি তরুণ বাঙালি সম্প্রদায় বর্তমানে ক্রমশ আগ্রহ হারাচ্ছে। এর ফলে এই দুই ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নতুন শব্দ বাংলাতে ঢুকবে না। তা ছাড়া, আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ফলে এই ভাষা দুটির বাংলাকে প্রভাবিত করতে পারার সম্ভাবনাও খুব ক্ষীণ।
দ্বিতীয় উক্তির কারণ – বাংলা ভাষা প্রাচীন কাল থেকেই আরবি-ফারসি শব্দ ব্যাপক পরিমাণে গ্রহণ করেছে। আর এইসব শব্দ যে বহুদিন বাংলায় প্রচলিত থাকবে সে-বিষয়ে লেখক নিঃসন্দেহ। তা ছাড়া, মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল থেকে শুরু করে হুতোম প্যাঁচার নক্শা পর্যন্ত যেসব আরবি- ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে নতুন লেখক সম্প্রদায় সেগুলিকে নতুন করে খুঁজে আবার সাহিত্যে প্রয়োগের চেষ্টা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে প্রাচীন বাংলা পড়ার কারণেই অচলিত অনেক আরবি-ফারসি শব্দ নতুন মেয়াদ পাবে।
ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না। – নব নব সৃষ্টি রচনা অবলম্বনে এই উক্তির সত্যতা বিচার করো।
সত্যতা বিচার – প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর নব নব সৃষ্টি প্রবন্ধে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি বাঙালির চিরকালীন পক্ষপাতের কথা বলেছেন। রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য—বাঙালি যেখানে যখনই সত্য-শিব-সুন্দরের খোঁজ পেয়েছে তখনই তা সাদরে গ্রহণ করতে চেয়েছে।
বাঙালির চিরন্তন ধারণা – কেউ গতানুগতিকতা বা প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে তাতে বাধা দিতে গেলে বাঙালি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আবার সেই বিদ্রোহই যদি উচ্ছৃঙ্খলতা বা নৈরাজ্যের দিকে যায় তখন বাঙালি তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছে। অর্থাৎ সত্য-শিব- সুন্দরের ধারণাকে বাঙালি চিরন্তন বলে গ্রহণ করেছে। বাঙালি জাতিসত্তা – লেখক লক্ষ করেছেন যে এই রুচি বা জীবনাদর্শকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে হিন্দু বা মুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর এই বিদ্রোহে বাঙালি মুসলমানরাও যোগ দিয়েছে। তার কারণ ধর্ম গেলেও জাতি বদলে গেলেও জাতিসত্তা একই থেকে যায়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি সমগ্র বাঙালি জাতিরই, কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নয়। লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, ধর্ম বদলালে জাতির চরিত্র বদলায় না। বাঙালি মুসলমানরাও বাঙালি জাতিসত্তারই অংশ। তার ধর্ম আলাদা হলেও এদেশের জল হাওয়াতেই তার চেতনা ও জীবনাদর্শের বিকাশ।
শেষের কথা; তাই ধর্ম বদলে যেতে গেলেও মনোভাবের কোনো বদল বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ঘটেনি।
‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধ অবলম্বনে বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষার শব্দের প্রবেশের মাধ্যমে নতুন নতুন ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও।
লেখকের বক্তব্যবিষয় –সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষা যে অন্য ভাষার উপর নির্ভরশীল সে কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অন্য ভাষা – পাঠান, মোগল এবং ইংরেজ — বিভিন্ন যুগে প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে বাংলা ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ ধার নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের মতো লেখকরা বিদেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর ছদ্মনামে লেখা চলিত ভাষার রচনাগুলিতে আরবি ও ফারসি শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবার আরবি–ফারসির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করাকে বোকামি বলে মনে করতেন।
বাংলা ভাষায় যথাযথ শব্দের অভাব – লেখকের মতে, শব্দ অনুসন্ধান ও তার ব্যবহারের জন্য সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার কাছে এখনও প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজির ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি। তার কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা শব্দ এখনও যথেষ্ট নেই।
অন্যভাষার চর্চা – তবে লেখক লক্ষ করেছেন, আরবি-ফারসি ভাষার চর্চা এদেশে বন্ধ হতে চলেছে আর বাংলাদেশেও এই ভাষাগুলি নিয়ে আগ্রহ কম।
ইতিকথা – তাই এই ভাষাগুলি থেকে ব্যাপকভাবে শব্দের নতুন করে বাংলায় প্রবেশের সম্ভাবনা নেই। তবে যেসব শব্দ ইতিমধ্যে বাংলায় রয়ে গেছে, তারা থেকে যাবে। সাহিত্যে তাদের ব্যবহারও হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মধ্য দিয়েও এরা নতুন মেয়াদ পাবে।
‘নব নব সৃষ্টি’ রচনাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।
সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে নামকরণের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। লেখক তাঁর ‘নব নব সৃষ্টি’ রচনায় যে–কোনো সৃষ্টিকর্মের নির্মাণে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্রহণ-বর্জন থাকে, তাকে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিছু ভাষা আছে যেমন সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রিক, আভেস্তা, এমনকি আরবি ইত্যাদি প্রাচীন ভাষাগুলি অনেকটাই আত্মনির্ভরশীল। আবার বাংলা, ইংরেজির মতো ভাষাগুলি অন্য ভাষা থেকেও শব্দ নেয়। এই শব্দরা স্থায়ীভাবে ভাষায় থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বেনামে বিদ্যাসাগর — সকলেই অন্য ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে নিজেদের সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করেই শব্দগ্রহণ চলে। এই গ্রহণের পথে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
তবে, আরবি-ফারসির প্রভাব কিছুটা ক্ষীণ হলেও, সাহিত্যে ইতিমধ্যেই তারা স্থান পেয়ে গেছে। পরীক্ষানিরীক্ষার কারণে এইসব শব্দও বাংলা ভাষায় স্থায়ী হয়ে যাবে। বর্তমানে আরবির তুলনায় ফারসির গ্রহণযোগ্যতাই বেশি। উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যে ফারসির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইকবালের মতো কেউ কেউ অবশ্য উর্দুকে ফারসির প্রভাবমুক্ত করার চেষ্টা করেছেন।
অন্য ভাষার ওপর নির্ভর না করেও সাহিত্যসৃষ্টি যে সফল হতে পারে, তার যথার্থ উদাহরণ হলো পদাবলি কীর্তন। বাঙালি—হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান—সবসময় স্বাধীনভাবে চলতে চায়। এই বিদ্রোহী সত্তা তাদের মধ্যে সর্বদা সক্রিয় থাকে। সব মিলিয়ে শব্দ ও ভাষা ঋণ নেওয়া এবং বর্জন—এই দুই বিপরীতমুখী স্রোতের মধ্য দিয়েই সাহিত্য গড়ে ওঠে। সৃষ্টির সেই বিচিত্র স্বরূপকে ধরার চেষ্টাই প্রবন্ধের নাম ‘নব নব সৃষ্টি’কে সার্থক করে তুলেছে।
আজকের এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের দ্বিতীয় পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘নব নব সৃষ্টি’ -এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নোত্তরগুলো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নবম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত আসে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে, তবে টেলিগ্রামে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত। ধন্যবাদ।

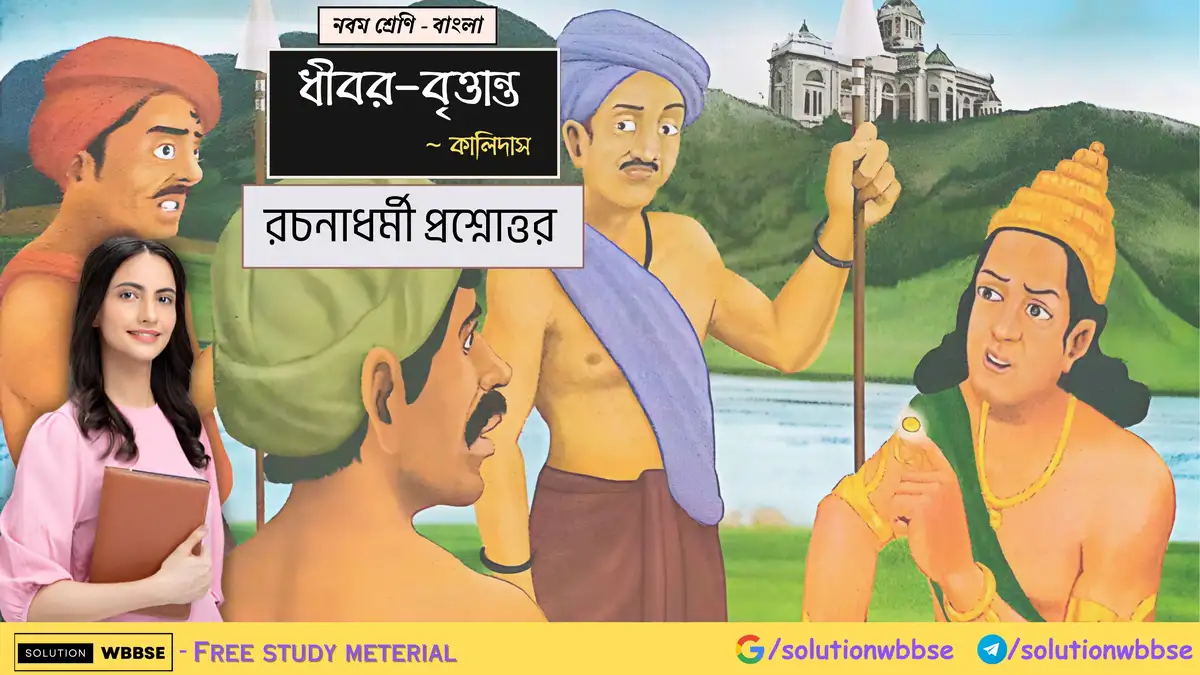
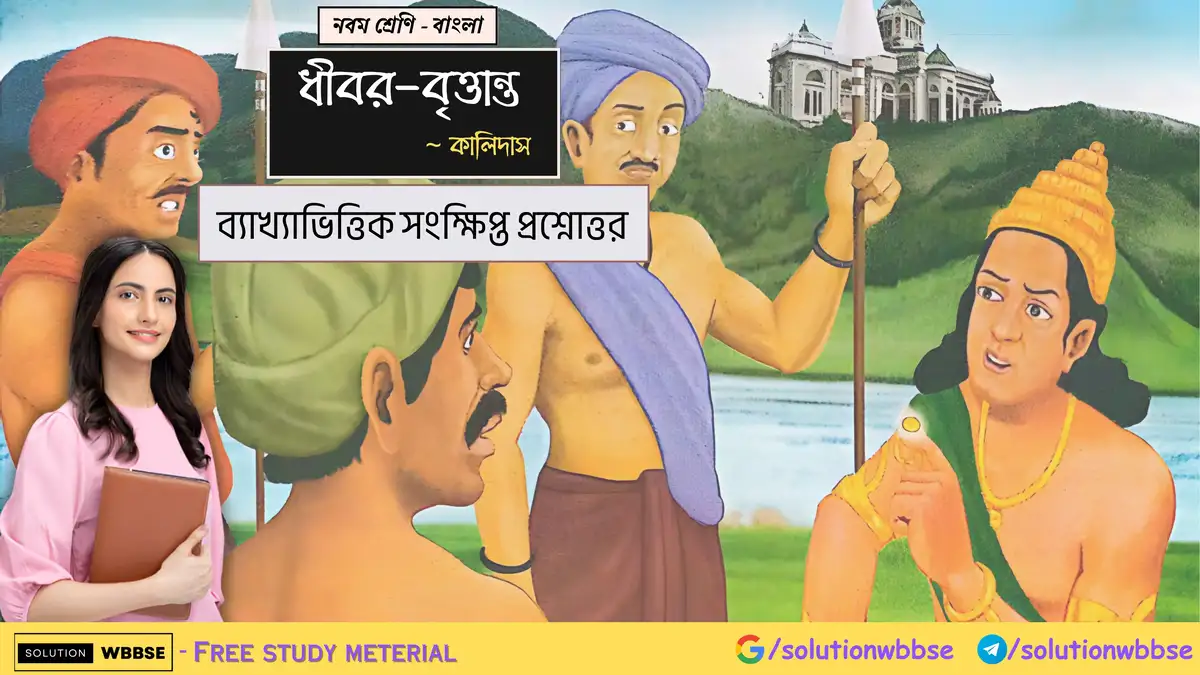
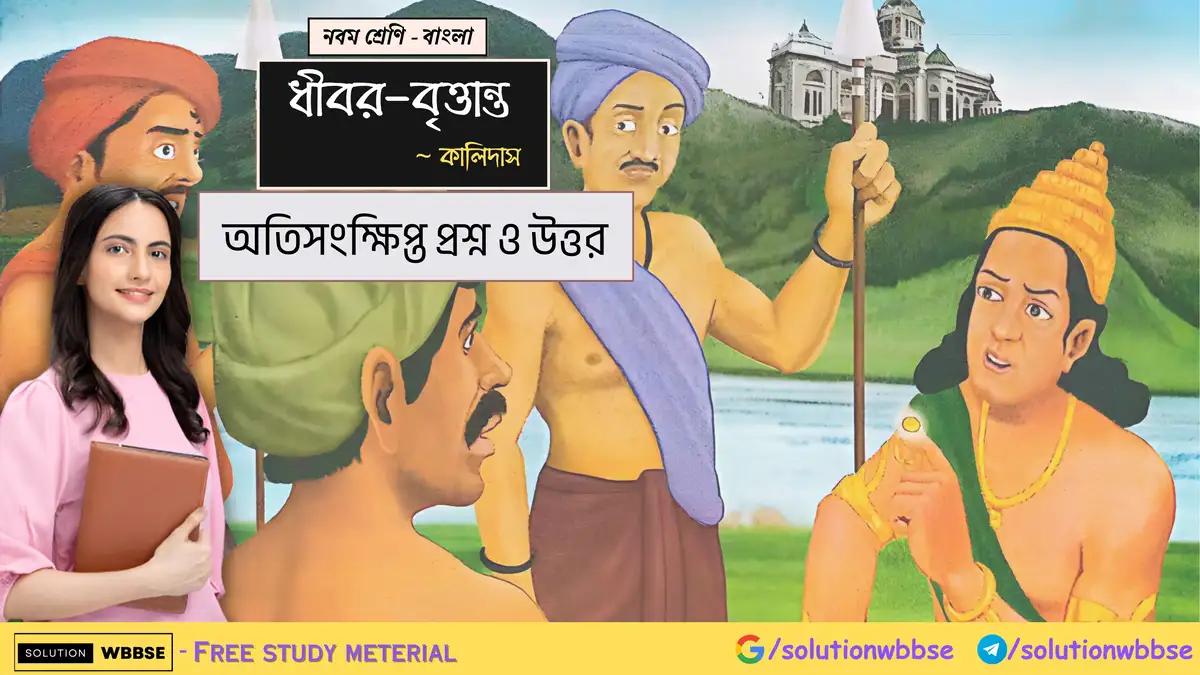
মন্তব্য করুন