আজকের এই আর্টিকেলে আমরা অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের ত্রিংশ অধ্যায় ‘হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’-এর বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এই অধ্যায়ের প্রশ্নাবলী শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো প্রায়ই অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় আসতে দেখা যায়। তাই, এই আর্টিকেলটি আপনার প্রস্তুতিতে সহায়ক হবে।
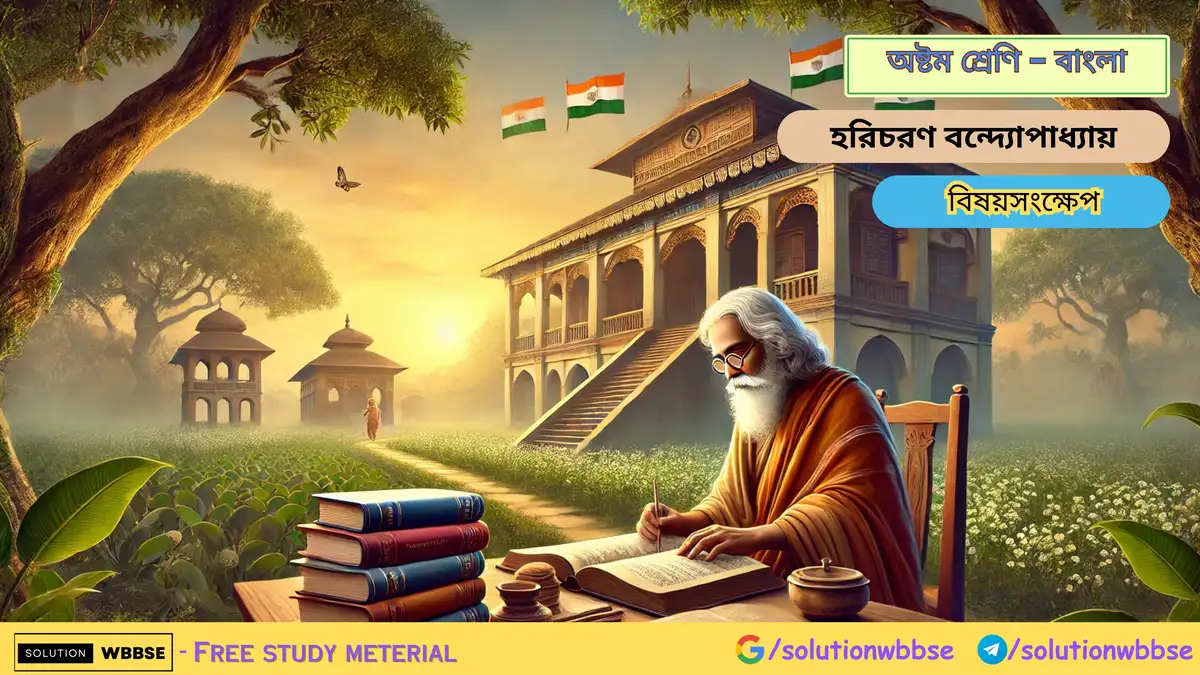
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যায়ের লেখক পরিচিতি
সাহিত্যিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে, কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরে। তিনি শান্তিনিকেতনে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ‘ইন্দ্রজিৎ’ ছদ্মনামে ‘দেশ’ পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল – ‘বন্ধনহীন গ্রন্থি’, তিনবন্ধু’, ‘ইন্দ্রজিতের খাতা’, ‘ইন্দ্রজিতের আসর’, ‘কালের যাত্রার ধ্বনি’, ‘শান্তিনিকেতনে একযুগ’, ‘প্রাণবন্যা’, ‘বধূ অমিতা’, ‘সাহিত্যের আড্ডা’, ‘অচেনা রবীন্দ্রনাথ’, ‘আপন মনের মাধুরী মিশায়ে’, ‘খেলা ভাঙার খেলা’, ‘শেষ পারানির কড়ি’ ইত্যাদি। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেহাবসান ঘটে।
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যায়ের পাঠপ্রসঙ্গ
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আলোচ্য প্রবন্ধে মহাত্মা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকর্ম আলোচনা করেছেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাঙালির বিদ্যাচর্চার যোগ নিবিড়। তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ বাংলার সমাজে সুপরিচিত। বাংলা ভাষার এমন এক অভিধান দুর্লভ এবং বিরল দৃষ্টান্ত। সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়নের নেপথ্যে হরিচরণের প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের কথা লেখক কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন। বাংলা ভাষায় এমন এক অভিধান রচনা করে হরিচরণ বাঙালি জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।
চব্বিশ পরগনার রামনারায়ণপুর গ্রামে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন হরিচরণ জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রকল্যাণ তহবিলের অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিএ তৃতীয় বর্ষের পড়াশোনা তিনি চালিয়ে যেতে পারেননি। অর্থাভাবে তাঁকে মাঝপথেই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। জীবিকার তাগিদে তিনি নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। পরে কলকাতার টাউন স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদ অলংকৃত করেন। এরপরেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে ঠাকুরবাড়ির জমিদারির কাজে যোগদানের সূত্রে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের জমিদারির পতিসর কাছারিতে সুপারিন্টেনডেন্টের পদে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার কালে রবীন্দ্রনাথ এই কর্মচারীর মেধা ও সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের উপর দখল দেখে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে অসেন। সেই থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে অবসরগ্রহণ না করা পর্যন্ত হরিচরণ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংস্কৃত বিষয়ের অধ্যাপকরূপে জীবন অতিবাহিত করেন। বিশ্বকবির একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধে সাড়া দিয়ে হরিচরণ ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ -এর মতো বৃহদাকার অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করেন।
কবি রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি, মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভা সন্ধানের দুর্লভ ক্ষমতা, উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে উপযুক্ত কাজ করিয়ে নেওয়ার দক্ষতা এ পাঠ্যে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বজায় রেখে হরিচরণ যেভাবে অভিধান প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাও এখানে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হয়েছে। মহৎ মানুষের মানসিকতা, তাঁদের অনুসন্ধিৎসা, কর্মযোগ এ পাঠের মাধ্যমে আমাদের গোচরে এসেছে। গদ্যাংশটি পাঠ করতে করতে আমাদের মন পরিভ্রমণ করে বুধমণ্ডলীতে, মহাত্মাগণের কর্মোদ্যোগের মধ্যে। মনীষীতুল্য ব্যক্তিত্বদের আন্তরিক পরিচয় এ পাঠ্যে লভ্য। প্রচারের অন্তরালে থেকে যাঁরা নিভৃতে লোকহিতের সাধনায় মগ্ন হন, তাঁরা আমাদের নমস্য। নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিরলস শ্রম মানুষকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়-হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবৃত্তান্ত আমাদের সে পথের সন্ধান দেয়।
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যায়ের বিষয়সংক্ষেপ
শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ সুযোগ্য মানুষদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকপদে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সত্যানুসন্ধান দৃষ্টি সেই মুহূর্তে আরও অনেকের সঙ্গে শ্রদ্ধেয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সন্ধান করে আনে। অপরিচয়ের দূরত্ব, পাণ্ডিত্যের প্রামাণিকতার অভাব, প্রখ্যাত না হওয়ার অসুবিধা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেনি। পাকা জহুরি যেমন সঠিক জহর চেনেন, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথও বাংলার পল্লি-অঙ্গন থেকে চয়ন করে এনেছিলেন ব্যক্তিত্বের সুরভিবৃন্দকে। প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ করে তাঁদের তিনি প্রতিভা বিকাশের উন্মুক্ত ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। সেইরূপ কতিপয় প্রতিভাধর মানুষের মধ্যে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম।
হরিচরণের মধ্যে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রটি উর্বর হয়েই ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিধান রচনার আদেশ দিলে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন। চিত্তের বিদ্যানুশীলনের গতিটি তাঁর সুপ্তই ছিল, বিশ্বকবি সে-গতির অভিমুখ নির্বাচন করে দিলেন। পালে লাগল হাওয়া, অভিধান রচনার তরিটি এগিয়ে চলল সমাপ্তির অভিমুখে। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর একনিষ্ঠ সাধনার ফল তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’। হরিচরণের শ্রমসাধ্য কাজের বর্ণনা দিয়েছেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অশক্ত শরীরে, ক্ষীণদৃষ্টি নিয়ে, শত প্রতিকূলতাকে হেলায় তুচ্ছ করে হরিচরণ অভিধান রচনায় ব্যাপৃত থেকেছেন। অদম্য মানসিক জোর তাঁকে এ কাজে সদা সচল রেখেছে। একক প্রয়াসে তাঁর এ উদ্যোগ এবং সফল রূপায়ণ এ গদ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যায়ের নামকরণ
আলোচ্য গদ্যের নামকরণ ‘হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক এর উপজীব্য তাঁর জীবনী। কিন্তু পাঠ শেষ করে বোঝা যায়, এ গদ্য নিছক জীবনী ছাড়িয়েও অনেক কিছু। শুধুমাত্র কালানুক্রমিক শুষ্ক তথ্য সমাবেশ নয়, বরং হরিচরণের একনিষ্ঠতার আন্তরিক পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। আনুষঙ্গিক ব্যক্তিচরিত্র, তাদের জীবনের কথা এসেছে হরিচরণের সূত্র ধরেই। হরিচরণকে খুঁজে বের করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু মনে রাখতে হবে জহরের উপস্থিতি, রত্বের ঔজ্জ্বল্য আছে বলেই জহুরির এত কদর। হরিচরণ এখানে রত্ন আর জহুরি রবীন্দ্রনাথ। কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এখানে এসেছে আরও এসেছে শান্তিনিকেতনের সূচনাযজ্ঞের কথা, শান্তিনিকেতনের ফলপ্রসু পরিবেশের কথা। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ তথা শান্তিনিকেতন যে রত্ন-সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন সে প্রসঙ্গও এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। তবে তার সব কিছুই এসেছে হরিচরণের প্রসঙ্গ ধরেই।
হরিচরণের একনিষ্ঠতা, তাঁর শ্রমসাধ্য কাজের প্রতি নিষ্ঠা, অধ্যবসায় সব কিছুই শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। গদ্যের ভরকেন্দ্রে রয়েছে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখকের সরস বর্ণনাগুণে এ পাঠ্য মনোগ্রাহী ও সাহিত্যরসাস্বাদী হয়ে উঠেছে। ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ -এর মতো সুবৃহৎ বাংলা অভিধান রচনা করে বাঙালি সমাজের কাছে চিরনমস্য হয়েছেন হরিচরণ। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের শ্রমসাধ্য প্রয়াস যখন ফলপ্রসু হল, তখন বাংলার বিদ্বজ্জন দেখলেন, এ কাজের মাহাত্ম্যকে। পর্বতপ্রমাণ, আয়াসসাধ্য কাজকে হরিচরণ যেভাবে অনায়াসে সুসম্পন্ন করলেন, তা বিস্ময়কর বৈ কী! গদ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছেন হরিচরণ। তাই গদ্যাংশের নামকরণ যথাযথ ও সার্থক।
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যায়ের শব্দার্থ ও টীকা
প্রথম অনুচ্ছেদ –
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় – রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ৭ পৌষ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (২২ ডিসেম্বর ১৯০১) শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আহ্বানে – ডাকে। নির্বিবাদে – বিবাদবিহীন; কোনো বিতর্ক বা সন্দেহ নেই যেখানে। সমকক্ষ – তুলনায়; সদৃশ। স্বেচ্ছায় – আপন ইচ্ছায়। স্বহস্তে – আপন হাতে। হঠকারিতা – বোকামি; না ভেবেচিন্তে কোনো কাজে করা। সাধ্যসীমা – আপন সাধ্যের মধ্যে; নিজ ক্ষমতার মধ্যে। সাধ্যাতীত – সাধ্যের অতীত; ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কাজ করা। মিথ্যা প্রতিপন্ন – মিথ্যা বলে প্রমাণ করে। সিদ্ধিলাভ – সাফল্য লাভ করা। মাস-মাহিনার চাকুরে – চাকরি করে যিনি প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আয় করেন। প্রয়াস – চেষ্টা। অকিঞ্চন – দরিদ্র; গরিব। কীর্তি – মহৎ কাজ। সুমহান – ভালো; মাহাত্ম্যপূর্ণ। বাহ্যত – বাইরের দিক দিয়ে। দৃষ্টিগোচর – চোখে দেখা যায় যা। নিহিত – সুপ্ত ছিল; ভিতরে ছিল। নিষ্ঠা – কাজে সততা ও স্থিতি। অভিনিবেশ – মনোযোগ। তদুপরি – তার উপর। গুণসন্নিপাতে – গুণের সমাবেশে। কার্য – কাজ।
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ –
কৃতিত্ব – কার্যকুশলতা; যোগ্যতা। প্রাপ্য – পাওয়ার যোগ্য। স্থান-মাহাত্ম্য – স্থানের গুণ বা গুরুত্ব। অপরিসীম – অনেক; বহু; সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা। বিদ্যাদান – বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যাচর্চা – বিদ্যাচর্চা করা বা অনুশীলন করা। বিদ্যা-বিকিরণ – বিদ্যা বিচ্ছুরিত করা। বিদ্যাকেন্দ্র – বিদ্যাচর্চা বা দানের স্থান। সর্বশক্তি – সব শক্তি; সমস্ত। নিঃসংকোচে – সংকোচবিহীনভাবে; দ্বিধাহীনভাবে।
তৃতীয় অনুচ্ছেদ –
নির্দেশে – আদেশে বা নির্দেশনায়। প্রবৃত্ত হন – আত্মনিয়োগ করেন; ব্যাহত হন। নবীন – নতুন; তরুণ। অভিজ্ঞতায় – অবগত। অপ্রবীণ – কম অভিজ্ঞ; কম প্রাজ্ঞ। প্রামাণিক – পাণ্ডিত্য প্রমাণের জন্য কোনো বিশেষ গ্রন্থ রচনা করা, যাতে সকলে রচনাকারের পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পেতে পারেন। সংশয় – সন্দেহ; দ্বিধা। বিন্দুমাত্র – একটুমাত্র; স্বল্পমাত্র। ন্যস্ত – নিহিত স্থাপিত। অধ্যাপক – মহাবিদ্যালয় (কলেজ) বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্লট – সাহিত্যের প্লট বলতে বোঝায় কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত কাহিনি, যে কাহিনির মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে অর্থাৎ গল্প বা উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়ণ। চোখ বুজে – চোখ বন্ধ করে অর্থাৎ পরম নির্ভরতায় বা গভীর বিশ্বাসে। প্রতিভাবান – প্রতিভা আছে যার; প্রতিভাধর। ছাই – ভস্ম। শীর্ণ – রোগা; কৃশ। বিবর্ণ – বর্ণহীন; রং নেই যাতে। অস্থি – হাড়। মজ্জা – অস্থিস্নেহ (Marrow)। সংযোগে – যুক্ত হয়ে। পরিপুষ্ট – সমৃদ্ধ; বলশালী। নিষ্প্রাণ – প্রাণহীন। প্রাণের স্পন্দনে – প্রাণের হিল্লোলে প্রাণবন্ত। অপূর্ব বিস্ময় – ভীষণ সুন্দর; খুব ভালো। ঐশ্বর্য – মূল্যবান সম্পদ। অনুচ্চারিত – যা উচ্চারিত হয়নি; অপ্রকাশ্য; সুপ্ত। প্রযোজ্য – যা ব্যাবহারিক; ফলপ্রসূ। আপাতদৃষ্টিতে – হঠাৎ করে; ক্ষণিক দেখায়। প্রচ্ছন্ন – সুপ্ত; অপ্রকাশিত। সর্বদর্শী – সব কিছু যিনি দেখতে পান; সমস্ত যাঁর নজরে আসে। এড়াতে – এড়িয়ে যেতে; উপেক্ষা করতে। সেরেস্তা – দফতর; অফিস। বৃহত্তম – খুব বড়ো। অনভিজ্ঞ – যার অভিজ্ঞতা কম। টোল – সংস্কৃত পাঠশালা; চতুষ্পাঠী। বহুভাষাবিদ – নানা ভাষায় দক্ষ বা অভিজ্ঞ। সর্বাগ্রগণ্য – সবার চেয়ে অগ্রগণ্য; মান্য ব্যক্তি। সংস্কৃতজ্ঞ – সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত। সাধুসন্ত – সাধক ও ধার্মিক; ভক্ত। বাণী – অমৃতবচন; সমাজহিতে প্রযোজ্য সদুপদেশ। বিস্মৃতপ্রায় – যা ভুলে যাওয়া হয়েছে; যা মানুষ মনে রাখেনি। পুনরুজ্জীবিত – পুনরায় জাগিয়ে তোলা; মানুষের স্মৃতিতে নিয়ে আসা। অনুপ্রেরণায় – উৎসাহে নির্দেশনায়। প্রাণপণে – সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সাধ্যে – ক্ষমতায়।
চতুর্থ অনুচ্ছেদ –
যাচাই – পরীক্ষা করা। রীতি – নিয়ম; পদ্ধতি। দৈনন্দিন – নিয়মিত; প্রতিদিনের। উদ্বৃত্ত – বাকি থাকে যা; প্রয়োজনের অতিরিক্ত। পনেরো আনা – এক টাকার যোলো ভাগের এক ভাগকে আনা বলে। পনেরো আনার অর্থ বেশিরভাগ বা প্রায় সবটাই। আটপৌরে – অষ্টপ্রহর ব্যবহারের উপযোগী; যা সবসময় ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালি – গার্হস্থ্য সংক্রান্ত; ঘর-সংসারের কাজ। সম্বল – সামর্থ্য; ক্ষমতা। মহল্লা – মহল। আমিন – জমি জরিপ বা মাপার কাজে নিযুক্ত জমিদারের কর্মচারী। সসংকোচে – সংকোচের সঙ্গে; দ্বিধার সঙ্গে। পান্ডুলিপি – লেখার খসড়া। বাক্যালাপ – কথা বলা; বাক্য বিনিময়। সহস্র প্রণালী – নানাবিধ পন্থা বা নিয়মকানুন। হস্তে অর্পণ – হাতে তুলে দেন। অবসরে – অবকাশে।
পঞ্চম অনুচ্ছেদ –
কর্মনিষ্ঠা – কাজের প্রতি গভীর মনোযোগ বা কাজে গভীর উৎসাহ। অতিক্রান্ত – সময় কেটে যাওয়া; সময় অতিবাহিত হওয়া। উৎসাহ – উদ্দীপনা। উদ্দীপনা – কাজ করার আন্তরিক প্রেরণা। তৎক্ষণাৎ – সঙ্গে সঙ্গে। নম্রহৃদয়ে – বিনয় সহকারে; অবনত হয়ে। নতমস্তকে – কবির আদেশ শিরোধার্য করে; রবীন্দ্রনাথের কথাকে মান্যতা দিয়ে। শিরোধার্য – শির বা মাথায় ধারণ করা; অবনত হয়ে মেনে নেওয়া। আর্থিক অনটন – আর্থিক টানাটানি বা অর্থকষ্ট। সংকলন – সংগ্রহ; অভিধান রচনার জন্য তথ্যসংগ্রহ। ক্লেশ – কষ্ট পীড়াদায়ক। অবিলম্বে – দেরি না করে; তাড়াতাড়ি। উদ্যোগী – তৎপর হলেন। আবেদনক্রমে – আবেদনের ভিত্তিতে। বিদ্যোৎসাহী – বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহী; শিক্ষা সম্পর্কে যার উৎসাহ আছে। বৃত্তি – একপ্রকার মাসিক বেতন; উপজীবিকা থেকে পাওয়া পারিশ্রমিক। ধার্য – নির্ধারণ। গৌরবের কথা – গর্বের কথা; অহংকারের কথা। মহানুভবতা – মহাত্মার ভাব, উদার ও মহৎ মানুষের মনোভাব। কৃতজ্ঞচিত্তে – উপকারীর প্রতি সশ্রদ্ধ মনে। স্মরণ করেছেন – মনে রেখেছেন। উপযাচক – যিনি স্বেচ্ছায় অন্যের উপকারে নিয়োজিত হন; কারো আহ্বানের অপেক্ষা না করে যে পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়। মুদ্রণকার্য – ছাপার কাজ। স্বহস্তে – নিজ হাতে। অর্ঘ্য – পূজার উপকরণ; কাউকে দেবতা জ্ঞান করে সশ্রদ্ধচিত্তে কিছু দেওয়া। অর্পণ – শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছু দেওয়া। করুণ উক্তি – বেদনাপূর্ণ উচ্চারণ। প্রেরণাদাতা – প্রেরণা বা উৎসাহ যিনি দেন। অভীষ্ট – ইচ্ছা; বাসনা; আকাঙ্ক্ষা। ভবিষ্যদ্বাণী – ভবিষ্যতে কী হবে তার জন্য আগাম কিছু বলে দেওয়া। অভিপ্রেত – ইচ্ছা; মনোবাসনা; যা বিশেষভাবে কাঙ্ক্ষিত। জীবননাশের শঙ্কা – মৃত্যুভয়।
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ –
সনে – বছরে; বঙ্গাব্দে। সামর্থ্য – ক্ষমতা। পরিবর্ধন – তথ্য সংযোজন; অভাব দূর করা। যৎকিঞ্চিৎ – অতি সামান্য। সম্বল – ক্ষমতা; সামর্থ্য। অনুরাগী – অনুরাগ বা ভালোবাসা যাদের আছে। নিয়মিত গ্রাহক – (অভিধান) ক্রয়ের একনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। আনুকূল্য – আন্তরিক সাহায্য বা সহযোগিতা।
সপ্তম অনুচ্ছেদ –
অত্যুজ্জ্বল – অত্যন্ত উজ্জ্বল; খুব ভালো। অভীষ্ট কার্য – যে কাজ প্রার্থিত; যা করতে চাওয়া হয়। লৌকিক পুরস্কার – যে পুরস্কার বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে দেওয়া হয়। স্বর্ণপদক – সোনার মেডেল। আশ্রমিক সংঘ – শান্তিনিকেতনের আশ্রমের বাসিন্দাদের সমিতি। ষোড়শোপচারে – ষোলো রকম অর্ঘ্য সহযোগে পূজা দেওয়া; এখানে হরিচরণকে যথাবিধিমতে সম্মাননা জ্ঞাপন। জ্ঞাপন – জানানো; অবগত করা।
অষ্টম অনুচ্ছেদ –
বিশেষজ্ঞ – বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি; ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি। ঘাটতি – কমতি; অভাব। সাহিত্য অকাদেমি – এটি একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। মূলত ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকে উৎসাহিত এবং তার মানোন্নয়নের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হয়। সাহিত্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ। পুনর্মুদ্রণ – পুনরায় ছাপা বা মুদ্রিত করা। পুনর্মার্জনা – পুনরায় পরিমার্জনা বা পরিবর্ধন করা।
নবম অনুচ্ছেদ –
অনতিপ্রশস্ত – খুব চওড়া নয় এমন। প্রকোষ্ঠে – ছোটো ঘরে। নিবিষ্ট মনে – মনোযোগ সহকারে।
দশম অনুচ্ছেদ –
চৌপদী – চারটি পঙ্ক্তিতে রচিত কবিতা। মগ্ন – মনোযোগী। গরতে – গর্তে। শব্দ-অবধি-জলে – শব্দসমুদ্রে। সমুদ্রে যেমন অগণিত জলকণা থাকে, তেমনি শব্দসমুদ্রের কল্পনা করে বলা হয়েছে সেখানেও অনেক শব্দ ও অর্থ রয়েছে যা সংগ্রহে হরিচরণ মগ্ন ছিলেন। মুঠাচ্ছ – মুঠো ভরে তুলে নিচ্ছ। অরথে – অর্থে; শব্দের মানে। বারিধি – সমুদ্র। নিবিষ্ট চিত্ত – মনোযোগী হৃদয়। আভিধানিক – যিনি অভিধান রচনা করেন।
একাদশ অনুচ্ছেদ –
পূর্ববৎ – আগের মতো। অভিনিবিষ্ট – মনোযোগী।
দ্বাদশ অনুচ্ছেদ –
সান্ধ্যভ্রমণ – সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণ। ক্ষীণদৃষ্টিবশত – চোখে কম দেখার জন্য। কুশলবার্তা – ভালোমন্দের খবরাখবর নেওয়া। দেহরক্ষা – মারা যাওয়া; পরলোকগমন করা। ‘দি ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার’ – ‘গিবন’ রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। গ্রন্থনামের অর্থ-রোমান সাম্রাজ্যের আক্রমণ এবং পতন। অবসাদের ভাব – বিষণ্ণ; ক্লান্তি। মগ্ন ছিলেন কাজে মনোযোগী ছিলেন। কর্মাবসানে – কাজশেষে। প্রসন্নচিত্ত – হৃষ্ট মনে; সন্তোষ। প্রশান্তি – শান্ত ও সমাহিত ভাব। বিচলিত – চঞ্চল।
আজকের এই আর্টিকেলে অষ্টম শ্রেণির বাংলা বিষয়ের ত্রিংশ অধ্যায় ‘হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’-এর বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় প্রায়শই আসে, তাই এই নিবন্ধটি আপনার প্রস্তুতির জন্য খুবই উপকারী হবে বলে আশা করছি। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা আরও সহায়তার প্রয়োজন হয়, টেলিগ্রামে আমার সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। এছাড়া, এই পোস্টটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না, যাতে তারাও উপকৃত হতে পারে। ধন্যবাদ!


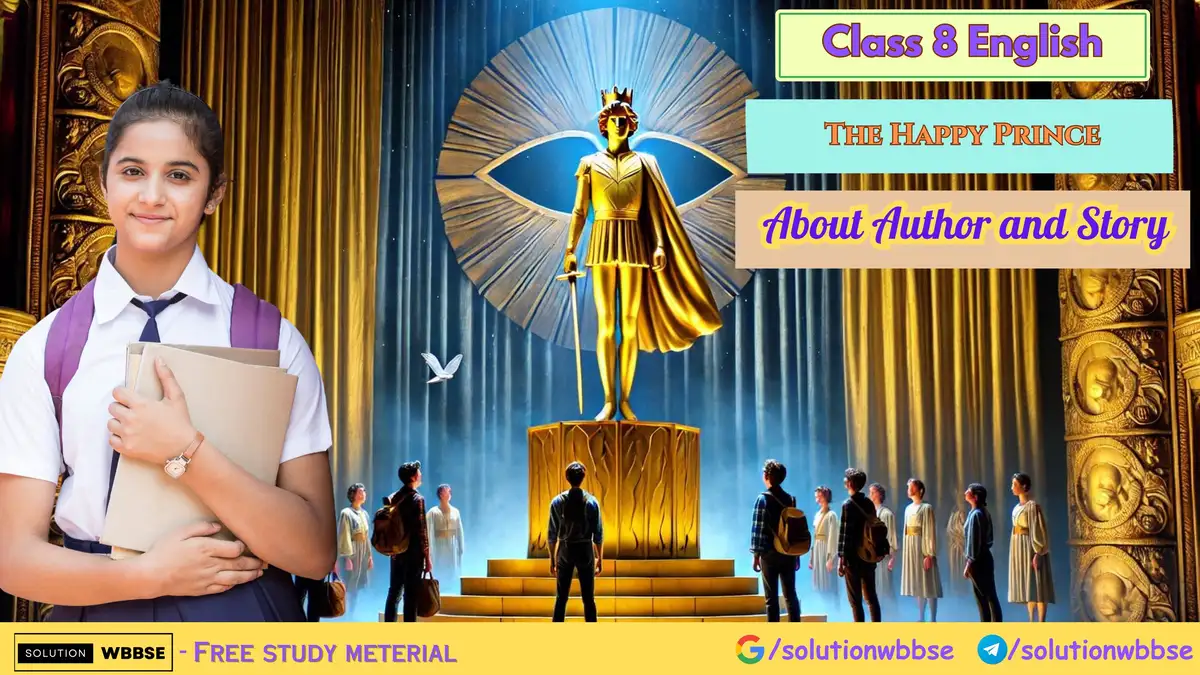
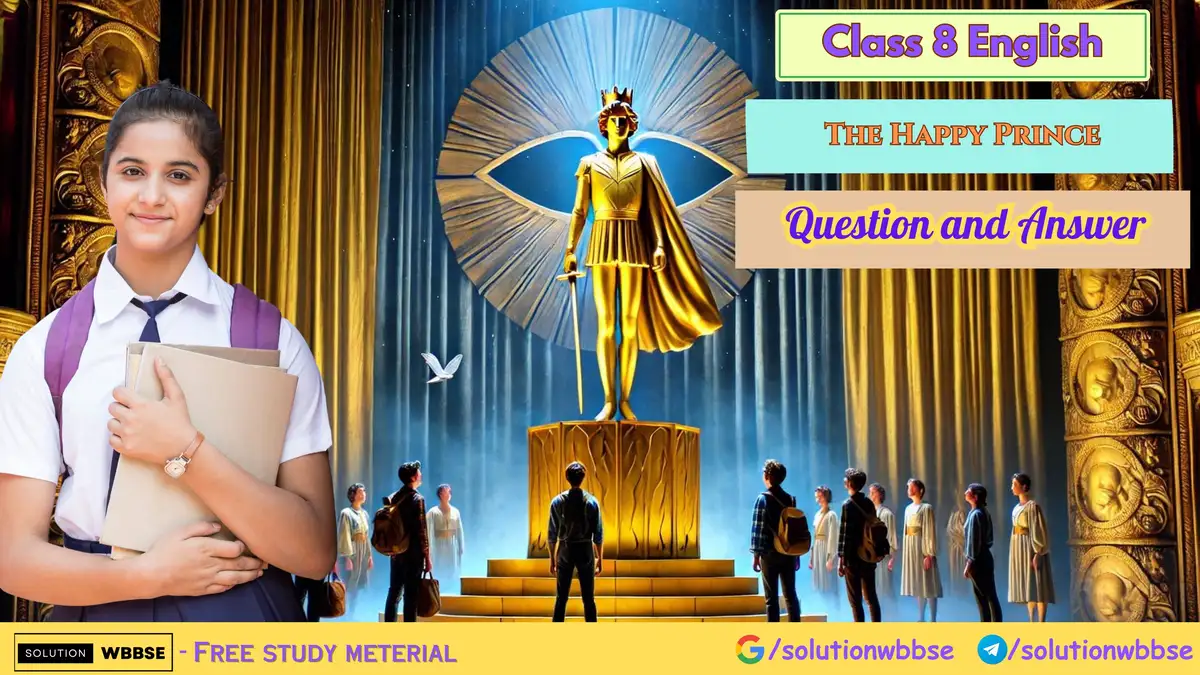
মন্তব্য করুন