আজকের এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের প্রথম পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ -এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নোত্তরগুলো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নবম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত আসে।
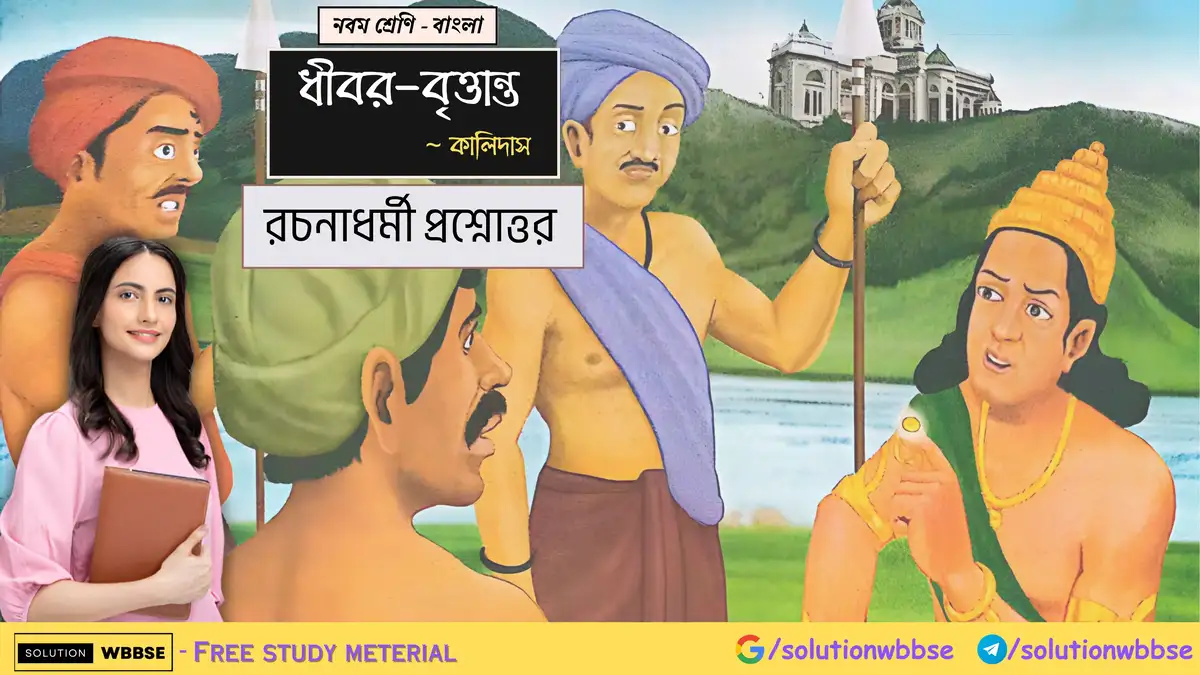
‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
ভূমিকা – নামকরণ যে-কোনো সাহিত্য নির্মিতিরই একটি প্রয়োজনীয় অংশ। বলা যেতে পারে, রচনাটি প্রাথমিকভাবে নামকরণ বা শিরোনামের কারণেই পাঠক মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠক নামকরণের মাধ্যমে রচনাটির বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। নামকরণ রচনাটিকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রতিটি সাহিত্যে নামকরণ উল্লেখযোগ্য বিষয়। সাধারণত কোনো ঘটনা, চরিত্র, বিষয়, বিশেষ ব্যঞ্জনা বা লেখকের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে নামকরণ করা হয়।
বিষয়কেন্দ্রিক নামকরণ – আলোচ্য ‘ধীবর বৃত্তান্ত’ পাঠ্যাংশটি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ -এর ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে সংগৃহীত। পাঠ্যাংশের নামকরণ বিষয়কেন্দ্রিক। একজন ধীবরের সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের রাজধানীর নগররক্ষক ও রক্ষীদের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে উক্ত নাট্যাংশে। নাটকের পূর্বকথা থেকে জানা যায় শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের বিবাহের কথা শুনে কণ্বমুনি শকুন্তলাকে নিয়ে রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে শচীতীর্থের জলে শকুন্তলার কাছ থেকে রাজনামাঙ্কিত প্রতীকি আংটিটি পড়ে যায় এবং একটি মাছ তা খেয়ে নেয়। দুর্বাসার অভিশাপে রাজা শকুন্তলাকে ভুলে যান ও অভিজ্ঞান না থাকায় নিজের পরিচয় দিতে ব্যর্থ শকুন্তলা অপমানিত হয়ে ফিরে যায়।
অন্যদিকে আংটি খেয়ে নেওয়া মাছটি ধরা পড়ে একজন ধীবরের জালে। মাছ কেটে আংটি পাওয়া গেলে সামান্য ধীবর তা বিক্রির জন্য নগরে ঘুরতে থাকে। রাজনামাঙ্কিত মহামূল্যের আংটি ধীবরের কাছে দেখে তাকে চোর সন্দেহে নগররক্ষক ও প্রহরীরা ধরে আনেন। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে ব্যর্থ ধীরবকে তার বৃত্তি-জাতি নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহ্য করতে হয়। নগর রক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক আংটি নিয়ে সত্যতা যাচাই করার জন্য রাজার কাছে গেলে জানতে পারে ধীবর নিরপরাধী। আংটি পাওয়া গেলে রাজা ধীবরকে মুক্তি দেন ও সমমূল্যের উপহারে পুরস্কৃত করেন। শাস্তি না পেয়ে পুরস্কৃত ধীবরকে দেখে রক্ষীরা ঈর্ষাণ্বিত হলে উদারমনস্ক ধীবর তার নিজ প্রাপ্য থেকে অর্ধেক দিয়ে দেন। সত্যবাদী, সৎ ধীবরের আচরণে খুশি হয়ে রাজশ্যালক তাকে প্রিয় বন্ধুর মর্যাদা দেন।
নামকরণের সার্থকতা – চোর সন্দেহে ধৃত ও পরে রাজার দ্বারা পুরস্কৃত ধীবর আলোচ্য পাঠ্যাংশের নায়ক ও মুখ্য চরিত্র। রাজনামাঙ্কিত আংটি নিয়ে নাটকটি শুরু হয়েছিল এবং নাটকের শেষে তা পুনরায় রাজার কাছে ফিরে যায় ধীবরের মাধ্যমে। ধীবরের সত্যবাদী, সৎ ও উদারমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধীবরকে কেন্দ্র করে নাট্যদৃশ্য আবর্তিত হয়। অতএব বলা যেতে পারে আলোচ্য নাটকটির বিষয়কেন্দ্রিক নামকরণ নিঃসন্দেহে যথার্থ ও সুপ্রযুক্ত হয়েছে।
‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশ অবলম্বনে ধীবর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।
ধীবরের পরিচয় – সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাস বিরচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ কাব্যনাটকের অনূদিত ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশের প্রধান চরিত্র একজন ধীবর বা জেলে। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে নাট্যাংশটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে গড়ে উঠেছে। নাটকের সূচনাতে দেখা যায় রাজনামাঙ্কিত দুর্মূল্যের আংটি চুরির অভিযোগে ধৃত ধীবর পেশায় মৎসজীবি। এই ব্যক্তি শত্রুাবতারে বাস করে। চোর সন্দেহে তাকে আটক করেন নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক ও নগররক্ষীদ্বয়।
বিনয়ী – আলোচ্য নাটকে ধীবর একজন সাধারণ মানুষ। তাই ঊর্ধ্বতন নগররক্ষক ও রক্ষীদের সঙ্গে কথোপকথনে সে বিনয়ভাব বজায় রেখেছে। মিথ্যে চোর সন্দেহে বারবার অপমানিত-লাঞ্ছিত হয়েও রাজশ্যালক বা রক্ষীদের অসম্মান করেনি ধীবর।
সত্যবাদী – ধীবর দরিদ্র হলেও সে সৎ, সত্যবাদী। মাছের পেট থেকে পাওয়া রাজার নামাঙ্কিত আংটি বিক্রি করতে গিয়ে সে রাজশ্যালক ও রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে। চোর অপবাদ, নানা লাঞ্ছনা সত্ত্বেও ধীবর সরলকণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বারবার জানিয়েছে সে চুরি করেনি। তার কথায় সততা লক্ষ করে রাজশ্যালক আংটির বৃত্তান্ত শোনেন এবং রাজার কাছে তা যাচাই করতে যান। পরবর্তীকালে ধীবরের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। আবার বিচারে যুক্তি পেয়ে ‘দিন আনি দিন খাই’ শ্রেণির ধীবর অকপট বলেছে – “আজ আমার সংসার চলবে কীভাবে?” দরিদ্র জেলে তার জীবন সমস্যা এই বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে। আবার পারিতোষিকের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভোলেনি যে।
পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল – জাল বড়শি নিয়ে মাছ ধরাই ধীবরের পেশা। নিজের এই সামান্য পেশার প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা বোধ ছিল তার। তাই রাজশ্যালক যখন তার পেশা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিল আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ধীবর প্রতিবাদ করে বলেছে – মানুষের জন্মগত বৃত্তি ঘৃণ্য হলেও তা পরিত্যাগ করা অনুচিত। সে আরও বলেছে যে, তার বৃত্তি প্রাণীহত্যা হলেও দয়াপরায়ণ ব্রাহ্মণও যজ্ঞের প্রয়োজনে নির্দয়ভাবে পশুবধ করেন।
উদার মানসিকতা – উর্দ্ধতন রাজরক্ষীদের কাছে ব্যঙ্গ-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেও ধীবর তার প্রাপ্ত পারিতোষিকের অর্ধেক অংশ তাদের দিয়েছে। যে রক্ষীরা বিনাদোষে তার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল নিচু শ্রেণির ধীবর প্রতিহিংসা বজায় না রেখে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। বন্ধুত্বের আহ্বান জানিয়েছে তার আচরণে।
‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশ অবলম্বনে রাজশ্যালক চরিত্রটি আলোচনা করো।
পরিচয় – সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাসের রচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ কাব্যনাটকের অনূদিত নাট্যাংশ ‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে রাজশ্যালক একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। রাজা দুষ্মন্তের রাজধানী সুরক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন রাজার শ্যালক। আলোচ্য নাট্যাংশে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। নাট্যাংশের শুরুতে দেখা যায়, দুই রক্ষীর সহায়তায় রাজদ্রব্য চুরির অপরাধে রাজশ্যালক ধীবরকে বন্দি করে এনেছে।
নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক চরিত্রটি বিচক্ষণ ও দায়িত্ব সচেতন। চোর অভিযোগে ধৃত ধীবরকে আত্মপক্ষ সমর্থনে বারবার বাধা দেওয়া হচ্ছিল দেখে রাজশ্যালক বলেন – “একে পূর্বাপর সব বলতে দাও। মধ্যে বাধা দিয়ো না।” বিচক্ষণ নগররক্ষক ধীবরের কথার সত্যতা যাচাই করতে আংটি নিয়ে রাজার কাছে গিয়েছিলেন। দায়িত্ব সচেতন এই ব্যক্তি যেমন ধৃতের জবানবন্দি সচেতনতা ধৈর্য্য নিয়ে শুনেছেন তেমনি বিচারের পর বন্দিকে সম্মানজনক মুক্তি দিয়েছেন। বাকি রক্ষীদের মতো রাজার আদেশের পূর্বে শাস্তি নিয়ে অলীক কল্পনা করেননি।
রসিক ও অহংকারী – রাজশ্যালক চরিত্রটিতে স্থূল রসিকতাবোধ লক্ষ করা যায়। মৎসজীবি ধীবরের পেশা নিয়ে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন – “তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখছি।” পদমর্যাদায় গর্বিত রাজশ্যালক অহংকারের সুরে নিচুশ্রেণির ধীবরকে জাত নিয়েও তাচ্ছিল্য করেছেন – “… এর গা থেকে কাঁচা মাংসের গন্ধ আসছে। এ অবশ্যই গোসাপ খাওয়া জেলে হবে।”
তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা – ধীবরের কাছ থেকে আংটি নিয়ে সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলেন রাজশ্যালক। আংটি পেয়ে স্বভাবগম্ভীর রাজার যে ক্ষণিক বিহ্বলতা তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তিনি। এর মধ্যে দিয়ে রাজশ্যালকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।
মহানুভবতা – রাজশ্যালক চরিত্রটি পূর্ণতা পায় নাট্যাংশের শেষ পর্বে। রাজাদেশে ধীবরকে রাজার দেওয়া পুরস্কারসহ মুক্তি দিয়েছিলেন নগররক্ষক। প্রথমে সুনজরে না দেখলেও ধীবরের সততা, মাজির্ত আচরণ তাকে প্রভাবিত করেছিল। নানাভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেও উদার ধীবর যে রক্ষীদের প্রতি প্রতিহিংসা বজায় রাখেনি, বরং তাদের অর্ধেক উপহার দিয়েছে তা রাজশ্যালককে মুগ্ধ করেছিল। তাই মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে জাত্যভিমানী নগররক্ষক সামান্য ধীবরকে ‘বিশিষ্ট প্রিয়বন্ধু’ বলে গ্রহণ করেছে।
‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশ অবলম্বনে রক্ষীদ্বয় অর্থাৎ জানুক ও সূচক চরিত্র বিশ্লেষণ করো।
পরিচয় – সংস্কৃত নাট্যকার কালিদাস -এর অনুবাদিত নাট্যাংশ ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে নগররক্ষায় নিযুক্ত রক্ষীদ্বয় জানুক ও সূচকের চরিত্ররেখা যথেষ্ট স্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যময়। তারা রাজশ্যালকের দুই অনুচর ও রাজকর্মচারী। প্রভুভক্ত দুই রক্ষী প্রভুর নির্দেশ মেনে বলেছে – “তা আপনি যা আদেশ করেন।” রাজকার্যে এদের কোনো শৈথিল্য নেই।
প্রথম রক্ষী – ধীবর যতবারই নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে চেয়েছে ততবারই তাকে নানানভাবে ব্যঙ্গ, অপমান, কটূক্তি ও হেনস্তা করেছে দুই রক্ষী। প্রথম রক্ষী ধীবরকে ব্যঙ্গাত্মক শ্লেষে ‘সদ্ ব্রাহ্মণ’ বলে অপমান করে। আবার ধীবরকে হত্যা করার পৈশাচিক লালসায় বলেছে – “একে মারার আগে এর গলায় যে ফুলের মালা পরানো হবে, তা গাঁথতে আমার হাত দুটো (এখনই) নিশপিশ করছে।” ধীবরকে পীড়া দিতে পারবে ভেবে মানসিকভাবে বেশ উৎফুল্ল হয়েছে।
দ্বিতীয় রক্ষী – দ্বিতীয় রক্ষীও ধীবরকে ‘ব্যাটা বাটপাড়’, ‘গাঁটকাটা’ ইত্যাদি অশোভন সম্বোধন করে। ধীবরের শাস্তি হিসেবে তাকে শকুনি কিংবা কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে ব’লে ভয় দেখায়। রাজার আদেশ তার মনের ইচ্ছা পূরণে বাধা হলে সে বলে- “এই জেলে যমের বাড়ি গিয়ে আবার ফিরে এল।” ধীবরকে শাস্তি দেওয়ার আনন্দে সেও উদ্গ্রীব ছিল।
উপসংহার – ধীবরের প্রতি দুই রক্ষী কতটা নিষ্ঠুর, আক্রোশপরায়ণ ও অমানবিক তাদের আচরণেই তার প্রকাশ ঘটে। রাজা আংটির সমমূল্য পারিতোষিক ধীবরকে দিলে রক্ষীদ্বয় মন থেকে তা মেনে নিতে পারেনি। তাই সূচক বলেছে ধীবরকে যেন শূল থেকে নামিয়ে একেবারে হাতির পিঠে বসানো হল। আবার পারিতোষিকের অর্ধেক ভাগ ধীবরের কাছ থেকে নিতেও তাদের সংকোচ হয়নি। আলোচ্য নাট্যাংশে দুই রক্ষীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে রাজকার্যে নিযুক্ত রাজকর্মচারিদের মনে বাসা বেঁধে থাকা লোভলালসার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তাই চরিত্র দুটি জীবন্ত হয়ে ওঠে।
‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে সমাজের যে খণ্ডচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা আলোচনা করো।
নগর সভ্যতার ছবি – সংস্কৃত মহাকবি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ কাব্যনাটকের সংক্ষিপ্ত অনূদিত নাট্যাংশ ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাটকে সমাজের কিছু ছবি খণ্ড খণ্ডভাবে ধরা পড়েছে। সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ, তাই তার প্রেক্ষাপটে সমাজজীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়। নাটকের পূর্ব অংশে যেমন তপোবনের শান্ত, স্নিগ্ধ, হিংসা-দ্বেষহীন ছবি ধরা পড়েছে, অন্যদিকে তেমনই নগরকেন্দ্রিক সমাজচিত্র নাটকের বিষয়বস্তু অংশে স্থান পেয়েছে। তপোবনে শকুন্তলা ও তার সখীদের রেখে মহর্ষি কণ্ব পরম নিশ্চিন্তে তীর্থে যান। ঋষি দুর্বাসা দ্বারা শকুন্তলা অভিশপ্ত হলে সখী প্রিয়ংবদার কাতর অনুরোধে তা ফিরিয়ে নিতে ঋষি বাধ্য হন। আবার মহর্ষি কণ্ব তীর্থ থেকে ফিরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর আয়োজন করেন দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো। তপোবনের ঘরোয়া সামাজিক চিত্র এখানে সুস্পষ্ট।
আবার নগরকেন্দ্রিক সমাজের শাসন, সমাজব্যবস্থা, মানসিক প্রবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে নাট্যাংশের মূল পর্বে। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলে যান, এখানে রাজার নির্লিপ্ততা, নারী অবমাননা দৃষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে নাটক পর্বে সাধারণ প্রজা ধীবরের প্রতি যে অভিযোগই থাকে রক্ষীদের দ্বারা প্রাপ্ত নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ, রাজশ্যালকের অহংকারী মনোভাব নগরসভ্যতার যথার্থ চিত্র ধরেছে। সমাজব্যবস্থায় নিম্নবিত্তের মানুষের প্রতি যে অবহেলা-বিদ্বেষতা ধীবর ও রক্ষীদের আচরণে স্পষ্ট। নির্দোষ ধীবরের মুক্তি ও পুরস্কৃত হওয়ায় শাসনব্যবস্থার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। আবার রক্ষীদের অকারণ হিংসা-লোভ সভ্য সমাজের মানুষের মানসিক প্রবৃত্তিকে দেখিয়েছে। আলোচ্য নাট্যাংশে ধীবরের মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনভাবনা-বাস্তবাদিতা প্রকাশ পেয়েছে।
অতএব দেখা যাচ্ছে, একটি নাটকের মধ্যে আমরা দুই ধরনের সমাজচিত্রের প্রতিফলন পেয়েছি।
‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের নাট্যরস ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে কতটা প্রকাশ পেয়েছে আলোচনা করো।
ঘনীভূত নাট্যরস – মহাকবি কালিদাস -এর ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। এখানে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে নাট্যদৃশ্য স্থাপন, চরিত্রগুলির সংলাপের মধ্যে নাট্যদ্বন্দ্বের চরম বিকাশ ও নাট্যরসের প্রবাহ রয়েছে। তবে পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত অংশে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখা বেশ কিছু ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। মূল নাটকের নামচরিত্র শকুন্তলার প্রসঙ্গ দিয়েই উক্ত নাট্যাংশের সূচনা হয়েছে এবং শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্তের পরিচয়সূচক একটি আংটি এখানে নির্ণায়কের ভূমিকা নিয়েছে। মূল নাটকের সূত্র ধরেই এখানে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ এবং আংটি পরিয়ে দেবার মধ্যে দিয়ে নাট্যরস দানা বাঁধতে থাকে। পতিগৃহে যাত্রাকালে শচীতীর্থে স্নানের পর অঞ্জলি দিতে গিয়ে ওই আংটি জলে পড়ে যায়। প্রবল নাটকীয়তায় আংটিটি একটি রুই মাছের পেট থেকে এক ধীবরের হাতে আসে এবং নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক ও তার দুই অনুচর রক্ষী ধীবরকে রাজনামাঙ্কিত আংটি নিয়ে নগরে দেখতে পেয়ে আটক করে।
দেখা যায়, ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ -এর কাহিনিনির্যাস এই নাট্যাংশে আংটির প্রসঙ্গে ঘনীভূত হয়েছে। ওই আংটি রাজশ্যালক রাজাকে দেখালে রাজার হৃদয় পরিবর্তন হয়। বলা যেতে পারে শকুন্তলার ওপর থাকা অভিশাপ খণ্ডিত হয় এবং বিস্তৃত ঘটনা স্মরণে এলে রাজা দুষ্মন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েন। ঘটনাক্রমে ধীবর নির্দোষ প্রমাণিতহয় ও পুরস্কারসহ তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত এই নাট্যাংশের কাহিনির মধ্য দিয়ে মূল নাটকের সুখসমাপ্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজার স্মৃতি ফিরে আসা শকুন্তলার সঙ্গে তার মিলনের সূচক। তাই বলা যায় নাট্যাংশের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের নাট্যরস প্রকাশ পেয়েছে।
‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশের সংলাপ-ভাষা ও উপমা প্রয়োগে নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় দাও।
ভূমিকা – সংলাপ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নাটকের চরিত্রগুলির পরিচয় প্রকাশ পায়। ভাষা ব্যবহারে সংলাপ নির্মিত হয় আর ঘটনার আবর্তে সংলাপ হয়ে ওঠে নাটকের প্রাণ। মহাকবি কালিদাস রচিত ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নামক অনুবাদ নাট্যাংশের সংলাপ যথেষ্ট নাটকীয় ও প্রাণবন্ত। ঘটনা ও চরিত্র নির্বিশেষে সংলাপের পরিবর্তন হয়। আলোচ্য নাট্যংশে রাজশ্যালক, দুই রক্ষী ও ধীবরের সংলাপ ব্যবহারে তাই ভিন্নতা দেখা যায়।
রাজশ্যালকের সংলাপ – নগর সুরক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালকের সংলাপে পদমর্যাদার অহংকার ও শ্লেষ দেখা যায় – “তা তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখছি” বা “… এ অবশ্যই গোসাপ খাওয়া জেলে হবে।” আবার ধৃতের জবানবন্দি ধৈর্য্য নিয়ে শোনা বা রাজার আদেশের প্রতি নিষ্ঠা এই বৈশিষ্ট্যগুলি তার সংলাপের মাধ্যমে সম্পাদক দেখিয়েছেন। শেষপর্বে নির্দোষ ধীবরের উদারতা দেখে রাজশ্যালক তাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে তাও নাট্যকার সংলাপে প্রকাশ করেছেন। রাজশ্যালকের সংলাপে আভিজাত্য, মার্জিত রুচির প্রভাব রয়েছে।
রক্ষীদ্বয়ের সংলাপ – দুই নগররক্ষী রাজকর্মচারী হলেও তাদের শিক্ষার মান যথেষ্ট ছিল না বলেই অনায়াসে ধীবরের উদ্দেশ্যে তারা ‘চোর’, ‘বাটপাড়’, ‘গাঁটকাটা’ প্রভৃতি মন্তব্য করেছে। নাট্যকার এই চরিত্রদ্বয়ের মুখে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করে চরিত্রের নীতিহীনতা, নির্দয়তাকে প্রকাশ করেছেন। ধীবরের মুক্তি ও পুরস্কার প্রাপ্তি দেখে তাদের ঈর্ষাণ্বিত সংলাপ ব্যবহারে লোভ-লালসা ফুটে উঠেছে।
ধীবরের সংলাপ – নিরপরাধ ধীবর একাধিকবার দৃঢ়তার সঙ্গে সত্য প্রকাশ করেছে রক্ষীদের কাছে। তার ক্রোধহীন অকপট উচ্চারণ দেখা যায় – “এখন আমাকে মারতে হয় মারুন …” সংলাপের মধ্যে। আবার নিজগুণে পারিতোষিক পেয়ে কৃতজ্ঞ ধীবর লালসার দমন করে তা ভাগ করে নিয়েছে দুইরক্ষীর সঙ্গে। ধীবরের এই ধৈর্যশীলতা তার সংযমী সংলাপ উচ্চারণে প্রকাশ পেয়েছে।
উপমা প্রয়োগ – উপমা প্রয়োগেও নাট্যকার চরিত্রানুযায়ী যথার্থতা অবলম্বন করেছেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দয়াশীল মনের পাশাপাশি যজ্ঞীয় পশুবধের নির্দেশ তার স্বভাববিরুদ্ধ। ধীবর নিজের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতায় এই উপমা ব্যবহার করেছে। আবার তার মুক্তির পর ব্যঙ্গ করে রক্ষীরা কখনও বলেছে – “এই জেলে যমের বাড়ি গিয়ে আবার ফিরে এল।” কখনও রাজানুগ্রহে ঈষাণ্বিত হয়ে বলেছে – “… এ যে শূল থেকে নামিয়ে একেবারে হাতির পিঠে চড়িয়ে দেওয়া …।” আলোচ্য নাট্যাংশে সংলাপ ব্যবহারে ও উপমা প্রয়োগে নাট্যকার দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন।
রাজার শ্যালকের হাতে ধরা পরার পর থেকে রাজদরবারে পারিতোষিক লাভ পর্যন্ত ধীবরের মানসিক যন্ত্রণার এক কল্পচিত্র অঙ্কন করো।
ধৃত ধীবর – সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম মহাকবি কালিদাস রচিত ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নামক অনুবাদ নাট্যাংশে ধীবর হল নামচরিত্র। চোর অপবাদ নিয়ে, নানা টানাপোড়েনের মধ্যে তার অস্তিত্বই এখানে নাট্যবিষয় হয়ে উঠেছে। সে একজন জেলে, শত্রুাবতারে থাকে, জাল-বড়শি ইত্যাদি দিয়ে মাছ ধরে কোনোমতে সংসার চালায়। এমন একটি অতিসাধারণ মানুষের হাতে একদিন মাছের পেট থেকে একটি রত্নখচিত, রাজনামাঙ্কিত ঝলমলে আংটি এলে সেটি বিক্রির চেষ্টা করতে গিয়ে সে রাজশ্যালকের হাতে ধরা পড়ে। বেশ বোঝা যায় এই অকারণ বন্দিত্ব সে মেনে নিতে পারেনি। দিশাহারা হয়ে অবশেষে আংটি লাভের গল্প রাজশ্যালককে শুনিয়ে, সে বলে, “এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন। কীভাবে এই আংটি আমার কাছে এল-তা বললাম।”
ধীবরের মানসিক যন্ত্রণা – রাজশ্যালক ও রক্ষীদ্বয়ের কথায় ও আচরণে ধীবরের মানসিক যন্ত্রণা বেড়েছে। তারা তাকে অপমানিত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। ধীবর যখন জানায় সে চুরি করেনি, তখন ব্যঙ্গ করে রক্ষী বলে যে, রাজা হয়তো সদ্ ব্রাহ্মণ বিবেচনা করে ধীবরকে আংটিটি প্রদান করেছেন। নিজের জীবিকার বর্ণনা করলে রাজার শ্যালক ধীবরের পেশাকে ‘বেশ পবিত্র’ বলে তাচ্ছিল্য করেছেন। রক্ষীরা বিচারাধীন ধীবরকে ‘চোর’, ‘বাটপাড়’, ‘গাঁটকাটা সম্বোধন করেছে। আবার তাকে ‘গোসাপ খাওয়া জেলে’ বলে রাজশ্যালক অপমান করেছেন। শুধু তাই নয়, তার সামনেই তাকে হত্যার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে বিষয়ে রক্ষীরা আলোচনা করেছে। কিন্তু ধীবরের কথার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর যখন সে মুক্ত হয় তখন সংসার চালানোর চিন্তা করতে থাকলে মহারাজ আংটির অর্থমূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ধীবরকে দান করেন। ঈর্ষাণ্বিত রক্ষীরা রাজার অনুগ্রহকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে বলে – তাকে যেন শূল থেকে নামিয়ে হাতির পিঠে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ থেকে মুক্তি এবং পারিতোষিক পেয়েও নিচুশ্রেণির নিম্নবিত্তের ধীবর ঊর্ধ্বতন রাজকর্মীদের কাছ থেকে একরকম মানসিক যন্ত্রণা পেয়েছে।
‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে রাজশ্যালক ও রক্ষীরা ধীবরের প্রতি প্রাথমিক ব্যবহার করেছিল আলোচনা করো।
অত্যাচারের সূত্রপাত – মহাকবি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের সংক্ষিপ্ত ও অনূদিত অংশ ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ -এর শুরুতেই দেখা যায় নগর রক্ষায় নিযুক্ত রাজ-শ্যালক এবং দুই রক্ষী ধীবরকে পিছমোড়া ক’রে হাত বেঁধে নিয়ে আসে যার মধ্য দিয়ে তাদের নির্দয় নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রকাশ পায়। ধীবর মাছের পেট থেকে রাজার নামাঙ্কিত যে আংটিটি পায় সেটি বিক্রি করার চেষ্টা করলে চোর অপবাদে রক্ষীরা তাকে ধরে আনে কোনো বিচার বিবেচনা ছাড়াই।
রাজশ্যালকের আচরণ – ধীবরটি যে চোর, এ বিষয়ে সন্দেহ না থাকায় রাজশ্যালকও তাকে প্রথমে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছেন। জেলে কায়ক্লেশে মাছ ধরে জীবিকার্জন করে, তা শুনে রাজশ্যালক তার প্রতি শ্লেষ করে বলেছেন – “তা তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখছি।” একজন বিচারাধীন ধৃতের প্রতি যে আচরণ নগরসুরক্ষায় নিযুক্ত কর্মচারী করতে পারে রাজশ্যালক ও তেমন আচরণ করেছে। ধীবর নির্দোষ প্রমাণিত হলে তাঁর আচরণ ও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু রক্ষীদের আচরণে কোনো রূপান্তর লক্ষ করা যায়নি।
রক্ষীদ্বয়ের ‘আচরণ’ – রক্ষীরা নানাপ্রকার প্রশ্নবাণে উত্যক্ত করার পাশাপাশি তার পেশা নিয়েও ব্যঙ্গ করেছে। ‘ব্যাটা চোর’ ‘বাটপাড়’, ‘গাঁটকাটা’ ইত্যাদি অশিষ্ট শব্দ প্রয়োগে ধীবরের প্রতি লাঞ্ছনা করতে একবারও তারা ভাবেনি। ধীবরের কাছ থেকে প্রকৃত কথা না শুনে তারা অভিযুক্ত ধীবরের বিচারপর্ব শেষ হবার আগেই তাকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছে। মৃত্যুর আগেই তার মৃতদেহে মালা পরাবার মতো হীনতা দেখিয়েছে। ধীবর আংটি চুরি করেনি জানালে প্রথম রক্ষী তাকে বলেছে – “তবে কী তোকে সদ্-ব্রাহ্মণ বিবেচনা করে রাজা এটা দান করেছেন?”
কিন্তু রাজার বিচারে ধীবর নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে পুরস্কৃত হলে তারা ঈর্ষাণ্বিত হয়েছে আবার ধীবর সেই পুরস্কারের ভাগ দিলে সেটি নিতেও তারা দ্বিধা করেনি। ধীবরের প্রতি তাদের হীন আচরণ তাদের চরিত্রের কোনো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য স্থাপন করতে পারেনি।
‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে ধীবরটিকে চোর সন্দেহে কারা ধরেছিল? শেষপর্যন্ত ধীবরের কী পরিণতি হয়েছিল?
কারা ধরেছিল – সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাস প্রণীত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের বাংলা অনুবাদ ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে নগররক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত রাজশ্যালক ও দুই রক্ষী ধীবরকে ‘চোর’ সন্দেহে ধরে এনেছিল।
ধীবরকে ধরার কারণ – ধীবর পুরুবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের নাম খোদাই করা একটি সোনার আংটি পেয়ে সেটি বিক্রির উদ্দেশ্যে জনসমক্ষে আসে। অশিক্ষিত ধীবর রাজনামাঙ্কিত আংটির গুরুত্বই জানত না। তাই মাছের পেট থেকে পাওয়া আংটির কারণে ধীবর কোনোভাবেই চোর অভিযুক্ত হতে পারে না। সামান্য ধীবর কীভাবে রাজার আংটি হাতে পেল তা না শুনে তাকে ‘চোর’, ‘গাঁটকাটা’ ইত্যাদি অপমানসূচক কটূক্তি করে রাজশ্যালক ও রক্ষীদ্বয় ধরে আনে।
ধীবরের পরিণতি – ধীবরকে পিছমোড়া করে বেঁধে আনার পর ‘ওরে ব্যাটা চোর’, ‘ব্যাটা বাটপাড়’, ‘গাঁটকাটা’ ইত্যাদি অশালীন মন্তব্য করার পাশাপাশি মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। তার পেশা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন রাজশ্যালক। আবার তাকে ‘গোসাপ খাওয়া জেলে’, বলে নিন্দনীয় কটূক্তিও করেছেন। রাজাদেশের পূর্বে ধীবরকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়ার বাসনা গোপন করতে পারেনি রক্ষীরা। ধীবরকে কীভাবে হত্যা করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করে উল্লসিত হয়েছে তারা। কিন্তু ধীবর নির্দোষ প্রমাণিত হলে রাজা তাকে উপযুক্ত পুরস্কার সহযোগে মুক্তির নির্দেশ দেন। পারিতোষিকের কারণে কৃতজ্ঞ ধীবর নিজের প্রাপ্য থেকে অর্ধেক অংশ রক্ষীদের দিয়ে দেয়। সত্যবাদী ও দৃঢ়চেতা ধীবরের উদারমনস্ক আচরণ রাজশ্যালককে মুগ্ধ করলে তিনি ধীবরকে ‘বিশিষ্ট প্রিয়বন্ধু’র মর্যাদা দেন।
একটি আংটিকে কেন্দ্র করে ঘটনার প্রবাহ যেভাবে আবর্তিত হয়েছে ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশ অবলম্বনে তার বর্ণনা দাও।
আংটিসূত্র – ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশটি মহাকবি কালিদাস লিখিত সংস্কৃত পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ অনূদিত, সংক্ষিপ্ত ও সম্পাদিত নাট্যরূপ। যেখানে দেখা যায় তপোবনে এসে মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে বিবাহ করা এবং তাকে রেখে রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার সময় শকুন্তলাকে রাজার একটি আংটি পরিয়ে দেওয়ার ঘটনা, যা সূচনায় বিশিষ্টতা পায়। আংটিটি রাজ-নামাঙ্কিত, মণিরত্নময় মূল্যবান। এই আংটি-সূত্রই প্রলম্বিত হয়ে নাট্যদৃশ্যের শেষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত, যার মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা রয়েছে।
ধীবরের বন্দিদশা – একটি বহুমূল্য আংটি নাট্যাংশের মূল বক্তব্যকেন্দ্রে অবস্থান করে নাট্যদৃশ্যটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আংটির গুরুত্ব প্রবলভাবে বেড়ে যায় কারণ এটি রাজা ও শকুন্তলার বিবাহ সম্পর্কের একমাত্র নিদর্শন হয়ে পড়ে। কিন্তু ঘটনাক্রমে আংটিটি শকুন্তলার হাত থেকে জলে পড়ে যায় এবং একটি মাছ তা খেয়ে নেয়। এরপর মাছটি জনৈক ধীবরের হাতে ধরা পড়ে। মাছের পেট থেকে ওই আংটি পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই ধীবর তা বিক্রি করে ভাগ্য ফেরাতে উদ্যোগী হয়। ওই ধীবর অবশেষে নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক ও তার দুই সঙ্গী রক্ষীর কাছে ধরা পড়ে বন্দি হয়ে রাজধানীতে আসে। ধীবরের কাছে রাজ-নামাঙ্কিত আংটি রাজশ্যালকের মনে সন্দেহের জন্ম দেয়। ধীবরের আংটিপ্রাপ্তির ঘটনায় অবিশ্বাস্যতা ছিল বলেই রাজশ্যালক স্বয়ং রাজার কাছে যান এবং ঘটনার সত্যতা প্রকাশিত হয়।
ধীবরের মুক্তি – নাট্যাংশের শেষে দেখা যায়, রাজা পুনরায় তাঁর আংটি ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে কোনো এক প্রিয়জনের চিন্তায় তিনি বিহ্বল হয়েছেন। তবে ধীবর শুধুমাত্র এই আংটির কল্যাণে রাজার আদেশে মুক্তি পেয়েছে ও উপযুক্ত পারিতোষিক লাভ করেছে।
“সখীরা মনে করলেন সেই আংটিই হবে ভবিষ্যতের স্মারকচিহ্ন।” – এখানে কোন্ আংটির কথা বলা হয়েছে? সেই আংটি কীভাবে ‘স্মারকচিহ্ন’ হতে পারে? আংটিটি কীভাবে হারিয়ে গিয়েছিল?
যে আংটির কথা বলা হয়েছে – সংস্কৃত সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’-এর অনুবাদ ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে যে আংটির কথা বলা হয়েছে, সেটি হল – তপোবনপালিতা, শকুন্তলার আংটি। রাজা দুষ্মন্ত তপোবনে শকুন্তলাকে বিবাহ করে তাকে রেখে রাজধানীতে ফিরে যাবার সময় শকুন্তলার হাতে পরিয়ে দেন এই আংটি। রাজনামাঙ্কিত এই আংটিটি ছিল মূল্যবান রত্নখচিত।
আংটি যেভাবে স্মারক চিহ্ন হয়ে ওঠে – শকুন্তলাকে বিবাহ করে রাজা দুষ্মন্ত তাকে নিজ নামাঙ্কিত মূল্যবান রত্নখচিত যে আংটি দেন, রাজা ও শকুন্তলার বিবাহ সম্পর্কে সেটি ছিল একমাত্র পরিচায়ক। দুর্বাসা মুনির দেওয়া অভিশাপ অনুযায়ী রাজা শকুন্তলাকে তখনই চিনতে পারবেন যখন কোনো স্মারক বা নিদর্শন শকুন্তলা দেখাবে। শকুন্তলার সখীরা তাই ভেবেছিলেন একমাত্র এই রাজনামাঙ্কিত আংটিই হবে শকুন্তলার পরিচয়জ্ঞাপক নিদর্শন বা স্মারক।
শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের উদ্যোগে পতিগৃহে যাত্রা করেছিলেন তখন পথে শচীতীর্থে স্নানের পর অঞ্জলি দেওয়ার সময় তার হাত থেকে খুলে আংটি হারানো পড়ে যায় রাজনামাঙ্কিত আংটি। এরপর একটি রুই মাছ তা খেয়ে নেয় ও ঘটনাক্রমে আংটিটি জনৈক ধীবরের হস্তগত হয়।
“আপনারা শান্ত হন। আমি এরকম কাজ (অর্থাৎ চুরি) করিনি।” – কার উক্তি? বক্তা কোন্ কাজ করেনি? উক্তিটির মধ্যে দিয়ে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছে?
বক্তা – সংস্কৃত সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের অনূদিত নাট্যাংশ ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ থেকে গৃহীত উদ্ধৃত উক্তিটির বক্তা রাজানামাঙ্কিত মূল্যবান আংটির চুরির অভিযোগে ধৃত ধীবর।
বক্তা যে কাজ করেনি – সাধারণ পেশাজীবী ধীবরটি নানা উপায়ে মাছ ধরে কোনোমতে সংসার চালায়। রাজার নামাঙ্কিত, মণিরত্নময়, বহুমূল্য আংটিটি চুরি করার কাজ সে করেনি।
বক্তা যা বলতে চেয়েছে – নগররক্ষার কাজে নিযুক্ত রাজশ্যালক এবং দুই রক্ষী জানুক ও সূচক একটি বহুমূল্য আংটি চুরির অপরাধে ধীবরকে আটক করেন। তার অবস্থা ‘দিন আনি দিন খাই’। মৎস্যশিকারের অতিসাধারণ উপকরণ জাল, বড়শি ইত্যাদি দিয়ে সে মাছ ধরে কায়ক্লেশে সংসার চালায়। এমন জীবনযাপনকারী ধীবরটি রাজার নামাঙ্কিত রত্নময়, বহুমূল্য আংটিটি পেয়েছিল মাছের পেট থেকে। সে তা চুরি করেনি। দুই রক্ষী তাকে ‘ওরে ব্যাটা চোর’ সম্বোধন করে বলে – “বল্-মণিখচিত, রাজার নাম খোদাই করা এই (রাজার) আংটি তুই কোথায় পেলি?” জিজ্ঞাসাবাদে যে চুরির অপরাধের ভয়ানক শাস্তির ইঙ্গিত ছিল তা ধীবর বুঝেছিল। তাই এই উক্তির মাধ্যমে ধীবর ভয়ভীতি অস্বীকার করে সত্যপ্রকাশের প্রাথমিক চেষ্টা করেছিল।
“ব্যাটা বাটপাড়, আমরা কি তোর জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেছি?” – কার উক্তি? ‘বাটপাড়’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? উদ্ধৃতিটির আলোকে বক্তার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।
বক্তা – সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন কবি কালিদাস -এর ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে এই উক্তির বক্তা হল নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালকের অনুচর দ্বিতীয় রক্ষী জানুক।
‘বাটপাড়’ -এর অর্থ – ‘বাটপাড়’ শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে – লুটেরা বা দস্যু ধরনের লোককে, যে আসলে দুর্বৃত্ত অন্যলোকের জিনিসপত্র লুটে নেয় বা ডাকাতি করে।
বক্তার চরিত্র – রাজনামাঙ্কিত মূল্যবান আংটি চুরির অপরাধে ধৃত ধীবরকে রক্ষী ‘বাটপাড়’ সম্বোধনে যে উক্তি করেছে, তাতে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যরেখা ফুটে উঠেছে। রাজকার্যে নিযুক্ত রক্ষী একজন রাজকর্মচারী। তাই প্রবল এক উন্নাসিকতা ও অহমিকার ভাব তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজপুরুষ, তথা রাজশ্যালকের একান্ত অনুচর এই রক্ষী প্রথম থেকেই ধীবরকে নানাভাবে অপমান করেছে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে ধীবরের বৃত্তি-জাতি নিয়ে রাজশ্যালকের বিদ্রুপে সঙ্গ দিয়েছে। ধীবর যে অপরাধের জন্য ধরা পড়েছে, তা প্রমাণিত না হলেও অভিযোগ গুরুতর। রক্ষী এটা জানত বলেই, ধীবরের উপর ক্রমে মানসিক চাপ বাড়াচ্ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল চাপ দিয়ে সত্যতা স্বীকার করিয়ে নেওয়া। কিন্তু ধৃতের আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে শুধুই লাঞ্ছনা গঞ্জনা করেছে। বারবার যে ‘চোর, ‘বাটপাড়’ ইত্যাদি অশিষ্ট সম্বোধন করেছে। এর থেকে বোঝা যায়, ধৈর্য্য, মানবিকতা বা শিষ্টাচারবোধ প্রায় নেই এই রক্ষীর মধ্যে।
“সূচক, একে পূর্বাপর সব বলতে দাও। মধ্যে বাধা দিয়ো না।” – কার উক্তি? এমন উক্তির কারণ কী? উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তার চরিত্রের কোন্ মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়?
বক্তা – সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের অনূদিত ও সংক্ষিপ্ত অংশ ‘ধীবর বৃত্তান্ত’। এখান থেকে নেওয়া আলোচ্য উক্তির বক্তা নগররক্ষায় নিযুক্ত, রাজপ্রতিনিধি তথা রাজশ্যালক।
এমন উক্তির কারণ – বক্তা নগর সুরক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক তার অনুচর নগররক্ষী সূচককে উক্তিটি করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন চুরির অভিযোগে ধৃত ধীবরকে রক্ষীরা জেরা করার ভঙ্গিতে শুধুই অপমান করেছে। তাকে নিজের সমর্থনে কিছু বলতে না দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে চলেছে। এই উক্তির মধ্যে দিয়ে তিনি ধীবরকে বিভ্রান্ত না করে ভয়হীনভাবে তাকে নিজের কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলেন।
বক্তার মানসিকতা – উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তার কর্তৃত্ব সুলভ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি রাজকার্যে অভিজ্ঞ। শাসনপদ্ধতিতে ধৃতের জবানবন্দি শোনাও যে জরুরি তা তিনি জানতেন। চুরির অপরাধে ধৃত সাধারণ খেটে খাওয়া ধীবরের কাছে মহামূলবান আংটি কীভাবে এসেছে তা জানাই ছিল রাজশ্যালকের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু রক্ষীদ্বয়ের প্রয়োজনের অতিরিক্ত নির্যাতন ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তায় সত্যি জানা যাবে না ভেবে বিচক্ষণ নগররক্ষক সূচককে বাধা দিতে বারণ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় রাজশ্যালক কর্তৃত্বপরায়ণ হলেও তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণ।
“তা তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখছি।” – উদ্ধৃতাংশের বক্তা কে? কাকে উদ্দেশ করে এই উক্তি? এই উক্তির মধ্যে যে শ্লেষ আছে কাহিনি অবলম্বনে তা লেখো।
বক্তা – মহাকবি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের সংক্ষিপ্ত ও অনূদিত নাট্যাংশ ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ থেকে গৃহীত উদ্ধৃতিটির বক্তা নগররক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত রাজশ্যালক।
যাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে – রাজশ্যালক ও তার দুই অনুচর ধীবরকে ‘চোর’ সন্দেহে নিষ্ঠুরভাবে ধরে আনার পর নানান প্রশ্ন করতে থাকে। একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ধীবর তার জীবিকা নির্বাহের কথা বললে রাজশ্যালক ব্যঙ্গ করে ধীবরের উদ্দেশে উদ্ধৃত শ্লেষাত্মক উক্তিটি করেন।
শ্লেষাত্মক উক্তি – রাজশ্যালক ও দুই রক্ষী ধীবরকে ‘চোর’ অপবাদ দিয়ে ধরে এনে নানান কটূক্তিপূর্ণ উক্তি ও প্রশ্নবাণে ধীবরকে উত্তেজিত করে। ধীবর যতবার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে চেয়েছে ততবারই তার সঙ্গে অমানবিক আচরণ ও অশালীন উক্তি করেছে রাজশ্যালক ও তার দুই অনুচর। তারই মাঝে সূচককে রাজশ্যালক বলেছেন ধীবরকে বাধা না দিয়ে পূর্বাপর সব বলার সুযোগ দিতে। ধীবর জাল, বঁড়শি সহযোগে মাছ ধরে তার জীবিকা নির্বাহের কথা জানালে রাজশ্যালক উদ্ধৃত ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্যটি করেন। ধীবর নিজের পেশার অবমাননা সহ্য করতে না পেরে বলে, মানুষের বৃত্তি যাই হোক না কেন, তা সৎ উপায়ে উপার্জিত হলে কখনোই নিন্দনীয় হতে পারে না। কিন্তু ধীবরের কাছ থেকে মূল্যবান আংটি পাওয়া গেলে রাজশ্যালক ভেবেছেন ধীবর জীবিকার দোহাই দিয়ে চুরির দায় ঠেকাতে চেয়েছে। তাই ধীবরকে মর্মে আঘাত করার জন্য রাজশ্যালক উক্ত শ্লেষোক্তি করেছেন।
“যে বৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে, সেই বৃত্তি নিন্দনীয় (ঘৃণ্য) হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।” – উক্তিটি কার? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? উক্তিটিতে যে দর্শন ফুটে উঠেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের অনূদিত ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশ থেকে গৃহীত উদ্ধৃত উক্তির বক্তা হলেন নাট্যাংশের প্রধান চরিত্র এক সাধারণ ধীবর।
প্রসঙ্গ – ধীবরের কাছে রাজার নামাঙ্কিত মূল্যবান আংটি পেয়ে রাজশ্যালক ও তার অনুচরেরা ‘চোর’ অপবাদ দেন। এর পাশাপাশি তার জাত, পেশা ইত্যাদি নিয়ে শ্লেষাত্মক উক্তি করতে থাকেন। ধীবর আংটি পাওয়ার বৃত্তান্ত জানাতে চাইলে তারা মনে করে ধীবর আত্মরক্ষার্থে গল্প রচনার চেষ্টা করছে। ব্যঙ্গাত্মক উক্তিতে রাজার শ্যালক ধীবরের পেশাকে ‘বেশ পবিত্র’ বলে উপহাস করলে বিদ্রুপের খোঁচাতে ধীবর উদ্ধৃত উক্তিটি করতে বাধ্য হয়।
দর্শন চিন্তা – ধীবর যথেষ্ট শিক্ষা ও জ্ঞানবোধের অধিকারী না হলেও তার অন্তর্নিহিতি অভিজ্ঞতা ও আত্মসম্মানবোধ যথেষ্ট ছিল তা বোঝা যায়। কর্মই ছিল তার কাছে ধর্ম। সেখানে জাতের বিচার কখনো প্রাধান্য পায় না। ধীবর রাজশ্যালককে বলেছে – “বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বভাবে দয়াপরায়ণ হলেও যজ্ঞীয় পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকেন।” অর্থাৎ কোনো পেশাই সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার হ’তে পারে না। সুতরাং ধীবর তার পেশাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছে ও সম্মানিত করতে চেয়েছে।
“এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন।” – কার উক্তি? কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে বক্তা এই উক্তি করেছিল? বক্তা কেন এত জোরের সঙ্গে এমন উক্তি করেছে?
বক্তা – প্রখ্যাত সংস্কৃত কবি কালিদাস রচিত সংস্কৃত নাটকের তরজমাকৃত ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে উদ্ধৃত উক্তি করেছে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র জনৈক ধীবর।
পরিপ্রেক্ষিত – ধীবর মাছ কেটে মাছের পেট থেকে বহু মূল্যবান রত্নখচিত রাজনামাঙ্কিত একটি উজ্জ্বল আংটি পেয়ে সেটি বিক্রির উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে দেখায়। কিন্তু রাজশ্যালক ও দুই রক্ষী তাকে ‘চোর’ অপবাদ দিয়ে ধরে আনে। ধীবর তাদের বহু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে অতি কষ্টে আংটি পাওয়ার বৃত্তান্ত জানায়। তারপরেই সে তার সততা ও দৃঢ়তায় এই উক্তি করে।
উক্তির কারণ – ধীবরের কাছে রাজ-নামাঙ্কিত বহু মূল্যবান আংটি দেখে রাজশ্যালক ও রক্ষীদ্বয় তার মুখ থেকে চুরির স্বীকারোক্তি না করাতে পেরে তার জাতি পরিচয়, পেশা ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে। কিন্তু ধীবর আত্মবিশ্বাসী, সৎএবং স্পষ্টবাদী। সে কখনোই ধৈর্য হারায়নি, অমানবিক আচরণের প্রত্যুত্তর না দিয়ে বরং বিনয়ের সঙ্গে আংটি প্রাপ্তির প্রকৃত সত্য সকলকে জানিয়েছে।
“তা প্রভু যা আদেশ করেন।” – উদ্ধৃতাংশের বক্তা কে? ‘প্রভু’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? উক্তিটিতে বক্তার কোন্ মনোভাব ধরা পড়েছে?
মহাকবি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের অনূদিত নাট্যাংশ ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশের বক্তা প্রথম রক্ষী সূচক।
উদ্ধৃতাংশে ‘প্রভু’ বলতে নগররক্ষার কাজে নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধি রাজশ্যালককে বোঝানো হয়েছে।
প্রসঙ্গ – ধীবরের মুখে আংটি পাওয়ার বিবরণ শুনে তার সত্যতা জানতে রাজার কাছে গিয়েছিলেন রাজশ্যালক। আংটি বিষয়ে ধীবরের বলা ঘটনা সত্য প্রমাণিত হলে রাজা আদেশ করেন ধীবরকে মুক্তি দিতে। এই রাজাদেশ রক্ষীদের জানালে সূচক প্রদত্ত উক্তিটি করেছিল।
বক্তার মনোভাব – উক্তিটি থেকে বক্তার প্রভুর প্রতি আনুগত্য ধরা পড়ে, রাজতন্ত্রের শাসন-পরিকাঠামোয় যা স্বাভাবিক। চোর সন্দেহে আটক ধীবরকে রক্ষীদ্বয় প্রথম থেকেই নানাভাবে পীড়ন করেছিল, অলীক কল্পনায় তার অমঙ্গল কামনা করে মনে মনে আনন্দ অনুভব করেছিল। মহারাজের হুকুমনামা হাতে নিয়ে রাজবাড়ি থেকে রাজশ্যালককে ফিরতে দেখে তারা ধীবরের সম্ভাব্য শাস্তির কথা ভেবে অযথা সুখ পেয়েছিল। অথচ সেই ধীবর কোনো শাস্তিভোগ না করেই অনায়াসে মুক্তি পেয়ে যাবে, তা সূচক ও জানুক দুজনেই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু প্রভুর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই তাদের। তাই হতাশ স্বরে অসন্তোষজনক এই উক্তি করেছিল।
“প্রভু, আজ আমার সংসার চলবে কীভাবে?” – কে, কাকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করেছে? ‘আজ’ বলে কোন্ দিনকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে? বক্তা সংসার চলা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে কেন?
সংস্কৃত মহাকবি কালিদাস রচিত ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নামক অনুবাদ নাট্যাংশে চুরির দায়ে ধৃত ধীবর নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালককে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করেছে।
উদ্ধৃতিতে ‘আজ’ বলতে, ধীবরের চুরির অপরাধে নগর রক্ষীদের হাতে ধরা পড়া এবং রাজাদেশে মুক্তির দিনটিকে বোঝানো হয়েছে।
সংশয় প্রকাশের কারণ – ধীবর শ্রমজীবী মানুষ। সে দরিদ্র হলেও সততার সঙ্গে পেশার প্রতি একনিষ্ঠ থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। সে জাল, বঁড়শি ইত্যাদি নানা উপায়ে মাছ ধরে সংসার চালায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই একদিন রোজগার না হলে তারপক্ষে সংসার চালানো দুরূহ হয়ে পড়বে। রুই মাছের পেট থেকে মূল্যবান আংটি পেয়ে সে ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে রক্ষীদের হাতে ধরা পড়লে তার রোজগার সেদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়। এরপর রাজাদেশে মুক্তি পেয়ে সমস্ত দিনের আর্থিক ক্ষতির কথা ভেবে সে হতাশ হয়েছিল। একদিকে মিথ্যে অভিযোগে রক্ষীদের দ্বারা হেনস্তা হওয়া এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত খাদ্যসংস্থান তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। তাই মিথ্যে অপবাদ থেকে মুক্তির খবর পেয়ে রাজশ্যালকের কাছে ধীবর অকপটে সংশয় প্রকাশ করেছে।
“প্রভু, অনুগৃহীত হলাম।” – ‘প্রভু’ কে? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি? বক্তার এত বিনয়ের কারণ কী?
কালিদাস রচিত ‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশ থেকে গৃহীত উদ্ধৃত উক্তিটিতে ‘প্রভু’ হলেন নগর রক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক।
প্রসঙ্গ – চুরির অপবাদ দিয়ে ধীবরকে ধরে আনার পর রাজশ্যালক ও দুই রক্ষী তাকে নানাভাবে পীড়ন করেছিল। আংটি সংক্রান্ত বিষয়ে জেরার নামে হেনস্তা করা হয়েছিল তাকে। কিন্তু রাজাদেশে মুক্তির আনন্দের মাঝেও ধীবর সংসার অতিবাহিত করার দুশ্চিন্তায় শঙ্কিত হয়েছিল। এরপর রাজশ্যালক যখন জানান তাকে রাজা আংটির অর্থমূল্যের সমান পারিতোষিক দিয়েছেন তখন ধীবর ‘প্রভু’র প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ উদ্ধৃত উক্তিটি করেছিল।
বিনয়ের কারণ – ধীবরকে রক্ষীদ্বয় যেভাবে মৃত্যুভয় দেখিয়েছে তাতে অশিক্ষিত অতি সাধারণ ধীবরের পক্ষে জীবনীশক্তি বজায় রাখাই দুরূহ ছিল। তারপক্ষে এত অপমান, লাঞ্ছনার পরেও রাজার দয়া পাওয়া কিংবা পারিতোষিক লাভ ছিল অকল্পনীয়। সে মনে মনে ভেবে নিয়েছিল তার ভবিষ্যৎ কঠিন শাস্তি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। অথচ অর্থপ্রাপ্তির কথা শুনে সে যেমন চমকে ওঠে, তেমনি কৃতজ্ঞতায় সে রাজশ্যালকের প্রতি বিনয় প্রকাশ করে।
“এ কিযা-তা অনুগ্রহ! এ যে শূল থেকে নামিয়ে একেবারে হাতির পিঠে চড়িয়ে দেওয়া হলো।” – বক্তা কে? প্রসঙ্গ নির্দেশ করো। উপমাটির স্বরূপ উদ্ঘাটন করো।
বক্তা – মহাকবি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের সংক্ষিপ্ত ও অনূদিত নাট্যাংশ ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ থেকে গৃহীত উদ্ধৃত উক্তিটির বক্তা হলেন নগররক্ষায় নিযুক্ত প্রথম রক্ষী সূচক।
প্রসঙ্গ – মাছের পেট থেকে রাজার নামাঙ্কিত, রত্নখচিত, বহুমূল্য একটি আংটি পেয়ে সাধারণ ধীবর বিক্রির চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই সময় নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক ও দুই রক্ষী তাকে ধরে এবং বন্দি করে নিয়ে আসে রাজধানীতে। রাজশ্যালক ধীবরের আংটিপ্রাপ্তির ঘটনা রাজাকে জানালে, প্রমাণ হয় আংটি পাওয়ার ব্যাপারে ধীবর যা বলেছে, তা সত্য। রাজা ধীবরকে মুক্তির নির্দেশ দেন এবং তার সততার জন্য আংটির সমমূল্যের পারিতোষিক প্রদান করেন। ধীবর রাজার এই দানকে, তাঁর অনুগ্রহ বলে স্বীকার করলে, ঈষাণ্বিত সূচক উপরোক্ত মন্তব্য করেছিল।
উপমার স্বরূপ – সূচকের ধারণা ছিল, রাজদ্রব্য চুরির অপরাধে ধীবর মিথ্যে বলেছে এবং সে অপরাধী। তাই রাজার হুকুমনামায় ধীবর সম্পর্কে কঠোর শাস্তির নির্দেশ থাকবে। কিন্তু রাজশ্যালক জানায় যে রাজার আদেশানুযায়ী ধীবর সমমূল্যের পারিতোষিক লাভ করে মুক্তি পেয়েছে। ধীবরের মুক্তির এবং পুরস্কৃত হওয়ার কথা সূচক মেনে নিতে পারেনি। তাই ধীবরের কথার সূত্রে সে তার মনের ভিতরে থাকা ঈর্ষা উক্ত উক্তিতে প্রকাশ করেছে। রাজতন্ত্রের নির্মম শাস্তি প্রথার একটি ছিল শূলে চড়ানো। ধীবরের শাস্তি নিয়ে সূচক এমনই কিছু ভেবেছিল। কিন্তু শুধু মুক্তিই নয় ধীবর পুরস্কার লাভ করলে ‘হাতির পিঠে চড়ানো’ হল বলে সূচক বিদ্রূপ করে। তার কাছে ধীবরের পাওয়া এই সম্মান ও মর্যাদা অকারণ। বক্তা আলোচ্য উপমায় ক্ষোভের প্রকাশ করেছে।
“… মুহূর্তের জন্য রাজা বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলেন।” – রাজা কে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। রাজার বিহ্বল হওয়ার কারণ কী?
রাজার পরিচয় – কালিদাস রচিত ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশের অন্তর্গত আলোচ্য উক্তিটিতে ‘রাজা’ বলতে পুরুবংশীয় রাজা দুষ্মন্তকে বোঝানো হয়েছে। ইনি কণ্বমুনির পালিতাকন্যা শকুন্তলার স্বামী।
প্রসঙ্গ – নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক ও দুই রক্ষী এক অতিসাধারণ ধীবরের কাছে রাজ-নামাঙ্কিত, মণিখচিত, বহুমূল্য একটি আংটি উদ্ধার করে। চুরির অপরাধে তারা ধীবরকে আটক করে রাজধানীতে নিয়ে আসে। ধীবরের থেকে আংটি প্রাপ্তির বিবরণ শুনে রাজশ্যালক তা জানানোর জন্য রাজার কাছে যান। রাজশ্যালক কিছু সময় পর ফিরে এসে বলেন, আংটি দেখে স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতির রাজা দুষ্মন্ত ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাজশ্যালক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।
বিহ্বল হওয়ার কারণ – আংটি সংক্রান্ত ঘটনায় ধীবরের সম্মানজনক মুক্তির আদেশ নিয়ে আসেন রাজশ্যালক। রাজার কাছ থেকে এসে তিনি জানান, আংটি দেখে রাজা কিছু সময়ের জন্য বিহ্বল হয়েছিলেন। রাজশ্যালক আরও বলেন শুধুমাত্র মূল্যবান বলেই যে স্বভাবগম্ভীর রাজা এমন করেছিলেন তা তার মনে হয়নি। বরং কোনো প্রিয়জনের স্মৃতি তাঁর স্মরণে এসেছিল বলেই তিনি উদাসীন হয়ে আংটির দিকে চেয়েছিলেন।
“এখন থেকে তুমি আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু হলে।” – কারা পরস্পরের বন্ধু হয়েছে? কীভাবে তারা বন্ধু হল?
যারা বন্ধু হয়েছিলেন – মহাকবি কালিদাস রচিত ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ নাটকের সংক্ষিপ্ত ও বাংলায় অনূদিত ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশের শেষপর্বে নগর রক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক ও ধীবর পরস্পর বন্ধু হয়েছিলেন।
নাট্যাংশের শুরুতে ধীবর রাজনামাঙ্কিত আংটি চুরির অপরাধে নগর রক্ষায় নিযুক্ত রাজশ্যালক ও দুই রক্ষীর হাতে ধরা পড়েছিল। রক্ষীরা তাকে নির্মমভাবে বেঁধে আনে রাজধানীতে।
যেভাবে তারা বন্ধু হলেন – ধীবরের জবানবন্দি না শুনে তারা সকলে নানাভাবে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিল। বিনয়ী ও সংযমী ধীবর এ সমস্ত নির্যাতনের পরেও বিনা উত্তেজনায় আংটি পাওয়ার ঘটনা জানালে রাজশ্যালক তার সত্যতা প্রমাণ করতে রাজার কাছে গিয়েছিলেন। রাজার কাছে ধীবরের সত্যতা প্রমাণিত হলে রাজার নির্দেশে ধীবর আংটির সমমূল্যের পারিতোষিক পেয়ে মুক্তি পায়। নিম্নবিত্তের সাধারণ ধীবরের প্রতি রাজার এই আচরণ রক্ষীরা মেনে নিতে পারেনি। তাদের ঈর্ষাণ্বিত দেখে সৎ ও উদারমনস্ক ধীবর নিজের অর্ধেক পুরস্কার তাদের দিয়ে দেয়। ধীবরের আচরণে তার প্রতি রাজশ্যালকের রূঢ় মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছিল। সামান্য ধীবরের এই আচরণ দেখে মুগ্ধ রাজশ্যালক তাকে ‘বন্ধু’ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।
বানান ও ব্যাকরণ সংশোধিত উত্তর:
“শকুন্তলা অপমানিতা হলেন রাজসভায়।” — কোন্ রাজসভায় শকুন্তলা অপমানিতা হন? তাঁর অপমানিতা হওয়ার কারণ কী?
রাজসভার পরিচয় – উল্লিখিত অংশে রাজা দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলার অপমানিতা হওয়ার কথা বলা হয়েছে।
শকুন্তলার অপমানিতা হওয়ার কারণ – তপোবনে মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে বিয়ে করে রাজধানীতে ফিরে যান। দীর্ঘকাল দুষ্মন্তের কাছ থেকে শকুন্তলার কোনো খোঁজ নিতে কেউ আসে না। দুঃখিনী শকুন্তলা স্বামীর চিন্তায় অন্যমনস্কা হয়ে থাকেন। তাই মহর্ষির আশ্রমে ঋষি দুর্বাসা এলে শকুন্তলা ঋষির উপস্থিতি টের পান না। অপমানিত দুর্বাসা অভিশাপ দেন যে, শকুন্তলা যাঁর চিন্তায় মগ্ন রয়েছেন, তিনি একদিন শকুন্তলাকে ভুলে যাবেন। শেষপর্যন্ত শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদার অনুরোধে দুর্বাসা বলেন যে, শকুন্তলা কোনো স্মারকচিহ্ন দেখাতে পারলে তাঁর এই অভিশাপের প্রভাব দূর হয়ে যাবে। এরপর সখীরা ভাবে যে, বিদায় নেওয়ার আগে যে আংটিটি দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেটিই হবে ভবিষ্যতের স্মারকচিহ্ন। মহর্ষি কণ্ব তীর্থ থেকে ফিরে শকুন্তলাকে স্বামীর ঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যাওয়ার পথে শচীতীর্থে স্নানের পর অঞ্জলি দেওয়ার সময় শকুন্তলার হাতের আংটিটি জলে পড়ে যায়। ফলে দুর্বাসার অভিশাপ বজায় থাকে। সভায় উপস্থিত হলে রাজা শকুন্তলাকে চিনতেও পারেন না; ফলে তাঁকে সেই রাজসভায় অপমানিতা হতে হয়।
“সখীরা মনে করলেন সেই আংটিই হবে ভবিষ্যতের স্মারকচিহ্ন।” — এখানে কোন্ আংটির কথা বলা হয়েছে? আংটিটি কীভাবে হারিয়ে গিয়েছিল?
উদ্দিষ্ট আংটি – উল্লিখিত অংশে দুষ্মন্ত রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় বিদায় মুহূর্তে শকুন্তলাকে যে আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই আংটির কথা প্রশ্নোদ্ধৃত অংশে বলা হয়েছে।
আংটি হারানোর ঘটনা – শকুন্তলাকে বিয়ে করে রাজা দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার পর দীর্ঘকাল শকুন্তলার খোঁজ নিতে কোনো দূত আসে না। এইসময় ঋষি দুর্বাসা তপোবনে এলে স্বামীর চিন্তায় অন্যমনস্কা শকুন্তলা তা টের পান না। অপমানিত দুর্বাসা অভিশাপ দেন যে, যাঁর চিন্তায় শকুন্তলা মগ্ন, সেই ব্যক্তি শকুন্তলাকে ভুলে যাবেন। শেষ অবধি শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদার অনুরোধে দুর্বাসা বলেন যে, কোনো নিদর্শন দেখাতে পারলে তবেই শাপের প্রভাব দূর হবে। সখীরা দুষ্মন্তের দেওয়া আংটিটাকেই এই স্মারকচিহ্ন বলে ধরে নেয়। মহর্ষি কণ্ব তীর্থ থেকে ফিরে যখন শকুন্তলাকে স্বামীর ঘরে পাঠানোর আয়োজন করেন, তখন আংটিটাই হয় শকুন্তলার সম্বল। কিন্তু পথে শচীতীর্থে স্নানের পর অঞ্জলি দেওয়ার সময় শকুন্তলার হাত থেকে খুলে আংটিটি জলে পড়ে যায়। এইভাবেই আংটিটি হারিয়ে যায়।
“ঘটনাক্রমে সেই আংটি পেল এক ধীবর” – কার আংটি সে পেয়েছিল? আংটি হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে ইতিহাসটি আছে তা লেখো।
আংটির মালিক – ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে ধীবর যে আংটিটি পেয়েছিল, তা ছিল রাজা দুষ্মন্তের।
আংটি হারানোর ইতিহাস – কালিদাসের ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে ধীবরের আংটি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে এক দীর্ঘ কাহিনি রয়েছে। মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে আশ্রমকন্যা শকুন্তলাকে বিয়ে করে রাজা দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরে যান। তারপর দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও তিনি শকুন্তলার খোঁজ করেন না। একদিন ঋষি দুর্বাসা কণ্বের আশ্রমে এলে স্বামীর চিন্তায় মগ্ন শকুন্তলা তাঁর উপস্থিতি টেরই পান না। অপমানিত ঋষি অভিশাপ দেন যে, যাঁর চিন্তায় শকুন্তলা মগ্ন হয়ে আছেন, তিনি শকুন্তলাকে ভুলে যাবেন। পরে সখী প্রিয়ংবদার অনুরোধে অভিশাপ কিছুটা লঘু করে দুর্বাসা বলেন যে, শকুন্তলা যদি প্রিয়জনকে কোনো স্মৃতিচিহ্ন দেখাতে পারেন, তাহলে তিনি এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। শকুন্তলার কাছে থাকা দুষ্মন্তের দেওয়া আংটিটাই স্মৃতিচিহ্ন বলে সখীরা ভেবে নেন। মহর্ষি কণ্ব তীর্থ থেকে ফিরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর উদ্যোগ নেন। কিন্তু যাওয়ার সময় শচীতীর্থে স্নানের পর অঞ্জলি দিতে গিয়ে শকুন্তলার হাত থেকে আংটিটি খুলে জলে পড়ে যায়। ফলে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে আর চিনতে পারেন না। ওদিকে, এক ধীবর মাছ ধরতে গিয়ে একটি রুই মাছ ধরে এবং তার পেটে এই আংটিটি পায়।
“যে বৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে, সেই বৃত্তি নিন্দনীয় (ঘৃণ্য) হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।” — কে, কোন্ প্রসঙ্গে মন্তব্যটি করেছে? এখানে বক্তার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা করো।
বক্তা ও প্রসঙ্গ – কালিদাসের ধীবর-বৃত্তান্ত নামক নাট্যাংশে বন্দি ধীবর রাজার শ্যালক এবং রক্ষীদের জানিয়েছিল, সে জাল, বড়শি ইত্যাদির সাহায্যে মাছ ধরে সংসার চালায়। তখন রাজার শ্যালক তার জীবিকা “খুবই পবিত্র” বলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে থাকে। এই বিদ্রূপের পরিপ্রেক্ষিতেই ধীবর চরিত্রটি রাজার শ্যালককে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছে।
বক্তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য – ধীবর তার এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রবল আত্মসম্মানবোধেরই পরিচয় দিয়েছে। সে রাজশ্যালককে তার পেশা নিয়ে কোনোরকম নিন্দাসূচক কথা না বলতে অনুরোধ করে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উদাহরণ দিয়ে সে বলে যে, ব্রাহ্মণ স্বভাবে দয়াপরায়ণ হলেও যজ্ঞের পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো পেশাই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না, সেটির কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। এভাবেই সে নিজের পেশার প্রতি হওয়া তাচ্ছিল্যের প্রতিবাদ করেছে।
“এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন।” – বক্তা কে? উক্তির প্রেক্ষাপটে বক্তার চরিত্র আলোচনা করো।
বক্তার পরিচয় – প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্যটির বক্তা ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশের অন্যতম চরিত্র ধীবর।
উক্তির আলোকে বক্তার চরিত্র – ধীবরের কাছে আংটিটি দেখে রাজশ্যালক এবং দুই রক্ষী তাকে চোর বলে সাব্যস্ত করে। ধীবর চুরির দায় অস্বীকার করায় তারা তার জাতি পরিচয় নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। ধীবর তখন নিজের পেশাগত পরিচয় দেয় — “আমি একজন জেলে। শক্ৰাবর্তে থাকি”। যদিও এর জন্য তাকে অনেক তির্যক ব্যঙ্গ শুনতে হয়। তখনই এই ধরনের কথার বিরোধিতা করে ধীবর জানায় যে, একটি রুইমাছকে টুকরো করে কাটার সময় তার পেটের ভিতরে সে আংটিটি পেয়েছে। পরে সে তা বিক্রি করার সময় তাকে ধরা হয়েছে। এই কথাগুলি বলার পরই ধীবর প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছিল। এই উক্তি প্রমাণ করে সে সৎ, স্পষ্টবাদী, আত্মবিশ্বাসী এবং একই সঙ্গে নম্র ও ভদ্রও। সে রুক্ষভাবে, কর্কশ স্বরে তার বিরুদ্ধে ওঠা অনৈতিক অভিযোগের জবাব দেয়নি; বরং বিনীতভাবে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। কিন্তু তার মধ্যে চরিত্রের দৃঢ়তা অত্যন্ত স্পষ্ট।
“এ অবশ্যই গোসাপখাওয়া জেলে হবে।” — কে, কখন, কেন এই মন্তব্যটি করেছেন? এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে যে বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে তা আলোচনা করো।
বক্তা ও প্রসঙ্গ – কালিদাসের লেখা ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে রাজশ্যালক ও রক্ষীদের কাছে ধীবর তার আংটি পাওয়ার বৃত্তান্তটি সবিস্তারে জানানোর পর রাজশ্যালক ধীবরের উদ্দেশ্যে প্রশ্নে উদ্ধৃত উক্তিটি করেন। তিনি জানুক নামে রক্ষীটিকে ডেকে বলেন যে, ধীবরের শরীর থেকে কাঁচা মাংসের গন্ধ আসছে, অতএব সে নিশ্চয়ই গোসাপখাওয়া জেলে। এখানে “গোসাপখাওয়া জেলে” বলতে অত্যন্ত নীচু জাতের জেলে সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ধীবরকে এর আগেও নানাভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে, তার পেশা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এখানে তেমনই ব্যঙ্গ করার জন্য মন্তব্যটি করা হয়েছে।
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ – রাজার শ্যালক ছিলেন নগররক্ষার কাজে নিযুক্ত। সেদিক থেকে দেখলে তিনি বিশেষ ক্ষমতাবান ও বিত্তশালী, সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তাই স্বাভাবিকভাবেই দরিদ্র ধীবর তাঁর অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠে। রাজশ্যালকের এই মন্তব্যের দ্বারা শুধু ধীবরের পেশাই নয়, তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সম্প্রদায়গত অবস্থান — এই সব কিছুর প্রতিই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বর্ণবিভক্ত সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি যে ঘৃণার মনোভাব দেখাত, তার কথাই এখানে বলা হয়েছে।
“মহারাজ এ সংবাদ শুনে খুব খুশি হবেন।” — কে, কাকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছিল? সংবাদটা কী ছিল? মহারাজের খুশির কারণ কী?
বক্তা ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি – ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে দুই রক্ষী রাজশ্যালককে উদ্দেশ্যে করে উদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছিল।
উল্লিখিত সংবাদ – ধীবরের কাছ থেকে রাজশ্যালক এবং রক্ষীরা রাজার নাম খোদাই করা রত্নখচিত আংটিটি উদ্ধার করে। ধীবর মাছের পেট থেকে ওই আংটি পাওয়ার কথা বললেও তারা তা বিশ্বাস করে না এবং ধীবরকেই চোর সাব্যস্ত করে। এই পরিস্থিতিতে আংটি পাওয়ার বিষয়টি রাজশ্যালক মহারাজকে সবিস্তারে জানাতে যায়। এখানে সংবাদ বলতে ধীবরের বলা এই আংটি প্রাপ্তির কাহিনিকেই বোঝানো হয়েছে।
মহারাজের খুশির কারণ – রক্ষীরা ভেবেছিল, মহারাজ তাঁর এই মূল্যবান আংটি ফিরে পেয়ে খুশি হবেন। এ ছাড়াও আংটি চোরকে ধরার জন্য তাঁর খুশি আরও বেড়ে যাবে। রক্ষীরা এরকম ভাবনার মধ্য দিয়ে একরকম আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজা খুশি হয়েছিলেন আংটি ফিরে পাওয়া এবং প্রিয়জনের কথা মনে পড়ার কারণে। অর্থাৎ ধীবরকে আটক করা কোনোভাবেই মহারাজের খুশির কারণ হয়নি; বরং ধীবরের কারণে আংটিটি ফেরত পেয়ে খুশি হয়ে তিনি ধীবরকে পারিতোষিক দিয়েছিলেন।
“এই তো আমাদের প্রভু, মহারাজের হুকুমনামা হাতে নিয়ে এদিকে আসছেন।” – ‘আমাদের প্রভু’ বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে? মহারাজের হুকুম শেষপর্যন্ত কীভাবে বক্তাকে হতাশ করে তা লেখো।
উল্লিখিত ব্যক্তি – কালিদাসের ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে “আমাদের প্রভু” বলতে দ্বিতীয় রক্ষী নগররক্ষার দায়িত্বে থাকা রাজার শ্যালকের কথা বলেছে।
বক্তার হতাশ হওয়া – দুজন রক্ষী আংটি চুরির অপরাধে ধীবরকে ধরে নিয়ে আসে এবং রাজার আদেশে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মহা উৎসাহে অপেক্ষা করতে থাকে। রাজশ্যালক রাজার কাছে গিয়েছিলেন আংটি পাওয়ার ঘটনা সবিস্তারে জানাতে। তাই রক্ষীরা অপেক্ষা করছিল ধীবরকে শকুন দিয়ে খাওয়ানো হবে না কি কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে, সেই নির্দেশ পাওয়ার জন্য। প্রথম রক্ষী এমনও জানিয়েছিল ধীবরকে মারার আগে যে মালা পরানো হবে, তা গাঁথার জন্য তার হাত নিশপিশ করছে। কিন্তু রক্ষীদের অপেক্ষা শেষপর্যন্ত হতাশায় পরিণত হয়। কারণ, রাজার কাছ থেকে ঘুরে এসে রাজশ্যালক জানান যে আংটি পাওয়ার বিষয়ে ধীবর যা যা বলেছে, তা সবই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ফলে রাজা ধীবরকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, মহারাজ খুশি হয়ে আংটির মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ধীবরকে দিয়েছেন বলেও শ্যালক জানান। এভাবেই মহারাজের হুকুম বক্তাকে অত্যন্ত হতাশ করেছিল।
“কারা পরস্পরের বন্ধু হয়েছে?” এমন বন্ধুত্বের কারণ কী?
অথবা, “তুমি আমার একজন বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধু হলে।” কোন্ ঘটনার মাধ্যমে এই বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল?
উদ্দিষ্ট বন্ধুদ্বয় – ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে উল্লিখিত প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটির বক্তা হলেন রাজার শ্যালক। ধীবরকে উদ্দেশ্য করে বলা এই কথার মাধ্যমে রাজশ্যালক ধীবরকে তাঁর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
বন্ধুত্বের কারণ – প্রাথমিকভাবে ধীবরের কাছে রাজার নাম খোদাই করা আংটিটি পেয়ে রাজশ্যালকও ধীবরকেই চোর বলে সন্দেহ করেছিল এবং তার পেশা নিয়ে বিদ্রূপও করেছিল। এমনকি “এ অবশ্যই গোসাপখাওয়া জেলে হবে” — এই জাতীয় বিরূপ মন্তব্যও তিনি করেছিলেন। কিন্তু মহারাজ যখন রাজশ্যালককে বলেন যে ধীবর আংটি পাওয়া সম্পর্কে যা বলছে তা সব সত্য, তখন রাজশ্যালকের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। রাজা আংটির সমমূল্যের অর্থ পুরস্কার হিসেবে রাজশ্যালকের হাত দিয়েই ধীবরকে পাঠিয়েছিলেন। এসব ঘটনা রাজশ্যালককে প্রভাবিত করে। রাজশ্যালক এরপরই ধীবরকে তাঁর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নেন। এর পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে:
- প্রথমত, ধীবরের সততা রাজার মাধ্যমে স্বীকৃত হওয়ার পরই রাজশ্যালক নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি নিজেকে সংশোধন করে নেন।
- দ্বিতীয়ত, রাজার মনোভাব বুঝে রাজশ্যালক আর ধীবরকে অবজ্ঞা করতে সাহস পাননি; বরং ধীবরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের মাধ্যমে রাজার প্রতি তিনি নিজের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।
“সেই আংটি দেখে মহারাজের কোনো প্রিয়জনের কথা মনে পড়েছে।” — মন্তব্যটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। আংটি দেখে রাজা কী করেছিলেন?
প্রসঙ্গ – কালিদাসের ধীবর-বৃত্তান্ত নামক রচনায় এক ধীবর একটি রুইমাছকে টুকরো করে কাটার সময় সেটির পেটের ভিতর থেকে একটি আংটি পায়। একজন সামান্য জেলের কাছে মণিখচিত এবং রাজার নাম খোদাই করা সেই আংটি দেখে নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজার শ্যালক এবং রক্ষীরা তাকে চোর সাব্যস্ত করেন। ধীবরের ব্যাখ্যা তাঁরা শুনতেই চান না। রাজার শ্যালক রাজাকে সমস্ত ঘটনা জানাতে রাজপ্রাসাদে যায়। কিন্তু ধীবরের সব কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। এই সময়ই রাজা তাঁর আংটিটি স্বচক্ষে দেখেন। এই স্মৃতিচিহ্ন দেখেই রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার কথা মনে পড়ে যায়। রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে রাজশ্যালক এসব কথাই রক্ষীদের উদ্দেশে বলেন।
রাজার প্রতিক্রিয়া – আংটি দেখে স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির রাজা মুহূর্তের জন্য বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে যে উচ্ছ্বাস তৈরি হয়, তার ফলে তিনি ধীবরকে আংটির মূল্যের সমপরিমাণ অর্থও পুরস্কার হিসেবে দেন। আংটিটি রাজার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা রাজার এই আচরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। আংটির মূল্য নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতিই এক্ষেত্রে রাজাকে আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল।
সংশোধিত উত্তর:
আংটি পাওয়ার পরে ধীবরের যে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা নিজের ভাষায় লেখো।
ধীবরের অভিজ্ঞতা – কালিদাসের ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে ধীবরের কাছে রাজার নাম খোদাই করা মণিখচিত আংটি দেখে নগররক্ষায় নিযুক্ত রাজার শ্যালক এবং দুজন রক্ষী পিছনে হাত বেঁধে তাকে ধরে নিয়ে আসেন। ধীবর আংটি চুরি করেনি জানালেও তাঁরা তা বিশ্বাস করেন না। প্রথম রক্ষী বিদ্রূপ করে জানতে চায়, তাকে সদব্রাহ্মণ মনে করে রাজা আংটিটা দান করেছেন কি না। ধীবর এইসময় রক্ষীদের তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপের মুখে পড়ে। সে জাল, বড়শি ইত্যাদি দিয়ে মাছ ধরার কথা বললে তা নিয়েও তাকে ব্যঙ্গ শুনতে হয়। ধীবর এর প্রতিবাদ জানায়। সে রুইমাছ কাটার সময় মাছের পেটে আংটি পাওয়ার কথা বলে। রাজশ্যালক ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে রাজার কাছে যান। রক্ষীরা চোর হিসেবে ধরা পড়ার শাস্তিস্বরূপ ধীবরকে হত্যার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্যালক ফিরে এসে জানান যে, ধীবর সবই সত্য কথা বলেছে এবং সে কারণে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, রাজা খুশি হয়ে ধীবরকে আংটির সমমূল্যের অর্থ দিয়েছেন বলেও তিনি জানান। ফলে দিনের কাজ বন্ধ হলেও ধীবরের ক্ষতি পুষিয়ে যায়। এভাবে আংটিকে কেন্দ্র করে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের শিকার হয় ধীবর।
ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যদৃশ্যে ধীবরের চরিত্রকে যেভাবে পাওয়া যায় তা নিজের ভাষায় লেখো।
ভূমিকা – কালিদাসের লেখা ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে ধীবর চরিত্রটির গুরুত্ব নাট্যাংশটির শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট হয়। কাহিনির ঘটনাপ্রবাহে ধীবর চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
পেশার প্রতি মর্যাদাবোধ – ধীবর চরিত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তার নিজের পেশার প্রতি মর্যাদাবোধ। তাই রাজার শ্যালক ব্যঙ্গ করে “তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখছি” মন্তব্য করলে ধীবর দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, “এরকম বলবেন না। যে বৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে, সেই বৃত্তি নিন্দনীয় (ঘৃণ্য) হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।” ধীবরের এই উক্তি সাহস এবং আত্মমর্যাদার পরিচায়ক।
সততা – ধীবর চরিত্রের সততার দিকটিও উল্লেখযোগ্য। আংটি পাওয়ার বিষয়ে সে রাজশ্যালক এবং রক্ষীদের যা যা বলেছে পরবর্তীকালে সবই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সততার অহংকারও ধীবরের ছিল। তাই রুই মাছের পেটের ভিতর আংটি পাওয়ার কথা উল্লেখ করে সে বলেছে, “এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন।” স্পষ্টভাষী ধীবর চুরির অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে তার প্রতি অবিচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাজশ্যালককে বলেছে, “আজ আমার সংসার চলবে কীভাবে?” এইভাবে ধীবর চরিত্রটিতে নিজস্বতা ফুটে উঠেছে।
ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে রক্ষীগণ ও রাজশ্যালকের ভূমিকা আলোচনা করো।
রক্ষীদের ভূমিকা – কালিদাসের লেখা ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে রাজশ্যালক এবং রক্ষীদের বেশ সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিকভাবে ধীবরের কাছে আংটিটি পেয়ে তাঁরা তাকে চোর বলে মনে করেছিলেন। পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় যেভাবে ধীবরকে নিয়ে আসা হয় তাতে বোঝা যায়, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে কতখানি আগ্রহী। ধীবরের প্রতি নিষ্ঠুর কৌতুকের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা। রক্ষীরা ধীবরকে “বাটপাড়”, “গাঁটকাটা” ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেছে। রক্ষীরা ধীবরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। রাজার আদেশ আসার আগেই রক্ষীরা “হয় তোকে শকুন দিয়ে খাওয়ানো হবে, না হয় কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে” — এই জাতীয় মন্তব্য চরম অবিবেচনা ও অমানবিকতার পরিচয় দেয়।
রাজশ্যালকের ভূমিকা – রাজশ্যালকও ধীবরের পেশা নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। তবে নগররক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজশ্যালককে তুলনায় কিছুটা দায়িত্ববোধসম্পন্নও মনে হয়েছে। তিনি মহারাজের আদেশের জন্য অপেক্ষা করেছেন কিংবা ধীবরকে তার কথা বলার সুযোগ দিতে চেয়েছেন। রাজার আদেশ অনুসারে ধীবরকে মুক্তি দেওয়াও রাজার প্রতি আনুগত্যের পরিচায়ক। শুধু তা-ই নয়, ধীবরের পাওয়া আংটিটি যে রাজাকে প্রিয়জনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, তা বুঝতে পেরে তিনি ধীবরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছেন। তিনি ধীবরকে তাঁর একজন বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধু বলেও গ্রহণ করেছেন।
ধীবর-বৃত্তান্ত পাঠ্যাংশে নাট্যধর্মের যে প্রকাশ ঘটেছে তা আলোচনা করো।
নাট্যধর্মের প্রকার – কালিদাসের ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে নাট্যকার ধীবরের চরিত্রটিকে তার পেশাগত আদর্শ, সাহস এবং স্পষ্ট ভাষণের মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। রাজশ্যালক এবং রক্ষীদের চরিত্রও যথাযথ। তাঁদের উত্তেজিত কথাবার্তা, ক্ষমতা অপপ্রয়োগের চেষ্টা, ধীবরকে তার পেশার জন্য ব্যঙ্গ করা — এসবই সমাজে নীচু শ্রেণির মানুষদের ওপর প্রভাবশালী মানুষদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মনোভাবকে ইঙ্গিত করে। তার সঙ্গে ধীবরের আংটি পাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজার শ্যালক এবং রক্ষীদের যে সংঘাত তার মধ্য দিয়েই নাট্যকার দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রক্ষীরা এবং রাজার শ্যালক আংটির জন্য ধীবরকে চোর সাব্যস্ত করে। ধীবর আংটি পাওয়ার আসল ঘটনা তাঁদের জানিয়ে বলে, “এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন।” রক্ষীরা ধীবরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এভাবেই দুটি আলাদা শ্রেণির মানুষের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সংলাপ রচনাতেও স্বাভাবিকতা বজায় রাখা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত সংলাপের ব্যবহার কাহিনিকে গতিশীল করেছে। রক্ষীদের সংলাপে “ব্যাটা”, “বাটপাড়”, “গাঁটকাটা” শব্দের ব্যবহার নাটকের সংলাপকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। যেভাবে নাট্যদৃশ্যের শেষে ধীবর চোর অপবাদ থেকে মুক্তি পেয়ে রাজার দ্বারা আংটির সমান দামের পুরস্কার পেয়েছে, তা কাহিনির নাটকীয় বিস্তার ঘটিয়েছে। এইভাবেই নাটকটিতে নাট্যধর্মের প্রয়োগ সার্থকভাবে লক্ষ্য করা যায়।
নাট্যকাহিনিতে উপস্থিত না থেকেও রাজা দুষ্মন্ত কীভাবে কাহিনিকে প্রভাবিত করেছেন তা আলোচনা করো।
কাহিনিতে দুষ্মন্তের প্রভাব – কালিদাসের ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশে অনুপস্থিত থেকেও রাজা দুষ্মন্ত সমস্ত ঘটনাধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেছেন। আংটি পাওয়ার বিষয়ে ধীবরের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে দেখতে রাজশ্যালক ও রক্ষীরা তাকে নিয়ে রাজবাড়িতে রাজার কাছে যান। বেশ কিছুটা সময় পরে তিনি রাজার আদেশ নিয়ে ফেরেন এবং রক্ষীদের জেলেটিকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।
রাজার পাঠানো পুরস্কারও রাজশ্যালক জেলেটির হাতে তুলে দেন। এইভাবেই নাট্যাংশের পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। চুরির অভিযোগে বন্দি জেলেটি বহু লাঞ্ছনা, অপবাদ ও বিদ্রূপ সহ্য করার পর এভাবেই মুক্তি পায় ও রাজার কাছে পুরস্কৃত হয়।
স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির রাজাকে রাজশ্যালক আংটিটা দেখালে তিনি মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েন। সেই ঘটনার উল্লেখ করে নাট্যকাহিনিতে সুকৌশলে তাঁর ফেলে আসা দিনগুলির চকিত আভাস দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের কাহিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ আংটিটির হারিয়ে যাওয়া ও সেটির ফিরে পাওয়াকে কেন্দ্র করে রচিত। ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশটিতে রাজা চরিত্রটি সরাসরি উপস্থিত নন। কিন্তু অভিযুক্ত জেলেটিকে সুবিচার দেওয়া ও পুরস্কৃত করার মাধ্যমে তিনি উপস্থিত না থেকেও নাট্যকাহিনিতে নিজের প্রভাব ও গৌরব বজায় রেখেছেন।
রাজার কাছে ধীবরের পাওয়া আংটিটির গুরুত্ব যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।
রাজার কাছে ধীবরের পাওয়া আংটির গুরুত্ব – ধীবর-বৃত্তান্ত নাট্যাংশটিতে শক্রাবর্তবাসী এক ধীবর কীভাবে রাজার নাম খোদাই করা মণিমুক্তাখচিত একটি আংটি বিক্রি করার সময় ধরা পড়ল এবং কীভাবেই বা মুক্তি পেল, সেই বৃত্তান্ত রয়েছে। মহর্ষি কণ্বের তপোবনে শকুন্তলাকে বিয়ে করে রাজধানীতে ফেরার সময় রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একটি আংটি উপহার দেন। দীর্ঘদিন রাজধানী থেকে কেউ শকুন্তলার খোঁজ না নেওয়ায় অস্থির শকুন্তলা দুষ্মন্তের চিন্তায় অন্যমনা হয়ে পড়েন এমনই সময় মহর্ষির আশ্রমে ঋষি দুর্বাসার আগমন ঘটলে স্বামীর চিন্তায় মগ্ন শকুন্তলা তাঁর উপস্থিতি খেয়াল করেন না। এই ঘটনায় অপমানিত ঋষি অভিশাপ দেন, যাঁর চিন্তায় তিনি মগ্ন, সেই ব্যক্তি তাঁকে ভুলে যাবেন। শকুন্তলার প্রিয় সখী প্রিয়ংবদার অনুরোধে ঋষি জানান, কোনো নিদর্শন দেখাতে পারলে তবেই এই শাপের প্রভাব দূর হবে। একদিন এক ধীবরের কাছ থেকে শকুন্তলাকে দেওয়া রাজার আংটিটি উদ্ধার হয় এবং রাজশ্যালক সেটি রাজার কাছে নিয়ে এলে সেই শাপের প্রভাব দূর হয়। রাজার সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি শকুন্তলার চিন্তায় বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাঁর যে কোনো প্রিয়জনের কথা মনে পড়েছে, রাজশ্যালকও তা বুঝতে পারেন। হারানো স্মৃতি ফিরে আসায় উচ্ছ্বসিত রাজা ধীবরকে আংটির সমান দামের অর্থ পুরস্কার হিসেবে দান করেন। রাজার কাছে আংটিটির গুরুত্ব যে কতটা তা এভাবেই নাট্যদৃশ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।
আজকের এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের প্রথম পাঠের দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ -এর কিছু রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নোত্তরগুলো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নবম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত আসে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে, তবে টেলিগ্রামে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত। ধন্যবাদ।






মন্তব্য করুন