এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের পঞ্চম পাঠের প্রথম অধ্যায়, ‘ভাঙার গান’ -এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে কবির পরিচিতি, কবিতার উৎস, কবিতার পাঠপ্রসঙ্গ, কবিতার সারসংক্ষেপ, কবিতার নামকরণ এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এই আর্টিকেলটি আপনাদের ‘ভাঙার গান’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবে এবং কবিতাটি ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া, নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে কবি ও কবিতার সারসংক্ষেপ সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে, তাই এই তথ্যগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
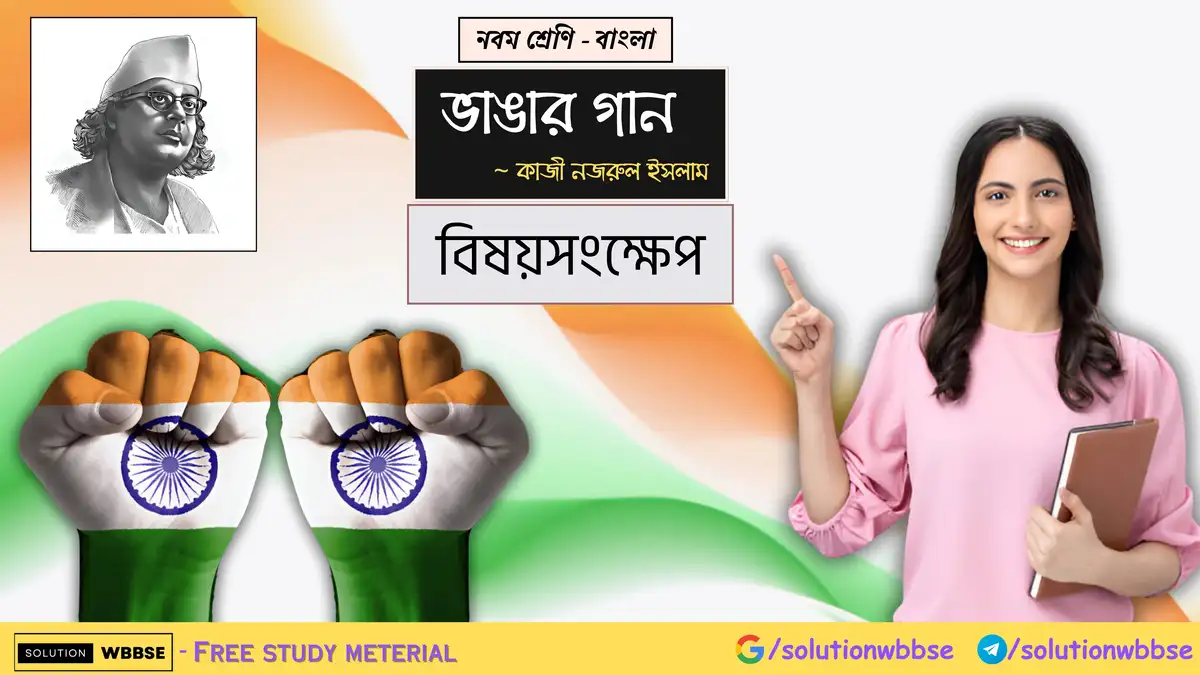
‘ভাঙার গান’ কবিতার কবি পরিচিতি
ভূমিকা –
রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নবীন কাব্যপ্রত্যয় ও জীবনবোধের অতি সহজ অথচ তীব্র জিজ্ঞাসা নিয়ে নজরুল সচকিত করে তুললেন বাঙালি পাঠককুলকে। রবীন্দ্রনাথের শান্ত ও সমাহিত ঋষিসুলভ জীবনবোধ থেকে সরে তিনি কবিতায় আনলেন উদ্দামতা, ঔদ্ধত্য ও অগ্নিগর্ভ চেতনা।
কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও শৈশব –
বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত জামুরিয়া থানার অধীনস্থ চুরুলিয়া গ্রামে 1306 বঙ্গাব্দের 11 জ্যৈষ্ঠ (1899 খ্রিস্টাব্দের 24 মে) কবির জন্ম। পিতার নাম ফকির আহমেদ ও মাতা জাহেদা খাতুন। কাজী ফকির আহমেদের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর চার পুত্রের অকালমৃত্যু হওয়ার পর নজরুলের জন্ম হয় বলেই তাঁর ডাক নাম হয় ‘দুখু মিঞা’।
দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেই কবির শৈশব অতিবাহিত হয়। 1908 খ্রিস্টাব্দে পিতার প্রয়াণের পরে আক্ষরিকভাবেই দু-বেলা আহারের সংস্থান কাজীর পরিবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মক্তবের পড়া শেষ করে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়ার বদলে তাঁকে অর্থ উপার্জনের চিন্তা করতে হয়েছে। অর্থের জন্য, পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গ্রামে গ্রামে মোল্লাগিরি, বাজারে খাদেমগিরি, মসজিদে ইমামগিরি, লেটোনাচের গান, পালা রচনা প্রভৃতি কাজ তাঁকে করতে হয়েছে।
কাজী নজরুল ইসলামের সেনাবাহিনীতে যোগদান –
রানিগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র নজরুল প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রাক্কালে সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধে 49 নং বাঙালি পল্টনের সৈনিকরূপে কাজী নজরুল প্রথমে লাহোরে যান এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যান করাচি। নজরুলের সৈনিক জীবন 1917 থেকে 1919 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সৈনিকের অবস্থান থেকে পরবর্তীকালে তিনি 49 নং বাঙালি পল্টনের কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদারের পদে উন্নীত হন।
কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক জীবন থেকে প্রত্যাবর্তন –
যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটনার ঘনঘটা থেকেই শুরু হয় কবির জীবনের নতুন অধ্যায়। সেনাবাহিনীতে থাকার সময়কালেই তিনি রচনা করতে থাকেন গল্প, কবিতা, গান ইত্যাদি। কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘মুক্তি’ 1919 খ্রিস্টাব্দে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’-য় প্রকাশিত হয়। নজরুল কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন ‘ক্ষমা’। পরিবর্তিত নামকরণটি করেন পত্রিকা সম্পাদক মুজাফ্ফর আহমদ। সেনাবাহিনীতে থাকার সময়েই তিনি ‘ব্যথার দান’ ও ‘হেনা’ নামে দুটি গল্পও রচনা করেন। পরবর্তীকালে বাঙালি পল্টন ভেঙে গেলে তিনি 1920 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতায় চলে আসেন।
কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি ‘মোসলেম ভারত’, ‘নবযুগ’ প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নজরুল কলকাতায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন – শুধু কবিতার কারণেই নয়, গানের জন্যও। বহু হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরেও নজরুল তাঁর গান ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে অনায়াসে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর গলায় অন্যান্য গানের পাশাপাশি এত বেশি করে রবীন্দ্রসংগীত ধ্বনিত হত যে তাঁকে বলা হত ‘রবীন্দ্রসংগীতের হাফিজ’।
পরবর্তীকালে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে কবির সংযোগ হয় এবং তিনিই প্রমাণ করেন যে, সুন্দর রচনার সঙ্গে সুন্দর সুরের সমাবেশ রেকর্ড বিক্রি বাড়িয়ে দেয়।
কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যসাধনা –
1922 খ্রিস্টাব্দে নজরুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘ব্যথার দান’ প্রকাশিত হয়। এ বছর তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’ প্রকাশিত হয়। 1922 খ্রিস্টাব্দের 11 আগস্ট আত্মপ্রকাশ করে কবির সম্পাদিত পত্রিকা ‘ধূমকেতু’, যার প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। এই সংখ্যা থেকেই অনুমান করা যায় তাঁর জনপ্রিয়তা কতখানি ছিল। সপ্তাহে দু-বার প্রকাশিত হত এই পত্রিকা। কবিগুরুর আশীর্বাদধন্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত জাতীয়তাবাদের কথা। ‘ধূমকেতুর পথ’ নামক লেখাতে কবি তাঁর সম্পাদকরূপের আদর্শ, নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সোচ্চারে বলেছেন – “দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি, তা সব দূর করতে ধূমকেতু হবে আগুনের সম্মার্জনী। … ধূমকেতু কোনো সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম।”
কাজী নজরুল ইসলামের কারাবরণ –
‘ধূমকেতু’ যে জাতির অচলায়তন মনকে অহর্নিশি ধাক্কা দিচ্ছে রাজশক্তি তা অনুধাবন করে এবং পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। 1923 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নজরুল ‘ধূমকেতু’-র কারণে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বাংলা সাহিত্যের জগতে নজরুলই প্রথম কবি যিনি তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই কারাবাসকালেই কবিগুরু তাঁর ‘বসন্ত’ নাটিকাটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন।
কাজী নজরুল ইসলামের লাঙল পত্রিকা –
পরবর্তী পর্যায়ে 1925 খ্রিস্টাব্দের 25 ডিসেম্বর নজরুল সম্পাদিত ‘লাঙল’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। ‘লাঙল’ পত্রিকার জন্যও রবীন্দ্রনাথের যে আশীর্বাণী ছিল সেটি হল –
“ধর, হাল বলরাম, আন তব মরু ভাঙা হল,
বল দাও, ফল দাও, স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।”
নজরুলের কবিতাই ছিল ‘লাঙল’-এর বিশেষ সম্পদ।
কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসম্ভার –
সত্যের খাঁটি উপাসক নজরুল ‘চড়া গলার কবি’। জাতি ও ধর্মের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলেই তিনি লোকপ্রিয়। তিনি তাই মানুষের কবি। তিনি বাংলার সাহিত্য এবং বাঙালির জীবনে প্রবল উন্মাদনার সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর এক হাতে ছিল অসি, অপর হাতে বাঁশি। কাব্যরচনার সবরকম অভ্যস্ত নীতি ও নিয়মকে অতিক্রম করে তিনি যে অবিমিশ্র নবীনতার স্বাদ এনেছিলেন তাঁর কবিতায় তা কালবৈশাখীর রুদ্ররূপকেই মনে করায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাই বলেছেন – ‘নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের জগতের ছন্দময় এক দুরন্ত ঝটিকা বেগ।’ কবির লেখা কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – ‘অগ্নিবীণা’, ‘বিষের বাঁশি’, ‘দোলনচাঁপা’, ‘ভাঙার গান’, ‘ফণিমনসা’, ‘সাম্যবাদী’, ‘সর্বহারা’, ‘সিন্ধু-হিন্দোল’, ‘ঝিঙে ফুল’। কবির সংগীতগ্রন্থ – ‘চন্দ্রবিন্দু’, ‘সুরসাকী’, ‘গানের মালা’, ‘রাঙাজবা’, ‘সন্ধ্যামালতী’ ইত্যাদি। তা ছাড়াও কবির শিশু কবিতা সংকলন ‘প্রভাতী’, উপন্যাস এবং গীতি আলেখ্য ইত্যাদি বিষয়ে রচনা আছে।
কাজী নজরুল ইসলামের কবিচেতনা –
নজরুল সার্থকভাবে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার কবি। কোনোরূপ ভৌগোলিক পরিবর্তনে কবির সৃষ্টির অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে না। তিনি যেমন কোনোদিনই গতানুগতিকতার স্রোতে চলেননি তেমনি তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য বাংলার কোমলকান্ত নিস্তেজ জীবনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে বৃহত্তর মুক্ত জীবনের ডাক শুনিয়েছিল। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন বলেই শেষজীবনে কবি নির্বাক, বোধহীন এবং কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েন। 1976 খ্রিস্টাব্দের 29 আগস্ট ভারতের বিদ্রোহী স্বাধীন কবি বাংলাদেশের ঢাকা শহরে চিরশান্তির লোকে পাড়ি দেন। ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি কবির মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বলেন – “তাঁর সক্রিয় জীবনে কবি যা লিখেছেন তা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। তাঁর মৃত্যু ভারত এবং বাংলাদেশকে রিক্ত করে দিয়েছে।” স্বাধীনতা এসেছিল এক বাংলা বিভক্ত হয়ে দুই বাংলারূপে। কিন্তু নজরুলকে বিভক্ত করা যায়নি। কারণ তিনি দুই বাংলার যোগাযোগের অন্যতম সেতু। তাই কবি-সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় লিখেছেন –
‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল।’
‘ভাঙার গান’ কবিতার উৎস
বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ‘ভাঙার গান’ গীতিকাটি ‘পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি’ থেকে প্রকাশিত ‘কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র’ (প্রথম খণ্ড) থেকে গৃহীত হয়েছে। আবদুল আজিজ আল আমান সম্পাদিত ‘নজরুল রচনা সম্ভার’ (প্রথম খণ্ড – নজরুল গীতি) গ্রন্থের ‘দেশাত্মবোধক পর্যায়’ অংশেও গানটির সন্ধান মেলে। কল্যাণী কাজী সম্পাদিত ‘নজরুল গীতি সমগ্র’, কাজী অনিরুদ্ধ সম্পাদিত ‘সুনির্বাচিত নজরুল গীতিকা স্বরলিপি’ গ্রন্থেও গীতিকাটি সংকলিত হয়েছে। গীতিকাটির মূল উৎসগ্রন্থ হল ‘ভাঙার গান’ (1924 খ্রিস্টাব্দ)। অবশ্য এই গীতিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত ‘বাংলার কথা’ পত্রিকায়। 1921 খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাস নাগাদ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন গীতিকাটি রচিত হয়েছিল।
‘ভাঙার গান’ কবিতার পাঠপ্রসঙ্গ
‘ভাঙার গান’ (1924 খ্রিস্টাব্দ) কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘ভাঙার গান’। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত ‘বাংলার কথা’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় নজরুলের এই গীতিকাটি। দেশবন্ধু তখন জেলে, 1921 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস নাগাদ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন নজরুল রচনা করেছিলেন ‘ভাঙার গান’। দেশবন্ধুজায়া বাসন্তী দেবীর অনুরোধে নজরুল তাঁর মেস বাড়িতে মুজাফ্ফর আহমদের উপস্থিতিতে তক্তাপোশে বসে অল্প সময়ের মধ্যেই রচনা করেছিলেন এই কবিতাটি, মুজাফ্ফর আহমেদ তাঁর নজরুল সম্পর্কিত স্মৃতিচারণায় এ কথা জানিয়েছেন। সম্ভবত তখনও গানটিতে সুরারোপ হয়নি। অনুমিত হয় গানটিতে তিনি সুরারোপ করেছিলেন কারাগারে বসে 1923 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। উক্ত গানের শীর্ষনাম ‘ভাঙার গান’ই কাব্যের নামরূপে গৃহীত হয়। প্রথম প্রকাশকালে ‘কারার ওই লৌহ-কপাট’ এইরূপ বানান ব্যবহৃত হয়েছিল।
1920 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট থেকে 1922 খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উন্মাদনা নজরুলের বিপ্লবী কবিচিত্তকেও স্পর্শ করেছিল। কিন্তু ‘সাম্যবাদী’ কবিতাগুচ্ছ প্রকাশের পর থেকে গান্ধি রাজনীতি থেকে সরে এসে তিনি গান্ধি রাজনীতির তীব্র সমালোচক হয়ে যান। আসলে নজরুলের যে মানসগঠন, তাতে গান্ধিনীতি খাপ খায়নি। যাই হোক দেশের এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে তিনি লেখেন এই গান –
‘কারার ওই লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট’
ভাঙার কাজে তিনিই প্রথম হাত লাগিয়ে আর সকলকে ডাক দিয়েছেন। অনুভূতির এই অকৃত্রিমতা ও সতেজতা নজরুলের কবিতায় আগাগোড়া বর্তমান।
নজরুলের এই ‘ভাঙার গান’টি সম্পর্কে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে একবার বলেছিলেন – “জেলে যখন ওয়ার্ডাররা লোহার দরজা বন্ধ করে, তখন মন কী যে আকুলি-বিকুলি করে কী বলব! তখন বারবার মনে পড়ে কাজীর ওই গান – “কারার ওই লৌহ-কপাট……প্রাচীর ভেদি।”
বিখ্যাত সাহিত্যিক ইন্দুভূষণ রায় তাঁর ‘নজরুল গীতি পরিচয়’ গ্রন্থে জানিয়েছেন, এই গানটি রচিত হয়েছে ইমানি বিলাবল রাগের ভিত্তিতে। তিনি কুমিল্লায় অবস্থানকালে অনেকগুলি গান লেখেন, তার মধ্যে ভাঙার গান ‘কারার ওই লৌহ-কপাট’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ‘নজরুল স্মৃতিমাল্য’ গ্রন্থে জানিয়েছেন, ইংরেজদের কারাগারে বন্দি দেশভক্তদের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। বাইরে বেরোনো বন্ধ হল। বন্দির সঙ্গে বন্দিরাও কথা বলতে পারত না। বন্দি নজরুল তখন গান ধরতেন –
“কারার ওই লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট”
গান শুনে বিক্ষুব্ধ বন্দিদের বুকে শিহরণ জাগত। তারা জেল কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হত। কবি এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দিকে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়ে সেলে বন্দি করে অন্যান্য কয়েদিদের থেকে দূরে সরিয়ে দিল। কবি তখন ‘শিকল পরার গান’ রচনা করে সেলের লোহার গরাদে হাতকড়ার ঘা দিয়ে বাজিয়ে গাইলেন –
“এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।।”
‘ভাঙার গান’ কবিতার বিষয়সংক্ষেপ
1924 খ্রিস্টাব্দে রচিত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘ভাঙার গান’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘ভাঙার গান’ গীতিকাটি মূলত পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের প্রেরণার মূলমন্ত্র।
আলোচ্য কবিতায় কবি পরাধীন ভারতবাসীকে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে কেবল জেলখানার লৌহকপাটই ভাঙতে বলেননি, সমগ্র ভারতবর্ষ যেভাবে ইংরেজ সরকারের ঔপনিবেশিক কারাগারে পরিণত হয়েছে, তার ভিত নড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন।
কবি তরুণ ভারতীয় বিপ্লবীদের নির্দেশ দিয়েছেন ভীম কারাগারের লৌহকপাটটিকে ভেঙে ফেলে লোপাট করবার জন্য। পাষাণবেদি আজ বিপ্লবীদের রক্তে জমাট হয়ে আছে। তরুণ সম্প্রদায়কে ঈশান মহাদেব শিবের সঙ্গে তুলনা করে কবি তাদের শিবের মতোই প্রলয়ংকর হয়ে উঠতে আহ্বান জানিয়েছেন। মহাদেব যেমন নতুন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রলয় নৃত্যে মেতে ওঠেন, পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত নতুন ভারত গঠনের লক্ষ্যে নজরুল তেমনি ধ্বংসের সাধনা করতে বলেছেন নবীন প্রজন্মকে। কবি তাদের উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন যে, মানুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ‘সাজা’ দেওয়ার অধিকার কোনো ‘রাজা’ বা ‘মালিক’ -এর নেই। ভগবানকে ফাঁসি দেওয়া যেমন হাস্যকর, অর্থহীন তেমনই বিপ্লবীদের ফাঁসি দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইকে থামানোর চেষ্টা বৃথা এবং অর্থহীন ব্যাপার।
কবি ‘পাগলা ভোলা’ অর্থাৎ তরুণ ভারতীয়দের আহ্বান করে বলেছেন, ‘পাগলা ভোলা’ যেন প্রলয় দোলার সাহায্যে হ্যাঁচকা টানে গারদগুলোকে ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেন। এই ‘পাগলা ভোলা’ নবজীবনের অগ্রদূত। তাই কবির নির্দেশ পাগলা ভোলা যেন জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ভাবনাহীন চিত্ত হয়ে হৈদরী হাঁক দিয়ে দুন্দুভি ঢাক কাঁধে নিয়ে মৃত্যুকে জীবনপানে ডেকে আনেন।
নজরুল লক্ষ করেছেন মহাদেব তাঁর প্রলয় নৃত্য শুরু করেছেন, আর নষ্ট করবার সময় নেই। বন্দি বিপ্লবীদের প্রতি কবির তাই নির্দেশ তারা যেন ওই ভীম কারার ভিত নাড়িয়ে দেয়, লাথি মেরে কারাগারের তালা ভেঙে দেয়, বন্দিশালায় আগুন জ্বালিয়ে সবকিছুকে লোপাট করে দেয়।
‘ভাঙার গান’ কবিতার নামকরণ
ভূমিকা –
সাহিত্যে নামকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নামহীন সৃষ্টি অনেকটা মস্তিষ্কহীন মানবদেহের মতো। যদিও সাহিত্যে নামকরণের নির্দিষ্ট কোনো রীতি প্রচলিত নেই, তবুও মোটামুটিভাবে নামকরণ চরিত্রকেন্দ্রিক, বিষয়কেন্দ্রিক ও ব্যঞ্জনাধর্মী – এই তিন ধরনের হয়ে থাকে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘ভাঙার গান’ মূলত একটি গীতিকা। গীতিকার নামকরণ সাধারণত হয় না। তবুও সংকলকগণ মূল গ্রন্থের নামানুসারে নাম দিয়েছেন ‘ভাঙার গান’। এখন বিষয়বস্তু আলোচনা করে দেখব সংকলকগণ কর্তৃক প্রদত্ত নামকরণ কতখানি সার্থক।
বিষয়বস্তু –
পরাধীন ভারতভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি নজরুল ইংরেজদের কারাগারে বন্দি অসংখ্য বীর বিপ্লবীদের উজ্জীবিত করতে চেয়ে কারাগারের কঠিন লৌহকপাটকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। পাষাণবেদি তখনও বীর বিপ্লবীদের রক্তে রঞ্জিত; তাই তরুণ ঈশানের কাছে কবির প্রত্যাশা, তরুণ ঈশান যেন তার প্রলয় বিষাণ বাজিয়ে ধ্বংস নিশান উড়িয়ে ‘প্রাচী’র প্রাচীরকে ভেদ করে। মহাদেব যেমন নতুন সৃষ্টির উদ্দেশে প্রলয় নৃত্যে মেতে ওঠেন, পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারত গঠনের লক্ষ্যে নজরুল তেমনি ধ্বংসের সাধনা করতে বলেছেন তরুণ প্রজন্মকে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ‘সাজা’ দেওয়ার অধিকার কোনো ‘রাজা’ বা ‘মালিকে’র নেই। ভগবানকে ফাঁসি দেওয়া যেমন হাস্যকর, সর্বনাশা ভাবনা, তেমনিই বিপ্লবীদের ফাঁসি দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইকে থামানোর চেষ্টা অর্থহীন। এই হীন তথ্যের প্রকাশে কবির তাই হাসি পায়। বিপ্লবীদের কবি বলেছেন প্রলয় দোলাতে গারদগুলোকে হ্যাঁচকা টান মেরে বিনষ্ট করে, মৃত্যুকে জীবনপানে ডেকে আনতে হবে। অপচয় করার আর সময় নেই। তাই কবি বিপ্লবীদের সত্বর গরাদ ভেঙে বন্দিশালায় আগুন জ্বালাবার নির্দেশ দিয়েছেন।
উপসংহার –
সমগ্র গীতিকা জুড়ে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ তরুণ বিপ্লবীদের যেমন কবি জেলখানার লৌহকপাট ভেঙে ফেলতে বলেছেন, ব্যাপক অর্থে আবার ভারতবর্ষের বুকে স্থাপিত ইংরেজ সরকারের ঔপনিবেশিক কারাগারটি ভেঙে ফেলারও আহ্বান জানিয়েছেন। ভাঙার কথা গীতিকাটিতে প্রাধান্য পেয়েছে বলে সংকলকবর্গ প্রদত্ত ‘ভাঙার গান’ নামকরণ সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।
এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের পঞ্চম পাঠের প্রথম অধ্যায়, ‘ভাঙার গান’ -এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবো। এখানে কবির পরিচিতি, কবিতার উৎস, কবিতার পাঠপ্রসঙ্গ, কবিতার সারসংক্ষেপ, কবিতার নামকরণ এবং এর প্রধান বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আর্টিকেলটি আপনাদের ‘ভাঙার গান’ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়েছে এবং কবিতাটি ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এছাড়া, নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে কবি পরিচিতি, কবিতার নামকরণ ও কবিতার সারসংক্ষেপ সম্পর্কিত প্রশ্ন আসতে পারে, তাই এই তথ্যগুলো জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

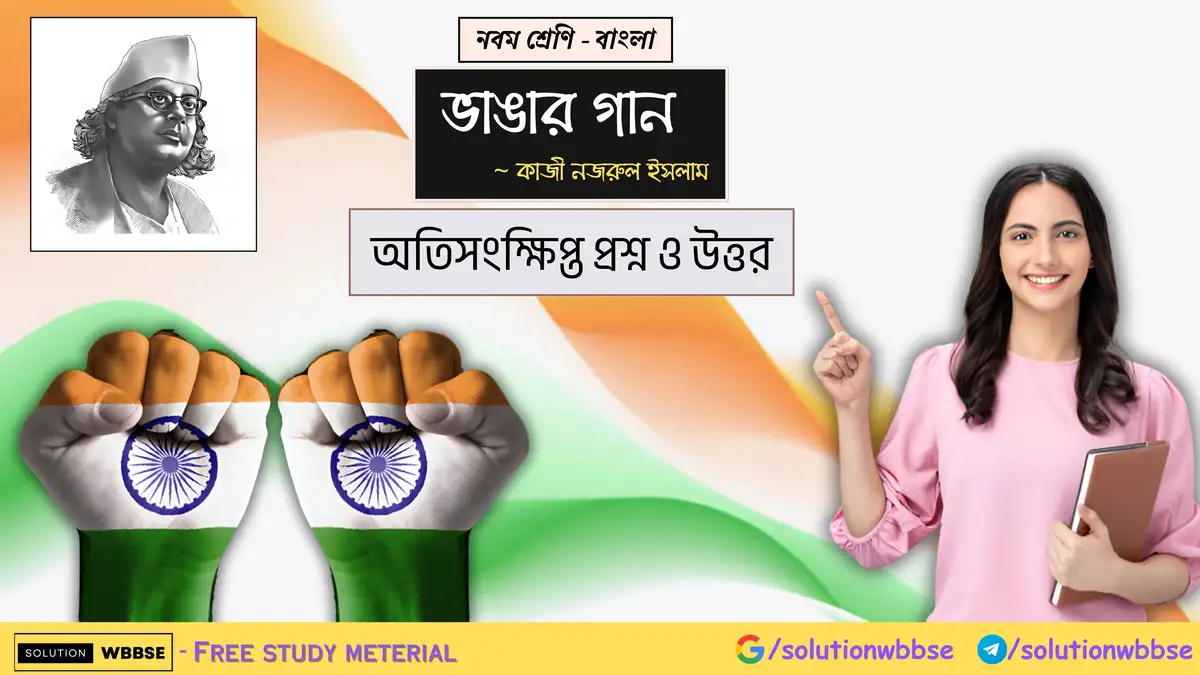


মন্তব্য করুন