ইতিহাসের ধারণা হলো অতীতের ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার অধ্যয়ন এবং ব্যাখ্যাকে বোঝায়, সেইসাথে সময়ের সাথে সাথে লোকেরা এই ঘটনাগুলিকে বোঝা এবং উপস্থাপন করেছে। এটি অতীতের ঘটনাগুলির কারণ এবং পরিণতিগুলির পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটগুলি যেখানে তারা ঘটেছে তা পরীক্ষা করা জড়িত।
ইতিহাসের অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আমাদের বর্তমানকে আরও ভালভাবে বুঝতে এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে দেয়। অতীতের ঘটনাগুলি পরীক্ষা করে, আমরা মানব সমাজের জটিলতা এবং দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারি, সেইসাথে ইতিহাস জুড়ে লোকেরা চ্যালেঞ্জ এবং দ্বন্দ্বের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

ইতিহাস কী?
সমাজবদ্ধ মানুষের অতীতাশ্রয়ী জীবনকাহিনীই হল ইতিহাস। এর মূল বিষয় হল সময় মানুষ ও সমাজ।অতীতের রাজনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কাজকর্মও ইতিহাসের অন্তর্গত।
ঐতিহাসিক তথ্য কী?
মানবসমাজের বিভিন্ন ঘটনা সমসাময়িক দলিল – দস্তাবেজ বা অন্যান্য লিখিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে নিহিত থাকে। একজন ঐতিহাসিক বা গবেষক এই সমস্ত উপাদান থেকে সঠিক তথ্য নির্বাচন করে ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। এধরনের সঠিকতথ্যই ঐতিহাসিক তথ্য নামে পরিচিত।
ঐতিহাসিকের কাজ কী?
ঐতিহাসিকের কাজ হল তথ্য উপস্থাপন ও তা বিশ্লেষণ। ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ভন র্যাঙ্কের মতে, যেমনভাবে ঘটনা ঘটেছিল ঠিক তেমনটাই উপস্থাপিত করা হল ঐতিহাসিকের কাজ। অন্যদিকে ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাকটনের মতে, ঐতিহাসিকের দেওয়া তথ্যের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ ছাড়া ইতিহাস অর্থহীন।
আধুনিক ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গুলি চিহ্নিত করো।
আধুনিক ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হল – যুক্তিবাদী, আপেক্ষিকতাবাদী, দৃষ্টবাদী, মার্কসবাদী, প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়াও রয়েছে অ্যানাল গোষ্ঠীর মতবাদ, জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, নিম্নবর্গীয় মতবাদ এবং সামগ্রিক সমাজ বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।
প্রচলিত ইতিহাসচর্চা কী?
প্রচলিত ইতিহাস বলতে বোঝায় রাজকাহিনী। রাজার যুদ্ধ জয়, দেশ শাসন, রাজস্ব আদায় ও সাংবিধানিক কাজকর্মের ইতিহাসই ছিল প্রচলিত ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়। বিংশশতকের গোড়া থেকে এই ধরনের ইতিহাসচর্চায় সমাজ ও অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়গুলিও যুক্ত হতে শুরু করে।
নতুন সামাজিক ইতিহাস কী?
১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে নাগরিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক আন্দোলনের কারণে ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সূচনা হয়। ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইতিহাসচর্চায় সমাজের অবহেলিত দিকগুলিসহ সমগ্র সমাজের ইতিহাস রচনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এভাবে গড়ে ওঠে নতুন সামাজিক ইতিহাস এবং এর বিভিন্ন দিকগুলি হল — সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, জাতি-বর্ণ ও জাতিবিদ্বেষ, হিংসা ও সম্প্রীতি।
নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চার প্রতিষ্ঠান ও তার মুখপত্রের নাম কী?
নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চার প্রতিষ্ঠানটি হল দ্য সোশ্যাল সায়েন্স হিস্ট্রি অ্যাসোশিয়েশন (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। এটির মুখপত্র হল সোস্যাল সায়েন্স হিস্ট্রি।
ভারতে নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চার কয়েকটি কেন্দ্রের নাম লেখো।
ভারতে নতুন সামাজিক ইতিহাসচর্চার কয়েকটি কেন্দ্রের নাম হল দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার সেন্টার ফর হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ সেন্টার।
খেলার ইতিহাস বলতে কী বোঝায়?
আধুনিক সভ্যতায় অবসর বিনোদন ও শারীরিক দক্ষতা প্রদর্শনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হল খেলা বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিস, গল্ফ, দাবা, রাগবি প্রভৃতি খেলার উদ্ভব, বিবর্তন, প্রসার ও প্রভাব সম্পর্কে শুরু হওয়া ইতিহাসচর্চা খেলার ইতিহাস নামে পরিচিত।
ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলার উদ্ভবকে কিভাবে চিহ্নিত করবে?
আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে ইংল্যান্ডে স্টিক অ্যান্ড বল নামক খেলা থেকেই ক্রিকেট খেলার উদ্ভব ঘটেছে। এই খেলা ছিল প্রাক শিল্প বিপ্লব পর্বের খেলা – তাই হস্তনির্মিত ব্যাট ও স্ট্যাম্প বেল, বল হত কাঠের তৈরি। আঠারো শতকে এই খেলা একটি পরিণত খেলার চরিত্র লাভ করে।
ক্রিকেট খেলার প্রাথমিক পর্বের কয়েকটি দিক চিহ্নিত করো।
প্রিয়ার ক্রিকেট খেলার প্রাথমিক পর্বের কয়েকটি দিক হল – 1. নির্দিষ্ট মাপের বল ও ব্যাট এবং ২২ গজের পিচ ও উইকেট ব্যবহৃত হত। 2. খেলার মাঠের আকৃতি ডিম্বাকৃতি হলেও এর দৈর্ঘ্য বা আয়তনের কোনো নির্দিষ্ট মাপ ছিল না। 3. প্রথমদিকে এই খেলার সময়সীমা নির্দিষ্ট না থাকলেও পরে তিনদিনের টেস্ট বা নির্দিষ্ট ওভারের একদিনের ম্যাচ শুর হয়।
ভারতে কিভাবে ক্রিকেট খেলার সূচনা হয়?
১৭২১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের সূত্র ধরেই ভারতে ক্রিকেট খেলার সূচনা হয়। তবে তা ভারত ইংরেজ সামরিক বাহিনি ও শ্বেতাঙ্গদের ক্লাব বা জিমখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আঠারো শতকের শেষে ভারতে প্রথম ক্রিকেট ক্লাব রূপে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় – ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব (১৭৯২খ্রিস্টাব্দ)।
ভারতে কীভাবে হকি খেলার সূচনা হয়?
ভারতে মূলত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর হাত ধরেই হকি খেলার প্রসার ঘটে এবং কলকাতায় ভারতে প্রথম হকি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দ)। বিশ শতকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে অলিম্পিক গেমসে ভারত প্রথম অংশগ্রহণ করে এবং শেষপর্যন্ত ফাইনাল খেলায় হল্যান্ডের কাছে ভারত ৩-০ গোলে পরাজিত হয়। ধ্যানচাঁদ ছিলেন ভারতের একজন বিখ্যাত হকি খেলোয়াড়।
পোলো খেলার সূচনা ও বৈশিষ্ট্য লেখো।
পোলো খেলার উদ্ভব হয় ইংল্যান্ডে। ঘোড়ার পিঠে চেপে পোলো স্টিকের সাহায্যে পোলো বলকে নিয়ন্ত্রণ করে বিপক্ষ দলকে পরাজিত করাই এই খেলার রীতি। ভারতে ইংরেজ শাসক ও সৈন্যদের মাধ্যমেই পোলো খেলার প্রসার ঘটেছিল।
খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চা বলতে কী বোঝায়?
মানুষের প্রতিদিনের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত ইতিহাসচর্চা খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চা নামে পরিচিত। এর মূল বিষয় হল দেশী ও বিদেশি খাবার গ্রহণ বা বর্জন, দেশজ ও ঔপনিবেশিক খাদ্যসংস্কৃতির মতে সংঘাত, স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সামঞ্ঝস্য রেখে খাদ্যাভ্যাস, বিভিন্ন ধরনের খাবারের উদ্ভব ও তার বিবর্তন আলোচনা।
ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে বাংলায় খাদ্যাভ্যাসে কী পরিবর্তন এনেছিল?
ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে বাঙালির ভাত, ডাল,সবজি, রুটি ও আমিষ (মাছ, মাংস) খাবারের পাশাপাশি পাশ্চাত্য খাবারের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিল। তবে এই আকর্ষণ শহরে বসবাসকারী ইংরেজি শিক্ষিত পেশাজীবি (শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রেণি) শ্রেণির একাংশের মধ্যেই সীমিত ছিল। এঁরা শাসক ইংরেজদের ভোজনসভায় উপস্থিত হয়ে এদেশীয় সামাজিক বিধিনিষেধ ভেঙে নিষিদ্ধ মাংস, চা, কফি, সিগারেট ও মদ্যপান করত।
শিল্পচর্চার ইতিহাস বলতে কী বোঝায়?
কলাশিল্পী যখন তার শরীরের কোনো নির্দিষ্ট বা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে আবেগ বা ভালো বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তখন তা শিল্পচর্চা নামে পরিচিত হয়। এর চারটি দিক, যথা — সংগীত, নৃত্য, নাটক ও চলচ্চিত্র। শিল্পচর্চার উদ্ভব, বিবর্তন ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করাই শিল্পচর্চার ইতিহাস নামে পরিচিত।
নৃত্যশিল্পের ইতিহাসের কয়েকটি দিক চিহ্নিত করো।
ছন্দ বা গানের তালে তালে মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনই হল নৃত্য। শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় নৃত্যের পাশাপাশি ভাবাবেগ প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের নৃত্য রয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিপ-হপ নৃত্য, চীনের ইয়াংকো নৃত্য, ভারতের কথক, ফ্রান্স ও রাশিয়ার ব্যালে নৃত্য।
চলচ্চিত্রের ইতিহাস বলতে কী বোঝায়?
১৮৩০-এর দশকের পরবর্তীকালে বাণিজ্যিকভাবে ক্যামেরার ব্যবহার ও স্থিরচিত্রের পাশাপাশি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উন্নত ক্যামেরার মাধ্যমে সচল ছবি তোলার প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ঘটে। প্রথমদিকে কোনো ঘটনা বা গল্পকে কেন্দ্র করে তৈরি এই সচল ছবি ছিল নির্বাক। শেষ পর্যন্ত বিশ শতকের গোড়ায় আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে সবাক ও সচল ছবি তৈরি হয়, যা চলচ্চিত্র নামে পরিচিত।
পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধির ধারণাটি কী?
আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে নারী পোষাক ছিল বেশ আঁটোসাঁটো অথচ বস্ত্রবহুল যা নারীকে স্বাচ্ছন্দের বদলে অস্বস্তি প্রদান করত। এইরূপ পোষাক পরিধানের ফলে নারীর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেত, অর্থাৎ এইরূপ পোষাক পরিধান অসুস্থতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শরীরের পক্ষে আরামদায়ক এবং হাঁটা চলার সুবিধার্থে পোষাক-পরিচ্ছদ রীতিতেও পরিবর্তন আসে।
উনিশ শতকে ভারতে পারসি ও বাঙালিবাবুদের পোষাক কেমন ছিল?
উনিশ শতকে ক্রমশ ভারতে পাশ্চাত্যরীতির পোষাক পরিচ্ছদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে প্রথমে পারসি ও পরে বাঙালি বাবুদের পোষাক পরিচ্ছদে পরিবর্তন আসে। পারসিরা ঢোলা ফুল প্যান্ট ও কলারবিহীন লম্বা কোট পরিধান করত। আবার বাঙালিবাবুরা ধুতির উপর কোট, মাথায় টুপি ও পায়ে বুট জুতা ব্যবহার করত।
যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস বলতে কী বোঝো?
প্রিয়ার জল, স্থল ও আকাশপথের যানবাহনের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া আসা এবং একস্থানে বসে টেলিগ্রাফ টেলিফোন-মোবাইল ফোন, চিঠিপত্র, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানের খবর সংগ্রহ বা প্রেরণ ব্যবস্থার উপর গড়ে ওঠা ইতিহাসচর্চা যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস নামে পরিচিত। এই ইতিহাসচর্চায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের উপর যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাবকে চিহ্নিত করা হয়।
ভারতে রেলপথ ব্যবস্থার প্রবর্তন কীভাবে হয়?
ভৌত্তর মূলত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্যে ইংরেজ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে রেলপথ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে (২৬ এপ্রিল, ১৮৫৩ খ্রি.)। প্রথমে মহারাষ্ট্রের বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত ছিল এর ব্যাপ্তি। পরবর্তীকালে গ্যারান্টি প্রথার মাধ্যমে ভারতে রেলপথের বিকাশ ঘটে।
ভারতে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন কীভাবে হয়?
ভারতে রেলপথের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনে টেলিগ্রাফের বিস্তার ঘটেছিল। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথমে কয়েক মাইল জুড়ে টেলিগ্রাফের বিস্তার ঘটলেও ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ৪৬টি টেলিগ্রাফ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৪,২৫০ মাইল এলাকা টেলিগ্রাফ যোগাযোগের আওতায় আসে।
স্থানীয় ইতিহাস বলতে কী বোঝায়?
ভৌগোলিকভাবে স্থানীয় প্রেক্ষিতে স্থানীয় সম্প্রদায় বা ব্যক্তি বা বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ইতিহাসই হল স্থানীয় ইতিহাস। স্থানীয় জনশ্রুতি, মিথ বা অতিকথ। মৌখিক পরম্পরাকে ভিত্তি করে স্থানীয় ইতিহাস রচনা করা হয়। এভাবে স্থানীয় ইতিহাসসমূহের সমন্বয়ে দেশের ইতিহাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।
শহরের ইতিহাস কী?
শহরের উদ্ভব, বিকাশ, বিস্তার ও অবক্ষয় সম্পর্কিত ইতিহাস চর্চা হল শহরের ইতিহাস। এছাড়া শহরের বাসিন্দা ও তাদের সমাজবিন্যাস এবং তাদের কার্যকলাপসহ শহরের আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে চিহ্নিত করাও এই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯২০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শহরের ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়।
সামরিক ইতিহাস বলতে কী বোঝায়?
রাষ্ট্রের উদ্ভব ও তার বিস্তার এবং ভৌমিক সাম্রাজ্যবাদ ও তার প্রসারকে কেন্দ্র করে প্রাচীনযুগেই যুদ্ধের সূচনা হয়।যুদ্ধ ইতিহাস অর্থাৎ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, যুদ্ধাস্ত্রের বিবর্তন, যুদ্ধের প্রকৃতি ও প্রভাবকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা থেকেই গড়ে উঠেছে সামরিক ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ঠান্ডাযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার কথা বলা যায়।
পরিবেশের ইতিহাস কী?
পরিবেশের অর্থাৎ প্রকৃতি জগতের সঙ্গে মানবসমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসই হল পরিবেশ ইতিহাস। পৃথিবী সৃষ্টির কাল থেকে মানুষের আবির্ভাব এবং পশুশিকারী জীবন থেকে আধুনিক মানব সভ্যতার উদ্ভবের পশ্চাতে পরিবেশের ভূমিকা ও অবদানকে চিহ্নিত করাই হল এই ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা থেকেই পরিবেশের ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছে।
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস বলতে কী বোঝায়?
বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশ ও বিবর্তন, প্রযুক্তির উদ্ভব ও তার অগ্রগতি এবং চিকিৎসাবিদ্যার বিবর্তন সম্পর্কিত ইতিহাসচর্চা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস নামে পরিচিত। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যা কিভাবে মানবসমাজ ও সংস্কৃতিকে এই দেশের আর্থ-সামাজিক, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা কেন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে তার অগ্রগতির পরিমাপ করাই এই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। আদিম সভ্যতা থেকে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার উত্তরণই হল এই ইতিহাসচর্চার পরিধি।
নারী ইতিহাস কী?
প্রচলিত পুরুষকেন্দ্রিক ইতিহাসের সংশোধন ঘটিয়ে সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে নারীর অবদান ও ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চাই হল নারী ইতিহাস। এই ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বে মহীয়সী নারীদের সম্পর্কে ইতিহাসচর্চা করা হলেও বর্তমানে সাধারণ নারীরাও এর অন্তর্গত। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে চিহ্নিত করাই এই ইতিহাসের প্রধানতম দিক।
সরকারী নথিপত্র ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বনের কারণ কী?
সরকারী নথিপত্র ব্যবহারকালে সতর্কতা অবলম্বনের কারণগুলি হল — এগুলি মূলত সাম্রাজ্যবাদী ও প্রশাসকের দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হয়েছে। তাই অনেকক্ষেত্রেই ঘটনার অন্য ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে ঘটনার গুরত্ব বৃদ্ধি বা হ্রাসের চেষ্টা করা হয়েছিল। তাই এগুলি ব্যবহারের সময় নিরপেক্ষ দৃষ্টি গ্রহণের পাশাপাশি সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্য, সংবাদপত্র প্রভৃতি তথ্যের সঙ্গে যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।
বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী সত্তর বছর থেকে কীভাবে স্বায়ত্বশাসনের ধারণা পাওয়া যায়?
সত্তর বছর থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতায় সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের উদ্ভবের ইতিহাস জানা যায়। বিপিনচন্দ্র তাঁর এই আত্মজীবনীর ছাত্রাবাস না জনরাজ্য অংশে দেখিয়েছেন কলকাতায় মেসগুলিতে ছাত্ররা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে মেস ম্যানেজার নির্বাচনের দায়বদ্ধতার সঙ্গে নিজেদের মেসজীবন পরিচালিত করত। এভাবে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক ধারণা থেকেই ভারতে স্বায়ত্ত্বশাসনের ধারণার ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়।
জীবন স্মৃতি থেকে উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসের কী কী উপাদান পাওয়া যায়?
রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ঔপনিবেশিক শিক্ষার কথা জানা যায়। এই গ্রন্থের শিক্ষারম্ভ প্রভৃতি অধ্যায়ের বর্ণনা থেকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও নর্মাল স্কুল-এর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পছন্দ হয়নি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি কিভাবে ব্যক্তি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উপাদান সরবরাহ করে?
জীবনস্মৃতি গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তি ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোটোবেলায় শিক্ষারম্ভ, ঠাকুর বাড়ির স্বাদেশিকতা, নীতিচর্চা, সাহিত্যচর্চার কথা জানা যায়। এছাড়া ব্রাত্ম আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের বিকাশের কথাও জানা যায় এই গ্রন্থ থেকে।
জীবনের ঝরাপাতা নামক আত্মজীবনী থেকে উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস কীভাবে জানা যায়?
জীবনের ঝরাপাতা নামক আত্মজীবনী থেকে উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার অভিজাত পরিবারের কায়দা-কানুন, দুধ-মাধাইমার মাধ্যমে সন্তান প্রতিপালন ব্যবস্থার কথা জানা যায়। এছাড়া সমাজে নারীর আচার-ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও জানা যায়। উপরন্তু নারী শিক্ষার কথা, বাঙালি সংস্কৃতির ও সাহেবি সংস্কৃতির কথা এবং ব্রাত্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের কথাও রয়েছে এই গ্রন্থে।
জওহরলাল নেহরুর চিঠিপত্রে কিভাবে দেশীয় রাজ্যগুলির ইতিহাস রচনায় উপাদান সরবরাহ করে?
কন্যা ইন্দিরাকে লেখা জওহরলাল নেহরুর চিঠি থেকে আধুনিক ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির ইতিহাস জানা যায়। তিনি এই গ্রন্থে দেশীয় প্রজাদের অর্থে দেশীয় রাজাদের বিলাস-বাসন ও শৌখিন গাড়ি চড়ার সমালোচনা করেছেন। পাশাপাশি এই প্রজাদের অন্নকষ্ট, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবের কথাও জানা যায় এই গ্রন্থ থেকে।
সোমপ্রকাশ কীভাবে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হয়ে উঠেছে?
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনায় প্রকাশিত সোমপ্রকাশ নামক সংবাদপত্র (যদিও প্রথমদিকে এটি ছিল। সাময়িক পত্র) ছিল নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশক। এই পত্রিকায় দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে নির্ভীক আলোচনা থাকত৷ এছাড়া ভারতস্থ ব্রিটিশ সরকারের নীতিও সমালোচিত হয়েছিল এবং একারণেই দেশীয় সংবাদপত্র আইনের মাধ্যমে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
ফটোগ্রাফ কিভাবে আধুনিক ভারতে ইতিহাসচর্চা উপাদান হয়ে উঠেছে?
আধুনিক ভারতের ইতিহাসে ১৮৫০-এর দশক থেকে ভারতের বিদ্রোহ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রসহ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিককে ফটোগ্রাফির আকারে ধরে রাখা শুরু হয়। আবার বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন মুহূর্তকেও ফটোগ্রাফির আকারে ধরে রাখা হয়েছে। এই ফটোগ্রাফগুলির নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ভারতের আধুনিক ইতিহাসচর্চার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধাগুলি কী?
ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধাগুলি হল — ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে দেশ বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গবেষণাকেন্দ্রের জার্নাল, মহাফেজখানা ও মিউজিয়ামের সংগৃহীত নথিপত্র ও গবেষণা গ্রন্থ থেকে তথ্য পাওয়া যায়। একই বিষয়ে অল্প সময়ে অল্পখরচে, অল্প পরিশ্রমে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ফলে দ্রুত গবেষণা বা পাঠপ্রস্তুতি করা সম্ভব হয়।
ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেট ব্যবহারের অসুবিধাগুলি কী?
ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেট ব্যবহারের অসুবিধাগুলি হল — ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ, এই সমস্ত তথ্যের তথ্যসূত্র থাকে না। কোনো বিষয়ের আকরগ্রন্থ বা মূল নথিপত্র পাঠ করে তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে যতটা নিশ্চিত হওয়া যায় ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ততটা নিশ্চিত হওয়া যায় না।
ইতিহাসের ধারণা (প্রথম অধ্যায়) মাধ্যমিক ইতিহাস প্রশ্ন ও উত্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ইতিহাস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা অতীতের ঘটনাবলি সম্পর্কে জানতে পারি। ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা বর্তমানকে বুঝতে পারি এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ইতিহাস আমাদেরকে সাহস, ত্যাগ, উৎসাহ, দেশপ্রেম, মানবতাবাদ ইত্যাদি গুণাবলী অর্জনে সাহায্য করে।




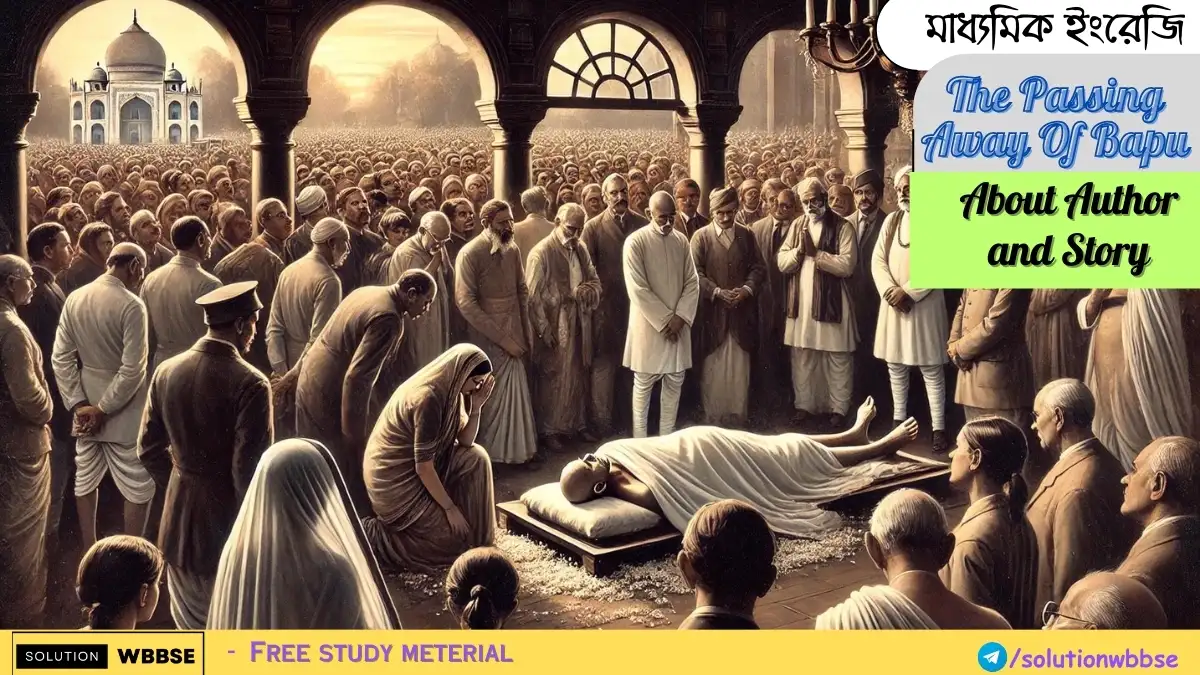
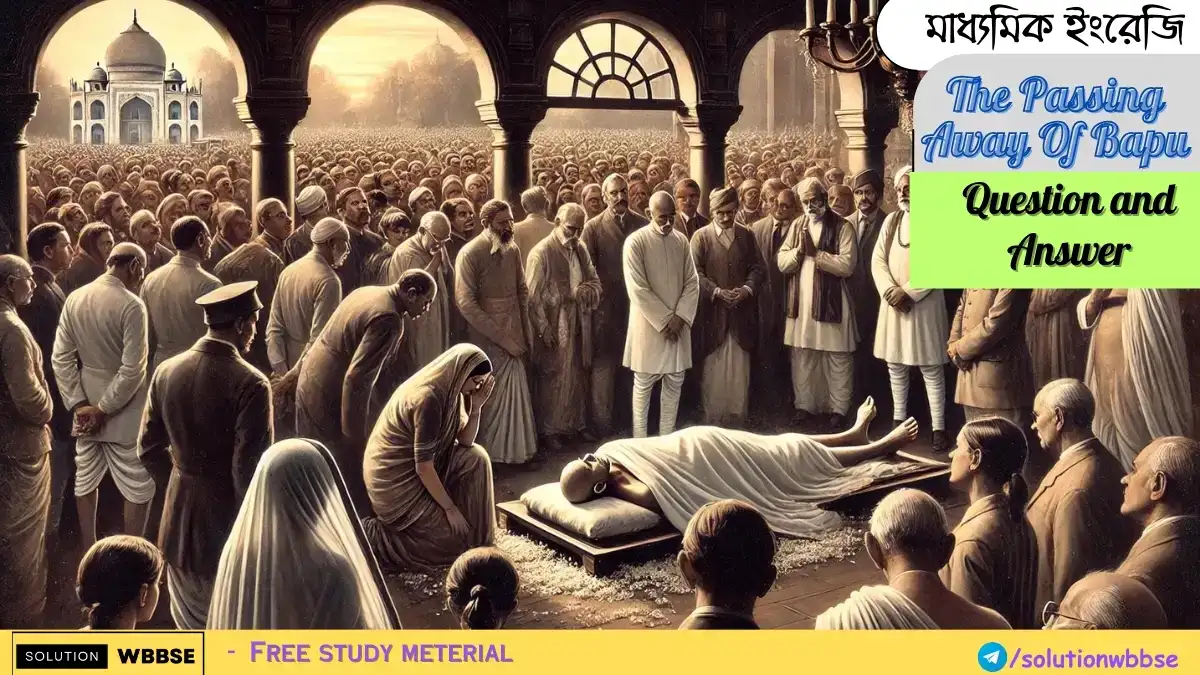
মন্তব্য করুন