নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাম গল্পটি নবম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের একটি অন্তর্ভুক্ত গল্প। এই গল্পটিতে একজন অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের কঠোর শাসন ও শিক্ষার প্রভাব একজন ছাত্রের জীবনে কীভাবে প্রতিফলিত হয় তা তুলে ধরা হয়েছে।
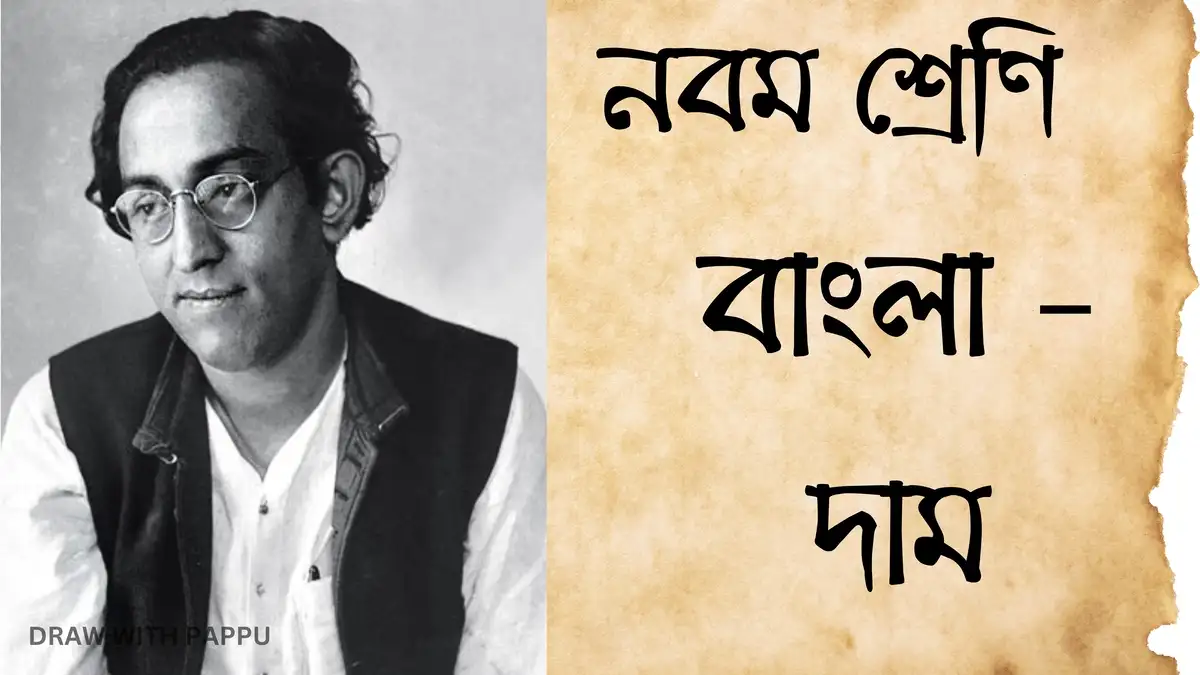
লেখক পরিচিতি
ভূমিকা – রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের লেখকদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম। উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, কবিতা — সর্বত্রই তিনি তাঁর কৃতিত্বের চিহ্ন রেখে গেছেন। মানবিক সম্পর্ক, বাংলার প্রকৃতি, ইতিহাসের কাহিনি তাঁর লেখায় গুরুত্ব পেয়েছে।
জন্ম এবং শৈশব – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুরের বালিয়াডিঙিতে (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) তাঁর জন্ম হয়। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বরিশাল জেলার বাসুদেবপুরের নামচিড়া গ্রামে। লেখকের বাবা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পুলিশ আধিকারিক হওয়ায় পিতার কর্মসূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁর শৈশব কাটে।
ছাত্রজীবন – বাবার বদলির চাকরির জন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবনের দিনগুলি কেটেছে দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল এবং কলকাতায়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজে ভরতি হলেও ১৯৩৫-এ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তাঁকে শহর ছাড়তে হয়। সেসময় সন্দেহভাজন বিপ্লবী হিসেবে গৃহবন্দি থাকায় তিনি কলেজের পরীক্ষাও দিতে পারেননি। পরে বরিশালের বিএম কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে ভরতি হয়ে ১৯৩৬ – এ ননকলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হিসেবে তিনি কলা বিভাগে ইনটারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৩৮ – এ তিনি ওই কলেজ থেকেই ডিস্টিংশন নিয়ে বিএ পাস করেন। এই বিএম কলেজেই তিনি স্বনামধন্য কবি জীবনানন্দ দাশকে তাঁর শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। ১৯৪১ – এ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন এবং এই পরীক্ষায় অসামান্য ফলাফলের জন্য তিনি ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক পান। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।
কর্মজীবন – এমএ পাস করার পর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অধ্যাপনাকেই নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেন। জলপাইগুড়ি কলেজে ১৯৪২-৪৫ পর্যন্ত পড়ানোর পর তিনি কলকাতার সিটি কলেজে ১৯৪৫ – ৫৫ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন।
সাহিত্যজীবন – ছাত্রাবস্থাতেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য- প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এই সময় থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যকর্মের জন্যই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রথম গল্পটি বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
উপন্যাস – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—উপনিবেশ (৩ খণ্ডে, ১৯৪৪-৪৭), সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (১৯৪৪), মন্দ্রমুখর (১৯৪৫), মহানন্দা, স্বর্ণসীতা, নিশিযাপন, শিলালিপি, ট্রফি (১৯৪৯), লালমাটি, কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫১), বিদূষক, বৈতালিক (১৯৫৫), অসিধারা (১৯৫৭), ভাটিয়ালি, পদসঞ্চার, অমাবস্যার গান, আলোকপর্ণা প্রভৃতি।
গল্পগ্রন্থ – তাঁর গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — গল্পসংগ্রহ, সাপের মাথায় মণি, শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প।
নাটক – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা বিখ্যাত নাটকগুলি হল — রামমোহন, ভাড়াটে চাই, আগন্তুক, পরের উপকার করিও না ইত্যাদি।
শিশু-কিশোর সাহিত্য – শিশু-কিশোর সাহিত্যেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদান অসামান্য। তাঁর ছুটির আকাশ, খুশির হাওয়া, পঞ্চাননের হাতি, গল্প বলি গল্প শোন, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ, সপ্তকাণ্ড হল ছোটোদের জন্য রচিত বিখ্যাত গল্প। তবে শিশু-কিশোরদের জন্য তাঁর অমর সৃষ্টি পটলডাঙার টেনিদা। তিনি কিছু রহস্য এবং অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনিও লিখেছেন, যেমন — চারমূর্তি, টেনিদা ও সিন্ধুঘোটক, ঝাউ বাংলোর রহস্য, কম্বল নিরুদ্দেশ ইত্যাদি।
কলাম – সুনন্দ ছদ্মনামে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় তিনি সুনন্দর জার্নাল নামে একটি কলাম লিখতেন।
প্রবন্ধ – তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থ হল সাহিত্য ও সাহিত্যিক, সাহিত্যে ছোটোগল্প (১৯৫৫), কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৫), ছোটোগল্পের সীমারেখা (১৯৬৯), বাংলা গল্প বিচিত্রা ইত্যাদি।
সম্মান ও স্বীকৃতি – বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৪৬ – এ আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।
জীবনাবসান – ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর কলকাতায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়।
উৎস
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা দাম ছোটোগল্পটি ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দের শারদীয়া তরুণের স্বপ্ন-তে প্রথম প্রকাশিত হয়।
বিষয়সংক্ষেপ
ছোটোবেলায় স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই ছিলেন দাম কাহিনির কথক সুকুমারের কাছে আতঙ্কস্বরূপ। অঙ্কের ভয় তাঁর কাছে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠত মারমুখী মাস্টারমশাইয়ের ভয়াবহ উপস্থিতিতে। তাই চিরকালই অঙ্ক সুকুমারের অপছন্দের বিষয় হয়েই থেকে গেছে, যদিও অঙ্কে অসাধারণ দক্ষ মাস্টারমশাই বিশ্বাস করতেন অঙ্ক না শিখলে জীবন বৃথা।
পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার অধ্যাপক হন সুকুমার। এরপর যখন লেখক হিসেবে সুকুমারের অল্পবিস্তর নামযশ হয়, তখন এক অনামি পত্রিকার তরফে তাঁর কাছে বাল্যস্মৃতি লেখার প্রস্তাব আসে। সুকুমার তাঁর বিভীষিকাময় অঙ্কের মাস্টারমশাইকে নিয়েই স্মৃতিকথাটি লেখেন এবং নগদ দশ টাকা পারিশ্রমিকও পান। তিনি তাঁর কিশোরমনের চোখে দেখা মাস্টারমশাইয়ের কঠিন রূপটিকেই তুলে ধরেছিলেন তাঁর লেখায়। সেখানে এ কথা উল্লেখ করতেও সুকুমার ভোলেননি যে শিক্ষক হিসেবে মাস্টারমশাইয়ের শেখানোর পদ্ধতিতে ভুল ছিল। কারণ জোর করে বা বকা মারার ভয় দেখিয়ে ছাত্রদের কোনো বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায় না।
এরপর বহুদিন পেরিয়ে যায়। সুকুমারকে বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে অতিথি করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে খুব আবেগভরা বক্তৃতা দেওয়ার পর সকলে যখন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখনই আচমকা তাঁর সাক্ষাৎ হয় ছোটোবেলার সেই অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে। বৃদ্ধ মাস্টারমশাই ছাত্রের নাম শুনে তাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন।
বিস্মিত সুকুমার জানতে পারেন যে তাঁর লেখা সেই বাল্যস্মৃতিটি এখন বৃদ্ধ মাস্টারমশাইয়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী। শিক্ষা, ছাত্র এবং অঙ্ক-অন্তপ্রাণ মাস্টারমশাই তাঁর সহজাত সারল্যে সুকুমারের সমালোচনাকেও উদারমনে গ্রহণ করেছেন। ছাত্রকে অঙ্ক শেখাতে না পারলেও ছাত্রের গর্বে তিনি গর্বিত। সুকুমারের যাবতীয় সমালোচনা যেন মাস্টারমশাইয়ের পায়ে ছাত্রের বিনম্র শ্রদ্ধা হয়ে ঝরে পড়েছে। সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত সুকুমার উপলব্ধি করেন যে কিশোর হিসেবে সেদিন তিনি শুধু মাস্টারমশাইয়ের শাসনকেই দেখেছিলেন, অনুভব করতে পারেননি ছাত্রদের প্রতি তাঁর অন্তহীন স্নেহ। মাস্টারমশাইয়ের সমালোচনা করে লিখে পাওয়া সেই দশটা টাকা সুকুমারের মনে চরম অনুশোচনা জাগিয়ে তোলে।
নামকরণ
সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাম থেকে আমরা সাহিত্যকর্মটির স্বরূপ সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করতে পারি। কথাসাহিত্যে সাধারণত নায়ক-নায়িকার নাম বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী অথবা ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ হয়।
লেখক দাম গল্পটিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে অনন্য মানবিকতার আলোয় ফুটিয়ে তুলেছেন। কাহিনির কথক সুকুমার ও তাঁর সহপাঠীদের কাছে স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই ছিলেন বিভীষিকা-স্বরূপ। তাঁদের অঙ্কভীতিকে ছাপিয়ে যেত মাস্টারমশাইয়ের মারের ভয়। ম্যাট্রিকুলেশনের পর অঙ্ক ও মাস্টারমশাইয়ের হাত থেকে মুক্তি পেলেও সেই ভয় সুকুমারকে বহুকাল তাড়া করে ফিরেছে।
পরবর্তীকালে বাংলার অধ্যাপক সুকুমার লেখক হিসেবে অল্পবিস্তর নাম করলে একটি অনামি পত্রিকা তাঁকে বাল্যস্মৃতি লেখার প্রস্তাব দেয়। সুকুমার অঙ্কের মাস্টারমশাইকে নিয়ে তাঁর ছোটোবেলার বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা লেখেন সেই স্মৃতিকথায়। সঙ্গে ছিল লেখকসুলভ কল্পনার খাদ আর মাস্টারমশাইয়ের সমালোচনা। লেখাটির জন্য তিনি দশ টাকা পারিশ্রমিকও পান।
এর বহুকাল পর বাংলাদেশের একটি কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে প্রৌঢ় সুকুমারের সঙ্গে হঠাৎ বৃদ্ধ মাস্টারমশাইয়ের দেখা হয়। সুকুমার জানতে পারেন তাঁর লেখা অনামি পত্রিকার সেই বাল্যস্মৃতিটি এখন মাস্টারমশাইয়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী। ছাত্র তাঁর কথা মনে রেখেছে, এটাই বৃদ্ধ মাস্টারমশাইয়ের গর্ব।
ছাত্রের সমালোচনাকে তিনি উদারমনে সন্তানের অধিকার বলে মেনে নিয়েছেন। সুকুমার বুঝতে পারেন কৈশোরে তিনি শুধু শাসনের ভীতিকেই বুঝেছেন, কিন্তু তার পিছনে লুকিয়ে থাকা মাস্টারমশাইয়ের স্নেহের মনোভাবটি বুঝতে পারেননি। মাস্টারমশাইয়ের পড়ানোয় হয়তো কিছু পদ্ধতিগত ভুল ছিল, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠার কোনো অভাব ছিল না। গুরু-শিষ্য উভয়ের উপলব্ধির আলোয় এই কাহিনিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ছাত্র-শিক্ষকের মানবিক সম্পর্ক, যা আজকের যুগের দিক থেকে খুবই সময়োপযোগী। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যাকে দাম দিয়ে কেনা যায় না, যেমন — স্নেহ, ভালোবাসা, মমতার সম্পর্কগুলি।
মাস্টারমশাইকে নিয়ে তাঁর ছোটোবেলার অভিজ্ঞতা বিক্রি করে সুকুমার দশ টাকা দাম পেয়েছিলেন — এটাই তাঁকে চরম আত্ম-অনুশোচনায় ভোগায়। মাস্টারমশাইয়ের উদ্দেশে করা সমালোচনা দাম দিয়ে বিক্রি করা যায়, কিন্তু তাঁর স্নেহ দাম দিয়ে কেনা যায় না। সবদিক আলোচনা করে বলা যায় যে, গভীর ব্যঞ্জনাময় দাম নামটি এই কাহিনিটির ক্ষেত্রে যথাযথক এবং সার্থক।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাম গল্পটি একটি শিক্ষামূলক গল্প। গল্পের মাধ্যমে তিনি পীড়ন-তাড়না করে শেখানোয় বিরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, পীড়ন-তাড়না করে শেখানো হলে শিক্ষার্থীর মনে ভয় ও বিদ্বেষ জন্মে। ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

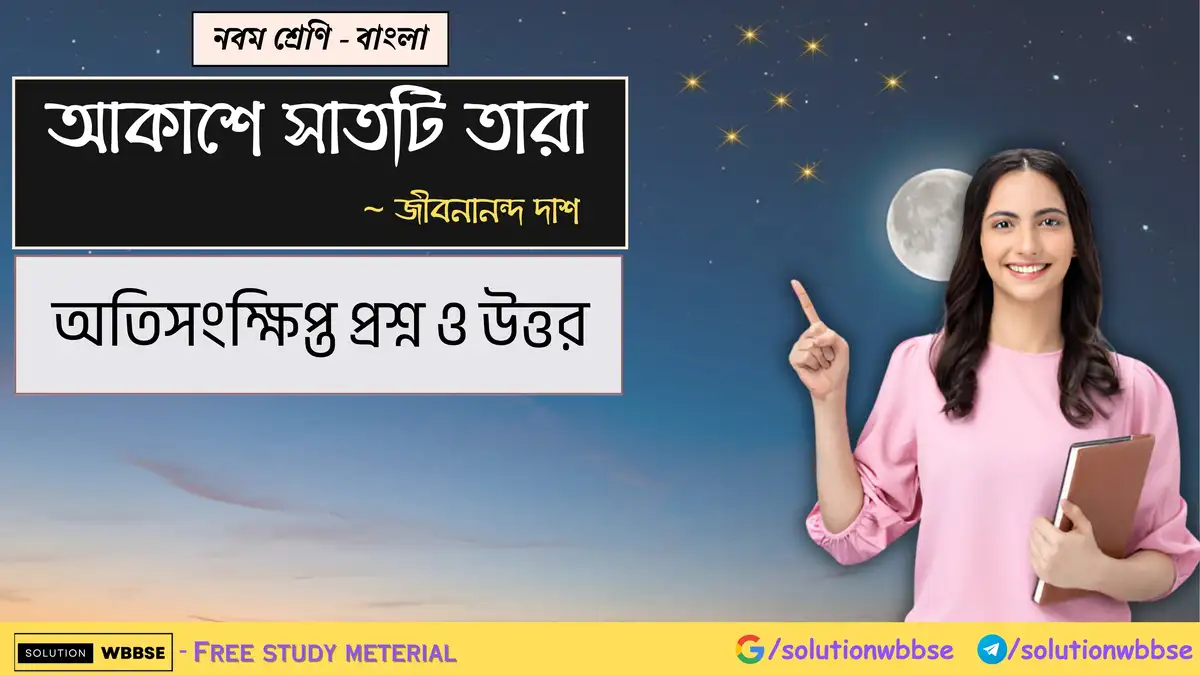
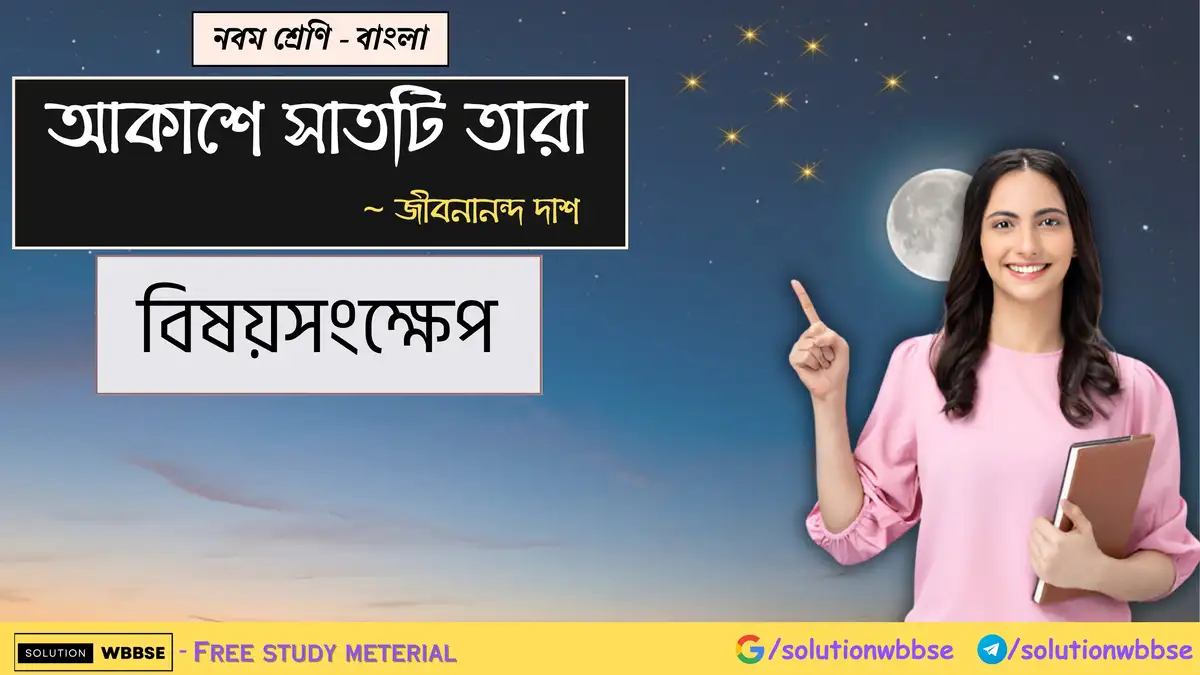
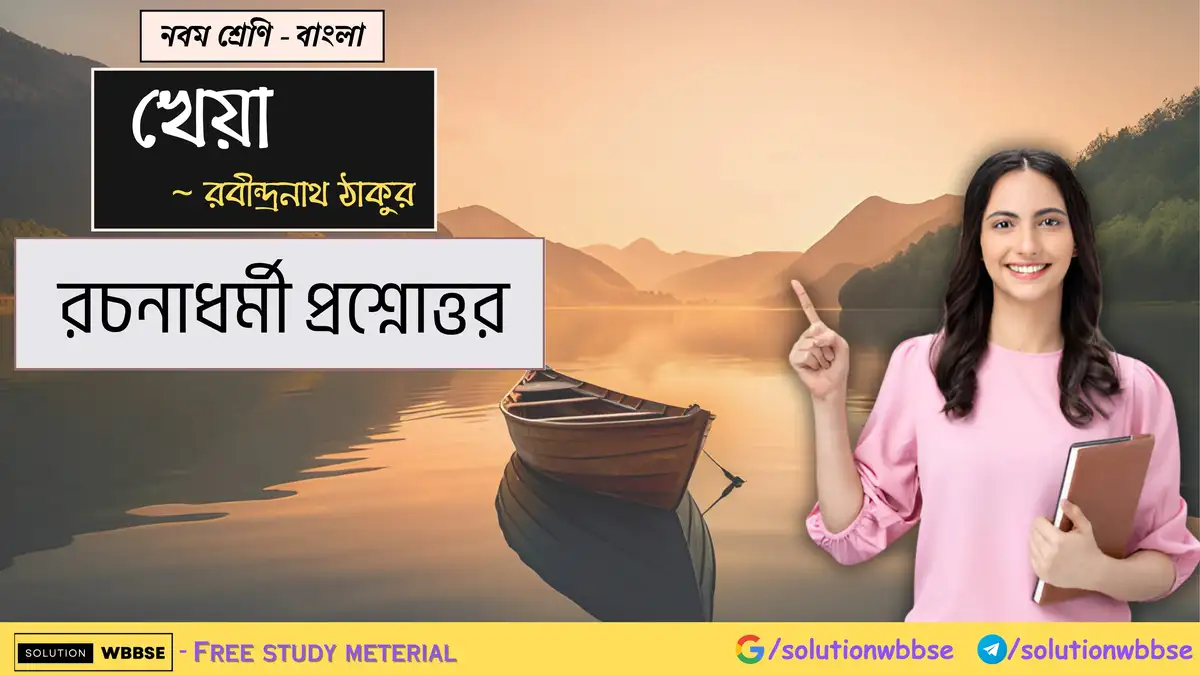
মন্তব্য করুন