আজকের আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক বাংলার সপ্তম পাঠের তৃতীয় বিভাগ, ‘নদীর বিদ্রোহ’ এর বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি পরীক্ষায় প্রায়শই দেখা যায়। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।
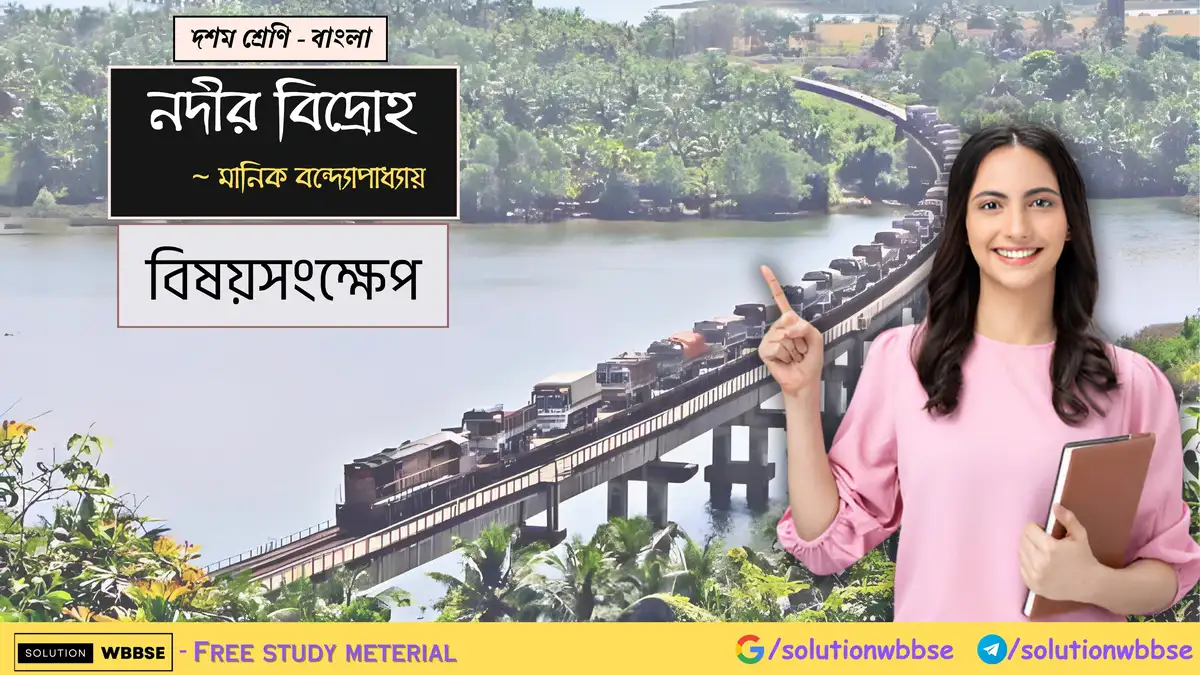
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক পরিচিতি
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ও শৈশব –
1908 খ্রিস্টাব্দের 29 মে, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল ঢাকার বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালবদিয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়ের নাম নীরদাসুন্দরী দেবী। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী, তাই চাকরিসূত্রে বাবাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈশব কেটেছে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে। তাঁর আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক। এই নামেই তিনি পরবর্তীকালে সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত হন।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাজীবন –
কলকাতা থেকে মানিকের বাবা টাঙ্গাইলে বদলি হওয়ায় মিত্র স্কুলের ছাত্র মানিক টাঙ্গাইল জেলা স্কুলে ভরতি হন। প্রতিবারই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেত মাঝিদের নৌকায় বা গাড়োয়ানদের গাড়িতে অথবা আস্তাবলে। মাত্র 14 বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারান। মেদিনীপুরে থাকাকালীন মানিক 1926 খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে পাস করেন। বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ন মিশন কলেজ থেকে 1928 খ্রিস্টাব্দে তিনি আইএসসি পাস করেন। ওই বছরই কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি গণিতে অনার্স নিয়ে বিএসসি-তে ভরতি হন। কলেজজীবনে গান গাওয়া, বাঁশি বাজানো এসবের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক লক্ষ করা যায়। সাহিত্যচর্চার নেশা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, তিনি একসময় প্রথাগত পড়াশোনা ছেড়ে দেন।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবন –
সাহিত্যের জগতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল কিছুটা হঠাৎ করেই। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র, তখন একদিন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় নামি পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপানোর প্রসঙ্গ ওঠে। কথাপ্রসঙ্গে মানিকের এক বন্ধু বলেছিলেন যে, নামকরা লেখক না হলে বিখ্যাত পত্রিকাগুলো লেখা ছাপায় না। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল, ভালো লেখা হলে অনামি লেখকের রচনাও নিশ্চয়ই ছাপা হবে। বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক বাধলে মানিক তাঁদের বলেন যে, তিন মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর কথা প্রমাণ করবেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই ‘অতসী মামী’ নামে একটি গল্প লিখে তখনকার নামি পত্রিকা বিচিত্রা-র অফিসে জমা দেন। লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটিই তিনি সেখানে ব্যবহার করেন। যথাসময়ে সেই গল্পটি ছাপা হয় এবং তা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইভাবেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনের শুরু। ‘অতসী মামী’ গল্পটি প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে মানিকের কাছে লেখার জন্য ডাক আসতে থাকে। তিনিও মনপ্রাণ দিয়ে লিখতে থাকেন। সাহিত্যচর্চাতেই তিনি বেশি করে মনোনিবেশ করেন। 1937 খ্রিস্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গশ্রী পত্রিকার সহসম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু পত্রিকার মালিকের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই সেই চাকরি থেকে তিনি ইস্তফা দেন। এরপর মানিক তাঁর ছোটো ভাই সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ‘উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস’ নামে এক প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস এবং ছোটোগল্প দুই-ই রচনা করেছেন। দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর সমান দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সবমিলিয়ে তিনি প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর লেখা ছোটোগল্পের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। দিবারাত্রির কাব্য বইটি তিনি একুশ বছর বয়সে লিখেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল – জননী (1935 খ্রিস্টাব্দ), পুতুলনাচের ইতিকথা (1936 খ্রিস্টাব্দ), পদ্মানদীর মাঝি (1936 খ্রিস্টাব্দ), দর্পণ (1945 খ্রিস্টাব্দ), শহরবাসের ইতিকথা (1946 খ্রিস্টাব্দ), চতুষ্কোণ (1948 খ্রিস্টাব্দ), স্বাধীনতার স্বাদ (1951 খ্রিস্টাব্দ), সোনার চেয়ে দামি (1951 খ্রিস্টাব্দ), ইতিকথার পরের কথা (1952 খ্রিস্টাব্দ), হলুদ নদী সবুজ বন (1956 খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – প্রাগৈতিহাসিক (1937 খ্রিস্টাব্দ), সরীসৃপ (1939 খ্রিস্টাব্দ), ভেজাল (1944 খ্রিস্টাব্দ), আজ, কাল, পরশুর গল্প (1946 খ্রিস্টাব্দ), লাজুকলতা (1950 খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি।
বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক উজ্জ্বল নাম। স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বাস্তবজীবন ও দর্শনকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলায় তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর রচনার মধ্যে মার্কসীয় দর্শন ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব রয়েছে।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষজীবন –
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবন কেটেছে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে। সংক্ষিপ্ত জীবনকালে বারবার নানাপ্রকার অসুখে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। 1956 খ্রিস্টাব্দের 3 ডিসেম্বর এই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে।
‘নদীর বিদ্রোহ‘ গল্পের উৎস
আলোচ্য ছোটোগল্পটির উৎস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত সরীসৃপ (শ্রাবণ, 1346 বঙ্গাব্দ) গ্রন্থ।
‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পের বিষয়সংক্ষেপ
‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পের মুখ্য চরিত্র নদেরচাঁদ একজন স্টেশনমাস্টার। নদীর সঙ্গে তার আত্মার যোগ যেন জন্ম থেকেই, কারণ নদীর ধারেই তার জন্ম; নদীর ধারেই সে মানুষ হয়েছে। চিরদিন সে নদীকে ভালোবেসেছে। তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গেই তাই নদী জড়িয়ে গেছে। স্টেশনমাস্টারি করতে এসেও এই ভালোবাসা একইরকম থেকে গেছে। বর্ষার জন্য পাঁচ দিন নদীকে দেখতে না পেয়ে ছেলেমানুষের মতো তার মন ছটফট করেছে পরম আত্মীয় নদীটিকে দেখার জন্য। তার মনে হয়েছে, নদীকে দেখতে না পেলে সে হয়তো আর বাঁচবে না। তাই বৃষ্টি থামলেই সে ছুটে যায় নদীর কাছে। কিন্তু ব্রিজের কাছাকাছি এসে নদীকে দেখে সে হতবাক হয়ে যায়। এটা ঠিক যে, পাঁচ দিন আগেও বর্ষার জলে ওই নদী পরিপুষ্ট ছিল। চঞ্চল নদীতে সে দেখেছিল পরিপূর্ণতার আনন্দের প্রকাশ। কিন্তু এখন সেই নদীকে এমন রূপে দেখে তার যেন কেমন অচেনা লাগল। নদীর সেই রূপ ভীষণই ভয়ংকর। নদীর জল ব্রিজে বাধা পেয়ে আবর্ত সৃষ্টি করেছে। তার জলপ্রবাহ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নদীর এই রূপ দেখে নদেরচাঁদ এক মজায় মেতে ওঠে। সে নদীর সঙ্গে খেলা শুরু করে। খেলার আনন্দে সে স্ত্রীকে লেখা চিঠিটিও ছুঁড়ে দেয়। তখন নদী যেন তার কাছে এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে ধরা দেয়। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেলেও সে বসে ভিজতে থাকে। নদেরচাঁদের মনে হয়, রোষে, ক্ষোভে উন্মত্ত নদী যেন বিদ্রোহ করছে। বাঁধের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই যেন নদী এভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ব্রিজ ভেঙে, মানুষের তৈরি বাঁধ চুরমার করে দিয়ে নদী যেন নিজের স্বাভাবিক গতি ফিরে পেতে চাইছে। একই সঙ্গে নদেরচাঁদ এটাও অনুভব করে, নদী যদি সমস্ত বাধা চূর্ণ করে মুক্তি পায় তাহলেও তার নিস্তার নেই। মানুষ আবার নদীকে বন্দি করবে, আবার নদীতে বাঁধ গড়ে তুলবে। তারপর হয়তো গভীর প্রশস্ত জলপূর্ণ নদীও নদেরচাঁদের দেশের নদীটির মতোই ক্ষীণস্রোতা হয়ে পড়বে। তাই যে রং করা নতুন ব্রিজের জন্য একসময় নদেরচাঁদের গর্ব হত, আজ সেই ব্রিজকেই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় তার। নদেরচাঁদ মনে মনে নদীর মুক্তি কামনা করতে থাকে। যখন সে এ কথা ভাবতে ভাবতে লাইন ধরে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই এক প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে তাকে পিষে চলে যায়। গল্পশেষে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় — নদেরচাঁদ নদীর পক্ষ নিয়ে যন্ত্রসভ্যতার প্রয়োজনীয়তাকে প্রশ্ন করেছিল, যন্ত্রসভ্যতা তার সেই স্পর্ধা মেনে নেয়নি।
‘নদীর বিদ্রোহ‘ গল্পের নামকরণ
যে-কোনো সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণের মাধ্যমেই কোনো সাহিত্যের বিষয়বস্তু বা ভাবটি পাঠকের কাছে ফুটে ওঠে। সাধারণত সাহিত্যের নামকরণ হয় তার বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক, চরিত্রধর্মী বা ভাব অনুযায়ী। আবার কখনও তা হয় ব্যঞ্জনাধর্মী।
‘নদীর বিদ্রোহ’ নামকরণটি ব্যঞ্জনাধর্মী। এখানে মানুষ এবং নদীর মধ্যেকার এক অদ্ভুত সখ্যের বর্ণনা পাই আমরা। গল্পে দুটি নদীর কথা জানা যায়। এদের একটি হল নদেরচাঁদের দেশের ক্ষীণস্রোতা নদী আর অন্যটি হল সেই নদী যার সঙ্গে স্টেশনমাস্টারি করতে এসে নদেরচাঁদের আলাপ হয়। ওই নদীটি ছিল বন্দি। বাঁধ দিয়ে মানুষ তাকে বন্দি করেছিল। ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদী এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে ধরা দিয়েছে। বর্ষার জলে এই নদীর পঙ্কিল জলস্রোতে দেখা দিয়েছে উন্মাদনা, চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার স্রোত।
মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য বাঁধ দিয়ে এই নদীকে বন্দি করেছে, তৈরি করেছে ব্রিজ। সব কিছুই মানুষ করেছে যন্ত্রসভ্যতার সাহায্যে, নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে। নিজেদের প্রয়োজনে তারা নদীর স্বাভাবিক গতিকে আটকে রেখেছে। আর সেই কারণেই এই গল্পে নদী যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে। যারা তাকে বন্দি করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সে এই ব্রিজ আর বাঁধ ভেঙে ফেলে সে যেন তার স্বাভাবিক গতি ফিরে পেতে চেয়েছে। আর তাই সে তার উন্মত্ত জলস্রোতের মধ্য দিয়ে সেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তখন ‘স্বাঁধ ভেঙে দাও’ মন্ত্রে যে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে নদীটি। তাই গল্পের প্রেক্ষিতে বিচার করলে ‘নদীর বিদ্রোহ’ নামকরণটি যথার্থ ও সার্থক হয়েছে বলা যায়।
আজ আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক বাংলার সপ্তম পাঠের তৃতীয় বিভাগ ‘নদীর বিদ্রোহ’ এর বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। যদি কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকে, তাহলে আমাকে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এছাড়া, এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে শেয়ার করুন যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।




মন্তব্য করুন