আজকে আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক বাংলার পঞ্চম পাঠের চতুর্থ বিভাগ, ‘পথের দাবী’ এর বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবো। এই বিষয়গুলি মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো পরীক্ষায় প্রায়শই দেখা যায়। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।
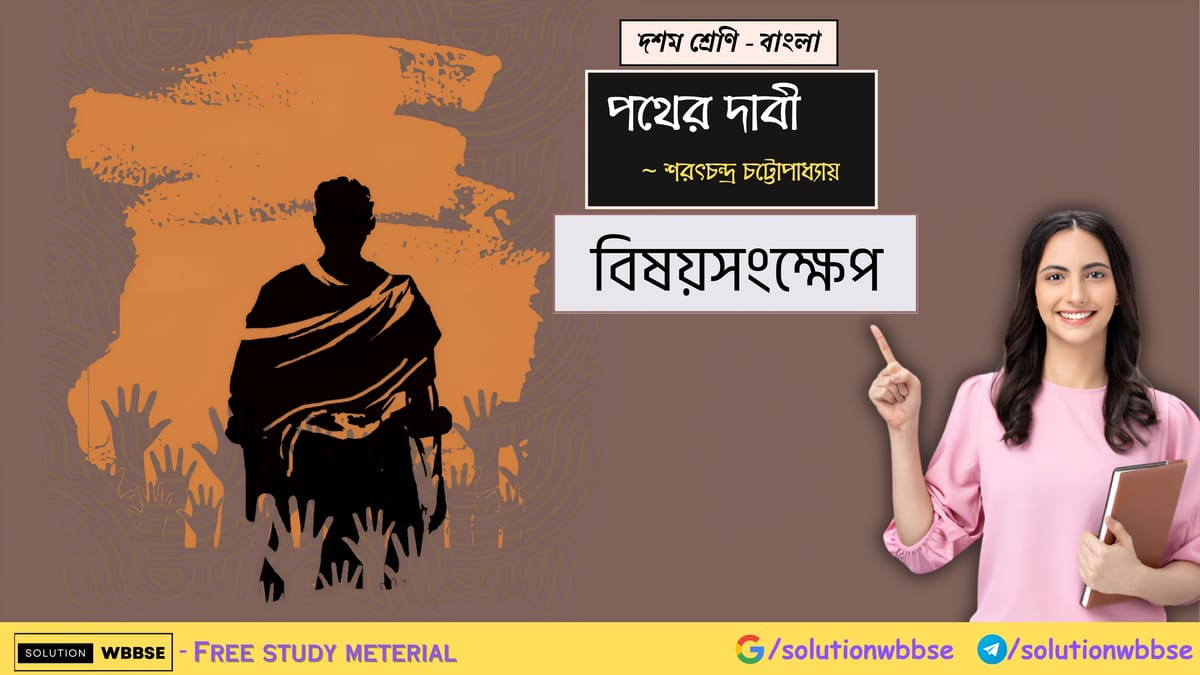
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – লেখক পরিচিতি
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা –
“আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল – আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আমার পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে শুধু স্বপ্ন দেখেই গেলাম।” কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের সম্পর্কে এ কথা বলেছেন। শরৎচন্দ্র 1876 খ্রিস্টাব্দের 15 সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মায়ের নাম ভুবনমোহিনী দেবী।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শৈশব ও ছাত্রজীবন –
শরৎচন্দ্রের ডাকনাম ছিল ন্যাড়া। দেবানন্দপুর তাঁর জন্মস্থান হলেও আর্থিক টানাটানির কারণে সেখানে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। ভাগলপুরে তাঁর মামারা ছিলেন ধনী গৃহস্থ। বালক শরৎচন্দ্রকে মামার বাড়িতে চলে আসতে হয়। ভাগলপুর থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 1889 খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে আসেন এবং ভর্তি হন হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে। কিন্তু কয়েক বছর পর অভাবের কারণে শরৎচন্দ্রের বাবা সপরিবারে ভাগলপুরে চলে আসেন, ফলে তাঁর লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। ভাগলপুরে এসে তিনি তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং 1894 খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। তারপর এফএ ক্লাসে ভরতি হলেও আর্থিক কারণে তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। 1896 খ্রিস্টাব্দেই তাঁর প্রথাগত পড়াশোনার সমাপ্তি ঘটে।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবন –
ভাগলপুরে বসবাস করার সময়েই তাঁর সাহিত্যচর্চার সূচনা হয়। সেখানে থাকতেই তিনি বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস রচনা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি ছাপা হয়নি। শুধু সাহিত্যচর্চা নয়, ভাগলপুরে থাকাকালীন তিনি গানবাজনা ও অভিনয়ের চর্চাও শুরু করেন। আদমপুর ক্লাবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ভাগলপুরে তাঁর অস্থিরচিত্ততার প্রকাশও লক্ষ করা যায়। তিনি দু-একটি চাকরিতে যোগ দিলেও তাতে মন বসাতে পারেননি। একবার সন্ন্যাসী হয়ে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণও করেছিলেন। 1903 খ্রিস্টাব্দে ভাগ্য অন্বেষণের জন্য তিনি রেঙ্গুনে চলে যান। যাওয়ার আগে ‘কুন্তলীন’ গল্প প্রতিযোগিতায় ‘মন্দির’ নামে একটি গল্প, পাঠিয়ে দেন। কিন্তু লেখক হিসেবে তিনি নিজের নামের বদলে তাঁর এক মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই ‘মন্দির’ গল্পটিই সে বছর ‘কুন্তলীন’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এটিই শরৎচন্দ্রের লেখা প্রথম মুদ্রিত রচনা। কর্মসূত্রে তিনি রেঙ্গুনে প্রায় দশ বছর ছিলেন। প্রবাসে থাকলেও সেই সময়েই তিনি বাংলা সাহিত্যের পাঠকমহলে কথাশিল্পী হিসেবে বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখা বড়দিদি যখন ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন প্রথম সংখ্যাগুলিতে লেখকের নাম ছিল না। অনেকেই সেটাকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে ভুল করেছিলেন। একে একে ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘রামের সুমতি’, ‘পথনির্দেশ’, ‘বিরাজ বৌ’, ‘পণ্ডিতমশাই’, প্রভৃতি প্রকাশের ফলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথাশিল্পী হিসেবে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেন। 1916 খ্রিস্টাব্দে তিনি রেঙ্গুন থেকে পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে আসেন এবং লেখাই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের একমাত্র জীবিকা। তাঁর লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল – শ্রীকান্ত (চার পর্ব), চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দত্তা, দেবদাস, পল্লীসমাজ, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস, দেনাপাওনা, পথের দাবী প্রভৃতি। স্বদেশ ও সাহিত্য, নারীর মূল্য প্রভৃতি তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। ‘অনিলা দেবী’, ‘নিরুপমা দেবী’ ইত্যাদি ছদ্মনামেও শরৎচন্দ্র লেখালেখি করেছেন। ছোটোগল্প অপেক্ষা উপন্যাসের দিকেই শরৎচন্দ্রের ঝোঁক ছিল বেশি। সেজন্য তাঁর লেখা ছোটোগল্পের সংখ্যা বেশ কম। সংখ্যায় কম হলেও তাঁর ছোটোগল্পগুলিও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে ‘মহেশ’, ‘অভাগীর স্বর্গ’ এবং ‘একাদশী বৈরাগী’ এই তিনটি গল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস পথের দাবী সেকালের বিপ্লবীদের প্রবল অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। বইটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। শরৎচন্দ্র বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি কিছুদিন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তৎকালীন রাজনীতির প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি সেই পদ ত্যাগ করেন।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুরস্কার ও সম্মান –
শরৎচন্দ্র 1923 খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগত্তারিণী’ সুবর্ণপদক পান। 1936 খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান ডিলিট উপাধি। তবু এইসব পুরস্কার তাঁর কাছে কিছুই নয়। তাঁর আসল পুরস্কার হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। আজও তারা তাঁকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছে।
জীবনাবসান –
1938 খ্রিস্টাব্দের 16 জানুয়ারি এই অমর কথাশিল্পীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা পঙ্ক্তি –
“যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মৃত্তিকা থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তাকে রাখিয়াছে ধরি।”
পথের দাবী পাঠ্যাংশের উৎস
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা মূল উপন্যাস পথের দাবী-র একটি নির্বাচিত অংশ এখানে পাঠ্যাংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।
পথের দাবী পাঠ্যাংশের পূর্বসূত্র
পথের দাবী উপন্যাসের শুরুতেই আমরা অপূর্ব এবং তার পরিবারের বর্ণনা পাই। অপূর্ব ছিল এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। এমএসসি পাস করার পর অপূর্বর কলেজের প্রিন্সিপাল বোথা কোম্পানিতে তাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেন। আর এই বোথা কোম্পানির নতুন অফিস ছিল রেঙ্গুনে। মায়ের খুব একটা মত না থাকা সত্ত্বেও অপূর্ব রেঙ্গুন যাত্রা করে নিজের চাকরিজীবনের সূচনা করতে। রেঙ্গুনে এসে অপূর্বর নানারকম অভিজ্ঞতা হয়। কখনও ভালো অভিজ্ঞতা, কখনও-বা খারাপ। চাকরি করতে গিয়ে অপূর্বর সঙ্গে এক মারাঠি ব্রাহ্মণের আলাপ হয় যার নাম রামদাস তলওয়ারকর। অপূর্বর তাকে ভালো লাগে। অপূর্ব রেঙ্গুনে যে বাড়িতে থাকত, সেই বাড়ির ওপরের তলায় এক সাহেব তার ক্রিশ্চান মেয়েকে নিয়ে থাকত। সাহেবটি অপূর্বর সঙ্গে যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার করলেও, তার ক্রিশ্চান মেয়েটি ছিল অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র। এই নতুন শহরে অপূর্বর সঙ্গে একটি খারাপ ঘটনা ঘটে। অপূর্বর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে চুরি হয়ে যায়। এই সময় ক্রিশ্চান মেয়েটি তাকে সাহায্য করে। তার জন্যই টাকাকড়ি ছাড়া অপূর্বর বাকি জিনিসপত্র চুরি হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। অপূর্ব এই চুরির ব্যাপারে আইনের সাহায্য নিতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্রিশ্চান মেয়েটি রাজি ছিল না। রেঙ্গুনের পুলিশকর্তা নিমাইবাবু ছিলেন অপূর্বর বাবার বন্ধু আর অপূর্বর একরকম আত্মীয়। অপূর্ব পুলিশ স্টেশন যাওয়ার সময় রাস্তাতেই নিমাইবাবুর সঙ্গে তার দেখা হয়। নিমাইবাবু সেই সময় জাহাজঘাটে যাচ্ছিলেন। তাদের কাছে খবর ছিল পলিটিকাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিক, যিনি রাজবিদ্রোহী এবং যাঁকে ধরার জন্য পুলিশকর্তারা ব্যস্ত, তিনি নদীপথে জাহাজে রেঙ্গুন আসছেন। অপূর্বকেও তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। অপূর্ব সব্যসাচীর কথা শোনামাত্র খুবই উত্তেজিত হয় এবং যেতে রাজি হয়। সিঙ্গাপুরে তিন বছর জেল খেটে সব্যসাচী রেঙ্গুনে আসছেন। সব্যসাচী ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আইন পাস করেছিলেন। সব্যসাচীকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে কথোপকথন চলে। জাহাজ জেটির গায়ে এসে যখন ভিড়ল, তারা সব্যসাচীকে খুঁজে পেলেন না। সবাই ভাবল সব্যসাচী হয়তো পালিয়েছেন। কিন্তু জগদীশবাবু সন্দেহের বশে কয়েকজনকে থানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। নিমাইবাবুও থানায় গেলেন আর অপূর্বকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইলেন। অপূর্ব, নিমাইবাবুর সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে গেল। অপূর্ব আর নিমাইবাবু পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার পরের ঘটনাই আমাদের এই নির্বাচিত পাঠ্যাংশে বর্ণিত হয়েছে।
বিষয়সংক্ষেপ
শরৎচন্দ্রের লেখা পথের দাবী উপন্যাসের একটি অংশ এই পাঠ্যাংশে নেওয়া হয়েছে। এখানে মূলত দেখা যায়, পুলিশ পলিটিকাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে ধরার জন্য ব্যস্ত। এজন্যই বর্মার তেলের খনির যেসব মিস্ত্রিরা চাকরির উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনে এসেছিল, তাদের সবাইকে পুলিশ স্টেশনে তদন্ত করা হয়েছিল। সন্দেহের কারণে একজনকে পুলিশ স্টেশনের একটি ঘরে আটক রাখা হয়েছিল। সে নিজের পরিচয় দেয় গিরীশ মহাপাত্র বলে। গিরীশ মহাপাত্রের আচরণ, সাজপোশাক এবং তার পকেট ও ট্যাঁক থেকে পাওয়া জিনিসপত্র দেখে পুলিশ বোঝে, সে ব্যক্তি কখনোই সব্যসাচী মল্লিক হতে পারে না। তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই গিরীশ মহাপাত্রই ছিল সব্যসাচী মল্লিক। সব্যসাচী মল্লিক নিজের দেশের জন্য লড়াই করছিলেন। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তিনি গিরীশ মহাপাত্রের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন।
অপূর্ব নামের চরিত্রটি যারা নিজের দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করতে চায়, তাদের সমর্থন করে। যদিও পুলিশের কর্তা তার আত্মীয়, তবুও অপূর্ব সব্যসাচীকেই নিজের বলে মনে করে। অপূর্ব গিরীশ মহাপাত্রকে পুলিশ স্টেশনে দেখেছিল এবং দ্বিতীয়বার দেখেছিল রেঙ্গুন থেকে ভামো নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় স্টেশনে। অপূর্ব চিনতে পেরেছিল, ওই ব্যক্তিই সব্যসাচী মল্লিক। কিন্তু সে-কথা অপূর্ব পুলিশকে জানায়নি, কারণ সে নিজের চোখের সামনে দেখেছে পরাধীন দেশে সাহেবদের হাতে দেশের মানুষের অপমান ও লাঞ্ছনা। অপূর্ব নিজেও সাহেবদের হাতে বিনা দোষে মার খেয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। তাই সে নিজেও চাইত এই পরাধীনতা থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত হোক। আমরা দেখি, ট্রেনে প্রথম শ্রেণির যাত্রী হয়েও অপূর্বকে নানাভাবে বিরক্ত করা হয়েছে, শুধুমাত্র সে ভারতীয় বলে। তাই সব্যসাচীর আন্দোলনকে অপূর্ব মনেপ্রাণে সমর্থন করত, সে-ও চাইত পরাধীন দেশ স্বাধীন হোক।
নামকরণ
নামকরণের মাধ্যমেই যে-কোনো সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বিষয় বা ভাব তার পাঠকের কাছে ফুটে ওঠে। সাহিত্যকর্মের নামকরণ সাধারণত বিষয়বস্তু, চরিত্র বা ভাব অনুযায়ী আবার কখনও-বা ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে থাকে।
এখানে শরৎচন্দ্রের লেখা পথের দাবী উপন্যাসের একটি নির্বাচিত অংশ আমাদের পাঠ্য হিসেবে নেওয়া হয়েছে। পাঠ্যাংশে আমরা গিরীশ মহাপাত্র চরিত্রটি পাই, যে আসলে একজন বিপ্লবী এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। তার আসল নাম সব্যসাচী মল্লিক, যে বিভিন্ন ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেরায়। দেশকে স্বাধীন করাই সব্যসাচীর জীবনের মূল লক্ষ্য। মূল উপন্যাসে সব্যসাচী মল্লিকের একটি সংগঠন ছিল যার নাম পথের দাবী। এই সংগঠনে সব্যসাচী ছাড়া আরও কয়েকজন ছিলেন যারা একত্র হয়ে দেশকে কীভাবে স্বাধীন করা যায় এবং এই স্বাধীনতালাভের জন্য কোন্ পথে আন্দোলন করা যায়, সেইসব বিষয়ে আলোচনা করতেন। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্যই ছিল দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করা এবং স্বাধীনতার জন্য একজোট হয়ে আন্দোলন করা। এই সংগঠনের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটি এগিয়েছে। আর এই সংগঠনের মূল কাণ্ডারি ছিলেন সব্যসাচী মল্লিক। সংগঠনটির নাম অনুযায়ী মূল উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে, আর আমাদের পাঠ্যাংশটি মূল উপন্যাসেরই একটি নির্বাচিত অংশ। মূল উপন্যাসটিতেও স্বাধীনতার ও বিদেশি শাসকের অত্যাচার থেকে মুক্তির দাবি প্রাধান্য পেয়েছে। তাই মূল উপন্যাসের নাম অনুযায়ী আমাদের পাঠ্যাংশের এই নির্বাচিত অংশটির নামও ‘পথের দাবী’ রাখা হয়েছে। সেদিক থেকে ‘পথের দাবী’ নামকরণটি সার্থক ও যথাযথ হয়েছে বলা যায়।
আজকের আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক বাংলার পঞ্চম পাঠের চতুর্থ বিভাগ, ‘পথের দাবী’ এর বিষয়সংক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রায়শই এগুলো পরীক্ষায় আসে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনার জন্য উপকারী হয়েছে। আপনার কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকলে টেলিগ্রামে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। এছাড়াও, পোস্টটি আপনার পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি কাজে লাগতে পারে। ধন্যবাদ।


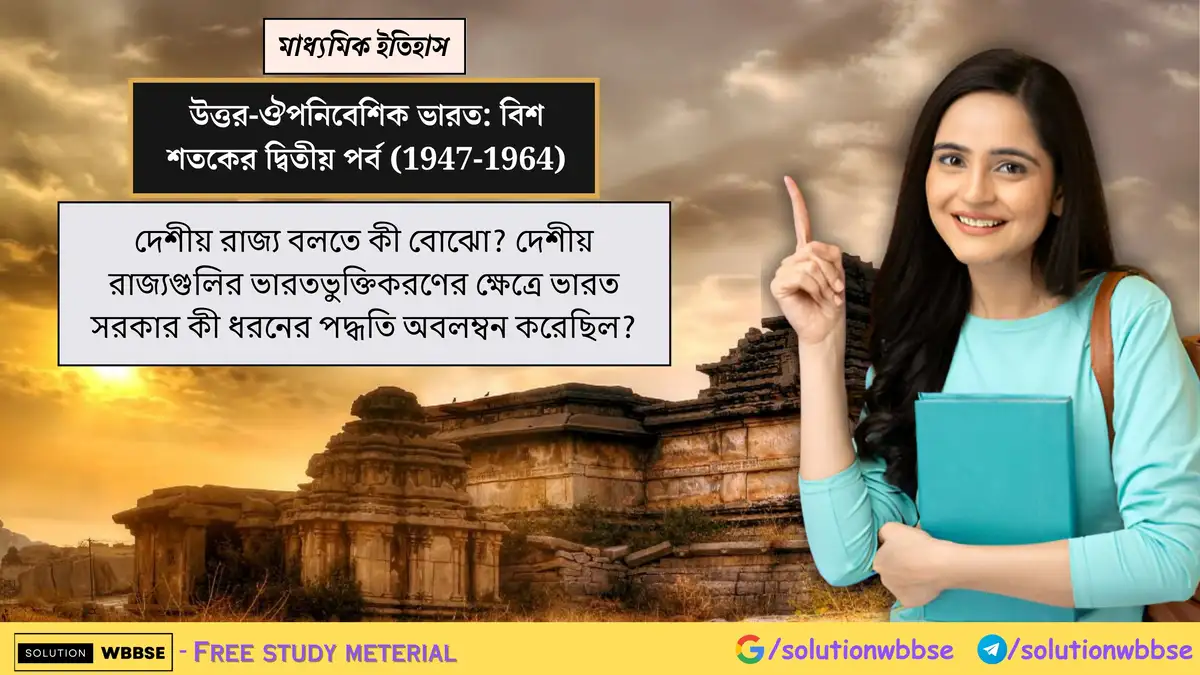
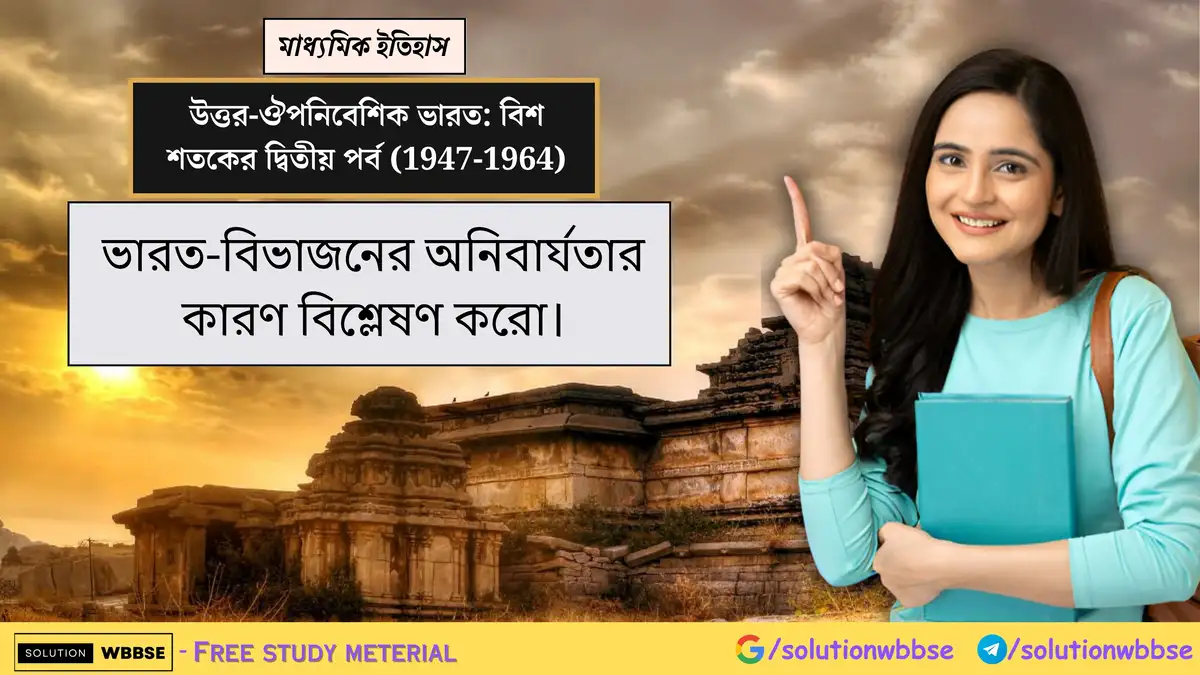
মন্তব্য করুন