আজকের এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের পঞ্চম পাঠের তৃতীয় অধ্যায়, ‘আমরা’ -এর কিছু ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নোত্তরগুলো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নবম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত আসে।

‘আমরা’ কবিতায় কবি বাঙালির কোন্ কোন্ গুণ ও কৃতিত্বের কথা বলেছেন?
বাঙালির গুণ ও কৃতিত্ব – সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত ‘আমরা’ কবিতায় বাঙালির বীরত্ব, যুদ্ধকুশলতা, অনমনীয় সংগ্রামী মানসিকতা, দার্শনিকতা, পাণ্ডিত্য, ধর্মসাধনা ও ধর্মপ্রচারে নিষ্ঠা, শিল্পকুশলতা, সাহিত্য ও সংগীত সৃজন দক্ষতা, নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মানবতা, স্বাজাত্যবোধ প্রভৃতি গুণ ও কৃতিত্বের কথা আলোচ্য কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে।
‘মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে’ – ‘মুক্তবেণীর গঙ্গা’ বলা হয়েছে কেন?
মুক্তবেণীর গঙ্গা বলার কারণ – গঙ্গা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতায় ‘মুক্তবেণীর গঙ্গা’ বলতে গঙ্গা-নদীর অবারিত গতিধারাকে বোঝাতে চেয়েছেন। গঙ্গার উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত গতিপথে বহু শাখা ও উপনদী রয়েছে। কিন্তু গঙ্গা অন্য কোনো নদ-নদীর সঙ্গে মিলিত না হয়ে মুক্তগতিতে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। গঙ্গা বাধা-বন্ধনহীন। তাই সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের জাদুতে তাকে মুক্তবেণী বলেছেন।
‘মুক্তি বিতরে রঙ্গে’ – গঙ্গাকে মুক্তি বিতরণকারী বলা হয় কেন?
মুক্তি বিতরণকারী গঙ্গা – ভারতীয় সংস্কৃতিতে পবিত্র নদী গঙ্গা মাতৃতুল্য। তার দুই তীরে হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে একাধিক সভ্যতা। গঙ্গা এক পুরাণ প্রসিদ্ধ চরিত্র। গঙ্গার খরস্রোতকে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর জটায় ধারণ করেছেন। হিন্দুধর্ম মতে তিনি পাপসংহারক। পৌরাণিক গাথায় উল্লেখ আছে ভগীরথ গঙ্গার দ্বারা তাঁর পূর্বপুরুষকে অভিশাপমুক্ত করেছিলেন। এই ভাবনা থেকেই গঙ্গাকে মুক্তি বিতরণকারী বলা হয়। বিজ্ঞান-ব্যাখ্যায় জলের অপর নাম জীবন এবং ভূ-ভারতের জীবন-সংযুক্ত ও উজ্জীবনকারী নদী গঙ্গা তাই আপন গুণেই মুক্তি বিতরণকারী। এ কারণেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘আমরা’ কবিতায় গঙ্গানদীকে মুক্তি বিতরণকারী বলেছেন।
‘ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট’ বলা হয়েছে কেন?
‘ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট’ বলার কারণ – উদ্ধৃত অংশটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। কবি বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বোঝাতে ‘ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট’ অংশটি ব্যবহার করেছেন। বঙ্গদেশের উত্তরে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা সূর্যোদয়ে স্বর্ণবরণ ধারণ করে এবং অন্যসময় রুপোলি আভাচ্ছন্ন থাকে। ‘কাঞ্চন’ শব্দের অর্থ সোনা। স্বর্ণবর্ণা কাঞ্চনজঙ্ঘা বঙ্গদেশের শীর্ষে মুকুটের ন্যায় বিরাজ করছে। তাই কবি আলোচ্য উপমাটি ব্যবহার করেছেন।
‘বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে’ বলার কারণ কী?
বঙ্গকে বাঞ্ছিত ভূমি বলার কারণ – জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। আলোচ্য কবিতায় বাঙালি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাতৃভূমি বাংলার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কবিতার প্রতি ছত্রে রচিত হয়েছে বঙ্গদেশ ও বাঙালি জাতির গৌরব গাথা। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতা তার সন্তানদের সোনার ধানে; পবিত্র জল হাওয়ায় বুক ভরা মমতার পরশে লালন করেছেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় এভাবেই মাতৃভূমি বাংলাকে আমরা পেয়েছে –
“নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।”
সন্তান যেমন মায়ের কোলকে শ্রেষ্ঠ আসন মনে করে, মায়ের স্নেহ স্পর্শ তার কাছে যেমন পরম প্রাপ্তি; তেমনি বাংলাদেশের মাটিতে, জল হাওয়ায় জীবন অতিবাহিত করা সকল বাঙালির একমাত্র বাসনা। এই কারণে আলোচ্য কবিতায় ‘বঙ্গ’কে ‘বাঞ্ছিত ভূমি’ বলা হয়েছে।
‘নাগেরি মাথায় নাচি।’ – বাঙালি সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে কেন?
একথা বলার কারণ – কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতায় বাঙালির বীরসত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে উদ্ধৃত কথাটি বলেছেন। বাঙালি জাতির সূত্রপাত ও বিকাশ অতি প্রাচীন। সভ্যতার সূচনালগ্নে পরিবেশ যখন বন্য প্রাণের হিংস্রতায় মুখর, তখনই অকুতোভয় বাঙালি তার সভ্যতা শুরু করে। এ কাজে যেমন হিংস্র জন্তুদের পদানত করে; তেমনই অজস্র প্রতিকূলতাকে জয় করতে করতে, জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বানিয়ে তাকে টিকে থাকতে হয়। বাঙালির এই বিপদজয়ী চরিত্রকেই সাপের মাথায় নাচা বলে উল্লেখ করেছেন কবি।
‘আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,’ – ‘চতুরঙ্গ’ বলতে কী বোঝায়?
‘চতুরঙ্গ’ কী – প্রশ্নোক্ত অংশটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা বাঙালির গৌরবগাথা প্রচারক কবিতা ‘আমরা’ থেকে নেওয়া হয়েছে। হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী ‘চতুরঙ্গ’ সৈন্যদল বলে পরিচিত। অতীতদিনে বাঙালি জাতির বীরসত্তার নিদর্শন হল তাদের চতুরঙ্গে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করা ও বিদেশিদের পরাজিত করা।
দশাননের পরিচয় দাও।
দশাননের পরিচয় – বিশ্রবা মুনি ও নিকষা রাক্ষসীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাবণ। তার দশটা মাথা, কুড়িটি হাত, গায়ের রং ঘোর কালো, কেশ প্রদীপ্ত এবং লাল ঠোঁট। তার হাত এতটাই লম্বা যে চাঁদ, সূর্য আটকাতে পারে। লঙ্কা থেকে কুবেরকে সরিয়ে রাবণ রাক্ষসরাজ্য স্থাপন করে। ব্রহ্মার বরে দেব-দৈত্য-দানব-যক্ষ-রক্ষ-নাগ প্রমুখের অবধ্য রাবণ মানুষ রামচন্দ্রের হাতে পরাজিত ও মৃত হন। পুরাণমতে তিনি বিষ্ণুর অভিশপ্ত দ্বাররক্ষক জয়।
শ্রীরামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
পরিচয় – রঘুবংশীয় রাজা দশরথ এবং রাণী কৌশল্যার অশ্বমেধযজ্ঞ লব্ধ পুত্র হলেন রাম। ভারতীয় সংস্কৃতির পুরুষোত্তম রাম বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য ‘রামায়ণের’ নায়ক। স্ত্রী সীতার অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে লঙ্কাধিপতি রাবণ সহ বহু রাক্ষস এবং অত্যাচারীদের তিনি বধ করেন। পুত্ররূপে, মিত্ররূপে, স্বামী এবং রাজারূপে তিনি অতুলনীয় আদর্শের অধিকারী। রাম বিষ্ণুরই এক অবতার। শ্রেষ্ঠ নীতি ও পরমসত্য তাঁর জীবনকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছে।
‘দশানন জয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের’ পরিচয় দাও।
রামচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজা রঘুর পরিচয় – কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘আমরা’ কবিতায় বাঙালির বীরত্বের প্রসঙ্গে দশানন জয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহ রঘুর কথা উল্লেখ করেছেন। সূর্যবংশীয় রাজা দিলীপের পুত্র হলেন রঘু। তাঁর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র রাম। রঘু ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁর নামেই তাঁর বংশনাম হয় রঘুবংশ। তাই রামকে রঘুপতি ও রাঘব বলা হয়। বীর বাঙালি এই ইন্দ্রজয়ী রঘুকেও পরাজিত করে।
বিজয়সিংহ -এর পরিচয় দাও।
বিজয়সিংহের পরিচয় – কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতায় বিজয়সিংহ -এর নাম উল্লেখ আছে। রাঢ়দেশের সিংহবাহুর পুত্র হলেন বিজয়সিংহ। পিতা তাঁকে বহিষ্কার করায় তিনি সমুদ্রযাত্রা করেন এবং লঙ্কায় পৌঁছে যান। লঙ্কা জয়ী বিজয়সিংহের নামানুযায়ী লঙ্কার নাম ‘সিংহল’ হয়।
‘চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লিনাথে।’ – চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে দিল্লিনাথের হটে যাওয়ার কাহিনিটি কী?
চাঁদ-প্রতাপ – প্রশ্নে প্রদত্ত অংশটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ নামক কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। চাঁদ রায় ছিলেন বিখ্যাত বারো ভূঁইয়ার অন্যতম। তাঁর রাজধানী ছিল শ্রীপুরে। তিনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তিনি আকবরের অধীনতা স্বীকার না করে আমৃত্যু যুদ্ধ করেন।
কাহিনি – অপর এক ভূঁইয়া প্রতাপাদিত্যও মোগলদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তিনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। তাঁর রাজধানী ছিল ধুমঘাটে এবং তিনি শাসন করতেন যশোহর, খুলনা ও বাসরগঞ্জে। চাঁদের ভাই কেদার মোগলদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। এ সত্য বোঝাতেই দিল্লিনাথের হটে যাওয়ার কথা বলেছেন কবি।
‘জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? ‘জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান’ বলার কারণ কী?
আদিবিদ্বান্ – সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতায় ‘জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্’ বলতে ‘সাংখ্যদর্শন’ -এর প্রণেতা মহর্ষি কপিলকে বোঝানো হয়েছে।
কারণ – ‘সাংখ্যদর্শন’ -এর উদ্ভাবক মহর্ষি কপিল, প্রথম বিদ্বান ও জ্ঞানের আধার বলে পরিচিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাঁর এই পরিচয়কেই কবি কবিতায় প্রকাশ করেছেন।
কপিল মুনিকে নিয়ে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনিটি সংক্ষেপে লেখো।
কপিলমুনির কাহিনি – সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়া রাক্ষসবেশী ইন্দ্র চুরি করে কপিল মুনির পাতালে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে রেখে এলে সগরের ষাট হাজার সন্তান মুনিকেই অশ্ব অপহরণকারী ভাবে। তাদের আক্রমণে রেগে গিয়ে কপিল মুনির শাপে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাদের বংশধর ভগীরথ গঙ্গাকে সাধনাবলে মর্ত্যে এনে গঙ্গাজলের পবিত্র স্পর্শে তাদের পাপ দূর করে তাদের মুক্ত করেন।
পাঠ্য কবিতায় প্রাপ্ত অতীশ দীপঙ্করের পরিচয় দাও।
অতীশ দীপঙ্কর – বিক্রমমণিপুররাজ কল্যাণশ্রীর পুত্র অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পূর্বনাম আদিগর্ভ চন্দ্রনাথ। উনিশ বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি ‘শ্রীজ্ঞান’ উপাধি পান। তিনি নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিক্রমশীলার মহাস্থবির হওয়ার পর তিব্বতে ধর্মপ্রচারের আমন্ত্রণ পেয়ে প্রথমে না গেলেও পরে যেতে তিনি সম্মত হন। 1040 খ্রিস্টাব্দে তিনি তিব্বত যাত্রা করেন এবং সেখানে ধর্মশিক্ষা, মন্ত্রদান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ‘বোধিপাঠপ্রদীপ’, ‘বোধিপাঠপ্রদীপপঞ্জিকা’ ইত্যাদি তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের আজ কেবল তিব্বতি অনুবাদ পাওয়া যায়।
‘বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,’ – বলা হয়েছে কেন?
কারণ – বিক্রমশীলার মহাস্থবির অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতের রাজা প্রচুর স্বর্ণ উপহার দিয়ে নিজের দেশে ধর্মপ্রচারের আমন্ত্রণ জানান। অতীশ দীপঙ্কর প্রথমে অসম্মত হলেও পরে বিক্রমশীলার উন্নতিকল্পে সমূহ ধন উৎসর্গ করে 1040 খ্রিস্টাব্দে তিব্বত যাত্রা করেন। সে সময় হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত পথে পায়ে হেঁটে যাওয়াই ছিল মুখ্য। তা ছাড়া ঝড়ঝঞ্ঝা, শীতাতাপ ইত্যাদির ভয়াবহতাও স্বাভাবিকভাবে বর্তমান। জাতিতে বাঙালি অতীশ দীপঙ্কর এসব কিছুকে অতিক্রম করে তিব্বত যান। বাঙালির ধর্মসাধনায় নিষ্ঠা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি গুণের কথা বোঝাতেই ‘আমরা’ কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রশ্নোদ্ধৃত পঙক্তিটি ব্যবহার করেছেন।
‘জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে’ – ব্যাখ্যা করো।
ব্যাখ্যা – বিক্রমশীলার মহাস্থবির অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মহিমা পাঠ্য ‘আমরা’ কবিতায় প্রকাশ করেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিব্বতের রাজার অনুরোধে তিনি তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের পরম জ্ঞান তিব্বতবাসীর মধ্যে প্রচার করেন এবং তাদের বৌদ্ধধর্মের সুমহানতায় দীক্ষিত করেন। তিনি বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে মানবতার দীপ্তিতে তিব্বতকে উজ্জ্বল করেন। এ কথাই প্রশ্নে দেওয়া উক্তিটিতে বলা হয়েছে।
‘কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
পক্ষদরের পক্ষশাতনের অর্থ – ইতিহাস অনুসারে নব্যন্যায়ের প্রবর্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ছাত্র সুতার্কিক পক্ষধর মিশ্রকে (জয়দেব মিশ্র) তাঁরই কিশোর ছাত্র বাঙালি রঘুনাথ শিরোমণি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। ‘পক্ষশাতন’ কথার অর্থ পক্ষচ্ছেদ। পণ্ডিতকে পরাস্ত বা তাঁর অহংকার চূর্ণ করা পক্ষধরের পাখা কাটারই শামিল। এ কারণেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘আমরা’ কবিতার উদ্ধৃতাংশে উপমাটি বর্ণনা করেছেন।
কবি জয়দেবকে ‘বাংলার রবি’ বলা হয়েছে কেন?
‘জয়দেব’-কে ‘বাংলার রবি’ বলার কারণ – জয়দেব বাঙালি কিনা সেই বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। আলোচ্য কবিতাটিতে কবি জয়দেবকে বাঙালি বলেছেন। নানা তথ্যের মধ্যে একটি মতানুযায়ী জয়দেব বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব নিবাসী ভোজদেব ও বামাদেবীর পুত্র। লক্ষণ সেনের রাজসভায় অন্যান্য সভাকবিদের মধ্যে ছিল তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁর রচিত ‘গীতগোবিন্দম্’ কাব্যটি শুধুমাত্র সংস্কৃতেই নয়, বাংলা সাহিত্যে ও পাঠক মনে আজও অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর সৃষ্টির মহানতা দেখে কবি তাঁকে কবিদের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়েছেন নক্ষত্রলোকের সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ কারণেই ‘ছন্দের জাদুকর’ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতাটির মধ্যে কবি জয়দেবকে ‘রবি’ অর্থাৎ সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে ‘বাংলার রবি’ বলেছেন।
সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদকে সুরভিত করা বলতে কী বোঝায়?
তাৎপর্য – কবি জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যধারার এক বিশিষ্ট কবি। স্বর্ণপদ্মের মতো উজ্জ্বল রহুমূল্য সংস্কৃত সাহিত্যধারায় তিনি নিজের সৃষ্টির লালিত্য ও সৌরভ সংযুক্ত করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য যদি পদ্মফুল হয় তবে জয়দেবের সৃষ্টি তাঁর সুঘ্রাণ বলে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বাঙালির গৌরবগাথা প্রচারক ‘আমরা’ কবিতায় মন্তব্য করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগেও সংস্কৃতে রচিত তাঁর ‘গীতগোবিন্দম্’ কাব্যটি বাঙালির মনে আশার আলো সঞ্চার করে।
বরভূধরের পরিচয় দাও।
‘বরভূধর’ – কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘আমরা’ কবিতায় বাঙালির স্থাপত্যকীর্তির পরিচয় দিতে গিয়ে ‘বরভূধরের’ কথা বলেছেন, যা ‘বোরোবুদুরের স্তূপ’ নামে পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাভাদ্বীপে, বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজবংশের রাজত্বকালে এটি স্থাপিত হয়। ছোটো একটি পাহাড়কে কেন্দ্র করে 400 ফুট চতুষ্কোণ ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নয়তলা প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপটি ছিল রাজবংশের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার প্রতীক। তবে এখানে বাংলার শিল্পের সঙ্গে মিল না থাকলেও তৎকালীন সময়ে বাংলায় রাজত্ব করেছেন পাল বংশ। বাণিজ্যিক সূত্রে ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কারণে বাংলার সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবত এই কারণে কবি বরভূধরের স্তূপকে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য বলেছেন।
ওঙ্কার-ধামের পরিচয় দাও।
ওঙ্কারধাম – সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতায় প্রাচীন বাংলার শিল্প-স্থাপত্যের উপাদান হিসেবে ‘বরভূধরের’ পাশাপাশি ‘আঙ্কোরভাট’-কেও উল্লেখ করেছেন। তিনি একে ‘ওঙ্কারধাম’ বলেছেন। ‘আঙ্কোর’ শব্দের অর্থ নগর, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে স্থাপিত মন্দির নগর কম্বোজ তথা বর্তমানে কম্বোডিয়ার রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের রাজত্বকালে 1112-1152 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গড়ে ওঠে আঙ্কোরভাট বিষ্ণুমন্দির। পরিখাবেষ্টিত মনোমুগ্ধকর অলঙ্করণ ও শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ মন্দিরটির স্থপতি সূর্যবর্মনের গুরু পণ্ডিত দিবাকর। এখানে রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য, সমুদ্রমন্থনের কাহিনি এবং রাজদরবারের চিত্র রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে প্রাচীন বাংলার শাসক পাল বংশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, বলা যেতে পারে। সেই কারণে দুই অঞ্চলের প্রাচীন স্থাপত্যের শিল্পশৈলীতে মিল লক্ষ করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ সম্ভবত এজন্যে ‘আঙ্কোরভাট’-কে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য নিদর্শন বলেছেন। শুধু আঙ্কোরভাট নয়, ‘বরভূধরের’ সঙ্গেও বাংলার শিল্পের প্রচুর মিল। এর কারণ হিসেবে গবেষকরা মনে করেছেন, বাংলার শিল্পীরা এই স্থাপত্যগুলির নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন। কম্বোডিয়াতে প্রথম শৈবধর্মের প্রভাব দেখা যায়। কবি ‘আঙ্কোরভাট’কে ‘ওঙ্কার-ধাম’ বলেছেন হয়তো এই যুক্তিতে।
‘ধেয়ানের ধনে মূর্তি’ দেওয়ার অর্থ কী?
‘ধেয়ানের ধনে মূর্তি’-র ব্যাখ্যা – কল্পনা বিমূর্ত, শিল্প মূর্ত। কল্পনার রূপকে স্থপতিরা মূর্তিরূপে গড়েন। কল্পনার দৃশ্যকে বাস্তবে পাথর ও ধাতুর সাহায্যে যে শিল্পরূপ প্রদান করা হয় তাই ভাস্কর্য। প্রাচীন বাংলার শাসক ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে ধীমান ও তার পুত্র বিটপাল ভাস্কর্য ও চিত্রের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় লামা তারানাথ তার বিবরণে ধীমান ও বিটপালের উল্লেখ করেছেন। পাল যুগে শিল্পকে উৎকর্ষতা প্রদানে এদের বিশেষ অবদান ছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতায় বাঙালির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রসঙ্গে এঁদের অবিস্মরণীয় ভাস্কর বলেছেন।
‘পট’ কী? আমাদের পট অজন্তায় অক্ষয় বলা হয়েছে কেন?
পট কী – ‘পট’ শব্দের আভিধানিক অর্থ, ছবি, চিত্রপট, ছবি আঁকার উপযুক্ত মোটা বস্ত্রখণ্ড বা Canvas। আলোচ্য কবিতায় কবি ‘পট’ বলতে ‘ছবি’ বা ‘চিত্র’ বুঝিয়েছেন। বাংলার নিজস্ব শিল্পধারার মধ্যে পট শিল্প অন্যতম।
আলোচ্য উক্তির কারণ – প্রায় 200 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে সপ্তম শতাব্দী অজন্তার গুহাচিত্র নির্মাণের সময়কাল। মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের গুহায় অঙ্কিত বুদ্ধের জীবনী, জাতকের কাহিনি, নারী চিত্র, শিকারের কাহিনি চিত্র, নৃপতির চিত্র প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার অঙ্গ। গুহার ছাদে, দেয়ালে, স্তম্ভে এবং পাথরের মূর্তিতে চুনের প্রলেপ দিয়ে নানা ছবি আঁকা হত। অজন্তার 17 সংখ্যক গুহায় হাতি ও সেনাবাহিনী পরিবৃত রাজা বিজয়সিংহের চিত্র ও তার সিংহলে অভিষেকের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, বাঙালি কোনো পটুয়া (যিনি পটচিত্র অঙ্কন করে) বাংলার পটচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি ও শৈলীর দ্বারা বাংলার রাজা বিজয়সিংহের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। বাঙালি জাতির গৌরবময় ইতিহাসের অন্যতম উদাহরণ এই অক্ষয় চিত্রাঙ্কন, যা এখনও অজন্তায় মর্যাদার সঙ্গে বিরাজ করে চলেছে।
‘মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,’ – এ কথা বলা হয়েছে কেন?
আলোচ্য উক্তির কারণ – কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘আমরা’ কবিতায় বাঙালির অতীত থেকে প্রবাহিত জীবন-ইতিহাস বর্ণনাসূত্রে উদ্ধৃতাংশটি ব্যবহার করেছেন। ‘মন্বন্তর’ অর্থাৎ প্রবল দুর্ভিক্ষ এবং ‘মারী’ অর্থাৎ লোকক্ষয় বা মড়ক যা প্রাচীন বঙ্গের নিত্যসঙ্গী ছিল। তৎকালীন সময়ে মহামারি এবং দুর্ভিক্ষে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। বিজ্ঞান বা সমাজের কোনো ক্ষমতা ছিল না তা প্রতিরোধ করার। কিন্তু বাঙালি তার আত্মবলে মন্বন্তর ও মহামারির প্রকোপ জয় করে সভ্যতা টিকিয়ে রেখেছিল। সমাজকে নতুন প্রাণশক্তি দান করেছিল। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন কবি।
বাঙালি অমৃতের টিকা কীভাবে পরে আছে?
অমৃতের টিকা – কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘আমরা’ কবিতায় বাঙালির বিজয়কীর্তি বর্ণনা করেছেন। সভ্যতা সৃষ্টির আদিপর্বে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঙালির জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল। আর্যের অশ্বমেধ ও দিগবিজয় পণ্ড করে, মগ-মোগলকে পরাস্ত করেও তাকে লড়াই করতে হয়েছে পরাধীনতার সঙ্গে। মহামারি-মন্বন্তরও তাদের জীবনীশক্তির ক্ষয় করতে পারেনি। কালের গতির সঙ্গে সভ্যতা তথা বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে। মানুষ রোগকে প্রতিহত করার উপায় জেনেছে। আবিষ্কার হয়েছে নানা জীবনদায়ী ওষুধ। ‘অমৃত’ অর্থাৎ যার মৃত্যু নেই। দেবতার আশীর্বাদে কালের নিয়মে তারা বেঁচে থাকার উপায় জেনেছে, অমৃতের টিকা তাদের রক্ষা করেছে।
দেবতাকে আত্মীয় বলা হয়েছে কেন?
দেবতাকে আত্মীয় বলার কারণ – বাঙালি ভগবানকে প্রিয়জন মনে করে। হিন্দু ধর্মানুসারে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা পরমাত্মা তথা ঈশ্বরে বিলীন হয়। বাঙালির কাছে মৃত আত্মীয় দেব তুল্য। ‘আকাশ প্রদীপ’ প্রসঙ্গে কবি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবিগুরু বলেছিলেন – ‘দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।’ তাদের কাছে পিতা মাতা-স্বজন সকলই ঈশ্বররূপে আরাধ্য। বাঙালি জীবনধারার এই প্রকাশে ‘ছন্দের জাদুকর’ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বাঙালির মহিমা প্রচারক ‘আমরা’ কবিতায় দেবতার আত্মীয়ের কথা বলেছেন।
আকাশে প্রদীপ জ্বালা হয় কেন?
‘আকাশ প্রদীপ’ জ্বালানোর কারণ – কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতায় ‘আকাশ প্রদীপ’ প্রসঙ্গ এনেছেন। কার্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে অর্থাৎ কালীপুজোর আগের দিন ভূতচতুর্দশী। এদিন সন্ধেবেলা পূর্বপুরুষের উদ্দেশে চোদ্দো প্রদীপ জ্বালানো হয়। মনে করা হয় এসময় পিতৃপুরুষরা যমলোক থেকে ঘরে ফেরেন। তাদের পথ প্রদর্শক হয়ে এই আকাশ প্রদীপ পথ দেখায়। তাই ‘আকাশ প্রদীপ’ জ্বালানো হয়।
‘আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;’ – আমাদের কুটিরে মানুষের ঠাকুরালি দেখা গেছে কীভাবে?
মানুষের ঠাকুরালি যেভাবে দেখা গেছে – ‘মানুষের ঠাকুরালি’-র অর্থ মানবদেহে দেবলীলার মহিমা। বাঙালি ঘরের সন্তান গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ প্রমুখকে আমরা অবতাররূপে মান্য করি। তাঁরা রক্তমাংসের মানুষ হয়েও কর্মগুণে দেবত্ব অর্জন করেছেন। আবার বাঙালির ভক্তি-বিশ্বাসে দেবতা কখনও তাদের সন্তান। কখনও সহচর হয়েছেন। সাধারণ মানুষের মতই ঐশ্বর্যময় দেবতা জীবন অতিবাহিত করেছেন মানুষের সংস্পর্শে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বাঙালির মহিমা প্রচারক ‘আমরা’ কবিতায় বলেছেন আমাদের কুটিরেই ঈশ্বর স্বয়ং মানুষরূপে আজীবন মানবধর্ম পালন করেছেন।
বিবেকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
‘বিবেকের’ পরিচয় – কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলের বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত (1863-1902 খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর ‘বিবেকানন্দ’ নামে পরিচত হন। তিনি বিএ পাস করে আইন পড়ার সময় পিতার মৃত্যুর কারণে পড়া বন্ধ করে দেন। রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য তাঁর জীবনে পরিবর্তন আনে। 1893 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা তাঁকে বিশ্বখ্যাতি প্রদান করেছিল। 1897 খ্রিস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ও 1899 খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠ স্থাপন করেন। ‘পরিব্রাজক’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘ভাববার কথা’, ‘বর্তমান ভারত’ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখ্য রচনা।
বিবেকানন্দকে ‘বীর সন্ন্যাসী’ বলা হয়েছে কেন?
‘বীর সন্ন্যাসী’ বলার কারণ – সর্বকর্মফল ত্যাগ করে ভগবানে আত্মনিবেদিত, স্থূলকর্ম ও জাগতিক মোহত্যাগী ব্যক্তিই হলেন সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণদেবের থেকে মানবসেবায় দীক্ষা নেওয়া নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর সন্ন্যাস নেন এবং বিবেকানন্দ নামগ্রহণ করেন। তিনি জগৎ জুড়ে বিশ্বমানবতা ও মানবমুক্তির বাণী প্রচার করেন। আর্ত, পীড়িতদের ত্রাণকর্মে তিনি নিজের জীবন তুচ্ছ করে দেন। সেবাশ্রম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। মানবকল্যাণে তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মদানকেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতায় ‘বীর সন্ন্যাসী’র মর্যাদা দিয়েছেন।
‘বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,-‘ বিবেকের বাণী জগৎময় কীভাবে ছুটেছে?
বিবেকের বাণী জগৎময় যেভাবে ছুটেছে – প্রশ্নে প্রদত্ত অংশটি ‘ছন্দের জাদুকর’ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা বাঙালির মহিমা প্রচারক ‘আমরা’ কবিতা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ নাম নিয়ে আমেরিকার শিকাগো শহরে 1893 খ্রিস্টাব্দের 11 সেপ্টেম্বর Parliament of Religions-এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে জগতকে চমৎকৃত করেন। তাঁর বেদান্ত সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু নরনারী তাঁর বক্তব্য ও ধর্ম মতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর এই বিশ্বখ্যাতিকে বলেছেন – ‘বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়।’
‘ব্যাঘ্রে বৃষভে’ সমন্বয় বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
‘ব্যাঘ্রে-বৃষভে’ সমন্বয় -এর ব্যাখ্যা – স্বজাতিপ্রেমিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘আমরা’ কবিতাটি তাঁর স্বাজাত্যবোধের পরিচায়ক। ‘ব্যাঘ্র-বৃষভ’ শব্দটি চলতি কথায় বাঘে-ষাঁড়ে বা বাঘে-গরুতে। এদের সমন্বয় বলতে বোঝায় বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্য। বৃহৎ বিশ্বকে ভেদাভেদ মুক্ত করে অভিন্ন ঐক্যবোধ সংবলিত বিশ্ব গড়ে তোলার মন্ত্র শুনিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পরাধীনতার কালে ভারতীয়দের অসম্মান করত জাত্যাভিমানী বিদেশি শ্বেতাঙ্গ শাসকদল। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছিল। তাঁর বক্তব্যে নিজেদের জাতি বর্ণ ভুলে মন্ত্রমুগ্ধের মতন বিদেশি মানুষজন বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, ভারতে সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিল। কবি এই সমন্বয় বোঝাতে ‘ব্যাঘ্ৰে-বৃষভে’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
‘তপের প্রভাবে বাঙালি সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,’ – জড়ের সাড়া পাওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
জড়ের সাড়া পাওয়া – আলোচ্য উদ্ধৃতিতে বাঙালি সাধক বলতে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে বোঝানো হয়েছে। মানুষের দীর্ঘকালের ধারণা ছিল উদ্ভিদের প্রাণ নেই, তারা জড় পদার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু জড় ও জীবের মধ্যে উত্তেজনাপ্রসূত বৈদ্যুতিক সাড়ার সমতা নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ‘Responses in the living and Non-living’ বইটিতে তিনি দেখান বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উত্তেজনায় উদ্ভিদ ও প্রাণী একভাবে সাড়া দেয়। উদ্ভিদ ও মানুষের মতই সজীব উপাদান। এতকালের চিরাচরিত বিশ্বের ধারণা, সেদিন পরিবর্তিত হয়েছিল বাঙালি এই বিজ্ঞান সাধকের তপস্যার ফলে। তাঁর কৃতিত্ব বিশ্বজগতে অবিস্মরণীয়। বাঙালি জাতির গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতায় জগদীশচন্দ্র বসুর উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানীর উদ্ভিদের প্রাণ আবিষ্কারের বিষয়কে কবি জড়ের সাড়া পাওয়া বলেছেন।
‘নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া’ কেন?
‘নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া’ কথাটি বলার কারণ – ‘আমরা’ কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভিদের প্রাণ আবিষ্কারের প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন। হিন্দু তন্ত্রসাধনার একটি অংশ হল ‘শব-সাধনা’। মৃত ব্যক্তির দেহের উপর অধিষ্ঠান করে সাধক এই সাধনা করেন। আর অন্যদিকে প্রাণহীন ‘জড়’ বলে পরিচিত বস্তুর মধ্যে অনুভূতি ও প্রাণস্পন্দন আবিষ্কার দুরূহ কাজ। সমগ্র জগতের দীর্ঘকালের মান্য তথ্যকে জগদীশ চন্দ্র বসু নিজের তপস্যার দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। তাই কবি বলেছেন তান্ত্রিকের শব সাধনার থেকে বৃহত্তর সাধনা হল বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর সাধনা।
‘বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালি দিয়েছে বিয়া,’ – বলার কারণ কী?
আলোচ্য উদ্ধৃতির কারণ – প্রশ্নে প্রদত্ত অংশটি ‘ছন্দের জাদুকর’ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা বাঙালির গৌরব প্রচারক ‘আমরা’ কবিতা থেকে সংকলিত। বাঙালি বিজ্ঞানী রসায়নবিদ স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় পারদ মার্কারি ও নাইট্রাইট মিশিয়ে মারকিউরাস নাইট্রাইট তৈরি করেছিলেন। পূর্ববর্তী রসায়নবিদরা এদের বিষম বা অসংগত বলে মনে করতেন। কিন্তু বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই তথাকথিত বিষম ধাতুর সংযোগ করেছিলেন বলে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিষমের বিয়া কথাটির প্রয়োগ করেছেন।
‘নব্য রসায়ণ শুধু গরমিলে মিলাইয়া’ বলার কারণ কী?
‘গরমিলে মিলাইয়া’ বলার কারণ – আলোচ্য উদ্ধৃতিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘আমরা’ কবিতার অন্তর্গত। ‘গরমিল’ শব্দের অর্থ অমিল। প্রথাগত অমিলসম্পন্ন বা বিষম ধর্মযুক্ত উপাদানের মধ্যে মিলসাধন করে বাঙালি বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় নতুন যৌগ আবিষ্কার করেছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বাঙালির জয়গাথা প্রচারক ‘আমরা’-কবিতায় প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এই আবিষ্কারের কথা বলেছেন। তাঁর আবিষ্কার বিশ্ববিজ্ঞান মহলে সাড়া ফেলেছিল। নতুন করে বিষম পদার্থের মিশ্রণে রাসায়নিক যৌগ গঠনের বিষয়কে কবি ‘গরমিলে মিলাইয়া’ বলেছেন।
পাঠ্য ‘আমরা’ কবিতায় কোন্ কোন্ বাঙালি সন্তানের নামের উল্লেখ আছে?
আলোচ্য কবিতায় উল্লিখিত বাঙালিরা – পাঠ্য ‘আমরা’ কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালির গৌরবকাহিনি প্রকাশে অতীত থেকে তাঁর সমকালীন উজ্জ্বল বাঙালিদের নামোচ্চারণ করেছেন। তাঁরা হলেন – বিজয়সিংহ, চাঁদ রায়, প্রতাপসিংহ, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জয়দেব, পালবংশীয় ধীমান ও তার পুত্র বিটপাল, শ্রীচৈতন্যদেব এবং বিবেকানন্দ। এ ছাড়া কবিতার মধ্যে ইঙ্গিতবাহী অনুচ্চারিত নামগুলি হল – কিশোর রঘুনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ।
‘বাঙালির কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,’ – ব্যাখ্যা করো।
আলোচ্য উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা – কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে বাঙালির কবি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিশ্বমানবতাবাদী কবি। মানুষ এক এবং অভিন্ন, জগৎ জুড়ে এক জাতি তথা মানবজাতি বিরাজ করবে, তারা বিবিধ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হয়েও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-শিল্প-সংগীতের মধ্য দিয়ে মানবতার এই পরম সত্যকে প্রকাশ করে মানুষের মাঝে মহাসম্মিলন ঘটানোর প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় ‘মহামিলনের গান’। এই কারণেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বাঙালির মহিমা প্রচারক ‘আমরা’ কবিতায় প্রশ্নে প্রদত্ত উদ্ধৃতিটির অবতারণা করেছেন।
‘বেতালের প্রশ্ন’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
‘বেতালের প্রশ্ন’ বিষয়ের ব্যাখ্যা – ‘আমরা’ কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের উৎকর্ষতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’-র উল্লেখ করেছেন। ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘বেতাল’ একজন শব, যাকে মন্ত্র বলে প্রেতে পরিণত করা হয়েছে। কাহিনি অনুযায়ী বেতাল রাজা-বিক্রমাদিত্যকে একটি করে বুদ্ধির প্রশ্ন করত, যা রাজাকে উভয় সংকটে ফেলত। কবি এখানে বলেছেন – সংকটকালীন মুহূর্তে গড়ে ওঠা কঠিন প্রশ্নগুলির জবাব দিয়েছে সত্যাগ্রহী বাঙালি জাতি। তারা বিশ্বের সকল সমস্যার ভয়হীনভাবে সমাধানের পথ দেখিয়েছে। বাঙালি জাতির গৌরবময় ইতিহাস তাদের জ্ঞানবোধ ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন কবি আলোচ্য অংশে।
‘সত্যে প্রণমি থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।’ – ব্যাখ্যা করো।
ব্যাখ্যা – কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতায় বাঙালি জাতির গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ব্রিটিশ অধীনস্থ বাঙালি পরাধনীতার যন্ত্রণার মাঝে প্রবল আত্মিক দ্বন্দ্ব ও মানসিক সংকটে উপনীত হয়েও তাদের সর্বস্ব পণ করেছিল সত্যের জন্য। সত্যের পথে আসা প্রতিবন্ধকতাকে তারা জয় করেছে সত্যের আশ্রয়ে। সত্যাগ্রহী এই বাঙালি জাতি নিজেদের সংকল্পে অবিচল থেকে সম্পন্ন মানসিক অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব ও সংকটকে দমন করেছিল।
‘শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,’ – শ্মশানের বুকে পঞ্চবটী রোপণ করার অর্থ কী?
অন্তর্নিহিত অর্থ – প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘আমরা’ কবিতা থেকে সংগৃহীত। এখানে ‘শ্মশানের’ একটি অর্থ মৃতদেহ দাহ করার স্থান। কবিতায় কবি ‘শ্মশান’ বলতে প্রাণহীন, উদ্যমহীন পরাধীন ভারতবর্ষকে বুঝিয়েছেন। আবার বট, অশ্বত্থ, বেল, অশোক ও আমলকী এই পাঁচ বৃক্ষের সমন্বিত এলাকাকে পঞ্চবটী বলা হয়। কবি আলোচ্য কবিতায় বলতে চেয়েছেন, মৃতপ্রায়, অনুভূতিহীন দেশে বাঙালি জাতি ‘পঞ্চবটী রোপন’ তথা প্রাণ সঞ্চার করেছে। যেখানে জীবনপ্রবাহ থেমে যায়, সেই শূন্যতা থেকেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙালি শাস্তিমন্ত্রে মহা-মানবতার সাম্রাজ্যের নবজন্ম ঘটিয়েছে।
‘তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।’ – ‘তাহারি’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তার ছায়ায় শতকোটির মিলের অর্থ কী?
‘তাহারি’ বলতে যাকে বোঝানো হয়েছে – সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা বাঙালির মহিমা প্রচারক ‘আমরা’ কবিতায় ‘তাহারি’ বলতে শ্মশানে রোপিত পঞ্চবটীর ছায়া বৃক্ষ বোঝানো হয়েছে।
পঞ্চবটীর ছায়ায় শতকোটির মিলনের অর্থ – শ্মশান-সদৃশ উদ্যমহীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্ন বাঙালিরাই দেখিয়েছিল। অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালের রচনা ও বক্তৃতা এবং দাদাভাই নৌরজির ‘স্বরাজ চাই’ আহ্বান একথার সাক্ষ্য। শ্মশানের ন্যায় উদ্যমহীন দেশে, নতুন যুগের সূচনার আশা জাগিয়ে বাঙালি, সমগ্র দেশবাসীকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিল। কবির কথায়, আদর্শহীন দেশে ‘পঞ্চবটী’ তথা মুক্তিমন্ত্রের দ্বারা বাঙালি জাতি শতকোটি মানুষের মহামিলন ঘটিয়েছিল। গ্রহণক্ষম বাঙালি জাতির এই কর্মকাণ্ডকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘জগতের শতকোটি’-র মিলন বলেছেন।
‘মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে’ – ব্যাখ্যা করো।
ব্যাখ্যা – কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘আমরা’ কবিতায় বাঙালির গর্বিত অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরে স্বজাতির মাহাত্ম্যপ্রচার করেছেন। একইসঙ্গে তিনি আশা রেখেছেন বাঙালির ভবিষ্যতের ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কেও। উদ্ধৃত পঙক্তিটি তেমনই এক আশার বাণী প্রচার করেছে। এ পঙক্তিতে কবি বলেছেন সৃষ্টির মধ্যে ঐশ্বর্যের যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাকে সম্পন্ন ও পরিপূর্ণ করে তোলার ক্ষমতা বাঙালির হাতেই আছে।
“আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থে — বরদা বঙ্গে —” এই পঙ্ক্তিটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
কবির বক্তব্য: উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
বঙ্গভূমির বর্ণনা করতে গিয়ে কবি উক্ত কথাটি বলেছেন। আমাদের এই বাংলায় রয়েছে অজস্র তীর্থক্ষেত্র। মানুষ বিশ্বাস করে, তীর্থদর্শন করলে পুণ্য অর্জন করা যায়, ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা যায়। বাঙালি জাতির সৌভাগ্য যে তারা এমন একটি দেশে বাস করে, যে দেশের মাটি তাদের শত তীর্থের পুণ্য আর বর দান করে।
“সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে —” এ কথা বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
কবির ভাবনা: উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে বাংলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর রয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কল্পনায় সাগর যেন বাংলামায়ের চরণ ছুঁয়ে আছে। বাঙালির সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পা ছুঁয়ে প্রণাম করার রীতি প্রচলিত আছে। তাই কবির মনে হয়েছে, তটভূমিতে আছড়ে পড়া অজস্র ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে সাগর যেন বাংলামায়ের চরণে তার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছে আর ঢেউয়ের মধুর ধ্বনি রচনা করছে মায়ের বন্দনাগান।
“সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।” — পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। অথবা, “আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়।” — ঐতিহাসিক ঘটনাটি কী?
তাৎপর্য: পালি ভাষায় লেখা সিংহলি দীপবংশ ও মহাবংশ পুরাণ অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ প্রাচীন বাংলার রাঢ় দেশের সিংহপুরের রাজপুত্র বিজয়সিংহ তাম্রপর্ণী (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) দেশের লঙ্কা নামক স্থানে গিয়ে নিজের রাজ্য ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামানুসারেই লঙ্কার ‘সিংহল’ নামকরণ হয়। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই কবি বলেছেন যে সিংহল নামের মধ্যেই রয়েছে বাঙালি বিজয়সিংহের বীরত্বের পরিচয়।
“কপিল সাঙ্খ্যকার/ এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।” — পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
ব্যাখ্যা: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতার উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটিতে বৈদিক ঋষি, সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলমুনির কথা বলা হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রে তাঁকে আদিপুরুষ বলা হয়েছে; আবার ভাগবত পুরাণে তাঁকে ভগবান বিষ্ণুর অবতারও বলা হয়েছে। বাংলার দক্ষিণতম প্রান্ত গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির একটি আশ্রম আছে। তাই কবি ধরে নিয়েছেন, তাঁর সাংখ্যদর্শনের রচনাভূমিও নিশ্চয়ই এই বাংলা। সত্যেন্দ্রনাথ শুধু জন্মসূত্রেই নয়, কর্মসূত্রেও যাঁরা বাংলার সান্নিধ্যে এসেছেন বা বাঙালি যাঁদের ভালোবেসেছে, তাঁদেরকেও বাংলার গৌরবগাথায় শামিল করেছেন।
“পক্ষধরের পক্ষশাতন করি/বাঙালির ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি” – পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা করো। অথবা, “কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি” – পক্ষধর কে? তাঁর পক্ষচ্ছেদন কীভাবে হয়েছিল?
উৎস: উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
ব্যাখ্যা: এখানে ‘বাঙালির ছেলে’ বলতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির কথা বলা হয়েছে। ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। কিশোর রঘুনাথ তৎকালীন মিথিলার প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। এর ফলে নব্যন্যায়চর্চার ক্ষেত্রে নবদ্বীপ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পক্ষধর মিশ্রের পরাজয়কেই কবি ‘পক্ষধরের পক্ষশাতন’ অর্থাৎ পক্ষধরের ডানা কাটা বলেছেন। এই ঘটনায় নিঃসন্দেহে বাঙালির গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল।
“করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন – কোকনদে।” — এই পঙ্ক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি কী বুঝিয়েছেন?
কবির ভাবনা: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘আমরা’ কবিতার উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটিতে কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যটির কথা বলেছেন।
সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যটি রচনা করেন। সুললিত ভাষায় রচিত তাঁর এই কাব্যটি সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সারা ভারতবর্ষেই গীতগোবিন্দ অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাই সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন যে গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্যের সোনার পদ্মকে সুগন্ধে ভরিয়ে তুলেছে।
“স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি” – পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
ব্যাখ্যা: খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে জাভা দ্বীপে (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) শৈলেন্দ্র রাজবংশের রাজত্বকালে গড়ে ওঠা সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপ হল বরভূধর। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই অঞ্চলের স্থাপত্যে পাল-সেন যুগের প্রভাবের কথাও জানা যায়। এই সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই সম্ভবত কবি বরভূধর স্তূপকে বাঙালির তৈরি বলেছেন।
“শ্যাম-কম্বোজে ওঙ্কার-ধাম – মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।” – পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
ব্যাখ্যা: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘আমরা’ কবিতা থেকে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি নেওয়া হয়েছে।
কম্বোজ (বর্তমান কম্বোডিয়া)-এ দ্বাদশ শতাব্দীতে খমের (Khmer) বংশীয় রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের সময়ে তৈরি প্রথমে হিন্দু এবং পরে বৌদ্ধ মন্দির হল ‘ওঙ্কার-ধাম’ বা আঙ্করভাট। প্রাচীন বাংলার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগের এবং ওই অঞ্চলের স্থাপত্যে পাল-সেন যুগের প্রভাবের কথা জানা যায়। সম্ভবত এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই কবি ‘ওঙ্কার-ধাম’ মন্দিরকে বাঙালির কীর্তি বলেছেন।
“ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর” — এই পঙ্ক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি কী বলতে চেয়েছেন?
কবির ভাবনা: উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
ধাতু, পাথর ইত্যাদি দিয়ে মূর্তি নির্মাণকারী শিল্পীকে ভাস্কর বলা হয়। শিল্পী তাঁর ধ্যানে অর্থাৎ মনের গভীর ভাবনা ও কল্পনায় যা দেখেন, তাকেই রূপ দেন মূর্তিতে অর্থাৎ ভাস্কর্যে। প্রাচীন বাংলার দুজন বিশিষ্ট ভাস্কর হলেন পাল যুগের বিট্পাল আর ধীমান। কবি বলেছেন, বাঙালির কল্পনাকে মূর্তিতে রূপ দিয়েছেন আমাদের এইসব ভাস্কর।
“বিট্পাল আর ধীমান — যাদের নাম অবিনশ্বর।” – বিট্পাল আর ধীমানের নাম অবিনশ্বর কেন?
অবিনশ্বর হওয়ার কারণ: বাংলায় পাল বংশের সময়কার দুজন প্রখ্যাত ভাস্কর হলেন বিট্পাল এবং ধীমান।
মনের গভীর কল্পনায় দেখা ছবিই রূপ পায় ভাস্করের হাতে। ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে ধাতু বা পাথরের বুকে তাঁরা খোদাই করেন অপূর্ব শিল্পকীর্তি। প্রাচীন বাংলায় পালবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে ভাস্কর বিট্পাল এবং ধীমান বাঙালির এরকমই কল্পনাকে রূপ দান করেছিলেন। তাঁদের হাত ধরে বাংলার স্থাপত্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল বলেই তাঁরা অবিনশ্বর।
“আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।” – এ কথা বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
কবির বক্তব্য: উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
অজন্তার সতেরো নম্বর গুহাতে হাতি ও অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে রাজপুত্র বিজয়সিংহের এবং সিংহলরাজ হিসেবে বিজয়সিংহের অভিষেকের দুটি ছবি আঁকা আছে। সিংহলি দীপবংশ ও মহাবংশ পুরাণ অনুসারে এই বিজয়সিংহ রাঢ় দেশের সিংহপুরের রাজপুত্র। অনেকের মতে তিনি বাঙালি। তাই সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন যে কোনো এক বাঙালি পটুয়া অর্থাৎ চিত্রশিল্পী অজন্তা গুহায় বাঙালির পট অক্ষয় করে রেখেছেন।
“আমরা দিয়েছি খুলি/মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।” — কবির বক্তব্য ব্যাখ্যা করো।
ব্যাখ্যা: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘আমরা’ কবিতার উদ্ধৃতাংশটিতে বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ কীর্তনগান ও বাউলগানের কথা বলা হয়েছে। কীর্তন হল রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান, আর ধর্মীয় সংস্কার ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত বাউল সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মিক সংগীত হল বাউলগান। আবেগপ্রবণ বাঙালি জাতি তার দুঃখ-বেদনা-ভালোবাসা, সর্বধর্মের মিলনের কথা সবই এই গানগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। তাই কবি বলেছেন, কীর্তন-গান আর বাউলগানে বাঙালি তার মনের দরজা খুলে দিয়েছে।
“আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি” – পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
ব্যাখ্যা: উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
‘ঠাকুরালি’ শব্দের অর্থ হল দেবতার মতো মহিমা। বাঙালির ঘরের ছেলে, যাঁরা নিজেদের কর্মকাণ্ডে দেবতার মতো মহিমা লাভ করেছেন, এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। তবে এঁদের মধ্যে যাঁরা জগৎ-বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি নিজের কর্মগুণে জীবিত অবস্থাতেই দেবতাসুলভ মহিমা লাভ করেছেন। বাঙালি শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায় এই রক্তমাংসের মানুষদেরও দেবত্বে উন্নীত করে পূজা করেছে।
“ঘরের ছেলে চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া” — এ কথা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
কবির বক্তব্য: বাঙালি তার ঘরের ছেলের মধ্যেই বিশ্বসম্রাটকে প্রত্যক্ষ করেছে। নিঃসন্দেহে কবি এখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকেই বুঝিয়েছেন। শুধু জমি এবং ক্ষমতার অধিকারী হলেই রাজা হওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যদেব ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ না করে, উচ্চ-নীচ ভেদ না করে, সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভালোবাসা বিতরণ করে মানুষের হৃদয়ের রাজা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই ভালোবাসার আদর্শ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তাই কবি উক্ত মন্তব্যটি করেছেন।
“বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।” — পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। অথবা, “নিমাই ধরেছে কায়া” – নিমাই কীভাবে কায়া ধরেছে লেখো।
তাৎপর্য: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি নেওয়া হয়েছে।
পঙ্ক্তিটির আক্ষরিক অর্থ হল বাঙালির হৃদয়ের অমৃত মন্থন করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব দেহ ধারণ করেছেন। ‘অমিয়’ শব্দের অর্থ অমৃত বা সুধা, অর্থাৎ যা পান করলে অমর হওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে অমিয় বলতে বাঙালির হৃদয়ের যাবতীয় সদ্গুণ যেমন দয়া-প্রেম-ভালোবাসা-ভক্তি-সততাকে বোঝানো হয়েছে। বাঙালি হৃদয়ের এই যাবতীয় গুণই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।
“বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়” — কবি কেন এই কথা বলেছেন?
মন্তব্যের কারণ: উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরের ধর্মমহাসসম্মেলনে প্রাচীন হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিকতা এবং দর্শন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্য শুধু আমেরিকাবাসীকেই নয়, সারা পৃথিবীর মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। জগৎজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিবেকানন্দের বাণী। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন তাঁর কাছে, গ্রহণ করেন তাঁর শিষ্যত্ব। এই কারণেই কবি উক্ত কথাটি বলেছেন।
“আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।” — পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।
উৎস: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।
তাৎপর্য: সদ্যোমৃত পুরুষের শবের ওপর ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে বসে তান্ত্রিক সাধনাকেই শবসাধনা বলে। তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। জগদীশচন্দ্র বসু বা প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে ধরনের বিজ্ঞানসাধনা বা চর্চার সূত্রপাত করেন, তা মানবজীবনের পক্ষে কল্যাণকর হলেও দীর্ঘ জ্ঞানতপস্যার ফসল।
“মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।” — পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
উৎস: আলোচ্য পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
ব্যাখ্যা: এই পঙ্ক্তিটিতে কবি বাঙালির রসায়নচর্চার কথা বলেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালির রসায়নচর্চার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। রসায়ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের মৌলের রাসায়নিক সংযোগে তৈরি করা হয় নিত্যনতুন যৌগ। ‘গরমিলে মিলাইয়া’ বলতে কবি এখানে যেসব মৌলের মধ্যে রাসায়নিক ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো মিল নেই, তাদের রাসায়নিক সংযোগকেই বুঝিয়েছেন।
“বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালি ধাতার আশীর্বাদে।” পঙ্ক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
উৎস: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি নেওয়া হয়েছে।
ব্যাখ্যা: এই কবিতাটিতে কবির গভীর জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। স্বদেশ ও স্বজাতি বিশ্বের অন্য কোনো দেশ ও জাতির তুলনায় কোনো অংশে কম নয়, বরং অনেক বেশি উন্নত—এই বোধই জাতীয়তাবাদের মূলকথা। ‘আমরা’ কবিতাটি হল বাংলা ও বাঙালির জয়গাথা। মানুষের বিশ্বাস হল, ঈশ্বর পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ করেন। কবি মনে করেন, বিধাতার আশীর্বাদে বাঙালি তাঁর এই কল্যাণময় কাজের দায়িত্ব নেবে।
“সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে” — পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো。
উৎস: উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
তাৎপর্য: এই কবিতাটিতে কবির জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি জগৎ ও জীবনের সব ক্ষেত্রেই বাঙালিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে দেখতে চেয়েছেন। কবিতাটির শুরু থেকেই কবি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালির কৃতিত্বের উল্লেখ করে তারপর উদ্ধৃত উক্তিটি করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, বাঙালির বহুযুগের সাধনা তথা কর্মপ্রচেষ্টা এতদিনে সাফল্য পেয়েছে। তাই তারা ‘জগৎ-প্রাণের হাটে’ অর্থাৎ বিশ্বের দরবারে তার স্বীকৃতি পেয়েছে।
“সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে” — পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
উৎস: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি নেওয়া হয়েছে।
তাৎপর্য: মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর জীবনের শেষ কিছু বছর পুরীধামে যে ভাবমগ্ন অবস্থায় কাটান, তাকে গম্ভীরাস্থিতি বলা হয়। এইসময় সমুদ্রের খুব কাছে একটি মঠে তিনি অবস্থান করতেন। এই ঘটনাটির সূত্র ধরেই সত্যেন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন যে বঙ্গদেশের দক্ষিণেও রয়েছে সমুদ্র। তাই ভাবপ্রবণ বাঙালিও মহাপ্রভুর মতোই সমুদ্রের হাওয়ায় শ্বাস নিয়ে গম্ভীরাস্থিতি অর্থাৎ নিজস্ব ভাবনায় ডুবে থাকে।
“তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।” পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।
উৎস: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘আমরা’ কবিতা থেকে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি নেওয়া হয়েছে।
তাৎপর্য: কবি বলেছেন, যেখানে জীবনের শেষ সূচিত হয়, সেই শ্মশানে বাঙালি পঞ্চবটী অর্থাৎ নতুন জীবনের স্বপ্নকে রোপণ করেছে। বাঙালির মধ্যে রয়েছে সেই প্রাণময়তা, যা জীবনকে পূর্ণ করে তোলে। বাঙালি তার হৃদয়ের শক্তিতে তাই শ্মশানকে পঞ্চবটীতেই শুধু রূপান্তরিত করে না, সব মানুষকে সে আপন করে নেয়। বাংলার ভূমিতে মিলে যায় গোটা পৃথিবীর মানুষ।
“প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশি” — কবি এখানে কোন্ ঘটনার কথা বলতে চেয়েছেন?
উদ্দিষ্ট ঘটনা: উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।
এই কবিতায় কবির জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতিকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ভারতীয়সুলভ; তাতে কোনো উগ্রতা নেই বা অন্য কোনো দেশের প্রতি হিংসা নেই। তাই তিনি হানাহানির মাধ্যমে এই শ্রেষ্ঠত্ব চাননি। কবি আশা করেছেন, বাঙালি তার প্রতিভা এবং সাধনার জোরেই জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করবে।
“লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি” — পঙ্ক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
উৎস: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি নেওয়া হয়েছে।
তাৎপর্য: এই কবিতাটিতে কবির জাতীয়তাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ উগ্রতাবিহীন। অন্য দেশ বা জাতির প্রতি কোনো ঘৃণার প্রকাশ আলোচ্য কবিতায় ঘটেনি। তিনি আশা করেছেন, বাঙালি একদিন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। তার জন্য ঈর্ষা-বলপ্রয়োগ-হানাহানির কোনো প্রয়োজন হবে না; বাঙালি তার প্রতিভা ও সাধনার মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করবে।
“মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।” — কবি কেন এ কথা বলেছেন ব্যাখ্যা করো।
এ কথা বলার কারণ: উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা ‘আমরা’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। বাঙালি জাতির মাতৃভূমি বাংলা শুধু একটি সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা দেশই নয়, অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও সমৃদ্ধ। এমন একটি দেশে জন্মগ্রহণ করা যে-কোনো মানুষের কাছেই অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। বাঙালি জাতি সুমহান ঐতিহ্য বহন করে আনছে। তার উত্তরসূরি হয়ে জন্মানোয় কবি ঈশ্বরের কাছে ঋণী। তাই তিনি বলেছেন, সারা পৃথিবীর মানুষকে মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করে বাঙালি জাতি দেবতার সেই ঋণ শোধ করবে।
আজকের এই আর্টিকেলে আমরা নবম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের পঞ্চম পাঠের তৃতীয় অধ্যায়, ‘আমরা’ -এর কিছু ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নোত্তরগুলো নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নবম শ্রেণীর বাংলা পরীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মিত আসে। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে, তবে টেলিগ্রামে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত। ধন্যবাদ।

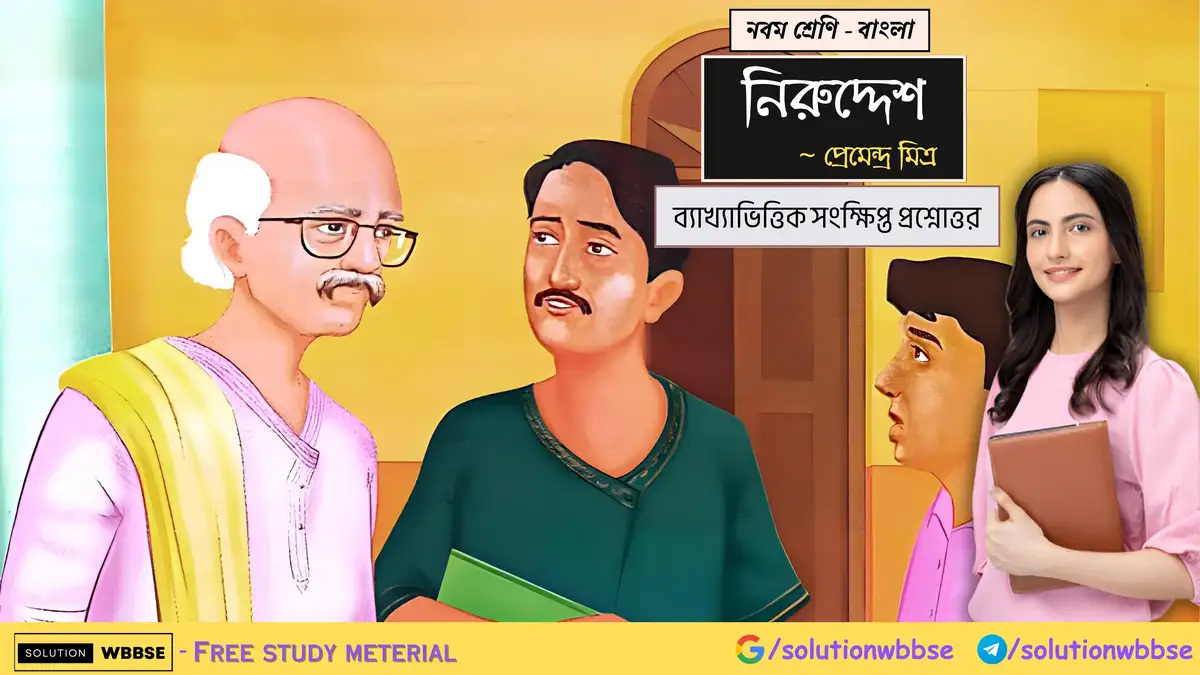
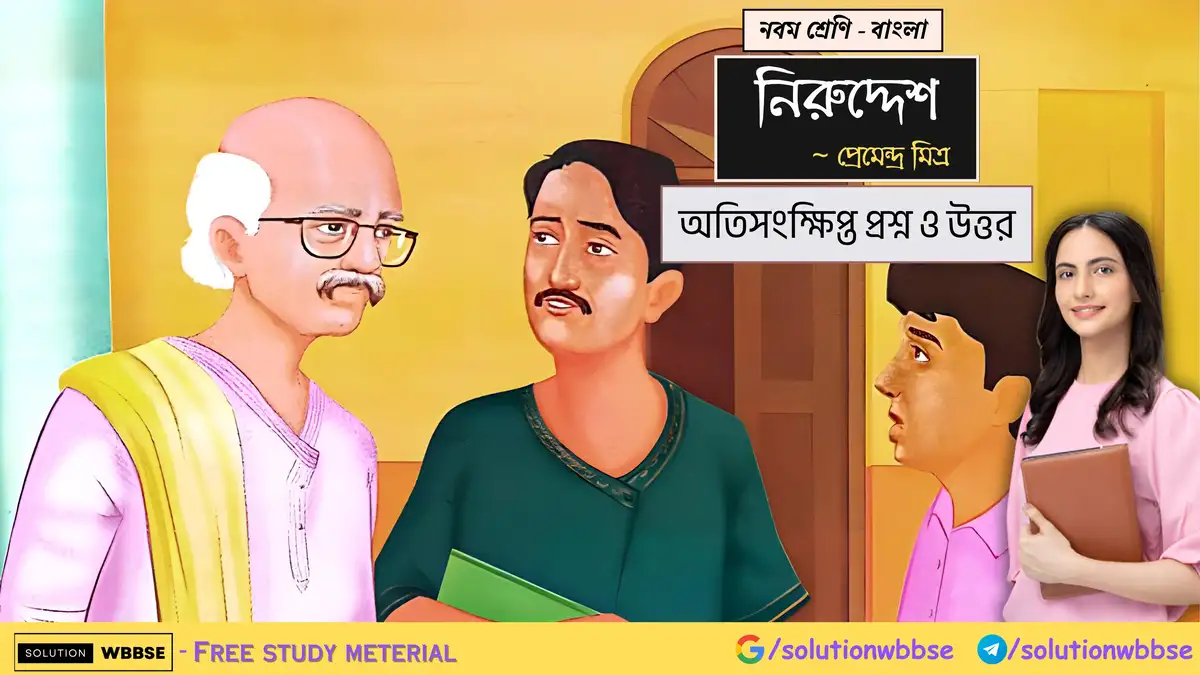

মন্তব্য করুন