আজকে আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক বাংলার সপ্তম পাঠের তৃতীয় বিভাগ, ‘নদীর বিদ্রোহ’ নিয়ে কিছু বিশ্লেষণধর্মী ও রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো প্রায়শই মাধ্যমিক পরীক্ষায় দেখা যায়। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।
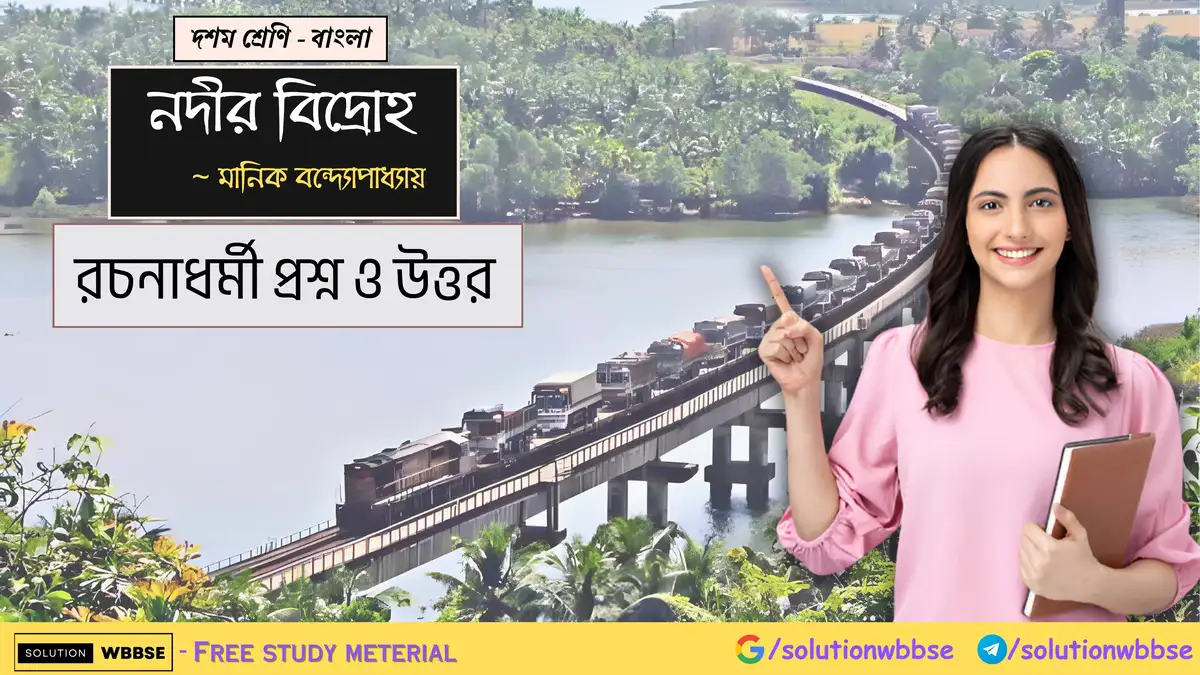
“ত্রিশ বছর বয়সে নদীর জন্য নদেরচাঁদের এত বেশি মায়া একটু অস্বাভাবিক।” — নদেরচাঁদের নদীর প্রতি এত ভালোবাসার কারণ কী? সেই ভালোবাসার পরিচয় দাও।
নদীর প্রতি ভালোবাসার কারণ – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদেরচাঁদের নদীর প্রতি ছিল অস্বাভাবিক মায়া। তাই স্টেশনমাস্টারের গুরুদায়িত্ব সামলেও নদীকে দেখার জন্য সে আকুল হয়ে ওঠে। প্রবল বর্ষণে পাঁচ দিন নদীকে না দেখতে পাওয়ায়, বৃষ্টি থামলেই সে নদীকে দেখার জন্য ছুটে যায়। নদীর জন্য এমনভাবে পাগল হওয়া তার মানায় না, কিন্তু বুঝেও সে নিজেকে বোঝাতে পারে না। বরং নিজের এই পাগলামিতে আনন্দ উপভোগ করে। এর একটা কারণও সে খুঁজে নেয়। নদীর ধারেই তার জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠা — তাই চিরদিনই নদীর প্রতি তার এত ভালোবাসা।
ভালোবাসার পরিচয় –
- নদীর জন্য কান্না – প্রথম জীবনে দেশের ক্ষীণস্রোতা নদীটি অনাবৃষ্টির কারণে শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে নদেরচাঁদ কেঁদে ফেলেছিল।
- নদীর প্রতি আকুলতা – একইভাবে কর্মক্ষেত্রে এসেও পাঁচ দিন প্রবল বৃষ্টির কারণে নদীকে দেখতে না পাওয়ায় আকুল হয়ে ওঠে সে। বৃষ্টি একটু থামতেই তার মনে হয় – “ব্রিজের একপাশে আজ চুপচাপ বসিয়া কিছুক্ষণ নদীকে না দেখিলে সে বাঁচিবে না।” বর্ষায় উন্মত্ত নদীর সঙ্গে সে খেলা করে। স্ত্রীকে লেখা চিঠিও সে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়।
- নদীকে সমর্থন – আবার ব্রিজ দিয়ে নদীকে বেঁধে রাখার চেষ্টাও মানতে পারে না সে। নদীর বিদ্রোহী চরিত্রকে সে মনে মনে সমর্থন করে। এভাবেই নদীর প্রতি তার ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে।
“নিজের এই পাগলামিতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।” – কার, কোন্ পাগলামির কথা এখানে বলা হয়েছে? কীভাবে সে পাগলামিতে আনন্দ উপভোগ করে লেখো।
অথবা, “নিজের এই পাগলামিতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।” – কার ‘পাগলামি’-র কথা বলা হয়েছে? গল্প অনুসরণে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পাগলামির পরিচয় দাও।
উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ও তার পাগলামি – কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে তিরিশ বছর বয়সেও নদীর জন্য নদেরচাঁদের অতিরিক্ত মায়াকে একটু অস্বাভাবিক বলেই মনে হত। নদেরচাঁদের নদীর প্রতি এই ভালোবাসাকেই ‘পাগলামি’ বলা হয়েছে।
পাগলামিতে আনন্দ উপভোগ –
- আপন হয়ে ওঠা – নদীর ধারেই নদেরচাঁদের দেশ। নদীই তার আবাল্য বন্ধু। স্টেশনমাস্টারের কাজে এসে আর-এক নদীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। এই নদীটিও তার আপন হয়ে ওঠে।
- চিন্তায় মশগুল থাকা – কাজের ব্যস্ততার মাঝেও সে এই নদীর চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকত। এই নদীটি বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে সে বিস্মিত হয়ে নদীর জলস্রোতের চঞ্চলতা দেখত। নদেরচাঁদের মনে হত | নদীর এই চঞ্চলতা যেন তার আনন্দেরই প্রকাশ।
- একাত্ম হয়ে ওঠা – দিবারাত্রি প্যাসেঞ্জার ও মালগাড়ির তীব্রবেগে ছোটাছুটি নিয়ন্ত্রণ করা যার কাজ, তার নদীর জন্য এমন পাগল হওয়া সাজে কি না সে প্রশ্ন নদেরচাঁদের মধ্যে প্রায়ই জাগত। নদেরচাঁদ নিজেও এ কথা বোঝে, কিন্তু মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না। আসলে মানসিকভাবে সে নদীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।
- সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে থাকা – নদীর সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে পেরে সে নিজেকে ধন্য মনে করত।
- শেষের কথা – নদীপ্রীতির এই পাগলামিতে নদেরচাঁদ উপভোগ করত এক অদ্ভুত আনন্দ, যা ছিল একান্তই তার নিজস্ব।
“নদীকে এভাবে ভালোবাসিবার একটি কৈফিয়ত নদেরচাঁদ দিতে পারে।” – কী কৈফিয়ত দিতে পারে? এই ভালোবাসার কীরূপ পরিণতি হয় লেখো।
কৈফিয়তের বিষয় – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদীকে ভালোবাসার একটা কৈফিয়ত নদেরচাঁদ ভেবেছিল। নদীর ধারে তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। তাই নদীর প্রতি তার এই ভালোবাসা চিরদিনের। অনাবৃষ্টির কারণে দেশের ক্ষীণস্রোতা নদীটি শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে নদেরচাঁদ কেঁদেছিল। আবার কর্মক্ষেত্রেও নদীর সঙ্গে তার সখ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।
ভালোবাসার পরিণতি – নদীর প্রতি এই ভালোবাসার চূড়ান্ত মূল্য নদেরচাঁদকে দিতে হয়েছিল। বর্ষায় নদীর যে উন্মত্ত রূপ তার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল, তাকেই নদীর বিদ্রোহ বলে মনে হয়েছে নদেরচাঁদের। মানুষ ব্রিজ তৈরি করে নদীকে বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু নিজের স্বাভাবিক গতির এই রোধ নদী মানতে পারেনি। ব্রিজ ভেঙে ভাসিয়ে দিয়ে সে নিজের চলার পথ করে নিতে চেয়েছে। নদেরচাঁদ জানে যে ব্রিজ ভাঙলেও মানুষ আবার তা গড়ে নেবে। তার মনে হয়, এই ব্রিজের কোনো প্রয়োজন ছিল না। নদেরচাঁদ যখন এসব চিন্তায় ডুবেছিল ঠিক তখনই একটি চলন্ত ট্রেন তাকে পিষে দিয়ে চলে যায়। যন্ত্রসভ্যতার প্রয়োজনীয়তাকে প্রশ্ন করার স্পর্ধা দেখিয়েছিল সে। প্রকৃতির প্রতি তার ভালোবাসার চূড়ান্ত মূল্য এভাবেই জীবন দিয়ে মিটিয়ে দিতে হয় নদেরচাঁদকে।
“মানুষ কি তাকে রেহাই দিবে?” – নদেরচাঁদের এ কথা মনে হওয়ার কারণ বর্ণনা করো।
- নদীর প্রতি ভালোবাসা – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে এক সাধারণ স্টেশনমাস্টার নদেরচাঁদ নদীকে ভালোবেসেছিল পরমাত্মীয়, বন্ধুর মতো। নদীর প্রতি সে এক অসম্ভব টান অনুভব করত। তার জীবনের যেন অর্ধেকটা জুড়েই ছিল নদী। যেখানেই সে থেকেছে, সেখানকার নদীকেই সে ভালোবেসেছে।
- নদীর বিদ্রোহের উপলব্ধি – স্টেশনমাস্টারের কাজ নিয়ে এসে সে পরিচিত হয় প্রশস্ত জলপূর্ণ অথচ বন্দি এক নদীর সঙ্গে। ব্রিজ, বাঁধ দিয়ে ওই নদীকে বন্দি করে রেখেছে মানুষ। একবার প্রবল বৃষ্টির পর নদীর উচ্ছ্বসিত ফেনিল জলরাশি দেখে নদেরচাঁদের মনে হয়েছিল নদী যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।
- নদীর প্রতিবাদী সত্তার অনুভব – ব্রিজ আর বাঁধকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে নদী যেন ফিরে পেতে চাইছে তার স্বাভাবিক গতি। নদী যেন যন্ত্রসভ্যতার বিরোধিতা করার মাধ্যমে পরোক্ষে প্রকৃতির লাঞ্ছনার প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
- মানুষের স্বার্থপরতা – এইরকম পরিস্থিতিতে নদেরচাঁদের মনে হয়েছে, আজ যদি নদী ব্রিজ, বাঁধ ভেঙে নিজের বন্দিদশা কাটিয়েও ওঠে, তবুও মানুষ তাকে রেহাই দেবে না। নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে আবারও নদীকে বন্দি করবে তারা। আবার মানুষ গড়ে তুলবে ব্রিজ, গড়ে তুলবে বাঁধ। প্রশস্ত নদীকে পরিণত করবে এক ক্ষীণস্রোতা নদীতে।
“জলপ্রবাহকে আজ তাহার জীবন্ত মনে হইতেছিল।” – কার জলপ্রবাহকে জীবন্ত মনে হল? জীবন্ত মনে হওয়ার কারণ কী ছিল তা বর্ণনা করো।
উদ্দিষ্ট ব্যক্তি – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘নদীর বিদ্রোহ’ ছোটোগল্পে নদেরচাঁদের নদীকে জীবন্ত বলে মনে হয়েছিল।
জীবন্ত মনে হওয়ার কারণ –
- নদীর প্রতি টান অনুভব – ইতিপূর্বে তার দেশের নদীটির সঙ্গে নদেরচাঁদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠলেও সেই নদীটি ছিল ক্ষীণ, রুগ্ণ। স্টেশনমাস্টারি করতে এসে নদেরচাঁদ এক নতুন নদীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। সে নদী ছিল প্রশস্ত, বর্ষায় তার জলপ্রবাহ হয়ে উঠত উদ্দাম, উন্মত্ত। আর এক অদ্ভুত ভালোবাসার টানে নদেরচাঁদ প্রতিদিন ওই নদীকে দেখতে ছুটে যেত। ব্রিজের ধারে বসে সে নদীকে দেখত।
- নদীর উন্মত্ততা – এইরকমই এক বর্ষার দিনে নদীর উদ্দাম জলস্রোত ব্রিজের ধারকস্তম্ভে বাধা পেয়ে ফেনিল আবর্ত রচনা করছিল। নদীর সেই আবর্তে নদেরচাঁদ খেলার ছলে তার স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি ছুঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল চিঠিটা পেয়েই নদী যেন সেটা তার নিজের স্রোতের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। নদেরচাঁদের মনে হল নদীও যেন তার সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়েছে। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে নদীর জলপ্রবাহ। নদীর এই খেলায় যোগ দেওয়া এবং জলপ্রবাহের এমন উন্মত্ততা – এই সব কিছু দেখেই নদেরচাঁদের নদীকে জীবন্ত বলে মনে হয়েছিল।
“আজ তার মনে হইল কী প্রয়োজন ছিল ব্রিজের?” – নদেরচাঁদের কেন ব্রিজটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল?
- নদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব – নদেরচাঁদ ছেলেবেলা থেকেই নদীকে ভালোবাসত। নদী তার জীবনের সঙ্গে যেন জড়িয়ে গিয়েছিল। কর্মসূত্রে যে নদীটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, সেই নদীটি ছিল প্রশস্ত; তার জলস্রোত ছিল উদ্দাম। এই নদীর সঙ্গে এক অদ্ভুত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নদেরচাঁদের। প্রতিদিন নদেরচাঁদ এক অদ্ভুত টানে ছুটে যেত এই নদীর কাছে।
- নদীর ভয়ংকর রূপ – একবার বর্ষায় নদীকে পাঁচ দিন দেখতে না পেয়ে তার মন ছটফট করেছিল। ছেলেমানুষের মতো আবার নদীকে দেখার জন্য সে উতলা হয়ে উঠেছিল। পাঁচ দিন প্রবল বর্ষণের পর সে আবার নদীকে দেখার সুযোগ পেল। নদীর কাছে গিয়ে সে দেখল, নদী এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।
- নদীর উন্মত্ততা – নদেরচাঁদের মনে হল, রোষে, ক্ষোভে নদী যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে যেন ব্রিজটাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলবে। কারণ, এই ব্রিজের জন্যই তার ওই স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ রয়েছে।
- বন্দিদশা থেকে মুক্তি – নদীটিকে দেখে তার মনে হল, সে যেন বন্দিদশা থেকে মুক্ত হতে চাইছে। তাই নতুন রং করা যে ব্রিজের জন্য একসময় নদেরচাঁদ গর্বিত ছিল, সেই ব্রিজটাকেই এ সময়ে তার অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হল।
“তারপর সে অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল।” – ‘সে’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তার মানসিক অবস্থাটি পাঠ্যাংশ অবলম্বনে আলোচনা করো।
‘সে’-র পরিচয় – ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পের উল্লেখিত অংশে ‘সে’ বলতে নদেরচাঁদের কথা বলা হয়েছে।
মানসিক অবস্থার বর্ণনা –
- খেলাসুলভ আচরণ – পাঁচ দিন নদীকে না দেখতে পাওয়ার পরে নদেরচাঁদ যেদিন নদীর কাছে এল, নদীর উন্মত্ত চেহারা দেখে প্রথমে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু তারপরে নদীর উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের সঙ্গে সে খেলায় মেতে ওঠে। এরই মধ্যে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি শুরু হলেও সে নদীর ধার থেকে ওঠে না।
- আচ্ছন্নতা – নদীর ভিতর থেকে আসা একটা অপরিচিত শব্দ বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিলে তাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। সেই ‘ভীষণ মধুর’ শব্দ তার সর্বাঙ্গকে অবশ ও অবসন্ন করে দেয়। ক্রমে দিনের আলো মিলিয়ে গিয়ে চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে। বৃষ্টি কিছুক্ষণ থেমে আবার প্রবলবেগে শুরু হয়।
- দিশেহারা হয়ে ওঠা – ব্রিজের উপর দিয়ে চলে যাওয়া একটা ট্রেনের শব্দ নদেরচাঁদকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনে। হঠাৎ কোনো আঘাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো একটা মানসিক বেদনা কিছুক্ষণের জন্য নদেরচাঁদকে দিশেহারা করে তোলে।
- ভীত ও অবিশ্বাসী – অতিকষ্টে নদেরচাঁদ উঠে দাঁড়ায় এবং তার মনে ভয়ের জন্ম হয়। তার মনে হয় যে, ক্ষোভে উন্মত্ত এই জলরাশির এত কাছে তার এমনভাবে বসে থাকা উচিত হয়নি। যে নদী এমনভাবে খেপে যেতে পারে নদেরচাঁদ তাকে যেন আর বিশ্বাস করতে পারে না।
“নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে।” — নদী কখন বিদ্রোহ করেছিল? এই বিদ্রোহের কোন্ কারণ নদেরচাঁদের বোধগম্য হয়েছিল লেখো।
নদীর বিদ্রোহের সময় –
- উন্মত্ত রূপ – ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে পাঁচ দিনের অবিরাম বৃষ্টির পরে নদীকে দেখার উৎসাহে নদেরচাঁদ নদীর কাছে যায়। ব্রিজের কাছাকাছি এসে যে নদীকে সে দেখে, তাতে সে পরিপূর্ণতার বদলে উন্মত্ততা দেখতে পায়। চেনা নদীর এই মূর্তি তার ভয়ংকর লাগে।
- মুশলধারায় বৃষ্টি – ব্রিজের মাঝামাঝি ধারকস্তম্ভের শেষভাগে বসে অন্যদিনের মতোই নদেরচাঁদ নদীকে দেখে, তার সঙ্গে খেলা করতে থাকে। এইসময়ই মুশলধারে বৃষ্টি নামে। মনে হয়, তিন ঘণ্টার বিশ্রামে মেঘে যেন নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে। নদেরচাঁদের মনের ছেলেবেলার আমোদ ক্রমশ মিলিয়ে গিয়ে তার সর্বাঙ্গ অবশ, অবসন্ন হয়ে ওঠে।
- চেহারার পরিবর্তন – ক্রমে দিনের আলো মিলিয়ে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে। বৃষ্টি কিছুক্ষণ থেমে আবার প্রবলভাবে শুরু হয়। নদীর সেই ক্ষোভে উন্মত্ত চেহারা দেখে নদেরচাঁদ ভয় পেয়ে যায়। এই সময়ে নদীর ওই ভয়ংকর রূপকেই নদেরচাঁদের ‘বিদ্রোহ’ বলে মনে হয়।
নদীর বিদ্রোহের কারণ –
- মানুষের বাধা সৃষ্টি – নদেরচাঁদ নদীর এই বিদ্রোহের কারণ বোঝার চেষ্টা করে। তার মনে হয় মানুষ নদীকে বাঁধার যে চেষ্টা করেছে তার তৈরি করা ব্রিজের সাহায্যে। নদী সেটাকে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। দু-পাশে মানুষের হাতে-গড়া বাঁধকে চুরমার করে সে স্বাভাবিক গতিতে বয়ে যেতে চায়।
- স্বাভাবিক মুক্তগতি – নিজের স্বাভাবিক মুক্ত গতি ফিরে পাওয়ার জন্যই যেন নদীর এই বিদ্রোহ।
‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্প অবলম্বনে নদীর প্রতি নদেরচাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিচয় দাও।
অথবা, ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদেরচাঁদের নদীর প্রতি যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব চিত্রিত হয়েছে তা আলোচনা করো।
- জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে স্টেশনমাস্টার নদেরচাঁদের জন্ম থেকেই যেন নদী তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। তাই বর্ষায় পাঁচ দিন নদীকে দেখতে না পেলে তার মন ছটফট করত, ছেলেমানুষের মতো উৎসুক হয়ে উঠত সে নদীর দেখা পাওয়ার জন্য।
- জীবনের অতিবাহক ও পরমাত্মীয় – নদীর ধারেই তার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন কেটেছে। স্টেশনমাস্টারের কাজ নিয়ে এসে তার পরিচয় হয় এক প্রশস্ত ও জলপূর্ণ এক নদীর সঙ্গে। নদীটিকে সে যেমন ভালোবেসেছিল তেমনই সে তার দেশের ক্ষীণস্রোতা নির্জীব নদীটিকেও নিজের পরমাত্মীয়ারূপে ভালো বেসেছিল। অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে যাওয়া নদীর জন্য ছেলেবেলায় সে এমনভাবে কেঁদেছিল যেন কঠিন রোগে তার কোনো পরমাত্মীয়া মৃত্যুমুখে পড়েছে।
- খেলায় মেতে ওঠা – বর্ষার জলে তার কর্মস্থলের কাছে অবস্থিত পরিপুষ্ট নদীটির উচ্ছল আনন্দের ছোঁয়া নদেরচাঁদের মনেও লেগেছিল। সেই নদীর পঙ্কিল জলস্রোতের আবর্তে সে তার স্ত্রীকে লেখা চিঠি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে এক অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠেছিল, তার মনে হয়েছিল নদী যেন সেই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্রোতের গভীরে তা লুকিয়ে ফেলছে।
- বন্দিদশা থেকে মুক্তি কামনা – বাঁধ আর ব্রিজের মধ্যে বন্দি থাকা নদীর মুক্তিলাভের কামনা করেছিল নদেরচাঁদ। নদীর বন্দিদশা নদেরচাঁদকেও নিদারুণ কষ্ট দিয়েছিল।
- উপসংহার – এইভাবে নদী কখনও নদেরচাঁদের পরমাত্মীয়, কখনও-বা বন্ধু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নদীর কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় অজান্তেই চলন্ত ট্রেন পিষে দিয়েছিল নদেরচাঁদকে। নদেরচাঁদ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নদীর প্রতি তার ভালোবাসার দাম চুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।
নদেরচাঁদ নদীকে ভালোবাসার প্রতিদান কীভাবে পেয়েছিল গল্পের প্রেক্ষিতে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।
- প্রাককথন – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘নদীর বিদ্রোহ’ ছোটোগল্পের প্রধান চরিত্র নদেরচাঁদের জীবনে ছেলেবেলা থেকেই নদী গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।
- নদীর প্রতি টান অনুভব – স্টেশনমাস্টার হিসেবে কর্মসূত্রে সে যেখানে এসেছে, সেখানেও ব্রিজ ও বাঁধ দিয়ে ঘেরা একটি নদী রয়েছে, এবং সেই নদীর প্রতি সে এক টান অনুভব করেছে। ব্রিজের মাঝামাঝি ইট, সুরকি, ও সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা ধারকস্তম্ভের শেষপ্রান্তে বসে প্রতিদিন সে নদীকে দেখেছে।
- নদীর বিদ্রোহ অনুভব – বর্ষার কারণে ওই নদীকে পাঁচ দিন দেখতে না পেয়ে সে ছেলেমানুষের মতো ছটফট করেছে।
- নদীর মুক্তি কামনা – বাঁধে ঘেরা নদীর জলোচ্ছ্বাস দেখে তার মনে হয়েছে নদী যেন বিদ্রোহ করছে। নদীর যন্ত্রণা সে-ও যেন মন থেকে অনুভব করেছে। তাই সে নদীর মুক্তি কামনা করেছে। যে রং করা ব্রিজের জন্য সে একদিন গর্ব অনুভব করেছে পরে নদীর বন্দিদশার কারণে সেই ব্রিজকেই তার অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।
- নদীকে ভালোবাসার প্রতিদান – এসব ভাবতে ভাবতে নদেরচাঁদ যখন রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেছে, তখনই একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন তাকে পিষে দিয়ে চলে গেছে। যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে গিয়ে নদীরই পক্ষ নিয়েছিল নদেরচাঁদ। তাই গল্পের শেষে নদীকে ভালোবাসার ফলস্বরূপ তার জীবনে নেমে এসেছে করুণ পরিণতি। নদীকে ভালোবাসার প্রতিদান সে এইভাবেই পেয়েছে।
নদীর বিদ্রোহ গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
যে-কোনো সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণের মাধ্যমেই কোনো সাহিত্যের বিষয়বস্তু বা ভাবটি পাঠকের কাছে ফুটে ওঠে। সাধারণত সাহিত্যের নামকরণ হয় তার বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক, চরিত্রধর্মী বা ভাব অনুযায়ী। আবার কখনও তা হয় ব্যঞ্জনাধর্মী।
‘নদীর বিদ্রোহ’ নামকরণটি ব্যঞ্জনাধর্মী। এখানে মানুষ এবং নদীর মধ্যেকার এক অদ্ভুত সখ্যের বর্ণনা পাই আমরা। গল্পে দুটি নদীর কথা জানা যায়। এদের একটি হল নদেরচাঁদের দেশের ক্ষীণস্রোতা নদী আর অন্যটি হল সেই নদী যার সঙ্গে স্টেশনমাস্টারি করতে এসে নদেরচাঁদের আলাপ হয়। ওই নদীটি ছিল বন্দি। বাঁধ দিয়ে মানুষ তাকে বন্দি করেছিল। ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদী এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে ধরা দিয়েছে। বর্ষার জলে এই নদীর পঙ্কিল জলস্রোতে দেখা দিয়েছে উন্মাদনা, চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার স্রোত।
মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য বাঁধ দিয়ে এই নদীকে বন্দি করেছে, তৈরি করেছে ব্রিজ। সব কিছুই মানুষ করেছে যন্ত্রসভ্যতার সাহায্যে, নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে। নিজেদের প্রয়োজনে তারা নদীর স্বাভাবিক গতিকে আটকে রেখেছে। আর সেই কারণেই এই গল্পে নদী যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে। যারা তাকে বন্দি করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সে এই ব্রিজ আর বাঁধ ভেঙে ফেলে সে যেন তার স্বাভাবিক গতি ফিরে পেতে চেয়েছে। আর তাই সে তার উন্মত্ত জলস্রোতের মধ্য দিয়ে সেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তখন ‘স্বাঁধ ভেঙে দাও’ মন্ত্রে যে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে নদীটি। তাই গল্পের প্রেক্ষিতে বিচার করলে ‘নদীর বিদ্রোহ’ নামকরণটি যথার্থ ও সার্থক হয়েছে বলা যায়।
নদীর বিদ্রোহ গল্পে নদেরচাঁদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক পাঠকের উদ্দেশে যে বার্তা দিতে চেয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।
- নদীপ্রীতি – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে জন্মভূমির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটিকে দিয়েই নদেরচাঁদের নদীপ্রীতির সূচনা। আর কর্মস্থলের নদীটি তার সেই আবেগের পরবর্তী পর্যায়। রবীন্দ্রনাথের বলাই যেমন গাছের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেই মনেপ্রাণে একটা গাছ হয়ে উঠেছিল, এই গল্পে নদেরচাঁদও নদীর কথা ভাবতে ভাবতে যেন নিজে নদী হয়ে গেছিল।
- নদী নিয়ে ভাবনা – নদীর শুষ্কতা, জলোচ্ছ্বাস যেন নদেরচাঁদেরই জীবনের জোয়ারভাটা। তার কাছে নদীকে বাঁধ দেওয়ার অর্থ জীবনের গতি রুদ্ধ করা। নদীর ওপর নির্মিত সেতু দেখতে সুন্দর; কিন্তু তাতে নদীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। নদেরচাঁদের কাছে নদীর ব্রিজ বা সেতু আগ্রাসী মানুষের ঔদ্ধত্যের প্রতীক। বর্ষায় নদীর জলোচ্ছ্বাস যেন সেই যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধেই নদীর বিদ্রোহের প্রকাশ। নদেরচাঁদ সেটাই অনুভব করে। ফলস্বরূপ নদীর ওপরের ব্রিজটির তখন নদেরচাঁদের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।
- যন্ত্রসভ্যতার প্রতিশোধ – গল্পের উপসংহারে এসব কথা ভাবতে ভাবতেই নদেরচাঁদ রেললাইনের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়। নদেরচাঁদের মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে যন্ত্রসভ্যতা যেন প্রকৃতির প্রতি তার ভালোবাসা এবং পক্ষপাতের মধুর প্রতিশোধ নেয়।
‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদীর সঙ্গে নদেরচাঁদের যে সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে, তার রূপটি বর্ণনা করো।
- কথামুখ – ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পে নদীর সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্পর্কের রূপটি গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে।
- সমর্পিত ভালোবাসা – নদেরচাঁদ তার স্ত্রীকে একটি বেদনাময় চিঠি লিখেছিল, এ কথা যেমন সত্য, তেমনভাবেই আরও বড়ো সত্য হল, শুধু নদীর সঙ্গে খেলার তুচ্ছ ছেলেমানুষি নেশায় পড়ে সে সেই চিঠিটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এভাবে স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসাকে সে যেন নদীর ভালোবাসার মধ্যে সমর্পণ করেছিল।
- হৃদয়যন্ত্রণার প্রকাশ – প্রিয় নদীটিকে একবার চোখের দেখা না দেখলে সে শান্তি পেত না। নদীর কুলুকুলু শব্দ আর বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ সংগীতের ঐকতান হয়ে নদেরচাঁদের দেহ-মনকে অবসন্ন করে, বিভোর করে তুলত। নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি করে নদীর স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে রাখার প্রতিবাদে নদেরচাঁদের হৃদয়ও যন্ত্রণায় ফেটে পড়তে চাইত।
- ভালোবাসার প্রতিশোধ – কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, তাকেও মরতে হয় যন্ত্রসভ্যতার কাছেই। চলন্ত রেলগাড়ি যন্ত্রদানবের মতোই মুহূর্তে নদেরচাঁদকে পিষে দিয়ে চলে যায় — প্রকৃতির প্রতি তার ভালোবাসার চরম প্রতিশোধ যেন নেয় যন্ত্রসভ্যতা।
‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পের নদেরচাঁদ চরিত্রটি আলোচনা করো।
- কথামুখ – নদীর বিদ্রোহ গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র নদেরচাঁদ। তার চরিত্রকে কেন্দ্র করেই কাহিনির বিকাশ ঘটেছে। সেখান থেকেই নদেরচাঁদের বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
- পরিচয় – নদেরচাঁদের বয়স তিরিশ বছর এবং সে স্টেশন মাস্টারের পদে চাকরি করে। দিনরাত মেল, প্যাসেঞ্জার আর মালগাড়ির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব তার।
- প্রকৃতি প্রেমিক – পেশাগত দায়িত্বের বাইরে নদেরচাঁদ আদ্যন্ত নন্দীপ্রেমিক। নদীর প্রতি তার এই ভালোবাসার সূচনা শৈশব-কৈশোরে দেশের ক্ষীণস্রোতা নদীটিকে কেন্দ্র করে। আর পরবর্তীতে তার বিকাশ কার্যক্ষেত্রের বড়ো নদীটিকে নিয়ে।
- রোমান্টিকতা – নদীর প্রতি নদেরচাঁদের ভালোবাসা প্রায় অস্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, এবং তার প্রকাশ দেখা যায় নদেরচাঁদের ছোটোবেলা থেকেই। দেশের নদী শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে নদেরচাঁদ প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। “দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতে পরমাত্মীয়া মরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিলে মানুষ যেমন কাঁদে।” পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্রে থাকাকালীন প্রবল বৃষ্টির কারণে পাঁচদিন নদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে সে পাগলের মতো হয়ে যায়। বৃষ্টি থামলেই সে নদীর কাছে যায়। এমনকি স্ত্রী-কে লেখা চিঠির পৃষ্ঠা জলে ভাসিয়ে সে নদীর সঙ্গে খেলা করে।
- নিজস্বতা – নদীকে নিয়ে নদেরচাঁদের ভাবনা একেবারেই তার নিজস্ব। বর্ষায় উন্মত্ত নদীকে দেখে তার মনে হয় মানুষের তৈরি বাঁধকে চূর্ণ করে সে নিজের বয়ে যাওয়ার পথ করে নিতে চায়। মানুষের সঙ্গে সভ্যতার এই লড়াই-এ নদীর জয়লাভ নিয়ে চিন্তিত হয় নদেরচাঁদ। ব্রিজের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তার মনে প্রশ্ন জাগে।
- ভাবুক – নদীর কথা ভাবতে ভাবতে ট্রেনের চাকায় পিষে যায় নদেরচাঁদ। প্রকৃতির পক্ষ নেওয়ায় যন্ত্রসভ্যতা যেন তার প্রতিশোধ নেয়। যেন বুঝিয়ে দেয় যে, নদেরচাঁদের মত মানুষরা এই সভ্যতায় টিকে থাকতে পারে না।
ছোটোগল্প হিসেবে ‘নদীর বিদ্রোহ’ কতদূর সার্থক বিচার করো।
ছোটোগল্পের মূলকথা – ছোটোগল্পে লুকিয়ে থাকে বৃহত্তর জীবনের ব্যঞ্জনা। ‘ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা/ছোটো ছোটো দুঃখকথা’ হলেও ছোটোগল্প ছোটো পরিসরে সমগ্র জীবনের ঘটনাকে তুলে ধরে। এর গতি হয় সোজা ও একমুখী। গল্পের শেষে মনে হয় – “শেষ হয়েও হইল না শেষ।” এই সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্যের আলোয় ‘নদীর বিদ্রোহ’ গল্পটি বিচার করা যেতে পারে।
ছোটোগল্প হিসেবে ‘নদীর বিদ্রোহ’ -এর সার্থকতা – নদেরচাঁদের নদীপ্রীতিই গল্পের মূল বিষয়। আর গল্পের ব্যঞ্জনায় উঠে এসেছে নদীর বিদ্রোহ। নদীকে মানুষ বাঁধ দিয়ে বন্দি করে। নদীর ওপর তৈরি করে কংক্রিটের ব্রিজ। যন্ত্রসভ্যতার তার প্রবল পেষণে পিষ্ট করে, রুদ্ধ করে, নদীর স্বাভাবিক গতিকে। নদেরচাঁদ মনে করেছে, এটাই নদীর শিকল। বর্ষায় নদী প্রাণ ফিরে পায়। তাই নদীর প্রবল স্রোতই তার বিদ্রোহের প্রকাশ। তার জলের ঘূর্ণিপাকই তার বন্দিদশার যন্ত্রণার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। নদেরচাঁদের মনে হয়েছে, পরিপূর্ণ নদী প্রাণশক্তির প্রতীক। মনে করলে নদী এই সব কিছু চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে, ভেঙে ফেলতে পারে কংক্রিটের ব্রিজ। নদীর দুরন্ত প্রবাহের মধ্যে নদেরচাঁদ নদীর বন্দিদশা থেকে মুক্তির চেষ্টা দেখতে পেয়েছে। একটিই মাত্র চরিত্রের ভাব ও ভাবনাকে কেন্দ্র করে পুরো গল্পটি আবর্তিত হয়েছে। গল্পের শেষে নদেরচাঁদ চরিত্রটির করুণ পরিণতি পাঠককে অতৃপ্তির বেদনায় অভিভূত করে। এভাবেই ছোটোগল্প হিসেবে ‘নদীর বিদ্রোহ’ স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী।
আজকের আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক বাংলার সপ্তম পাঠের তৃতীয় বিভাগ, ‘নদীর বিদ্রোহ’ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী ও রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকে, তাহলে টেলিগ্রামে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। এছাড়াও, এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জন বা যার প্রয়োজন হতে পারে তার সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।


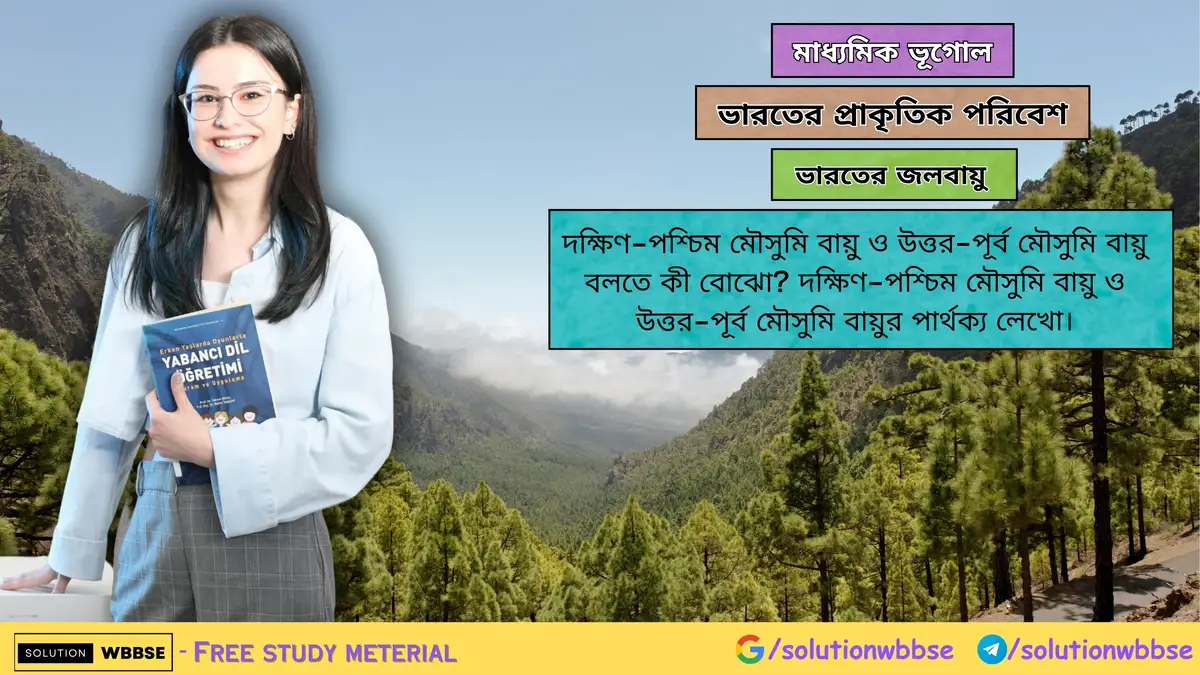
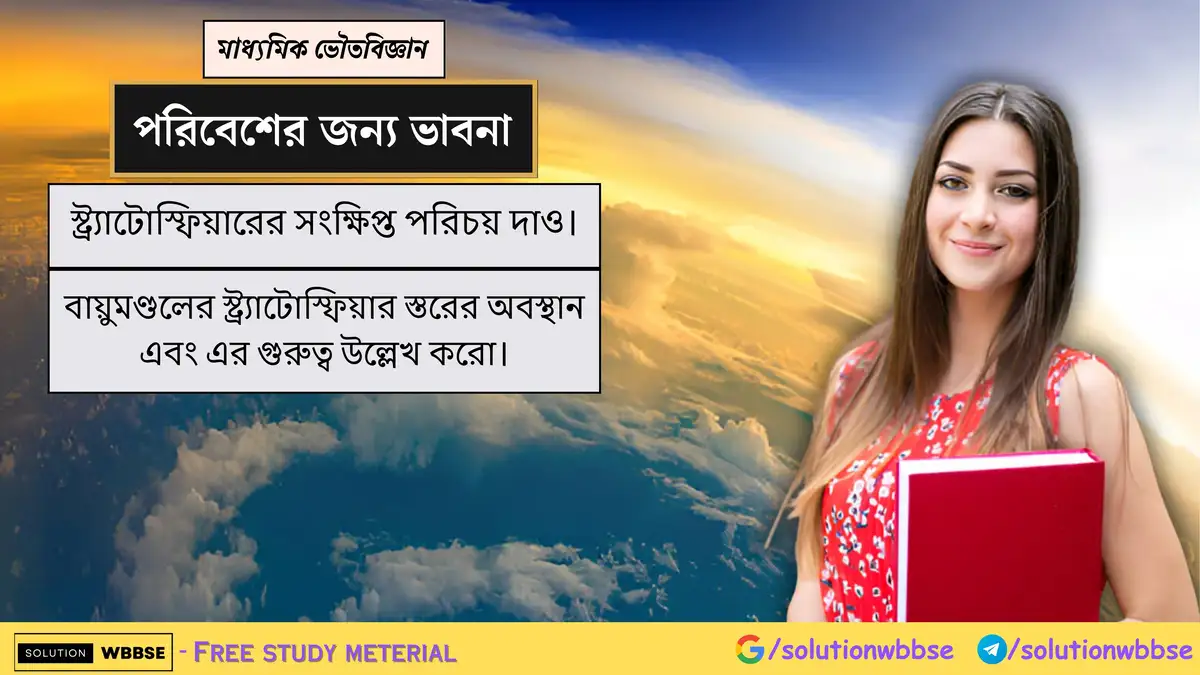
মন্তব্য করুন