আজকে আমরা আমাদের আর্টিকেলে মাধ্যমিক বাংলার ষষ্ঠ পাঠের প্রথম বিভাগ, ‘সিন্ধুতীরে’ থেকে কিছু বিশ্লেষণধর্মী ও রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পূর্বের পরীক্ষায় এগুলি প্রায়শই দেখা গেছে। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হবে।
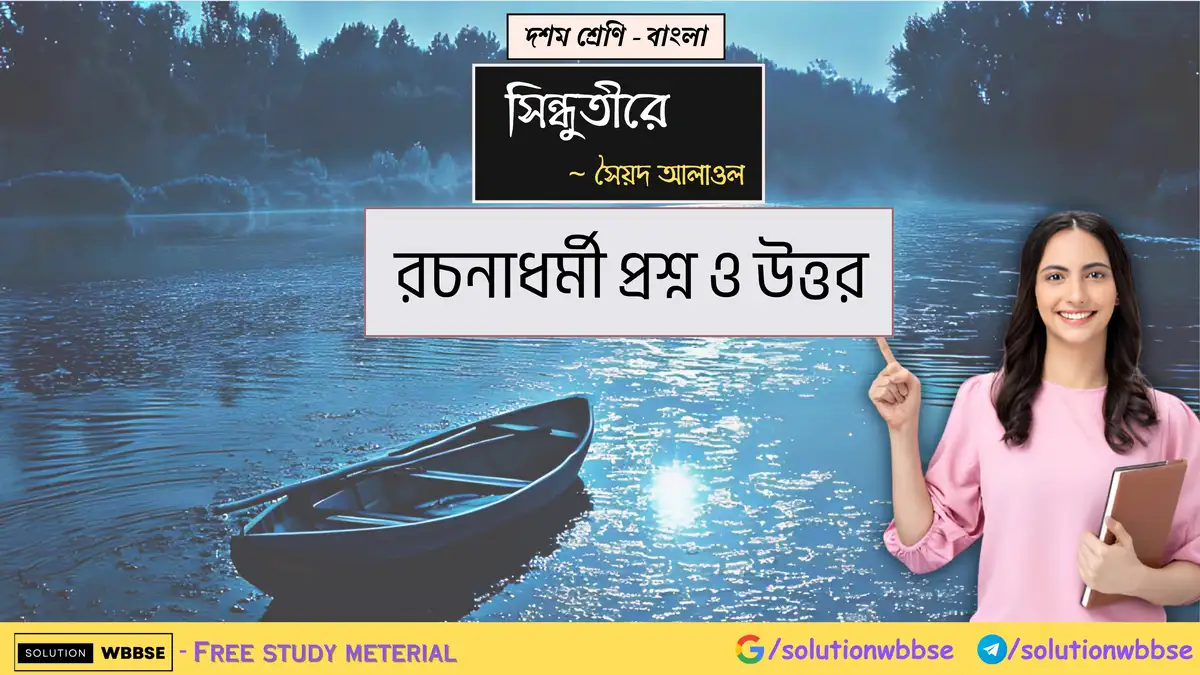
“সিন্ধুতীরে দেখি দিব্যস্থান।” – এই দিব্যস্থানের পরিচয় দাও। এখানে যে উদ্যানটির কথা আছে তা উল্লেখ করো।
দিব্যস্থানের পরিচিতি – সৈয়দ আলাওল অনূদিত পদ্মাবতী কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতাংশে যেখানে সমুদ্রের মধ্যে মান্দাসে করে পদ্মাবতী গিয়ে পৌঁছোন, সেখানেই ছিল এক দিব্য পুরী। কবির কথায় তা ছিল ‘মনোহর দেশ’। সেখানের মানুষের জীবনে কোনো দুঃখকষ্ট ছিল না। সমাজে নৈতিক আদর্শ ছিল অত্যন্ত উঁচুতে – “সত্য ধর্ম সদা সদাচার।” অর্থাৎ মানুষজন ছিল ধার্মিক এবং সৎ আচার-আচরণে অভ্যস্ত।
উদ্যানের পরিচয় – সমুদ্রতীরে অবস্থিত দিব্যস্থানটি সমুদ্রকন্যা পদ্মকে আকৃষ্ট করেছিল। এর উপরিভাগে ছিল প্রচুর ফলফুলে পরিপূর্ণ এক পর্বত। তার পাশে সুরম্য এক উদ্যান রচনা করেছিলেন সমুদ্রকন্যা পদ্মা। সেখানে নানা মনোহর ফুল ফুটে থাকত। তাদের সুগন্ধে চারপাশ ভরে থাকত। বিভিন্ন উপকারী বৃক্ষে নানা ফল ধরে থাকত। তারই মধ্যে ছিল এক অতি মনোরম প্রাসাদ – ‘বিচিত্র টঙ্গিা’। সেই প্রাসাদ স্বর্ণনির্মিত এবং নানান রত্নে সেটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। সেই রত্নখচিত প্রাসাদে আলো পড়লে নানান রঙের বর্ণালি বিচ্ছুরিত হত। তাই কবিতায় প্রাসাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ‘হেম রত্নে নানা রাঙ্গি’। অর্থাৎ, সোনা এবং মণিমাণিক্যের ছটায় চারদিক আলো করে বহু বর্ণে শোভা পাচ্ছিল এই অপূর্ব পুরী। এভাবেই মনোরম উদ্যানটি সম্পূর্ণতা পেয়েছিল।
“দেখিয়া রূপের কলা বিস্মিত হইল বালা/অনুমান করে নিজ চিতে।” – কে, কাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন? সেই কন্যা সেখানে কীভাবে এসেছিল? তাঁকে দেখে কী মনে হয়েছিল?
উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় – সৈয়দ আলাওল অনূদিত পদ্মাবতী কাব্যের ‘পদ্মা-সমুদ্রখণ্ড’ থেকে নেওয়া ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতায় সমুদ্রকন্যা পদ্মা অচেতন সিংহল-রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।
কন্যার আগমন – ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে রত্নসেনের কাছে দান ভিক্ষা করে প্রত্যাখ্যাত হয় সমুদ্র। তখন সমুদ্রের অভিশাপে রত্নসেনের নৌকা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে একটি মান্দাসে রত্নসেন ও সখীসহ পদ্মাবতী আশ্রয় নিলেও সেটিকে রক্ষা করা যায়নি। দু-টুকরো হয়ে পদ্মাবতী রত্নসেন থেকে আলাদা হয়ে পড়েন। প্রবল ঢেউ পদ্মাবতীদের মান্দাসটিকে তীরে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছোনোর আগেই ভয়ে সখীসহ পদ্মাবতী চেতনা হারান। যেখানে তাঁরা পৌঁছোন তা ছিল এক মনোরম পুরী।
কন্যাকে দেখে প্রতিক্রিয়া – পদ্মাবতীকে দেখে পদ্মার মনে হয়েছিল যে, ইন্দ্রের অভিশাপে স্বর্গের নর্তকী বিদ্যাধরী যেন স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। পদ্মাবতীর ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ এবং আলুথালু বেশ দেখে পদ্মা এ-ও অনুমান করেন যে, ওই কন্যার ওপর দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে গেছে। এলোমেলো চুল এবং বেশ-বাসের এই অবস্থা দেখে পদ্মার মনে হয় যে, হয়তো সমুদ্রযাত্রার পথে দুরন্ত ঝড়ে বাতাসে নৌকা ভেঙে তাঁরা এই বিপদে পড়েছিলেন। সমুদ্রের কষ্টেই তাঁর এই অজ্ঞান অবস্থা।
“অচৈতন্য পড়িছে ভূমিতে।” – কার কথা বলা হয়েছে? তাকে দেখে কার, কী মনে হয়েছিল? তিনি এই অবস্থায় কোন্ ভূমিকা নিয়েছিলেন?
উদ্দিষ্ট ব্যক্তি – সৈয়দ আলাওল অনূদিত পদ্মাবতী কাব্যের ‘পদ্মা-সমুদ্রখণ্ড’ থেকে সংকলিত ‘সিন্ধুতীরে’ নামক কাব্যাংশের উল্লিখিত অংশে পদ্মাবতীর কথা বলা হয়েছে।
উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনোভাব – পদ্মাবতীর বিস্ফারিত চোখ, এলোমেলো পোশাক এবং চুল দেখে সমুদ্রকন্যা পদ্মা অনুমান করেন যে, সমুদ্রের প্রবল বাতাসে নৌকা ভেঙে বোধহয় মেয়েটির এই কষ্ট। শুধু তা-ই নয়, গভীর সহানুভূতি দিয়ে পদ্মা দেখতে পান যে, মেয়েটির শ্বাস তখনও অল্প অল্প পড়ছে। স্নেহশীল পদ্মা বিধাতার কাছে মেয়েটির জীবন প্রার্থনা করেন। তিনি প্রত্যাশা করেন তাঁর পিতার পুণ্যের ফলে এবং তাঁর নিজের ভাগ্যের কারণে যেন মেয়েটির জীবন ফিরে আসে।
পদ্মার ভূমিকা – পদ্মাবতীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার আশায় পদ্মা শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেই থেমে থাকেননি, বরং তাঁর চিকিৎসারও যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সখীগণ-সহ পদ্মাবতীকে বস্তু দিয়ে ঢেকে উদ্যানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর সখীদের নির্দেশ দেন। সেখানে তন্ত্রাচারের মাধ্যমে, বিধিমতো মন্ত্রপাঠ করে নানা মহাগুণসম্পন্ন ঔষধের দ্বারা তাঁদের চিকিৎসা করা হয়। আগুন জ্বালিয়ে পায়ে ও মাথায় সেঁক দেওয়া হয়। চার দণ্ডের মতো যত্নের সঙ্গে শুশ্রূষা হওয়ার পরে চার সখীসহ পদ্মাবতী চেতনা ফিরে পান।
“পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন।” – পঞ্চকন্যা কে কে? তাদের অচৈতন্যের কারণ কী? কীভাবে তারা চেতনা ফিরে পেয়েছিল?
পঞ্চকন্যার পরিচয় – সৈয়দ আলাওল রচিত পদ্মাবর্তী কাব্যের অংশবিশেষ ‘সিন্ধুতীরে’ কাব্য-কাহিনিতে বর্ণিত পঞ্চকন্যার মধ্যমণি হলেন সিংহল-রাজকন্যা পদ্মাবতী। আর তাঁর চারজন সখী হলেন চন্দ্রকলা, বিজয়া, রোহিণী ও বিধুন্নলা।
অচৈতন্য হওয়ার কারণ – স্বামী রত্নসেনের সঙ্গে রাজকন্যা পদ্মাবতী সমুদ্রপথে চিতোরে ফেরার সময় হঠাৎ তাঁদের জলযানটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে এবং ডুবে যায়। রত্নসেন এবং সখীসহ রাজকন্যা কোনোরকমে একটি মান্দাসে আশ্রয় নেন। শেষপর্যন্ত মান্দাস দ্বিখণ্ডিত হয়ে চার সখীসহ রাজকন্যা রত্নসেনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। খণ্ডিত ভেলায় ভাসতে ভাসতে তাঁরা সমুদ্রতীরের ভূমিতে পৌঁছান। কিন্তু প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অসম লড়াই, দৈহিক ক্লেশ ইত্যাদির প্রভাবে রাজকন্যা ও তাঁর সখীরা জ্ঞান হারান।
চেতনা ফিরে পাওয়া – পঞ্চকন্যার এই অবস্থায় দেবতা সমুদ্রকন্যা পদ্মা নিরঞ্জনকে স্মরণ করেন এবং তাঁর সখীদের চিকিৎসাকর্মে ব্রতী হওয়ার নির্দেশ দেন। প্রাণপণ সেবাশুশ্রূষা করে পঞ্চকন্যার জীবন রক্ষাই ছিল তাঁর মনের ইচ্ছা। সেই অনুযায়ী শুকনো কাপড় দিয়ে সখীসহ রাজকন্যার শরীর আবৃত করা হয়। আগুন জ্বেলে সর্বাঙ্গ সেঁক দেওয়া হয় এবং তন্ত্রমন্ত্র সহকারে মহৌষধ প্রয়োগ করা হয়। একটানা চার দণ্ড সেবাশুশ্রূষার পর পঞ্চকন্যা চেতনা ফিরে পান। দয়ালু পদ্মার আন্তরিক সেবাযত্নে সখী-সহ পদ্মাবতীর জ্ঞান ফিরে আসে।
‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশটিতে কবির রচনারীতির যে বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায় লেখো।
রচনারীতির বিশেষত্ব – ‘সিন্ধুতীরে’ -এর সংক্ষিপ্ত পরিসরেও অচৈতন্য অপরিচিতা রাজকুমারী পদ্মাবতীর প্রতি সমুদ্রকন্যা পদ্মার যে সহানুভূতি ও ভালোবাসা তা মানবিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন।
ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগে বিশেষত্ব – ধীর লয়ের ত্রিপদী ছন্দে এই আবেগকে ধরাশ করেছেন কবি। আবার শেষে ভণিতায় পাঁচালির রীতিও ব্যবহার করেছেন –
“শ্রীযুত মাগন গুণী মোহন্ত আরতি শুনি
হীন আলাওল সুরচন।।”
- শব্দ প্রয়োগের – আরবি-ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আলাওলের কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ কম। পরিবর্তে তৎসম শব্দের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায় – ‘সদাচার’, ‘সুতা’, ‘পুষ্প,’ ‘মনোহর’, ‘স্বর্গভ্রষ্টা’, ‘কেশ’ ইত্যাদি।
- কাব্যিক শব্দ প্রয়োগ – কাব্যিক শব্দের ব্যবহারেও আলাওল দক্ষতা দেখিয়েছেন। যেমন – ‘মাঝারে’, ‘চিতে’, ‘তুরিত’ ইত্যাদি। আলাওল আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন, ফলে তাঁর ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতাটি পড়লে গল্প পড়ার আনন্দ উপভোগ করা যায়।
- সাবলীল লেখনী – পরপর প্রতিটি দৃশ্যকেই তিনি ছবির মতো সাজিয়ে তুলেছেন। সেই দৃশ্যগুলিকে অত্যন্ত সুমধুর ও সুপাঠ্য করে তুলেছে তাঁর দক্ষ সাবলীল লেখনী। ঘটনার পরম্পরাটিকেও তিনি সাজিয়েছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে।
- নাটকীয়তা – যেভাবে ঘটনা তৈরি করা হয়েছে তা কাব্যাংশটিকে নাটকীয়তা দিয়েছে। শেষে কবি আলাওল লিখেছেন – “হীন আলাওল সুরচন।” অনস্বীকার্য যে, ‘সিন্ধুতীরে’ আলাওলের একটি সুরচনা।
‘সিন্ধুতীরে’ কবিতায় পদ্মার চরিত্রটি যেভাবে পাওয়া যায় আলোচনা করো।
অথবা, ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতা অবলম্বনে সমুদ্রকন্যার আচার-আচরণ ব্যাখ্যা করো।
- কথামুখ – সৈয়দ আলাওলের অনূদিত পদ্মাবতী কাব্যের ‘পদ্মাসমুদ্রখণ্ড’ থেকে সংকলিত ‘সিন্ধুতীরে’ কবিতায় পদ্মাই সবথেকে সক্রিয় চরিত্র। সে সমুদ্রকন্যা। কাহিনিতে তাঁর কিছু বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়।
- সৌন্দর্যপ্রিয় – পদ্মার মধ্যে ছিল সৌন্দর্যপ্রিয়তা। তাই যে উদ্যান তিনি তৈরি করেছেন সেখানে নানা মনোহর ফুল সুগন্ধ বিস্তার করেছে, গাছে নানা ফল ধরেছে। তাঁর প্রাসাদটিও ছিল সোনায় মোড়া। তার ওপরে নানান রত্নের সজ্জা সেই প্রাসাদের সৌন্দর্যও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
- প্রাণচঞ্চল – পদ্মা ছিলেন প্রাণচঞ্চল। তাই রাত্রি শেষ হতেই দেখা যায় সকালবেলা সখীদের সঙ্গে হাসিখেলায় মেতে উঠে তিনি তাঁর প্রিয় উদ্যানের দিকে চলেছেন। সখীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত মধুর।
- মানবিক – পদ্মা চরিত্রটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর মানবিকতায়। অপরিচিতা পদ্মাবতীকে সমুদ্রতীরের মান্দাসে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁর উৎকণ্ঠা, ঈশ্বরের কাছে তাঁর কাতর প্রার্থনা যেন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার সেতু তৈরি করেছে। তাঁরই নির্দেশে পদ্মার সখীরা তন্ত্র-মন্ত্র-মহৌষধি সহযোগে আগুনের সেঁক দিয়ে পদ্মাবতীর চেতনা ফিরিয়েছে। মধ্যযুগের কবিতায় আলাওলের সৃষ্ট এই চরিত্রটিতে মানবিকতা এক অসামান্য বিশেষত্ব। এভাবেই সমুদ্রকন্যা পদ্মা হয়ে উঠেছেন অনন্যা।
‘সিন্ধুতীরে’ কবিতার মূল চরিত্র পদ্মাবতী ও পদ্মার পরিচয় দাও। পদ্মাবতীকে দেখে পদ্মার ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া আলোচনা করো।
পদ্মাবতীর পরিচয় – পদ্মাবতী ছিলেন সিংহল রাজকন্যা। তাঁর পিতা ছিলেন গন্ধর্বসেন। পদ্মাবতীর অপরূপ সৌন্দর্যের কথা শুনে চিতোর রাজা রত্নসেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে রত্নসেনের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিয়ে হয় এবং বিয়ের পরে দেশে ফেরার সময় তাঁরা সামুদ্রিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন।
পদ্মার পরিচয় – অন্যদিকে, পদ্মা ছিলেন সমুদ্রকন্যা। সমুদ্রতীরে তাঁর যে সুরম্য উদ্যান আছে এবং সোনায় মোড়া যে প্রাসাদ তিনি তৈরি করেছেন, তা পদ্মার সৌন্দর্যপ্রিয়তার অসামান্য উদাহরণ। সখীদের নিয়ে হাসিখেলায় প্রাণচঞ্চল রূপেই পদ্মাকে কবিতায় পাওয়া যায়।
পদ্মার ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া – পদ্মাবতীর বিস্ফারিত চোখ, এলোমেলো পোশাক এবং চুল দেখে সমুদ্রকন্যা পদ্মা অনুমান করেন যে, সমুদ্রের প্রবল ঝড়ে নৌকা ভেঙেই বোধহয় মেয়েটি এই কষ্ট পেয়েছে। শুধু তা-ই নয়, গভীর সহানুভূতির সঙ্গে পদ্মা দেখেন যে, মেয়েটির শ্বাস তখনও অল্প অল্প পড়ছে। স্নেহশীল পদ্মা বিধাতার কাছে মেয়েটির জীবন প্রার্থনা করেন। তিনি প্রত্যাশা করেন, তাঁর পিতার পুণ্যের ফলে এবং তাঁর নিজের ভাগ্যের কারণে মেয়েটির জীবন যেন ফিরে আসে। পদ্মাবতীকে দেখে পদ্মার মনে হয়েছিল যে, ইন্দ্রের অভিশাপে স্বর্গের নর্তকী বিদ্যাধরী যেন স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। পদ্মাবতীর ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ এবং এলোমেলো বেশ দেখে পদ্মা এ-ও অনুমান করেন যে, ওই কন্যার ওপর দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে গেছে। এলোমেলো চুল এবং বেশবাসের এই অবস্থায় পদ্মার মনে হয় যে, হয়তো সমুদ্রযাত্রার পথে দুরন্ত ঝড়ে নৌকা ভেঙে তাঁরা এই বিপদে পড়েছেন। সমুদ্রের কষ্টেই তাঁর এই অজ্ঞান অবস্থা।
“সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশ অবলম্বনে সৈয়দ আলাওলের কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।
- কথামুখ – আলাওলের ‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশের শুরুতেই সমুদ্রকন্যা পদ্মার দিব্যপুরীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
- সৌন্দর্যপ্রীতি – সেই মনোহর পুরীর বর্ণনায় আলাওলের সৌন্দর্যপ্রীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। পদ্মার প্রাসাদের নিকটে এক পর্বত অবস্থিত। তার পাশে ছিল ফুল ও ফলে ভরা অপূর্ব এক উদ্যান। কবির ভাষায় –
“নানা পুষ্প মনোহর সুগন্ধি সৌরভতর
নানা ফল বৃক্ষ সুলক্ষণ।
তাহাতে বিচিত্র টঙ্গি হেমরত্নে নানা রঙ্গি
তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ।।”
- শব্দ প্রয়োগ – মধ্যযুগে রচিত এই কাব্যের ভাষা তৎসম শব্দ নির্ভর হয়েও হৃদয়স্পর্শী। কাহিনি-কাব্যের ধারা অনুযায়ী আলাওল ঘটনাক্রমকে গল্পের মতো সাজিয়েছেন।
- উদার মানবিক চরিত্রের প্রকাশ – সমুদ্রকন্যার উদার মানবিক চরিত্রের প্রকাশ কাব্যাংশটিকে সর্বজনীন করে তুলেছে। সম্পূর্ণ অপরিচিতা পদ্মাবতীর জন্য তাঁর উদ্বেগ এবং তাঁকে সুস্থ করে তোলার জন্য তাঁর আকুলতা নিখাদ মানবিক।
- রূপমাধুরীর বর্ণনা – কাব্যের নায়িকা পদ্মাবতীর রূপমাধুরীর বর্ণনায় আলাওল অসামান্য। অচৈতন্য পদ্মাবতীকে দেখে সমুদ্রকন্যার মনে হয়েছে – “ইন্দ্রশাপে বিদ্যাধরি/কিবা স্বর্গভ্রষ্ট করি/অচৈতন্য পড়িছে ভূমিতে।” অর্থাৎ ‘নিপতিতা চেতন রহিত’ নারীর রূপসৌন্দর্যে স্বর্গীয় ছোঁয়া থাকতে পারে, কিন্তু সে যে এই মর্তপৃথিবীর একজন, তাতে কোনো সংশয় নেই।
- রূপচরিত্রের নির্মাণ – মানব-মানবীর রূপচরিত্র নির্মাণে আলাওল এভাবেই বিরল দক্ষতা দেখিয়েছেন। এইভাবে ‘সিন্ধুতীরে’র স্বল্প পরিসরেও আলাওলের উচ্চ কবিপ্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে।
“সিন্ধুতীরে” কাব্যাংশটির নামকরণ কতদূর সার্থক হয়েছে তা বিচার করো।
নামকরণ সাহিত্যের প্রবেশের চাবিকাঠি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ‘সিন্ধুতীরে’ নামকরণটি কবির দেওয়া নয়। কাব্যকাহিনির বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে সংকলকগণ এ ধরনের নামকরণ করেছেন।
সিংহল-রাজকন্যা পদ্মাবতী তাঁর স্বামীর সঙ্গে চিতোরে ফেরার সময় সামুদ্রিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েন। তাঁদের জলযানটি সমুদ্রে ডুবে যায়। একটি মান্দাসে রত্নসেন ও সখীসহ পদ্মাবতী আশ্রয় নিলেও সেটি রক্ষা পায়নি। প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝায় মান্দাস দ্বিখণ্ডিত হয়ে পদ্মাবতী রত্নসেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দুর্যোগজনিত কষ্টে রাজকন্যা জ্ঞান হারিয়ে সমুদ্রতীরে পড়ে থাকেন। সাগরকন্যা পদ্মা ভোরবেলা সুরম্য উদ্যানে এসে এই দৃশ্য দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি সখীদের নির্দেশ দেন অচৈতন্য রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। সখীরাও সেই নির্দেশ অনুযায়ী রাজকন্যা পদ্মাবতীকে উদ্যানের মাঝখানে নিয়ে এসে চার দণ্ড ধরে নানা সেবাযত্নের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন। এটাই হল সংক্ষিপ্ত কাব্যকাহিনি। এখানে লক্ষণীয় যে, যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে। কাব্যাংশটির শুরুতেও এই সমুদ্রতীরবর্তী ‘দিব্যস্থান’-এর শোভা-সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে।
সিন্ধুতীরে শব্দটির অর্থ সমুদ্রতীরে। সেই স্থাননামের উল্লেখেই কাব্যাংশটির নামকরণ করা হয়েছে। এই অংশে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনা এবং বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সমুদ্রতীরকেন্দ্রিক। যে চরিত্রদের কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে, তার চেয়ে যে স্থানটিতে কাহিনিটি ঘটেছে, সেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে নামকরণটি বিষয়কেন্দ্রিক এবং যথাযথ হয়েছে বলা যায়।
‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশ অবলম্বনে পদ্মার মনোহর প্রাসাদের বর্ণনা দাও। সখী-সহ রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপ দেখে সমুদ্রলক্ষ্মীর কী ধারণা হয়েছিল?
মনোহর প্রাসাদের বর্ণনা – ‘সিন্ধুতীরে’ কাব্যাংশে দেখা যায় সমুদ্রতীরে দিব্যস্থানে ফুলেফলে ভরা এক সুরম্য উদ্যান রচনা করেছিলেন সমুদ্রকন্যা পদ্মা। সেই উদ্যানের মধ্যেই ছিল তাঁর সুরম্য প্রাসাদ। তা ছিল অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং বৈচিত্র্যময় – ‘বিচিত্র টঙ্গি’। তা ছিল স্বর্ণনির্মিত এবং নানান মূল্যবান রত্নে সাজানো। সেই রত্নখচিত প্রাসাদে আলো পড়লে বর্ণালি বিচ্ছুরিত হত। ‘হেম রত্নে নানা রঙ্গি’ অর্থাৎ সোনা ও রত্নাসম্ভারে তা বিচিত্র দেখতে লাগছিল।
পদ্মাবতীর রূপদর্শনে সমুদ্রলক্ষ্মীর ধারণা – সমুদ্রতীরের অসামান্য পরিবেশে সখীদের নিয়ে উদ্যানে যাওয়ার সময়ে সমুদ্রকন্যা পদ্মা লক্ষ করেন সমুদ্রতীরের মান্দাসটিকে। দ্রুত কাছে গিয়ে অচেতন চার সখীর মধ্যে থাকা পদ্মাবতীকে তিনি লক্ষ করেন। পদ্মাবতীকে দেখে সমুদ্রকন্যার মনে হয় রূপ ও সৌন্দর্যে তিনি স্বর্গের অপ্সরা রম্ভাকেও পরাজিত করতে পারেন – “দেখিয়া রূপের কলা বিস্মিত হইল বালা”। সমুদ্রকন্যার মনে হয়, ইন্দ্রের অভিশাপে স্বর্গের গায়িকা বিদ্যাধরী যেন স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ, আলুথালু বেশ ইত্যাদি দেখে পদ্মার মনে হয় যে, তাঁর ওপর দিয়ে কোনো ঝড় বয়ে গেছে। ছবিতে আঁকা মূর্তির মতো সুন্দরী মেয়েটির তখন সামান্যমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসই বইছিল।
আজকের আর্টিকেলে আমরা মাধ্যমিক বাংলার ষষ্ঠ পাঠের প্রথম বিভাগ, ‘সিন্ধুতীরে’ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী ও রচনাধর্মী প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে। আশা করি, এই আর্টিকেলটি আপনাদের উপকারে এসেছে। যদি কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা থাকে, তবে আপনি আমাকে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। এছাড়াও, পোস্টটি শেয়ার করে আপনার পরিচিতদের সহায়তা করতে পারেন যারা এর প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।


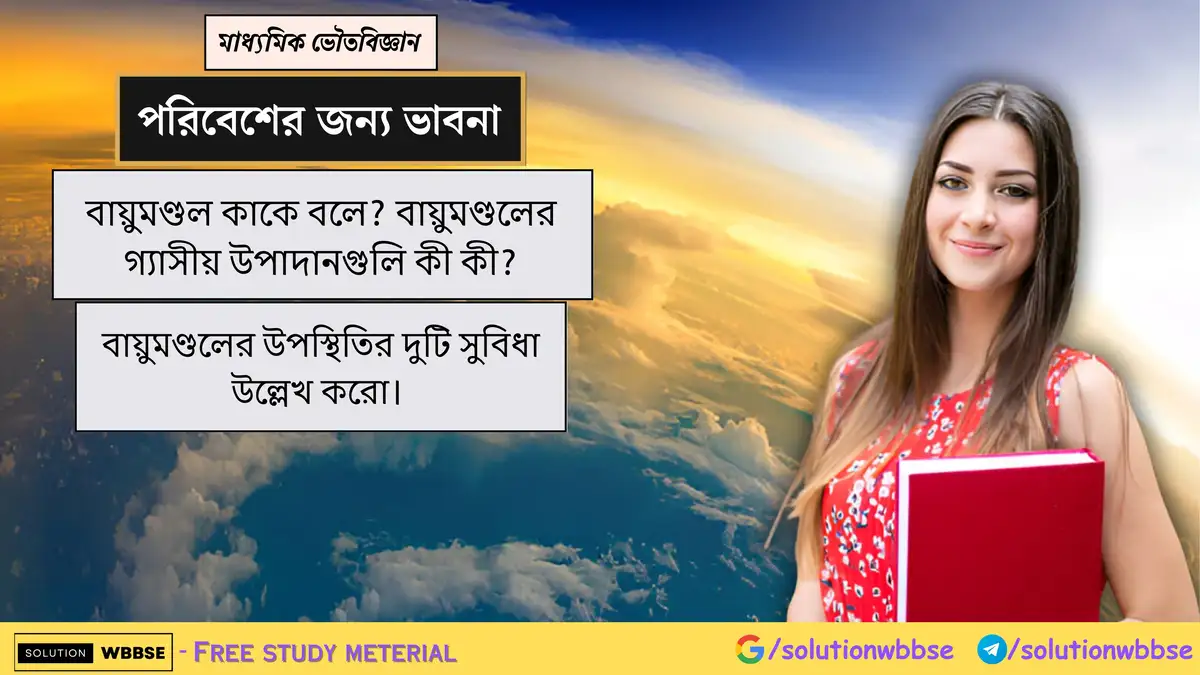
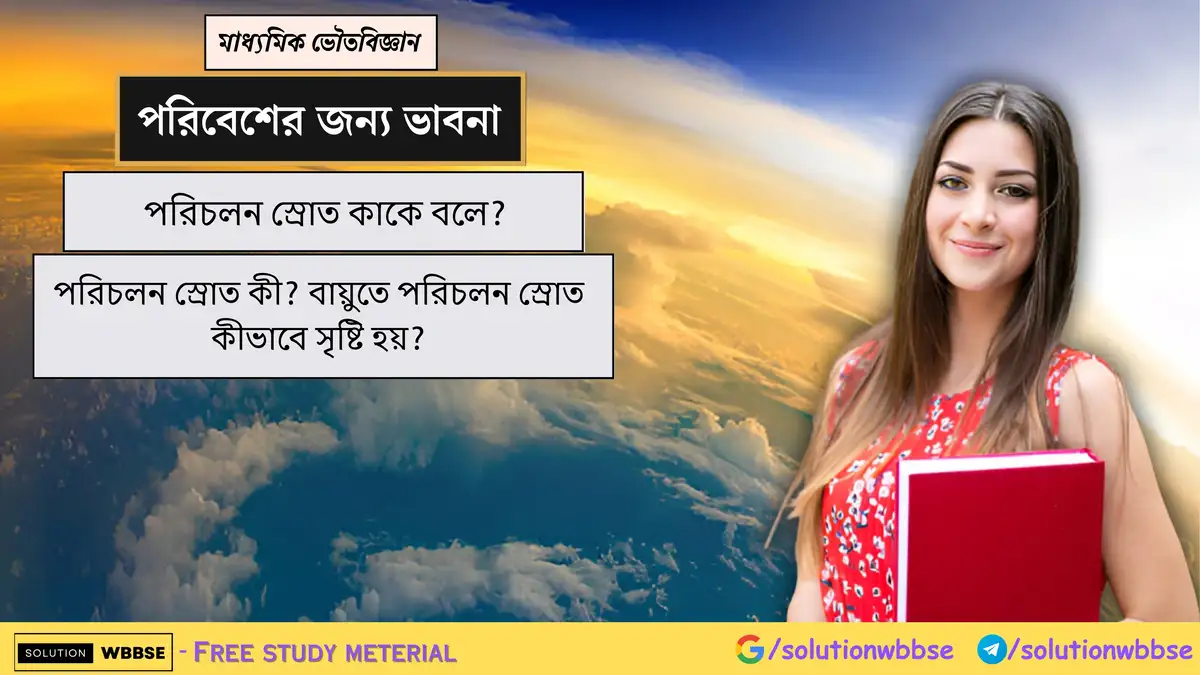
মন্তব্য করুন