আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের অষ্টম অধ্যায় ‘পশ্চিমবঙ্গ (প্রাকৃতিক পরিবেশ)’ এর ভৌগোলিক কারণ ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করবো। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
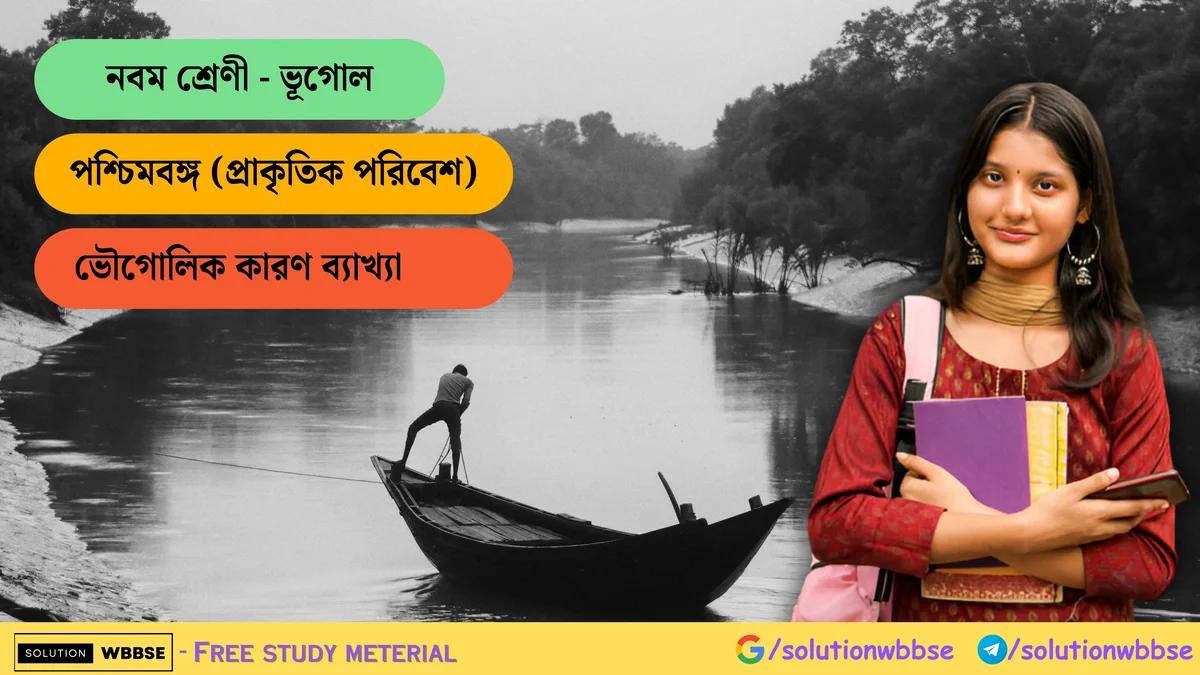
পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চলকে ‘ডুয়ার্স’ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
‘তরাই’ কথার অর্থ ‘স্যাঁতসেঁতে নিম্ন ভূমি’। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশের স্যাঁতসেঁতে ভূমিকে তরাই বলে। এই তরাই অঞ্চলের অপর নাম ডুয়ার্স।
কারণ – ‘ডুয়ার্স’ কথার অর্থ হল দরজা (door)। তরাই -এর পূর্ব দিকে আলিপুরদুয়ারের উত্তর অংশকে ডুয়ার্স বলে। এই পথ দিয়ে ভুটানের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করা হয়। যেহেতু তরাই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ভুটানে প্রবেশ করা হয়, তাই তরাই অঞ্চলের অপর নাম ডুয়ার্স।
সুন্দরবন অঞ্চলকে ‘সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল’ বলা হয় কেন? ভৌগোলিক কারণ সহ ব্যাখ্যা করো।
পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে এখনও বদ্বীপ গঠনের কাজ চলছে বলে এই অঞ্চল সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত।
ভৌগোলিক কারণ –
- জোয়ারভাটা – জোয়ার ও ভাটার কারণে ভাগীরথী-পদ্মা ও অসংখ্য শাখা নদী যেমন – ভৈরব, জলঙ্গি, মাথাভাঙ্গা, কালিন্দী প্রভৃতি নদী প্রচুর পরিমাণে পলি, বালি, কাদা প্রতি বছরই মোহানা অঞ্চলে সঞ্চিত করে চলেছে।
- অসংখ্য নদী চরের সৃষ্টি – সুন্দরবন অঞ্চলের নদী ও সমুদ্রের মিলিত কার্যের ফলে অসংখ্য নতুন নতুন চর গড়ে উঠছে। পরে চরগুলির চারপাশে ক্রমশ বালি, পলি, কাদা জমে বিস্তৃত হয়ে মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং নিত্যনতুন বদ্বীপ গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে।
উদাহরণ – সাম্প্রতিককালে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী মোহানার নিকট একটি নতুন নদী দ্বীপ গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যার নাম দিয়েছে ‘পূর্বাশা’ এবং কেন্দ্রীয় সরকার নাম দিয়েছে ‘নিউমুর আইল্যান্ড’ এবং বাংলাদেশ সরকার নাম দিয়েছে ‘দক্ষিণ তালপট্টি’।
ভাগীরথী-হুগলি নদীকে ‘পশ্চিমবঙ্গের জীবনরেখা’ বলা হয় কেন? আলোচনা করো।
গঙ্গা নদীর একটি শাখা নদী হল ভাগীরথী-হুগলি। এই নদী পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ও দীর্ঘতম নদী। এই নদীকে ‘পশ্চিমবঙ্গের জীবনরেখা’ বলার কারণ –
- উর্বর কৃষিভূমি – ভাগীরথী-হুগলি নদী অববাহিকায় নদীর নবীন পলি সঞ্চয় হয়ে বিস্তীর্ণ উর্বর কৃষিভূমি তৈরি হয়েছে, যা কৃষি উৎপাদনে সহায়ক।
- হুগলি শিল্পাঞ্চল গঠন – হুগলি নদীর জল, জলপথে পরিবহণ, উর্বর মাটিতে পাট চাষ প্রভৃতি অনুকূল পরিবেশ থাকায় হুগলি নদীর উভয় তীরে পাট শিল্প গড়ে উঠেছে।
- পরিবহণ ও কলকাতা বন্দর – পরিবহণের মাধ্যম হিসেবে জলপথ সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। ভাগীরথী-হুগলি নদীর তীরে কলকাতা বন্দর গড়ে উঠেছে। এই বন্দর সমগ্র পূর্ব ভারতের বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি-রপ্তানিতে সাহায্য করে।
এছাড়া ভাগীরথী-হুগলি নদী পানীয় জল, নদীর মাছ প্রভৃতি জোগান দিয়ে থাকে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নতিতে ভাগীরথী-হুগলি নদীর অসীম গুরুত্ব থাকায় এই নদীকে ‘পশ্চিমবঙ্গের জীবনরেখা’ বলে।
কংসাবতী নদীকে ‘মেদিনীপুরের দুঃখ’ বলা হয় কেন? তার উৎপত্তি ও গতিপথসহ ব্যাখ্যা কর।
কংসাবতী নদীর গতিপথ – কাঁসাই বা কংসাবতী নদীটি পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে হুগলি নদীতে মিশেছে।
‘মেদিনীপুরের দুঃখ’ বলার কারণ –
- মৃদু ভূমি ঢাল – কংসাবতী নদীর উৎস থেকে মধ্য প্রবাহ পর্যন্ত ভূমির ঢাল বেশি থাকার কারণে ওই অঞ্চলে জল জমতে না পারলেও নদীর নিম্নপ্রবাহ অর্থাৎ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভূমির ঢাল একেবারে কমে যাওয়ায় উৎস অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হলে মেদিনীপুর জেলাটি বন্যায় প্লাবিত হয়।
- অগভীর নদীখাত – কংসাবতী নদীর গভীরতা খুবই কম হওয়ায় বর্ষার সময় জলের চাপে নদীর দুকূল প্লাবিত হয়ে মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে এই নদীকে ‘মেদিনীপুরের দুঃখ’ বলা হয়।
পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের সমভূমি অঞ্চল বন্যাপ্রবণ কেন? কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।
অথবা, উত্তরবঙ্গের নদীগুলি বন্যাপ্রবণ।
পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে জলপাইগুড়ির দক্ষিণ, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলা নিয়ে ‘উত্তরের সমভূমি অঞ্চল’ গঠিত। এই সমভূমি অঞ্চলে প্রায়ই বন্যার সৃষ্টি হয়।
বন্যাপ্রবণ হওয়ার কারণ –
- নিম্ন সমতল ভূমি অবস্থান – কালিন্দী নদীর বামতীরের অংশ অর্থাৎ ‘তাল’ অঞ্চলের কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর ও মালদা জেলার পশ্চিমাংশের ভূমিভাগ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা বেশ নীচু হওয়ায় বর্ষাকালে জলের চাপে বন্যার সৃষ্টি হয়।
- প্রায়শই নদীর গতিপথের পরিবর্তন – উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত মহানন্দা, কালিন্দী, জলঢাকা, তোর্সা প্রভৃতি নদীগুলি অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন হওয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গতিপথের প্রায়ই পরিবর্তন হয়, ফলে বর্ষার সময় জলের গতিবেগ বেশি হওয়ায় প্লাবন দেখা দেয়।
- অগভীর নদীখাত – ক্ষয়কার্যের ফলে মহানন্দা, কালিন্দী, জলঢাকা, তোর্সা প্রভৃতি নদীখাতে পলি, বালি, নুড়ি, কাঁকর সঞ্চিত হওয়ায় নদীখাত অগভীর হয়ে পড়ে। ফলে প্রবল জলের চাপে নদীর দুকূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী অংশে বন্যার সৃষ্টি হয়। উপরিউক্ত কারণে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের সমভূমি অঞ্চল বন্যাপ্রবণ।
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের নদ-নদীর বালির রঙে পার্থক্য কেন দেখা যায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।
নদীর উৎস, গতিপথের শিলার প্রকৃতি, নদীর জলের গতিবেগ প্রভৃতির ওপর নদ-নদীর বালির রং নির্ভর করে। যেমন –
উত্তরবঙ্গের নদ-নদীর সাদা বালি – পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক প্রভৃতি নদীর বালির রং সাদা। কারণ – নদীগুলি সুউচ্চ হিমালয় ও তিব্বতীয় উচ্চভূমি থেকে সৃষ্টি হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। নদী গতিপথের গ্রানাইট শিলা প্রবল জলস্রোতে ক্ষয় হয়ে সাদা রং -এর বালির সৃষ্টি হয়।
পশ্চিমের নদ-নদীর লাল বালি – পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদীর বালির রং লাল। কারণ – নদীগুলির গতিপথে রয়েছে (লৌহযুক্ত) লাল বর্ণের ল্যাটেরাইট মাটি। নদীগুলি বৃষ্টির জলে পৃষ্ট, তাই গ্রীষ্মে শুষ্ক থাকে ও আবহবিকারের ফলে লাল শিলা ভেঙে যায় ও লাল বালি সৃষ্টি হয়।
পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ নদী পূর্ববাহিনী কেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।
পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ নদী যেমন – অজয়, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি পূর্ববাহিনী কারণ –
ভূমির ঢাল – পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের ভূমির ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। তাই এই ঢালু ভূমির ওপর দিয়ে নদীগুলি প্রবাহিত হওয়ায় নদীগুলি পূর্ববাহিনী।
উৎস ও মোহানা – ছোটোনাগপুর মালভূমির উচ্চ অংশ থেকে নদীগুলি উৎপন্ন হয়ে পূর্ব দিকে ভাগীরথী-হুগলি নদীতে মিশেছে। তাই নদীগুলির গতিপথ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, অর্থাৎ নদীগুলি পূর্ববাহিনী।
শুষ্ক ঋতুতে পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের নদীগুলির সমভূমি প্রবাহে জল না থাকার কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।
পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের প্রধান নদীগুলি হল – দামোদর, অজয়, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষী, হলদি ইত্যাদি। এইসব নদীগুলির সমভূমি প্রবাহে শুষ্ক অঞ্চলে জল থাকে না। কারণ –
বাঁধ নির্মাণ – উচ্চ ও মালভূমি অঞ্চলে নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে জল ধরে রাখা হয়। ফলে সমভূমি প্রবাহে জল থাকে না।
বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী – মালভূমি অঞ্চলের নদীগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট। শুষ্ক ঋতুতে অল্প বৃষ্টি হয়। নদীগুলির উৎস অঞ্চল বা মধ্যপ্রবাহে সামান্য জলপ্রবাহ থাকলেও সমভূমি প্রবাহে এসে আর জল প্রায় থাকে না।
বেশি উষ্ণতা – গ্রীষ্মকালে মালভূমি অঞ্চলে উষ্ণতা বেশি থাকে। গড়ে প্রায় 40° সে। অধিক উষ্ণতায় জল বাষ্পীভূত হয়। ফলে নদীর জল নিম্ন প্রবাহে তেমন থাকে না।
পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের প্রধান নদীগুলি হল – দামোদর, অজয়, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষী, হলদি ইত্যাদি। এইসব নদীগুলির সমভূমি প্রবাহে শুষ্ক অঞ্চলে জল থাকে না। কারণ –
- বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী – মালভূমি অঞ্চলের নদীগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট। শুষ্ক ঋতুতে অল্প বৃষ্টি হয়। নদীগুলির উৎস অঞ্চল বা মধ্যপ্রবাহে সামান্য জলপ্রবাহ থাকলেও সমভূমি প্রবাহে এসে আর জল প্রায় থাকে না।
- বেশি উষ্ণতা – গ্রীষ্মকালে মালভূমি অঞ্চলে উষ্ণতা বেশি থাকে। গড়ে প্রায় 40° সে। অধিক উষ্ণতায় জল বাষ্পীভূত হয়। ফলে নদীর জল নিম্ন প্রবাহে তেমন থাকে না।
- বাঁধ নির্মাণ – উচ্চ ও মালভূমি অঞ্চলে নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে জল ধরে রাখা হয়। ফলে সমভূমি প্রবাহে জল থাকে না।
পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে ভৌমজলস্তর সমৃদ্ধ না হওয়ার কারণ কী? বিস্তারিত ব্যাখ্যা করো।
পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল অর্থাৎ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলায় ভৌমজলস্তর সমৃদ্ধ নয়। কারণ –
- স্বল্প বৃষ্টিপাত – বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। ফলে মাটির নীচে ভৌম জলস্তর কম হয়।
- কঠিন শিলার অবস্থান – পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল কঠিন গ্রানাইট শিলায় গঠিত। এই শিলা অপ্রবেশ্য হওয়ায় বৃষ্টির জল মাটির নীচে যেতে পারে না, ফলে ভৌমজলস্তর কম।
- ভূমির ঢাল – পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। তাই বৃষ্টি হলে জল দ্রুত ঢাল বেয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে বৃষ্টির জল মাটির নীচে প্রবেশ করার সময় কম পায়। তাই পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে ভৌমজলস্তর সমৃদ্ধ নয়।
- বাষ্পীভবনের আধিক্য – মালভূমি অঞ্চলে উষ্ণতা বেশি থাকায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে জল ভূ-গর্ভে প্রবেশ করতে পারে না। তাই ভৌম জলস্তরসমৃদ্ধ হয় না।
পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে খাঁড়ি সৃষ্টির কারণ কী?
সুন্দরবন, গাঙ্গেয় বদ্বীপের সক্রিয় অংশ। এই অঞ্চলে অসংখ্য সংকীর্ণ নদী ফানেল আকৃতির উপত্যকা সৃষ্টি করেছে। এদের খাঁড়ি বলে। সুন্দরবন অঞ্চলে খাঁড়ি সৃষ্টির কারণ
- জোয়ারভাটার প্রভাব – বঙ্গোপসাগরের জল জোয়ারের সময় নদী দিয়ে ক্রমশ স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসে, আবার ভাটার সময় ফিরে যায়। এর ফলে নদী উপত্যকায় ফানেল আকৃতির খাঁড়ি সৃষ্টি হয়।
- ভূমির অবনমন – ভূমিরূপ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ভূমির অবনমনের ফলে সুন্দরবনে অসংখ্য খাঁড়ি সৃষ্টি হয়েছে।
- নদীর চওড়া মোহানা – মোহানার কাছে সমুদ্রের তরঙ্গের আঘাতে নদীর আকৃতি ফানেলের মত হয়। তাই নদী মোহানায় খাঁড়ি সৃষ্টি হয়।
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর পার্থক্য কিসের কারণে ঘটে? উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করো।
সমুদ্র থেকে ভিন্ন দূরত্বে অবস্থানের কারণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর বিস্তর পার্থক্য ঘটতে দেখা যায়। যেমন – পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় অঞ্চলে সমভাবাপন্ন কিন্তু সমুদ্র উপকূল থেকে দূরবর্তী মালভূমি অঞ্চলে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু লক্ষ করা যায়।
স্থলভাগ ও জলভাগের পাশাপাশি অবস্থান –
সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুপ্রবাহ – সমুদ্র সংলগ্ন স্থানগুলিতে স্থলভাগ ও জলভাগ পাশাপাশি অবস্থান করায় বায়ুচাপের পার্থক্য বেশি হয়। ফলে দিন ও রাতে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তন ঘটে। দিনের বেলা এই অঞ্চলে স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় বেশি গরম হওয়ায় নিম্নচাপের ফলে সমুদ্রের দিক থেকে সমুদ্র বায়ু এবং রাতের বেলায় এর বিপরীত অবস্থার ফলে স্থলভাগ থেকে স্থলবায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। যেমন – দিঘা ও কাঁথি উপকূল অঞ্চল।
মালভাগগুলির পাশাপাশি অবস্থান –
স্থলবায়ুপ্রবাহ – যে সমস্ত স্থান সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত, তার পাশের স্থানটির ও সমুদ্র থেকে দূরত্ব অনেক বেশি থাকে। ফলে সেই দুটি স্থলভাগের মধ্যে দিন ও রাতে বায়ুচাপের তারতম্য খুবই কম। বায়ুপ্রবাহ এই অঞ্চলে ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়। সেই জন্য সমুদ্র থেকে দূরবর্তী স্থানগুলির জলবায়ু চরমভাবাপন্ন প্রকৃতির। যেমন – পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় চরমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখা যায়।
পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণ অংশের উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের প্রধান কারণগুলি কী কী? বিশদভাবে ব্যাখ্যা করো।
উষ্ণতার পার্থক্যের কারণ –
- উচ্চতাগত কারণ – উচ্চতা বাড়লে উষ্ণতা কমে। তাই উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে উষ্ণতা কম ও দক্ষিণ অংশে উষ্ণতা বেশি।
- অক্ষাংশগত কারণ – পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশের অক্ষাংশের মান উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের অক্ষাংশ অপেক্ষা কম অর্থাৎ, দক্ষিণ অংশ নিরক্ষরেখার বেশি সান্নিধ্য লাভ করেছে বলে এখানে উষ্ণতা বেশি এবং পার্বত্য অঞ্চলে উষ্ণতা কম।
- শীতল বায়ুর প্রভাব – শীতল উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে এসে প্রথম বাধা পায় বলেই এখানে উষ্ণতা কম। এই বায়ু পার্বত্য অঞ্চলের বাধা পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে যত প্রবাহিত হয়, ততই শীতলতা কমতে থাকে।
- বঙ্গোপসাগরের সান্নিধ্য – বঙ্গোপসাগরের সান্নিধ্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে উষ্ণতা সমভাবাপন্ন।
এই সকল কারণে পার্বত্য অঞ্চলে শীতকালের উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে এবং গ্রীষ্মকালে 15°C -এর মতো হয় এবং দক্ষিণবঙ্গে গ্রীষ্মকালের তাপমাত্রা অত্যধিক হয়।
বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের কারণ –
বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু যখন পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে, তখন তা উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলেই সর্বপ্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু এই বায়ু যখন দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয় তখন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উত্তরবঙ্গের তুলনায় কমতে থাকে। উত্তরবঙ্গে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 400 সেমি। আলিপুরদুয়ার জেলার সিঞ্চল পাহাড়ের বক্সাদুয়ারে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এখানে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 450 সেমি।
পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ – কলকাতায় 180 সেমি, বর্ধমানে 150 সেমি, পুরুলিয়ায় 120 সেমি এবং সুন্দরবন অঞ্চলে 200 সেমি ইত্যাদি।
পশ্চিমবঙ্গের শীতকাল শুষ্ক ও গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র হয় কেন? এই জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের কারণগুলি বিশদে আলোচনা করো।
পশ্চিমবঙ্গের শীতকাল শুষ্ক প্রকৃতির এবং গ্রীষ্মকাল উষ্ণ আর্দ্র প্রকৃতির। তার কারণ নিম্নালোচিত –
পশ্চিমবঙ্গের শুষ্ক শীতকাল –
- সূর্যের দক্ষিণায়ণ – পশ্চিমবঙ্গের ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে লম্বভাবে কিরণ দেয়। উত্তর গোলার্ধের ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণতা তখন যথেষ্ট কম হয়, ফলে শীত ঋতু শুরু হয় এবং শুষ্কতা বিরাজ করে।
- তিব্বতের শুষ্ক শীতল বায়ুপ্রবাহ – দক্ষিণ গোলার্ধে প্রবল উষ্ণতার ফলে ওই অঞ্চলের নিম্নচাপ কেন্দ্রের বায়ু শূন্যতাকে পূরণ করতে তিব্বত অঞ্চল থেকে শীতল ও শুষ্ক বায়ু এই রাজ্যের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে শীত ঋতু শুষ্ক প্রকৃতির হয়।
পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণ আর্দ্র গ্রীস্মকাল –
- লম্ব সূর্যরশ্মি – কর্কটক্রান্তিরেখার ওপর সূর্যের লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবেশ করে ও মাঝে মাঝে কালবৈশাখী ঝড় হয়, ফলে আর্দ্রতা বাড়ে।
- মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ – মে মাসের শেষের দিকে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু (মৌসুমি বায়ু) পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করায় উষ্ণতা প্রশমিত হয়ে আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে। ফলে গ্রীষ্মকালে এ রাজ্যে উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু দেখা যায়।
পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল স্থানটি কোথায় অবস্থিত? এই অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের প্রধান কারণগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।
পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক বৃষ্টিবহুল স্থান হল আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সাদুয়ার (455 সেমি)। এটি পার্বত্য অঞ্চলেই অবস্থিত। পার্বত্য অঞ্চলে সর্বাধিক বৃষ্টি হয়। তার কারণ –
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বাধা – সমুদ্র থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দার্জিলিং হিমালয় অংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায়। এখানে গড়ে 300-400 সেমি বার্ষিক বৃষ্টি হয়।
অরণ্যের অবস্থান – পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্য বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প ত্যাগ করে, ফলে পার্বত্য অঞ্চলে আর্দ্র বায়ুর জোগান বাড়ে ও প্রচুর বৃষ্টি হয়।
পশ্চিমবঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত হওয়ার প্রধান কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।
পশ্চিমবঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চলের প্রধানত সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত প্রকৃতির। উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি অধিক লবণযুক্ত বলে চাষের উপযোগী নয়। এখানে ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। এখানকার মাটি লবণাক্ত হওয়ার প্রধান কারণ হল –
- সমুদ্রের লোনা জলের অনুপ্রবেশ।
- এই বদ্বীপ অঞ্চলের উচ্চতা খুব কম, প্রায় 3-5 মিটার।
- অঞ্চলটি অসংখ্য খাঁড়ি, শাখানদী, বালুচরযুক্ত হওয়ায় জোয়ারের সময় অঞ্চলটি প্লাবিত হয় এবং ভাটার সময় জল সরে গেলে নবীন পলিমাটিযুক্ত দ্বীপ ও চরাগুলিতে প্রচুর লবণ কণার সঞ্চয় হতে দেখা যায়। বহু বছর ধরে মাটিতে এভাবে লবণ কণা সঞ্চয়ের ফলে এখানকার মাটি লবণাক্ত হয়ে গেছে।
পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের লবণাক্ত মাটিতে কাদার প্রাধান্য থাকে, কিন্তু দিঘা-কাঁথি উপকূলে বালির পরিমাণ বেশি হয়। একই লবণাক্ততা সত্ত্বেও এই দুই অঞ্চলের মাটির গঠনে পার্থক্যের ভৌগোলিক কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।
পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত প্রকৃতির। এই লবণাক্ত মাটিতে কাদার ভাগ বেশি, কারণ –
- নদীবাহিত কাদা ও পলির সঞ্চয় – সুন্দরবন অঞ্চলে গঙ্গা ও তার উপনদীগুলি থেকে বাহিত প্রচুর পরিমাণে পলি ও কর্দমের সঞ্চয় হয়, ফলে ওই লবণাক্ত মাটিতে কাদার ভাগ বেশি দেখা যায়।
- সামুদ্রিক কর্দমের সঞ্চয় – জোয়ারের সময় খাঁড়িগুলি জলপূর্ণ হয়ে পড়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক কর্দম এই অঞ্চলের নীচু ভাগে জমা হয় এবং মাটি কর্দমময় হয়ে পড়ে।
আবার অন্যদিকে দিঘা ও কাঁথি উপকূল অঞ্চলের মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি, কারণ –
- ক্ষয়কার্যের ফলে উপকূলের গঠন – দিঘা ও কাঁথি উপকূলে সমুদ্র তরঙ্গের ফলে উপকূল গঠিত হয় বলে জলের টানে মাটির কর্দম কণা জলে অপসৃত হওয়ায় মাটি বালিময় হয়ে পড়েছে।
- বালুকণার সঞ্চয় – সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা আনীত বালুকণা সঞ্চিত হয়ে উপকূল গঠিত হয় বলে মাটি বালিময় হয়েছে।
সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে ওঠার প্রাকৃতিক কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।
ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে ওঠার জন্য কিছু প্রাকৃতিক পরিবেশ দরকার, যেমন – পর্যাপ্ত উষ্ণতা, প্রচুর বৃষ্টিপাত, লবণাক্ত মৃত্তিকা, জোয়ার-ভাটার জল ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনেই একমাত্র এই উপযুক্ত পরিবেশগুলি পাওয়া যায়।
ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে ওঠার কারণ –
- সুন্দরবনের গড় উষ্ণতা গ্রীষ্মকালে 29°C-30°C ও শীতকালে 20°C-21°C।
- এই অঞ্চলে বছরে গড় বৃষ্টিপাত প্রায় 160-200 সেমি।
- সমুদ্রের নিকটবর্তী বলে এখানকার মাটি লবণাক্ত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদগুলি লবণাক্ত মাটিতে শ্বাসমূল, ঠেসমূলের সাহায্যে বেঁচে থাকতে পারে।
- বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থান করার জন্য এখানকার নদীগুলিতে জোয়ার-ভাটা হয়।
এই কারণগুলির জন্য সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ বনভূমি গড়ে উঠেছে।
Class 9 Geography All Chapter Notes
আমরা আমাদের আর্টিকেলে নবম শ্রেণীর ভূগোলের অষ্টম অধ্যায় ‘পশ্চিমবঙ্গ (প্রাকৃতিক পরিবেশ)’ এর ভৌগোলিক কারণ ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রশ্নগুলো নবম শ্রেণীর ভূগোল পরীক্ষার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নগুলি নবম শ্রেণীর পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় প্রায় দেখা যায়। আশা করি এই আর্টিকেলটি আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অসুবিধা হলে, আপনারা আমাদের সাথে টেলিগ্রামে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাছাড়া নিচে আমাদের এই পোস্টটি আপনার প্রিয়জনের সাথে শেয়ার করুন, যাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে। ধন্যবাদ।



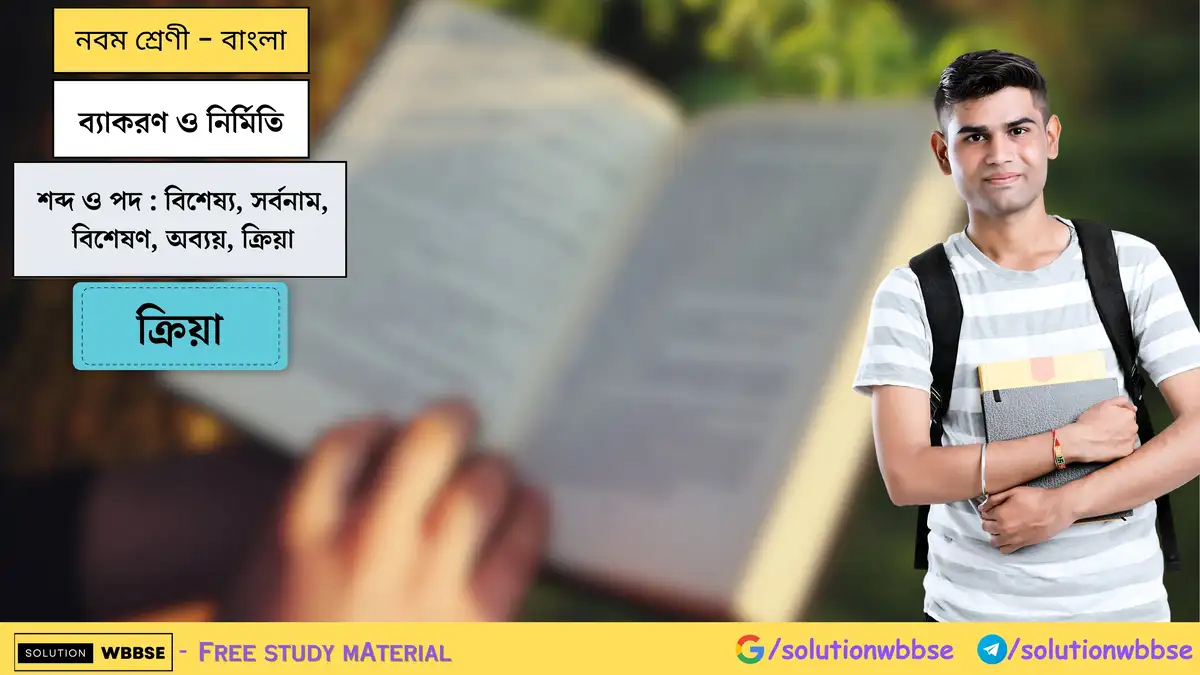
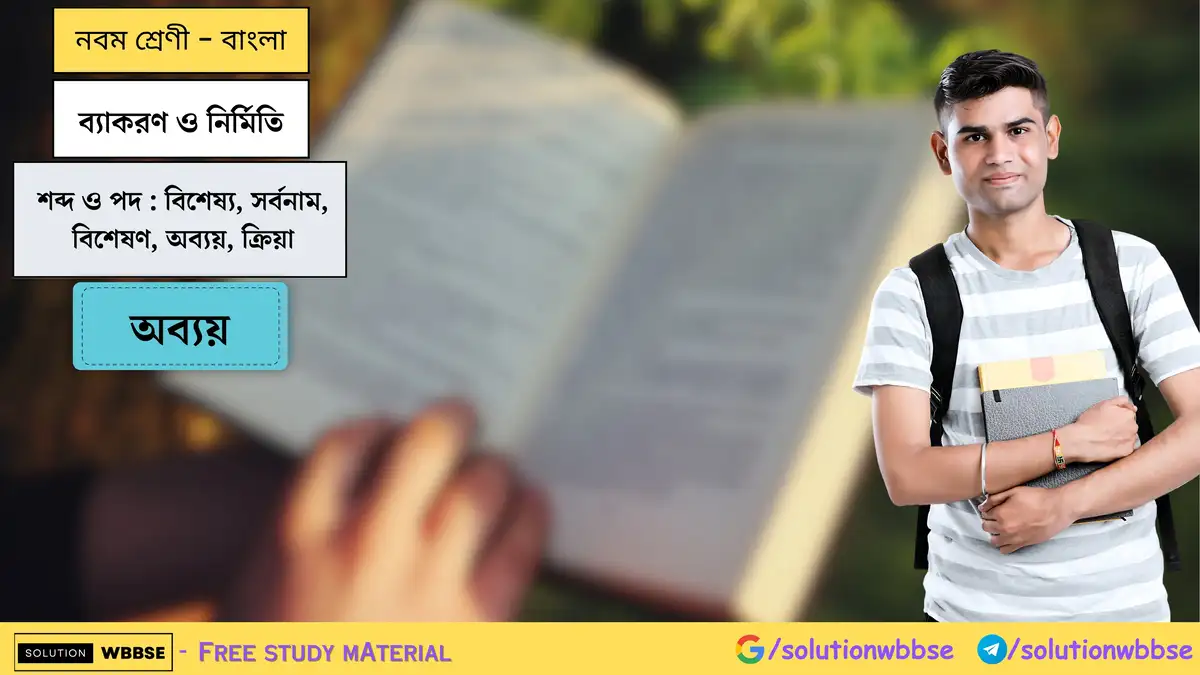

মন্তব্য করুন